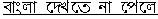২১ জৈষ্ঠ্য ১৩৩৮, রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালাদেবীকে লিখছেন,—
‘বৈষ্ণব যেখানে বোষ্টম নয় সেখানে আমিও বৈষ্ণব, খৃষ্টান যেখানে খেষ্টান্ নয় সেখানে আমিও খৃষ্টান’।
হেমন্তবালা তাঁর পুজো আচ্চা বিশ্বাস দিয়ে ঘেরা জগৎটির পক্ষ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে এবং অনুপম রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনটাকে ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিগুলিতে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত এবং সস্নেহ আন্তরিকতায় ধরা দিয়েছেন। খুব সহজ করে নিজের দর্শনটিকে প্রকাশ করেছেন। কেন তিনি কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখেননি তা এমন সরল করে বোধহয় আর কোথাও বলেননি। পত্রলেখিকার প্রতি তাঁর কোনো আক্রমণ নেই, শুধু যুক্তি দিয়ে সত্যবোধটিকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। প্রাসঙ্গিক বোধে আরো কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধার করছি।
‘... যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না। ... দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ-সামর্থ্য সময় প্রীতি ভক্তি সবই দিচ্চে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্চে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোনো দেশেই নেই, এর প্রধান কারণ এই যে, এ দেশে হতভাগা মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা নিচ্চেন হরণ করে। ...’
৩১ জৈষ্ঠ ১৩৩৮
‘আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুন্ঠেও নয়,—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে—সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে—যে দেবতা স্বর্গের তাঁর মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়।’‘ঐ’
‘আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার-করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই, বোঝে না; নিজের দেশ আরো কম বোঝে। অতএব আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না। আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশ স্বজাতির উপরে। আমার এই অপরাধে যদি আমি স্বদেশের লোকের অস্পৃশ্য, সনাতনীদের চক্ষুশূল হই তবে এই আঘাত আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে’।১২ আষাঢ় ১৩৩৮
এক সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল হেমেন্তবালাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলির থেকে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত উদ্ধার করে প্রকাশ করবেন কিন্তু পরে সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। তাঁর এই মতবদলেরও একটা সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল অবশ্যই। তাঁর মনে হয়েছিল চিঠিগুলির মধ্যে যদি প্রাণশক্তি থাকে তবে আপনি আবরণ ভেদ করে আবিষ্কৃত হবে। তাঁর ধারণা পুরোপুরি ঠিক ছিল। আজ বারবার রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধকে উপলব্ধি করতে আমরা চিঠিগুলির কাছে ফিরে ফিরে যাই। আবিষ্কার করার আনন্দ পাই।
তবে ধর্মবোধের এই স্বচ্ছতায় পৌঁছতে তাঁর একটি নিজস্ব যাত্রাপথ আছে। জীবনের ধাপগুলি ভাঙতে ভাঙতে তিনি পূজামন্দিরের বাইরে যাত্রা করেছেন। সাধারণত আমাদের দেশে মানুষ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্প্রদায়সীমার মধ্যে আরো নিবিষ্ট হয়, চারপাশের ঘেরাটোপ আরো ঘন হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটি ঘটেছে। তিনি একটি একটি করে সম্প্রদায় বন্ধনের সংস্কার বেড়িগুলি মোচন করতে করতে পথ হেঁটেছেন। আমরা এই যাত্রাটিকে একটু দেখতে চাইব। বাইশে শ্রাবণে তাঁর এই সাধনচর্যাটি ফিরে দেখার চেষ্টা করি।
জন্মসূত্রেই একটি মুক্তি জড়িয়ে ছিল তাঁকে, অন্য অর্থে আপাত বন্ধনও বলা যায়। সমাজ চিহ্নিত করেছিল যশোরের কুশারী বংশকে পীরালি ব্রাহ্মণ বলে। সাহস করে পীরালি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করেছিলেন ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ। সেই গল্প অনেকেরই জানা। সমাজের প্রত্যাখ্যান গায়ে জড়িয়েই বিস্তার ঘটল শাখাটির। যশোর থেকে কলকাতা—কুশারী থেকে ঠাকুর। সাধারণ অবস্থা থেকে ধনসমৃদ্ধি, পীরালি ছাপ তো ঘুচল না। এমনকি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পরেও নয়। বিবাহ ইত্যাদিতে যথেষ্ট অসুবিধা হত। এই ইতিহাস তো গোড়া থেকেই সংবেদনশীল মনে জাতপাতের সংকীর্ণতা নিয়ে বিরুদ্ধতা জাগাবে এটা অনুমান করা যায়। শুধু জাতপাত নয়, গোড়া থেকেই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা বিরূপতা লক্ষ্য করি।
১২৯২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি ব্যঙ্গকৌতুকময় রচনার কিছুটা উদ্ধার করছি। ‘ডেঞে পিঁপড়ের মন্তব্য’ লেখাটিতে শুধু জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা নয়, ঔপনিবেশিকতার আসল চেহারাটিও যেন খুলে দেখাতে চাইছেন তরুণ লেখক।
‘... ওরা সব পিঁপড়ে, যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে পিপীলিকা। আমি হচ্ছি ডেঞে, সমুচ্চ ডাঁইবংশসম্ভূত, ঐ পিঁপড়েগুলোকে দেখলে আমার অত্যন্ত হাসি আসে। ... পিঁপড়েদের দেখে আমার অত্যন্ত মায়া হয়, ওদের উপকার করবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত বলবতী হয়ে ওঠে। এমন কি আমার ইচ্ছা করে, সভ্য ডেঞে সমাজ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে, দলকে-দল ডেঞে ভ্রাতৃবৃন্দকে নিয়ে পিঁপড়েদের বাসার মধ্যে বাস স্থাপন করি এবং পিঁপড়ে সংস্কারকার্যে ব্রতী হই— ... তারা উন্নতি চায় না—তারা নিজের শর্করা নিজে খেতে এবং নিজের বিবরে নিজে বাস করতে চায়, তার কারণ তারা পিঁপড়ে, নিতান্তই পিঁপড়ে। কিন্তু আমরা যখন ডেঞে তখন আমরা তাদের উন্নতি দেবই, এবং তাদের শর্করা আমরা খাব ও তাদের বিবরে আমরা বাস করব—আমরা এবং আমাদের ভাইপো, ভাগ্নে, ভাইঝি ও শ্যালকবৃন্দ।’
এই ছবিতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের রূপক আছে এমনটা মনে হয়। সেই সঙ্গে এটাও ভুলতে পারি না যে চিরকাল ওপর থেকে করুণাকণা বর্ষণ করে ‘দরিদ্রনারায়ণের’ সেবার প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ‘লোকহিত’ কোমর বেঁধে অন্ত্যজ ও নিম্নবর্গের জন্য হিত সাধন নয়। পথটা একটু কঠিন তাই আমাদের তেমন পছন্দ হয় না, বারবার তিনি ভবিষ্যতে বলবেন আত্মশক্তির জাগরণের কথা।
গোটা জীবন জুড়েই নানা বিতর্কে জড়াতে হয়েছে তাঁকে, পরিপার্শ্বের চাপ আজকের থেকে অনেক বেশি ছিল এটা মাথায় রেখে তেমনি একটি বিতর্কের উল্লেখ করছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ আচার্যের বসা উচিত কিনা এই নিয়ে বিরোধটি পাকিয়ে উঠেছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তখন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক। সেই পত্রিকায় বিরোধটি বিধৃত হয়ে আছে।
রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন,
‘শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে কোন এক বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীগ্রহণ করিতে দেখিয়া আদি সমাজের একজন উপাসক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। ... বেদীগ্রহণ সম্বন্ধে একদিন ব্রাহ্মসমাজে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানি। সে সম্বন্ধে পিতৃদেবের পত্র পাঠ করিলেই জানা যাইবে যে, অব্রাহ্মণ বা উপবীতত্যাগী আচার্য্য বেদী গ্রহণের অধিকারী নহেন এরূপ প্রস্তাব তাঁহার ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ, উপবীতধারী বা উপবীতত্যাগী সকলেই যোগ্যতা অনুসারে বেদীর কার্য্য করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে অপরপক্ষে যে অনৌদার্য্য ছিল তাহা তাঁহার ছিল না।’
এই প্রসঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা সামগ্রিক ভাবে সমাজ সম্পর্কে তাঁর সুগভীর ও সর্বার্থে মানবিক চিন্তনকে তুলে ধরে। এখন আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা এবং নিম্নবর্গের ইতিহাসের রূপকাররা ‘Us’ আর ‘Them’ এই দুটি ধারণার কথা বারবার বলছেন। সব সময়ই রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে-প্রতিষ্ঠানে এই ‘অপর’ এর ভেদচিহ্ন আমাদের বিযুক্ত করছে। রবীন্দ্রনাথ একশো বছরেরও পূর্বে কী বলেছিলেন একটু দেখা যাক,
‘ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মঙ্গলের ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে পদে পদে “আমরা” ও “তোমরা” বাঁধের দ্বারা বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মকে ও সাম্প্রদায়িক জয়পরাজয়ের আস্ফালনের সামগ্রী করিয়া অকারণে যাঁহারা কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করিয়া তোলেন তাঁহারা কেবলমাত্র ব্রাহ্ম নামটাকে গ্রহণ করিয়া উপবীতধারী অথবা অন্য কাহারও চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের ব্রাহ্ম নামই উপবীতের অপেক্ষা অনেক প্রবল ভেদচিহ্ন, এবং তাহার অহঙ্কারও বড় সামান্য নহে। অহঙ্কারের দ্বারা অহঙ্কারকে মথিত করিয়া তোলা হয়, সেই অহঙ্কারের বাধাই সকলের চেয়ে বড় বাধা এই কথা মনে নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক চাপল্যের মাঝখানে অবিচলিত থাকিয়া আমরা যেন এই প্রার্থনাকেই চিত্তের মধ্যে বিনম্রভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি যেএর পরেও কটুবাক্য বর্ষণ বন্ধ হয়নি। ইঙ্গিত ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের থেকে রবীন্দ্রনাথ পদত্যাগ করুন। শরচ্চন্দ্র ঘোষ এতদূর পর্যন্ত বলেছেন তাঁকে, ‘আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রক্ষা করা আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হইলে আপনি প্রকাশ্য ভাবে সাধারণসমাজে মিলিত হউন, আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাবকে পরিবর্তন করিবার আপনার অধিকার নাই।'
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তুঃ।'
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হতে চাননি কোনোদিন। তবে পরবর্তীকালে সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ যখন জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্মানিক সভ্য করা চেষ্টা করেন তখন প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। এমনকি ভোটাভুটি পর্যন্ত গড়ায় ব্যাপারটি এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বেশি ভোট পড়ে মুখ বাঁচলেও বিপক্ষে ভোট কম পড়েনি। কেন তাঁর দিকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন চিরকালই একটু কম থাকতেন, তত্ত্ববোধিনীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অব্রাহ্মণ আচার্য সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তিবিস্তার করেছেন তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—
‘আমি বরঞ্চ সমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে রাজি আছি কিন্তু সমাজকে অশ্রদ্ধা করিতে সম্মত নহি। অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইলে সমাজ অশ্রদ্ধা করিবে এ কথাকে শ্রদ্ধা করিলে সমাজকে অশ্রদ্ধা করা হয়। যুক্তিহীন অর্থহীন আচারই যে হিন্দু সমাজের প্রকৃতিগত এ কথাকে আমি শেষ পর্য্যন্তই অস্বীকার করিব। ... কোনমতে ব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া দিলেই অদ্যকার হিন্দুসমাজ যদি আমাকে শ্রদ্ধা করে তবে সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া মানবসমাজের চিরকালীন সত্যধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিতে পারিব না।'
ঐ সময়ই তত্ত্ববোধিনীতে আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মদর্শন বিশেষ করে লোকায়ত সাধকদের নিয়ে। অজিতকুমার চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন কবীরের প্রসঙ্গে মুসলমান ইতিহাসের সুফীধর্ম ও দর্শন সঞ্জাত কবিতাগুলি আলোচনা প্রয়োজন, আমাদের জানা উচিত মুসলমান আগমনে কেবল যে হিন্দুমন্দিরের দেবদেবী ধ্বংস হয়েছিল তা নয়, সুফী ভক্তিবাদ ও তার সাহিত্যের সঙ্গেও ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয় ঘটে।
‘এই একেশ্বরবাদের কথা তো ভারতবর্ষে নূতন নহে, সুতরাং এই সময়ে মুসলমানের আঘাতে ভারতবর্ষের চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, মুসলমান যে ধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে তাহা আমাদেরি জিনিস, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের বিরোধ নাই। কিন্তু মুসলমান যে এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছে, তাহা যে নিরাকার ও রূপরসবর্জিত তাহা নহে,—সকল আকারকে সকল রসকে পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রকাশ। কিছুই তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই; তিনি সকল ঘট পূর্ণ করিয়াও সকলকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে নানাস্থানে যে ধর্ম্মের আন্দোলন জাগিল তাহার মর্ম্মগত কথা ইহাই। বাংলায়, পঞ্জাবে, উত্তর ভারতে ও দক্ষিণে, চৈতন্য, নানক, কবীর, দাদূ, রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই ভাবের বন্যায় সমস্ত দেশকে ভাসাইয়া দিলেন, হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাহাদের দলের মধ্যে সমান স্থান লাভ করিল।'[কবীর / অজিতকুমার চক্রবর্তী]
তত্ত্ববোধিনী কী বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে তা এইসব লেখালেখি থেকে স্পষ্ট। এ সবই একলা চলার ইতিকথা। আরো কিছুটা পিছিয়ে এমন একটি একলা হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন অশোক সেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ ‘রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ’-এ। ‘ইংরাজ ও ভারতবাসী’ প্রবন্ধটি প্রথম বক্তৃতাকারে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির আসনে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে সম্রাট আকবরের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মনির্বিশেষে প্রজাপালনের প্রশংসা ছিল। সকল ধর্মমতের মধ্যে বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্য বিধানে আকবরের ভূমিকাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে ইংরেজ শাসনে ঐক্যের প্রাকার উঠলেও তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ‘আকবরের নামে দেশের লোক এত নাচে কেন?’ তাঁর মতে আকবরের চেয়ে বেশি হিন্দুর অনিষ্ট কোনো মোগল সম্রাট করেননি, ‘তিনি বন্ধুত্বচ্ছলেই হিন্দুর সর্বাপেক্ষা গুরুতর শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন।’
সকলেই জানেন বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। সক্রিয় রাজনীতিতে পরিপূর্ণ ভাবে অংশগ্রহণ করে বক্তৃতা দিয়েছেন, গান বেঁধে গেয়েছেন, মিছিলে পা মিলিয়েছেন। কিন্তু একটা সময় তিনি সরে গেলেন। কেন তাঁর এই সরে যাওয়া তা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা আছে। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসটি আমাদের পথ দেখায় অবশ্যই। তাঁর অনুভবে ধরা পড়েছিল আন্দোলনের অন্তর্গত ছিদ্রগুলি। দেশের সমস্ত সম্প্রদায় মিলতে পারছে না, বরং আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছে ভাঙনের জীবাণু। এক ঝোঁকা হয়ে পড়ছে ব্যাপারটা, বয়কট নিয়ে জবরদস্তি ছাড়াও নেতাদের অনেকেই বড়ো করে তুলছেন গীতা, শিবাজী উৎসব, ভবানীপূজা, আনন্দমঠ, শক্তিরূপিণী কালিকা ইত্যাদি হিন্দু ভাবাদর্শের নানা দিক যা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে জাগিয়ে তুলছে সংশয়, সন্দেহ, বাড়ছে বিচ্ছিন্নতা। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে অতিশয়পন্থা, ‘গুলি বন্দুক বোমার আগুনে’ অন্য বাঁক নিচ্ছে আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের আত্মত্যাগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু কদাপি তিনি সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেননি। জোরজুলুম, জবরদস্তিকে তিনি বরাবর ঘৃণা করেছেন। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে সন্দীপ আর তার দলবলের জোর করে দোকান লুট, দোকানের বিদেশি কাপড় কেড়ে নিয়ে পোড়ানো মনে পড়তে পারে। মুসলমান সম্প্রদায় এবং নিম্নবর্গের হিন্দুদের সঙ্গেও এক সম্পর্ক-ফাটল তৈরি হয়েছিল ঐ সময়। পরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ধারণা ভুল ছিল না একেবারেই। সেবারে আটকানো গেলেও ১৯৪৭-এ দেশভাগ আর আটকানো গেল না।
১৯২১-সালে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা তাঁর ‘সত্যের আহ্বান’ প্রবন্ধটি পড়লে আজ তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি আমাদের একই সঙ্গে বিস্মিত ও বিষন্ন করে। কতো ভাবেই না তিনি আমাদের সাবধান করতে চেয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু এ-কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি, ‘যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশে, যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে।’ তিনি তো তখন জানতেন না ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি বিহারের ভয়ংকর ভূমিকম্পকে গান্ধী অস্পৃশ্যতারূপ পাপের শাস্তি বলে ঘোষণা করবেন আর এই অবৈজ্ঞানিক ‘উক্তি’র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে তাঁকে।
হিন্দু মুসলমানের মিলন কোনো বাইরের স্লোগান দিয়ে ঘটানো যেতে পারে এ কথা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ওটা তাঁর মতে সুবিধাবাদী হাত মেলানো—তাই টিঁকবার নয়। চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা দুই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সহজ নয়। কিন্তু দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়, আর তার জন্য কী প্রয়োজন তা তিনি বারবার বলেছেন। রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় কখনো হাত মিললেও ভেতরে রন্ধ্র রয়ে গেছে। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘শনি’। ‘হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয়পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না।’ একজন ইঙ্গভাবাপন্ন ভদ্রলোকের প্রসঙ্গ তুলেছেন তিনি, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর ছিল খুব লোভ। সবই বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতেন শুধু গ্রেট-ইস্টারনের ভাতটা বাদ দিয়ে। কারণ ‘মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না।’ এই সংস্কারের জন্যই মুসলমানের সঙ্গে মেলাও তাঁর পক্ষে অসাধ্য। হিন্দুমুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বর্বর বুশম্যানের প্রসঙ্গ এনেছেন, পরকে দেখবামাত্র বুশম্যান তাকে বিষবাণ মারে।
‘হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারিদিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।’
এই আচার ও বাহ্যবিধান সর্বস্বতাকে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন ধর্মতন্ত্র, মানবের নিত্যধর্মের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই। ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই পালটাতে হবে—এ ছাড়া কোনো শর্টকাট নেই। এককালে দুই সম্প্রদায়ে একরকমের মিল ছিল। তার মূলে মধ্যযুগীয় সন্তদের অবদান কম ছিল না। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা কাছাকাছি ছিলাম। কিন্তু সেই সহজ ধর্মবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্গত হয়ে আমরা ধর্মের অভিমান আরো বাড়িয়ে তুলেছি। একেবারে টায়ে টায়ে তুলনা দিয়ে তিনি বলেছেন হিন্দুরা মসজিদের সামনে ঠাকুর নেবার সময় ঢাকে জোরে কাঠি দিয়েছে, মুসলমানরা কোর্বানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধাই দুদলের প্রেরণা। এই অভিশাপ থেকে উদ্ধার পাবার পথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্টভাষায় লিখে গেছেন। তবে সে পথ এক ভিন্ন যাপনপ্রণালী—সংস্কার মুক্তির দীক্ষা।
‘নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গে ও সাক্ষাৎ আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়।’
ভাবতে খুব অবাক লাগে ১৯৩১-সালে তিনি প্রখর ভবিষ্যচিন্তায় ধরে ফেলেছিলেন আরো কঠিন সময় আসছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অনৈক্য ঘোচাতেই হবে, মানুষে মানুষে ভেদচিহ্ন মোছার প্রয়াস নিতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা যে আসন্ন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু সে কেমন স্বাধীনতা হবে তা নিয়ে অন্তরে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না।
‘সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেই খানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।’
১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হয়েছেন তাই সমুদ্রহৃদয় যন্ত্রণামথিত করে তাঁকে দেখতে হয়নি কীভাবে রক্তপিচ্ছিল পথে ধ্বংস হত্যা ভ্রাতৃবিরোধের চুনকালি মেখে তাঁর খণ্ডিত দেশের মানুষ জগৎসভায় মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। মুণ্ড হেঁট হলেও হাতে কিন্তু অস্ত্র আছে, অর্জুনবিষাদ যোগ ঘটেনি।
আমাদের সমাজের বদ্ধমূল বর্ণাশ্রম ও জাতপাত নিয়ে বহুবার বহু লেখায় তিনি মতপ্রকাশ করেছেন। ‘হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান’ কবিতাটি যেন চিরকাল তাঁর মর্মে গেঁথে ছিল। কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলির মধ্যেও তিনি সন্ধিৎসু আর্তিতে খুঁজে ফিরেছেন মিলনের পথ। ‘গোরা’ উপন্যাসটির কথা বিশেষভাবে সকলের মনে পড়বে। বিখ্যাত কন্নড কথাসাহিত্যিক ইউ, আর, অনন্তমূর্তি একবার শঙ্খ ঘোষকে বলেছিলেন ভারতের সর্বত্র ‘গোরা’ উপন্যাস নিয়ে আলোচনাচক্র করা উচিত। ভেদবুদ্ধির বিনাশ-ওষধি আছে ওই উপন্যাসে এই ধারণা ছিল তাঁর। চরঘোষপুরে গোরার অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত বহু আলোচিত। অন্যায়কারী ব্রাহ্মণের বাড়িতে জলপান করতে যাবার পথে বাঁক নিয়ে গোরা ফিরে এল সেই নাপিতের বাড়িতেই, যারা স্বামী স্ত্রী বিপন্ন মুসলমান বালক তমিজকে আশ্রয় দিয়েছে, পালন করছে সন্তানস্নেহে।
এই প্রবন্ধে আমরা একটু দেখে নিতে চাই জাতিভেদের তত্ত্বটি তিনি কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পাশ্চাত্যের শ্রোতার কাছে বলবার সময় তিনি জানিয়েছিলেন মানুষের মধ্যে যে জাতিগত বৈচিত্র্য আছে তা বহুজাতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষ অনুভব করেছিল। এই অনুভূতি মিথ্যা নয়, কিন্তু ‘... she failed to realise was that in human beings differences are not like the physical barriers of mountains, fixed for ever—they are fluid with life's flow, they are changing their courses and their shapes and volume. Therefore in her caste regulations India recognised differences, but not the mutability which is the law of life.’
ভারতবর্ষ একধরনের অচল অটল জগদ্দল সীমানা-টানা সমাজ তৈরি করে নেতিবাচক শান্তি ও শৃঙ্খলা তৈরি করেছিল। ‘world-game of infinite permutations and combinations’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন এই বৈশ্বিক পরিবর্তনের অনন্ত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছে ভারতবর্ষ।
‘She treated life in all truth where it is manifold, but insulted it where it is ever moving. Therefore Life departed from her social system and in its place she is worshipping with all ceremony the magnificent cage of countless compartments that she has manufactured.’
এই সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ কীভাবে অক্ষত ছিল, কীভাবে গড়ে উঠেছে শিল্প-বাণিজ্য, কীভাবে নিশ্চিত হয়েছে জীবিকাসমূহ তার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে দেখিয়েছেন কীভাবে এক একটি সওদাগরি বা একএকটি পেশাকে ভারতবর্ষে একএকটি বর্ণের উপর বা তার উপবিভাগ জাতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে প্রতিযোগিতা কমে গেছে, ঈর্ষা বা ঘৃণা, আপাতদৃষ্টিতে কমেছে কিন্তু গোটা প্রক্রিয়াটি যেহেতু বংশগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, ভারতবর্ষ এক অচলায়তনে পরিণত হয়েছে।
“... India laid all her emphasis upon the law of heredity, ignoring the law of mutation, and thus gradually reduced arts into crafts and genius into skill’
কিন্তু পাশাপাশি পশ্চিমী ব্যবস্থার অসাম্য ও অশান্তির কথাও তিনি সমানভাবে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষ সাম্যময় সাফল্যে পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু পাশ্চাত্যে ভেদাভেদ, অসাম্য কম ভয়ানক নয়।
অর্থাৎ সেখানে ভিন্নতাকে স্বীকার করাই হয় না।‘... the West, being more favourably situated as to homogeneity of races, has never given her attention to this problem, and whenever confronted with it she has tried to make it easy by ignoring it altogether.’
হ্যামারগ্রেনকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভোলেননি। সুইডিশ এই ভারতপ্রেমিক রামমোহন রায়ের রচনা পড়ে এই দেশকে ভালোবেসেছিলেন। বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন মানুষটি। মৃত্যুর পর তাঁকে যেন দাহ করা হয় এই ছিল তাঁর অনুরোধ। কিন্তু কার্যকালে হিন্দুসমাজ অভূতপূর্ব সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছিল। ‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পটি হিন্দুসমাজের এই অমানবিক আচরণের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—‘জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়’, সমূল সংহার ও বিপজ্জনক ভয়াবহ অন্যজাত–অসহিষ্ণুতা কি অক্ষরে অক্ষরে দেখিয়ে দেয়নি ‘সুসভ্য’ পাশ্চাত্যের জাতিবর্ণভেদ সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টি কতোখানি সত্যসন্ধ?
গ্রন্থপঞ্জি :
১. রবিজীবনী : বিভিন্ন খণ্ড – প্রশান্ত কুমার পাল – আনন্দ ২. রবীন্দ্র রচনাবলী – চতুর্বিংশ খণ্ড -- বিশ্বভারতী ৩. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংগ্রহ (১৩১৮) – সম্পাদনা : বারিদবরণ ঘোষ – বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৪. চিঠিপত্র – নবম খণ্ড – বিশ্বভারতী ৫. Nationalism – Rabindranath Tagore – Penguin India ৬. রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ – অশোক সেন – বিশ্বভারতী ৭. আরেক রকম পত্রিকা—সম্পাদনা : কালীকৃষ্ণ গুহ – সমাজচর্চা ট্রাস্ট
২২শে শ্রাবণ ২০১৫ উপলক্ষ্যে লিখিত; পরবাসে প্রকাশিত সেপ্টেম্বর ২০১৫