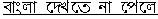মৈত্রেয়ী দেবীকে একবার বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ‘দেখো রবিঠাকুর গান মন্দ লেখে না। একরকম চলনসই তো বলতে হবে...কম গান লিখেছি? বাংলাদেশকে গানে ভাসিয়ে দিয়েছি।... আমাকে ভুলতে পার, আমার গান ভুলবে কেমন করে?’(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)
রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন, সেই দেশ নিশ্চয় শুধু মাটি দিয়ে নয়, মানুষ দিয়েও গড়া। আর সেই ‘বাংলাদেশ’-এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যাকে নিশ্চয় ঠাকুরবাড়ি এবং শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখার কথা ভাবা চলে না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই শেষ বয়সে তাঁর গানের সর্বত্রগামিতার সম্ভাবনা অনুভব করেছিলেন। এই সম্ভাবনাকে স্বাগত জানাবার মত উদারতার অভাব তাঁর কোন দিনই ছিল না, তিনি দিলীপকুমার রায় আর সাহানা দেবীর মত শিল্পীকে সুরের মূল কাঠামো বজায় রেখে এক্সপ্রেশনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, নিজের ‘শেষ খেয়া’ (দিনের শেষে ঘুমের দেশে) কবিতায় পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরারোপ সানন্দে অনুমোদন করেছিলেন—যদিও তাঁর মৃত্যুর পর ‘গীতবিতান’-এর পরিমার্জিত সংস্করণে সেটিকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়নি।
শিল্পীর প্রকাশভঙ্গির স্বাধীনতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে রাখা দরকার, ‘সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনে কম বেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাত আছে এ কথাটি ভুলো না।’ (সংগীত চিন্তা) এই স্বাধীনতা তিনি দিয়েছিলেন অ-বাংলাভাষী গায়ক কুন্দনলাল সায়গলকেও। সায়গলের রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাল করে শুনলে মনোযোগী শ্রোতা বুঝতে পারবেন, দু-একটি ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ ‘আমি তোমায় যত’ গানটির কথা বলা যেতে পারে) তাঁর গায়নে স্বরলিপি-নির্দিষ্ট স্বর সামান্য এদিক-ওদিক হয়েছে, কিন্তু তাতে মূল সুরের বা প্রকাশভঙ্গির বিরাট কিছু ক্ষতি হয়ে যায়নি। সে-কালে রেকর্ড বের করতেও তেমন সমস্যা হয়েছিল বলে জানা যায় না। অথচ বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতির প্রতাপ বাড়ল যে সময় থেকে, তারপর - এরকমই কিছু সামান্য শৈল্পিক স্বাধীনতা নিতে গিয়ে, প্রকাশভঙ্গি, লয় এবং যন্ত্রানুষঙ্গে কিঞ্চিৎ পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাসকে কতখানি যন্ত্রণায়, অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়েছিল—সঙ্গীতপ্রেমী বাঙালিমাত্রেই সে ইতিহাসের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। অবশ্য তিনি প্রতিবাদের হাতিয়ার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকেই, স্বপক্ষ সমর্থনে তাঁরই উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। ‘রুদ্ধসঙ্গীত’-এর পাতায় পাতায় আছে সেই নান্দনিক প্রতিস্পর্ধার বিবরণ।
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মূর্ছনা আত্মস্থ করলেও তা যে ঐতিহ্যের পরিপন্থী হয় না, সে পথ রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন, তাই তাঁর গানে কয়েকটি ‘নিয়ামক’ বাদ্যযন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া গানের স্বাভাবিক গতিকে নষ্ট করার জবরদস্তি মাত্র। ‘মাতামহীর আমলের জীর্ণ কাঁথা’ জড়িয়ে গানকে বাঁচিয়ে রাখা যায়—এ জিনিস স্বয়ং কবিই ভাবতে পারেননি—এই ছিল দেবব্রতর বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করেই এক্সপ্রেশনের স্বাধীনতার প্রশ্নে বরাবর বিতর্কিত, বিদ্রোহী থেকেছিলেন তিনি—যাঁর মন্দ্রসপ্তক-আধারিত গায়নে ‘ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি’র অনুভূতি, ‘পুবসাগরের পার হতে’ ভেসে আসা বর্ষার ঝাপটা আর ‘কেন চেয়ে আছ গো মা’র বেদন-অভিব্যক্তি আজও অমলিন।
এই এক্সপ্রেশনের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বরলিপি-অনুশাসনের প্রশ্নও। বিষয়টি একটু পরিষ্কার করা দরকার। স্বরলিপি শিকেয় তুলে যেমন খুশি গেয়ে যাওয়া অবশ্যই অভিপ্রেত নয়, আবার নিতান্ত প্রাণহীন ভাবে কেবল স্বরলিপি ধরে ধরে গলা মেলালে গানের ভাবরূপ অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্র-শতবর্ষে সাহানা দেবী একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, স্বরলিপির মধ্যেকার যে সুর, তাকে অনুধাবন করতে পারলে তবেই গায়ন সার্থক হয়। স্বরলিপিকে অগ্রাহ্য করার কথা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না। যা বলা হচ্ছে, তা হল সুরের অন্তর্নিহিত ভাব অনুভব করে, মেধাবী শিল্পীর অভিব্যক্তি-ক্ষেত্রে নিজস্বতা প্রকাশের অধিকার। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সঙ্গীত চিন্তায় রাগরাগিণীর চুলচেরা স্বরসঙ্গতির কাছে ‘অন্ধ দাস্যবৃত্তি’র চেয়ে ভাবকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, “যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা হয়, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন—আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমন কী ঘুষ খাইয়াছি যে তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব? … বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ,… ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ।”
এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে পরবর্তী কালের এমনই ‘আর একজন ভাবুক’ শিল্পীর বক্তব্য—“রবীন্দ্রনাথ সায়গলকে রেকর্ড করার যে-স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাতে মনে হয় আজ উনি বেঁচে থাকলে তেমন-তেমন শিল্পীকে কিছু স্বাধীনতা হয়তো দিতেন। স্বরলিপি নিরেটভাবে ফলো করলে শিল্পীর নিজস্ব কোনও অবদান থাকে না। ওটা একধরনের স্বরলিপি-চর্চাই হয়ে যায়। নিষ্প্রাণ স্বরলিপি-চর্চা দিয়ে কোনও গানকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। স্বরলিপি হচ্ছে একদম আনকোরা শিল্পীকে পথে বেঁধে রাখার জন্য। কিন্তু একজন খুব বড় শিল্পী যদি সামান্য একটু স্বাধীনতা নেন তাতে গানের মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।” বলছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর শুরু এবং শেষের কথাগুলি যেন রবীন্দ্রনাথের মানসিকতারই অনুরণন—“প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।” সাহানা দেবী না হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁর ব্যক্তিগত পত্রালাপে এই স্বাধীনতার অনুমোদন পেয়েছিলেন। কিন্তু হেমন্ত? তাঁর না ছিল সরাসরি রবীন্দ্রসান্নিধ্যের সৌভাগ্য, না ছিল তথাকথিত শান্তিনিকেতনী শিক্ষার ছাপ। আর সঙ্গীত চিন্তা মুখস্থ করে নিশ্চয় তিনি সাক্ষাৎকার দিতে বসেন নি। তা সত্ত্বেও তাঁর নিজস্ব অনুভবের প্রতিটি স্তর রবীন্দ্রভাবনাকে আত্মস্থ করে নেওয়ার অকৃত্রিম দীপ্তিতে উজ্জ্বল।
তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত সংক্রান্ত উপলব্ধির বিস্তারিত আলোচনায় আসার আগে একটু দেখে নি, সৃষ্টির অনন্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ নিজে কতখানি গান ‘শিখে’ছিলেন? তাঁর নিজের জবানিতেই পাই—‘আমার দোষ হচ্ছে—শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি, ঝুলিভর্তি করেছি তা দিয়েই।... বাল্যকালে স্বভাব দোষে আমি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। ... রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যারা অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়েনি—কিন্তু কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।’
এই যদি হয় বাংলার সর্বকালের সেরা গীতস্রষ্টার আত্মবিশ্লেষণ, তাহলে তাঁর গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক রূপকার, যিনি প্রথাগত ‘প্রশিক্ষণ’বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে- কী বলছেন? ‘আমার বিরুদ্ধে রাবীন্দ্রিক মহলের অনেকেরই অভিযোগ এই যে আমি কোনো রবীন্দ্রসংগীতের গুরুর কাছে গান শিখিনি। কিন্তু এর উত্তরে এই কথাই বলব—আত্মপ্রকাশের দুর্বার তাগিদে আমি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে[ই] একাধারে গুরু ও পথদ্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছি। আমার যা কিছু শিক্ষা সাধনা সব তাঁরই কাছে। আমি ক্ল্যাসিকাল গান শিখিনি। কিন্তু ওই যে একটি মানুষকে অধ্যয়ন ও অনুসরণ করে গানের মধ্যে কোথায় কীভাবে ক্ল্যাসিকাল ডিগনিটি আনতে হয় অজানতেই কিছুটা রপ্ত হয়ে গেছে। এটা আমার কোনো সচেতন প্রয়াসজাত বস্তু নয়। আর আমার এই অন্বেষণে আলোকস্তম্ভের মতো পথ দেখিয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতগুলি। ... রবীন্দ্রনাথের গানের ছোটখাটো ইঙ্গিত, পথরেখা ধরে আমি এমন একটা নির্মল আনন্দের রাজ্যে পৌঁছেছি যে কারো কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা আমায় আর দমাতে পারবে না।’
সুরের আগুন বইতে বলা এরকম আপাত-সরল অনেক কথাই তাঁর অন্তরের গভীরতম প্রদেশের রবীন্দ্র অনুধ্যানের ফসল। তাঁর কাছে “রবীন্দ্রসংগীতের মানে কোনো বিশেষ ছাঁদের প্রাণহীন উচ্চারণ নয়। এ হচ্ছে নিভৃতলোকের অতি সুকুমার, অতি পেলব, অস্ফুট অনুভবের মধুর প্রকাশ। এ অনুভব নিজেকে জানান দিতে চায় না বলেই এর প্রকাশভঙ্গিতে একটা সলাজ মধুরতা থাকা দরকার। এই কথাটি মনে না রাখলে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে যাওয়াই একটা পণ্ডশ্রম।”
এই কথা মনে করিয়ে দেয় সঙ্গীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি, “আমার গান আপন মনের গান—তাতে আনন্দ পাই, শুনলে আনন্দ হয়। যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয় … যারা অফিস থেকে আসছে, দূর থেকে শুনতে পেলে এটা তাদের জন্যও ভাল - গান ঘরের মাধুরী পাবার জন্য, বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্য নয়।” রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসারে পঙ্কজ মল্লিকের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে হেমন্ত তো এই কাজটিই করেছেন। সারাদিনের ক্লান্তি, কর্মজীবনের জটিলতা থেকে কি মুক্তি মেলে না, যখন বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজও ইয়ারফোন লাগিয়ে শুনি ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়’ অথবা ‘ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু’র মত গান? তিনি যে সময় গান গেয়েছেন, তাতে ‘বাইরের হাততালি’র কথা না হয় পেশাদারি কারণে, জলসার উদ্যোক্তা আর রেকর্ড কোম্পানির দাবিতে তাঁকে ভাবতে হয়েছিল, কিন্তু গান যখন তাঁর কণ্ঠ থেকে শ্রোতার কানে আসে, তখন শিল্পী ও শ্রোতার সেই নিভৃত প্রাণের সংযোগের চেয়ে বড় কিছু থাকে না। ‘একাকী গায়কের নহে তো গান’- একথাও রবীন্দ্রনাথেরই। তাহলে বলাই যায়, আত্মগত প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে কিন্তু কোন বিরোধ নেই নিরালার অব্যক্ত মাধুরীকে শ্রোতা সাধারণের কাছে পরিবেশন করায় নিবেদিত শিল্পী-সত্তার। যা নিভৃতলোকের, আপনার জিনিস, তাকে বাইরে নিয়ে এসে সার্বিক করে দেওয়াই শিল্প ও শিল্পীর ধর্ম, কিন্তু সে প্রকাশ যেন হয় নান্দনিক, সুন্দর, হৃদয়স্পর্শী, অনুচ্চকিত।
এই অনুচ্চকিত অথচ নান্দনিক, আত্মপ্রত্যয়ী আত্মপ্রকাশ হেমন্তর ব্যক্তিত্ব ও গায়নে বিশেষ একটি মাত্রা যোগ করেছিল। প্রশ্ন উঠতেই পারে, দেবব্রতর মতই তো তিনি শান্তিনিকেতনী বৃত্তের বাইরের মানুষ, তাহলে তাঁর গায়ন নিয়ে সমস্যা হয়নি? এ প্রসঙ্গে তিনি দু জায়গায় দু রকম কথা বলেছেন। একবার বলেছেন, ‘অনেক রেকর্ড ওরা বাতিল করল, তখন ওদের সঙ্গে ঝগড়া করিনি।’ আবার অন্যত্র বলছেন, “কখনও আমার রেকর্ড নিয়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে কোনো বিবাদ ঘটেনি। কারণ আমার ওপর তাঁদের এ বিশ্বাস আছে যে স্বরলিপি নির্দিষ্ট গানকে আমি কখনও স্থানচ্যুত করব না, আর এ-বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কঠোরতা আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ রবীন্দ্রসংগীতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য এই নিয়মবদ্ধতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নইলে রবীন্দ্রসংগীত ও নিধুবাবুর টপ্পাতে কোনো প্রভেদ থাকে না।” তবে এর সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, “সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব স্বরলিপি সামনে রেখে গান গাইবার যে প্রথা শান্তিনিকেতন চালু করেছে সেটা আমি একটুও সমর্থন করি না। বড় শিল্পীদেরও দেখেছি স্বরলিপি সামনে রেখে গাইতে। কোনো শিল্পী যখন আপনহারা হয়ে গান—তখন স্বরলিপির দিকে দৃষ্টি যায়? না যেতে পারে?”
এই ভিন্নধর্মী বয়ানের একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। আলাপচারিতার ঢং-এ বলা ‘অনেক’ মানে হয়ত ‘একাধিক’—দু-তিন বার, আর ‘বিবাদ ঘটেনি’ অর্থাৎ বিবাদ তিনি ঘটতে দেন নি; অথবা প্রাথমিক ভাবে কোন আপত্তি উঠলেও তিনি হয়ত তার সুচারু সমাধানে আগ্রহী থেকেছেন আত্মসম্মান বজায় রেখেও; যাতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন রকম মতান্তর বাইরে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তাই প্রাথমিক আপত্তি কাটিয়ে অনুমোদন পাওয়া সহজতর হয়েছে। তাঁর কোন্ কোন্ রেকর্ডের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে এরকম ঘটেছিল এবং পরে বাধা কেটে গিয়েছিল—সে কথা জানার উপায় আজ আর নেই। শোনা যায়, মৈত্রেয়ী দেবীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতায় তাঁর দেওয়া সুর অনুমোদিত না হলে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন, তবে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, অধ্যাপক নিমাইসাধন বসুকে এ বিষয়ে কিছু জানান নি। নিমাইসাধনবাবু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পরে এ কথা জানতে পেরে দুঃখপ্রকাশ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। তবে এ ধরনের ঘটনা খুব বেশি ঘটেছে বলে মনে হয় না। যিনি সহজ সখ্যের সুরে সুচিত্রা মিত্রকে হেসে বলতে পারেন, ‘ওই একটা জায়গায় কড়ি মা তো? ও আর লাগবে না, পাস করতে হলে এতেই কর, না হলে কোর না’—তাঁর পক্ষে কী সম্ভব আর কী নয়, কে বলতে পারে!
ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও, শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যে নিয়ত আস্থাশীল হেমন্ত আবারও বলেছেন, “শান্তিনিকেতনী অথবা রাবীন্দ্রিক কথাগুলিতে আমি বিশ্বাসী নই। কোন বিশেষ গায়নরীতি বিশেষ শিল্পীকে মানায়—তার নেচার টেম্পারামেন্টের সঙ্গে খাপ খাওয়ার দরুন। ঐ ধরনের গায়কিতে তিনি সিদ্ধ বলেই সার্থক। কিন্তু তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন বলেই তাঁর মতো করে গেয়ে সকলেই জনপ্রিয় হতে পারবেন একথা ভাবাটা ভুল।” প্রায় একই ধরনের সুর শোনা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেই, ঐতিহ্য, আধুনিকতা, নতুনত্ব এবং স্বকীয়তার প্রসঙ্গে—“যে পূর্ণতা পূর্বতন রূপে আপনাকে প্রকাশ করেছে, সেই পূর্ণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি, তবে ব্যর্থ হল আমাদের শিক্ষা। ... তানসেন অনুকরণের কথা বলেন নি, এবং কোন গুণীই ... তা বলতে পারেন না। এই যে গতানুগতিকতা এটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। ... আজ চাই নতুনের সন্ধান।” (সঙ্গীত চিন্তা)
এই কারণেই শিল্পী হেমন্তর চোখে রবীন্দ্রনাথ এমন এক জনমননায়ক, যিনি একই সঙ্গে লোকায়ত এবং লোকোত্তর। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম পথপ্রদর্শক হয়েও ‘গুরুগিরি’ প্রথায় বিশ্বাসী নন, তিনি চান ‘মাঝিও আমার গান গাইবে’, এবং সেইজন্য তিনি এক সময় ‘বড় বড় রাগে বড় বড় তালে’ গান ছেড়ে দিয়ে ‘আধুনিক’ গান আরম্ভ করেন—যে ধরনের গান ব্রাহ্ম প্রার্থনাসঙ্গীতের উঁচু বেদি থেকে নেমে এসেছে মানুষের মধ্যে। এ কোন পণ্ডিতের বিদগ্ধ আলোচনা নয়, এক শিল্পীর এই সরল অথচ গভীর অনুধ্যানে দেখি অচলায়তনের সেই ঠাকুরদার ছবি, যিনি জ্ঞানীর কাছে সমীহসর্বস্ব ‘গুরু’, আর সাধারণ মানুষের আপনজন! এই বোধ প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে ‘রাবীন্দ্রিক’ না হয় যদি, সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘রৈবিক’ তো অবশ্যই।
বাংলায় নাট্যগীতির সার্থকতম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের গানে অত্যন্ত স্বাভাবিক বাণীর গভীর অর্থবাহী স্বতঃস্ফূর্ত নাটকীয় অভিব্যক্তি, এবং স্পষ্ট উচ্চারণ; বর্জনীয় কেবল অতিনাটকীয়তা। এই ধারাকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্ব অনেকাংশে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। যখন তাঁর কণ্ঠে শুনি, ‘তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে’, তখন আলোর আঁধারনাশী শক্তির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে শব্দের, সুরের কম্পন। ‘সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে/ সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে/ পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে/ বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী’—এই বাণী তাঁর কণ্ঠে সুরসংযোগে উচ্চারিত হলে—আলোর উদ্ভাস, হাওয়ার গতি, আর পাষাণ-বিদারী জলধারার প্রবল আত্মপ্রকাশের আর্তি যেমন করে মূর্ত হয়ে ওঠে, তার খবর দরদী শ্রোতাদল না রেখে পারেন কি?
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁর মতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করতে পারেন নাকি পুরুষ শিল্পীরাই। এ মত অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এর ঠিক পরেই তিনি বলছেন, “রবীন্দ্রনাথের বেলায় যাকে নারীশোভন মনে হয় তার এক কারণ তাঁর সরু বাঁশির মত গলা আর তাঁর গানেরই আশ্চর্য কমনীয়তা।” এখানে কবির অল্পবয়সের কণ্ঠের কথা বলা হচ্ছে, যা শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। যাই হোক, তাঁর গানে যে এক অর্ধনারীশ্বর সত্তা আছে সে কথা একপ্রকার স্বীকার করেই নিচ্ছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথের গানের এই কমনীয়তা নিয়ে কিন্তু তাঁকেও কম সমালোচনা শুনতে হয় নি এককালে। ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’ গানটিকে ছি ছি করেছিল সে কালের গোঁড়া শুদ্ধিবাদীরা। এই গানটি সহ অনুরূপ অনেক গান—বিশেষ করে বৈষ্ণব প্রেমভাবনায় অনুপ্রাণিত ‘আমার মন মানে না’, ‘আমি কান পেতে রই’, ‘আমি তোমার প্রেমে’, ‘শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা’—হেমন্তর কণ্ঠে শুনলে মনে হয় ‘একই কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণ’। টেনর আর ব্যারিটোনের আশ্চর্য সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে এই নান্দনিক পুরুষ-প্রকৃতি সম্মিলন প্রাণ পায় তাঁর গায়নে।
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আরও একটি বিশেষ ভাবগত দিক ধরা দিয়েছে অভূতপূর্ব সার্থকতায়—যা অন্যান্য অনেক শ্রদ্ধেয় এবং সফল শিল্পীর কাছেও বোধহয় খুব বেশি পাওয়া যায়না, একথা বললে হয়তো নিতান্ত অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথের গানে বাহ্যিক পর্যায় বিভাজনের অন্তরালেও রয়েছে এক অন্তর্নিহিত পর্যায়-সম্মিলনের ভাব। ‘প্রেম’ আর ‘পূজা’ কিভাবে এক হয়ে যায়, সে কথা তিনি নিজেই স্পষ্ট বলে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতির গানেও যে প্রেম বা বিচিত্রের ভাব লুকিয়ে আছে (‘ছিন্নপত্র’-এর ছত্রে ছত্রে তার আভাস ছড়িয়ে আছে), স্বদেশের গানের অন্তরালে মিলেমিশে যেতে পারে প্রকৃতি আর পূজার ভাবধারা—সে কথা বোধহয় এই ‘অপ্রাতিষ্ঠানিক’ শিল্পীর মত করে আর কেউ মনের মধ্যে লাগিয়ে দিতে পারেননি। তিনি যখন উচ্চারণ করেন, ‘সমাজ সংসার মিছে সব/ মিছে এ জীবনের কলরব’, তখন ‘এমন দিনে তারে বলা যায়’-এর মত একটি প্রেম পর্যায়ের গানের আনুষঙ্গিক প্রকৃতি(বর্ষা)যাপন যেন বয়ে আনে নিরালায় বসে ‘পূজা’র ভাবসাদৃশ্য। এই অভিযাত্রা আরও দেখি—‘স্বদেশ’ থেকে ‘প্রকৃতি’ ও ‘পূজা’য় (‘অয়ি ভুবনমনমোহিনী’, ‘ও আমার দেশের মাটি’), ‘বিচিত্র’ থেকে ‘প্রকৃতি’ ও প্রেমে (‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি’, ‘তুমি কি কেবলই ছবি’), পূজা থেকে প্রেমে (‘আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে’, ‘চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে’)।
তরুণ মজুমদারের ‘দাদার কীর্তি’ ছবির জনপ্রিয়তার সুবাদে ‘চরণ ধরিতে’ গানটি বহু-আলোচিত, তাই আবারও তার আলোচনায় না গিয়ে বরং ‘প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়’ গানটির কথাই ধরা যাক। গানটি বিচিত্র পর্যায়ের। কিন্তু গানের বাণীতে স্পষ্ট এক ফাল্গুনী প্রতীক্ষার আবেশ—প্রকৃতি আর বসন্তের অনুষঙ্গ ছাড়া এ গানের ভাবরূপ আদৌ ধরা দেয় কি? একটু মনে করে দেখুন, হেমন্ত কীভাবে এ গানটি পরিবেশন করেছেন। তাঁর অল্প বয়সের রেকর্ডিং-এ ধরা পড়ে বিচিত্র পর্যায়ের উপযোগী দ্রুতলয় আর নতুনত্বের, আশ্চর্যের অনুভূতি—শুনলে মনে হয় প্রায় শ্বাসবিরতি-বিহীন, বাধাবন্ধহীন, এক বসন্তবাতাস যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা গানের শরীর জুড়ে। সেই সঙ্গে গানের প্রকৃতি-পটভূমি পূর্ণতা পাচ্ছে ‘ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা’, ‘ফাগুন মাসে কী উচ্ছ্বাসে’, ‘বনের বাতাস এলোমেলো’—শব্দবন্ধগুলি উচ্চারণের সময়কার স্বরপ্রক্ষেপে। এই গানটি আবার হেমন্ত গাইলেন ‘একটুকু ছোঁয়া লাগে’ ছবিতে, সেখানে নায়ক-নায়িকার অর্ধস্ফুট প্রেমের অনুষঙ্গে গানটির দৃশ্যায়ন আরও একবার অভিনব গায়নের রসে শ্রবণসুখ দেয়। এখানে গানটি মধ্য লয়ে গাওয়া—বিমূর্ত প্রতীক্ষার ভাব যেন এক সাকার রূপ নিয়েছে। ‘এসেছে কি’, ‘আসে নি কি’, ‘সে কি এল’—এই কথাগুলি যেন গাওয়া হয় বিশেষ কোন ‘অলখ জনের চরণশব্দে মেতে’, পর্দায় দেখা যায় নায়িকার পা দুটি চঞ্চল হয়ে উঠছে, সে নিজেকে কল্পনা করছে বধূরূপে। চিত্ররূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ‘বিচিত্র’ রবীন্দ্রসঙ্গীতটির এমন প্রেম-ব্যঞ্জনাসহ প্রয়োগের সামনে দাঁড়িয়ে ‘অবাক হয়ে শুনি’ ছাড়া বোধহয় আর কিছু বলার থাকে না।
আর একটি গানের কথা বলে শেষ করতে চাই, গানটি অনেক শিল্পী গাইলেও দেবব্রত এবং হেমন্তর কণ্ঠেই বোধহয় সর্বাধিক জনপ্রিয়। ‘জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে’ গানটি দেবব্রত গেয়েছেন প্রার্থনা সঙ্গীতের মেজাজে; প্রতিটি স্তবকের শেষে শোনা যায় মৃদু ঘণ্টাধ্বনির অনুরূপ বাদ্যানুষঙ্গ। ‘বন্ধু হে আমার’ তাঁর অভিব্যক্তিতে হয়ে ওঠে চিরসখাকে উদাত্ত আবাহন জানাবার মন্ত্র। ভাবলে বাঙালি হিসেবে গর্ব হয়, ইংরেজি এবং রাশিয়ান সংস্করণে তাঁর গাওয়া এই গান বিদেশে প্রার্থনাগীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সত্যি অসাধারণ সেই অনুভূতি। আর হেমন্ত গেয়েছেন অসীমকে আপন সীমার মাঝে পাবার অনির্বচনীয় মাধুর্যে, স্নিগ্ধগম্ভীর সমর্পণের অপার মুগ্ধতায়। ‘বন্ধু হে আমার’- তিনি যখন উচ্চারণ করেন, মনে হয় নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন জীবনদেবতার আলিঙ্গনে। তাঁর পরিবেশনায় ‘আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া/ তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া’ হয়ে ওঠে লোকোত্তরকে লোকায়ত করে, আপন হৃদয়ে সম্পৃক্ত করে নেওয়ার মরমিয়া অনুভূতি। দুই শিল্পীর ক্ষেত্রেই ‘গানের বেদনায়’ আমরা ‘যাই যে হারায়ে’—কিন্তু একজনের গায়নে সেই হারিয়ে যাওয়া দীর্ঘশ্বাসের মত, অন্যজনের কণ্ঠে তা হারিয়ে খুঁজে পাবার আনন্দাশ্রু।
“আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো ... একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে—এইটিই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে।” রবীন্দ্রনাথের এইটুকু চাওয়ার মান কারও চেয়ে কোন অংশে কম রাখেননি তথাকথিত ‘রাবীন্দ্রিক’ বৃত্তের বাইরে দিয়ে চলা এই দুই ‘রসতীর্থ পথের পথিক’। সময় বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসন, কোন কিছুই শেষ পর্যন্ত তাঁদের গানের ওপর স্টিম রোলার চালাতে পারেনি। প্রত্যেক বার পঁচিশে বৈশাখ তাঁদের কথাও নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। দুজনের পথ এবং মানসিকতা আলাদা হলেও পরস্পরের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন ছিল গভীর। নিজেকে ‘ব্রাত্য’ মনে করতে করতে হতাশায় জর্জরিত ‘কাকা’ (দেবব্রত বিশ্বাস)কে তাঁর শেষ অনুষ্ঠানে, রবীন্দ্রসদনে সংবর্ধনা দেবার উদ্যোগও ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরই। মর্মরমূর্তির আড়াল থেকে হয়ত সেদিন হেসেছিলেন তিনি—যাঁর উদ্দেশে বলা যায়, ‘শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়/ মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।’