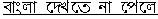“[W]hat a state of society is that, which knows of no better instrument for its own defense than the hangman, and which proclaims through the ‘leading journal of the world’ its own brutality as eternal law?”
--Karl Marx “Capital Punishment”, The London Times (January 1853)
“What dehumanizes you inexorably dehumanizes me”
---‘Ubuntu’ (Ancient African philosophy/wisdom) (as quoted by Desmond Tutu)
সময়টা চল্লিশের শেষ, পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরু--সুরমা ঘটক যখন শিলং জেলে বসে তাঁর দিনলিপি লিখছেন। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্যমুক্ত ভারতবর্ষ তখন সবে আধুনিক গণতন্ত্রে দীক্ষিত হওযার পথে পা বাড়িয়েছে, সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়াসে নানা কর্মকাণ্ড চলছে দেশ জুড়ে। আবার, ঠিক সে মুহূর্তেই যুবসম্প্রদায়ের একাংশকে যেতে হচ্ছে জেলে, নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা ধাঁধা, paradox-ঘেরা সময়।
যে কোনও জেল-দলিলের মতই সুরমাও এক আশ্চর্য surreal অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। সেসময় রাজনৈতিক বন্দীদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা ছিল না, অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে ‘সহবাস’ ছাড়া উপায় ছিল না। পাগল, ভিখিরি, খুনী, বারবনিতাদের চারপাশে নিয়েই বন্দী জীবন। তাদের যন্ত্রণার চিত্কার, কান্না রাতের ঘুম কেড়ে নিতো। জেলের কুঠরির মধ্যে আর্থিক-সামাজিক, রাজনৈতিক অসাম্য--এক কথায় সভ্য সমাজের যাবতীয় contradiction-গুলিকে কিছুতেই দূরে ঠেলে সরিয়ে রাখা যায় না। সমস্ত বিকৃতি, বীভত্সতা নিয়ে সে একেবারে সামনে এসে পড়ে আমাদের মধ্যবিত্ত sensibility, অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে--সেই কথাই এই ডায়েরীতে ছড়িয়ে আছে। এক জায়গায় খুশবু বলে একটি মেয়ের কথা বলেন লেখিকা: “[খুশবু] কখনো বিচ্ছিরী ভাষায় গালাগালি দিত.....। দিন নেই, রাত নেই ওর একটানা গান ও চিত্কার চলছেই, গভীর রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে ওর গান ও চিত্কারের সুর আসতো কানে। ঘুম দুচোখে প্রায় ছিলই না, কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। সমস্ত শরীরে কয়েকটা হাড় ছাড়া কিছু ছিল না। গায়ের একটা জামাকেই বারবার সেলাই করে গায়ে দিত। কম্বল দিলে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে চারদিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতো...।”
আরেক জায়গায় লিখছেন, ““ক্যান্নো ও কম্ডি এসেছিল মদের কেসে। বেশীরভাগ সময়েই শুয়ে কাটাত। হেরমনের ছিল খুনের কেস। এখনো বিচার হয়নি। স্বামীকে খুন করে ও এসেছে জেলে। ....এমন একটা স্নিগ্ধতা ছিল ওর চোখের চাউনিতে ....আমরা এসেই পেলাম এই কয়জনকে, আর (ছিল) পাগলী। ঘরে ঢুকেই দেখি আমাদের ঘরটার পাশেই একটা সেলের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা ভূটিয়া মেয়ে, হাতে ভাতের থালা। নিজের ভাষায় কী জানি সব বলছিল। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর দিকে। ....যুদ্ধের বাজারে পতিত-জীবন আরম্ভ করে। ....যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর বিদেশী সৈনিকেরা সব দেশে ফিরে যায়। ওদের মত মেয়েদের জীবনে জীবিকা-নির্বাহের পথে একটা ছেদ পড়ে।”
“এই সমাজ ব্যবস্থাই জন্ম দিয়েছে ওদের ...”, লিখতে লিখতে ঘুরে ফিরে এ কথা মনে হয়। সেই সমাজ বদলানোর অঙ্গীকারেই তো সুরমাদের জেলে আসা।
দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি নথিবদ্ধ করতে করতে হঠাত্ কখন পাঁচিলের বাইরে চোখ চলে যায়। জেলের ভেতরের যন্ত্রণার কথা ভুলে মন চলে যায় বাইরে খোলা আকাশের নীচে। পাহাড়, নদীতে ঘেরা অপূর্ব শিলং শহর। কী অনায়াস, স্বচ্ছন্দ সেই যাতায়াত!—“বাইরে নাশপাতি, পীচ, প্লাম গাছে ফুল কবে শেষ হয়ে গেছে। সিজনফ্লাওয়ার, সুইটপী আর বেড়ার গায়ে সাদা মে ফ্লাওয়ার-এর দিনও শেষ হয়ে লতান গোলাপ গাছে ফুটেছে থোকা থোকা লাল গোলাপ। ঝোপের মত গাছে ফরগেটমি নট’ আর পাহাড়ে পাহাড়ে ক্রিসেনথিমাম ও রডডেনড্রোন গুচ্ছ...।” প্রকৃতির এই নির্লিপ্ত-নির্বিকার উপস্থিতি গোটা অভিজ্ঞতাকেই যেন আরও অবাস্তব করে তোলে। বন্দীজীবনের বিচ্ছিন্নতা, অসুস্থ পরিবেশ বাধ্য করে নতুন করে ভাবতে। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে ঘিরে গড়ে ওঠা জেল ইত্যাদির মত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, অভ্যস্ত ধারণাগুলির প্রতি বিশ্বাস যেন আর অটুট থাকে না। ভূমিকায় লিখছেন: “তরুণী বয়সে যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম সে সমাজ আজও গড়ে ওঠেনি। আজও মহানগরীর রাজপথে-পথে মেয়েদের মিছিল--আন্দোলনের নয়--জীবনের। জীবনে বেঁচে থাকাটাই তো সবচেয়ে বড়। তাই মেয়েরা সংসার পেতেছে খোলা আকাশের নীচে--ফুটপাতে-রান্না, শোয়া, শিশু-প্রতিপালন চলছে--শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফান, খরা-বন্যা-দুর্ভিক্ষের পরিক্রমায়”। শিলং অঞ্চলের খাসিয়া সমাজ, মেয়েদের কথা বারবার এসেছে, কারণ তারাই ওই অঞ্চলের আদিবাসীদের অন্যতম—“আগে জানতাম খাসিয়া পাহাড়ে, গ্রামে সবারই জমি আছে—শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছাপ নেই এখানে। কিন্তু সে ধারণা ভেঙে গেল। বর্তমানে সবারই জমি নেই। আগে জমি বা ঘরের জন্য খাজনা দিতে হতো না। এখন খাজনা দিতে হয়। জমিতে উত্পন্ন ফসলে আগে দিন কেটে যেত। কিন্তু এখন আর পেট ভরে না। তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য বাঁচবার তাগিদে সবাই বেছে নিচ্ছে বিভিন্ন পথ। তারই পরিচয় পেলাম যত দিন যেতে লাগলো। আমাদের দৃষ্টি অনেক খুলে গেল....” ইত্যাদি।
আরেকটি ছোট্ট ঘটনা: “সামান্য কাপড় চুরির কেসে ছ-মাসের জেল হয়েছে কিশোরী মেয়ে পেরিনার। চেরপুঞ্জীর কাছ থেকে দূর ওয়ার বস্তি বা গ্রাম থেকে ও এসেছে। ঘরে মা-বাবা, ভাই-বোন সবাই আছে।....স্থানীয় কোনও এক বাড়িতে কাজ করত। সেই বাড়ির মালিকেরই কাপড় চুরি করে।..."
এতকাল পরে ডায়েরিটি পড়তে পড়তে মনে হয় আলগোছে যেন কিছু মূল প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব এখানে ওখানে আলগোছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এইটিই বোধ হয় দিনলিপিটির অন্যতম গুণ--পাঠকের সামনে মেলে ধরে একটা মস্ত খোলা ক্যানভাস। তারই ওপরে ভেসে ওঠে ছবিগুলো। সেই টুকরো পর্যবেক্ষণ, মন্তব্যগুলির ভেতরের যোগসূত্রগুলি কালের ব্যবধানে কেমন করে যেন চোখের সামনে আপনিই স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। আর তাই এই ছোট্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী নাড়াচাড়া করতে করতে আজকের রাজনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের বিবর্তনেরধারার প্রেক্ষিতে ফেলে একটু দেখে নেওয়ার সাধ নিতান্তই স্বাভাবিক। পাঠকের ইচ্ছে হতেই পারে একটু দেখে নিতে হিংসা, সামাজিক অপরাধ মোকাবিলায় সমাজ কতটুকু এগল। খুঁজতে গিয়ে নজরে পড়ছে এক মস্ত ‘অচলায়তন’। মানসিক বিকৃতি, হিংসা, যা বহুলাংশেই দারিদ্র-জাত, যখন সামনে এসে পড়ে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনকে বিঘ্নিত করে তখনই আমরা তাকে কোনরকমে জেলখানার অন্ধকার কুঠরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। সমস্যার মূল বিষয়গুলিকে এড়িয়ে এ এক সহজ রাস্তা। ‘সহজ’, কিন্তু সর্বনেশে। ডায়েরীটি বিশেষ করে এদেশে বসে পড়তে পড়তে চোখের সামনে আরেকটা ছবি ভেসে ওঠে। আমেরিকার জেলগুলিও তো উপছে পড়ছে পেরিনার-র মত কত অসংখ্য কিশোর-কিশোরীর ভিড়ে। কিছুটা ভিন্ন পরিস্থিতি, ইতিহাস হলেও মূল মানবিক সমস্যার প্রকৃতি এক। কোথায় শিলং, আর কোথায় আমেরিকা, তবুও মানবিক সমস্যাগুলিকে দেশ-মহাদেশের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক গণ্ডিতে কিছুতেই বেঁধে রাখা যায় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেল-ব্যবস্থা বা ‘কারাগার’-কে সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ধরে নেওয়ার মধ্যেই যে একটা মস্ত সমস্যা নিহিত—একথা দ্বিধাহীন স্বরে ঘোষণা করেছেন এদেশের অন্যতম মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী এঞ্জেলা ডেভিস (Angela Davis)। শ্রীমতি ডেভিসের মত স্পষ্ট করে এ কথা বলতে না পারলেও সুরমা-র এই ডায়েরীটিতে তার আভাস রয়েছে। সুরমা ঘটকদের সময় থেকে বেশ কয়েক দশক পেরিয়ে নতুন শতাব্দীতে এসে পৌছেছে আমাদের সমাজ, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির কল্যাণে, “বিশ্বায়নের” দৌলতে গোটা পৃথিবী আজ একাকার (চলন-বলনে, পোশাকে-আশাকে)। অথচ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা যেন সেই মধ্যযুগে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের প্রগতিশীল চিন্তার বিবর্তনের ঢেউ কিছুতেই কেন জানি না (এক্ষেত্রে অবশ্যই ‘হিংসা নিয়ন্ত্রণ’ সংক্রান্ত) আমাদের চৈতন্যকে তেমন করে নাড়া দিতে পারছে না। ‘হিংসা’-কে ‘হিংসা’ দিয়েই মোকাবিলা করায় আজও আমাদের বিশ্বাস অটুট। এমন কী ‘খুনের বদলে খুন’ “ন্যায়বিচার”-হিসেবেই গণ্য। দম বন্ধ হয়ে আসে। এই অসহায়তার বোধ এবং বিভ্রান্তির কিনারায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এবিষয়ে কিছু বিকল্প প্রচেষ্টা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়ত একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
দক্ষিণ আফ্রিকা:
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দক্ষিণ আফ্রিকা-র “Truth and Reconciliation Commission”-এর মত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার কথা। সাতাশ বছরের কয়েদী-জীবন শেষ করে নেলসন ম্যান্ডেলা যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর সামনে এক ক্ষত-বিক্ষত সমাজ। বহুদিনের জমে থাকা যন্ত্রণার জ্বালা যে হিংসার উর্বর জমি সে কথা মনে রেখে মানুষের আবেগের স্রোতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটালেন ডেসমনড টুটু এবং নেলসন ম্যান্ডেলা। এই দুই মহর্ষির নেতৃত্বে তৈরী হল “Truth and Reconciliation Commission”। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল সদ্যজাত সমাজ, সুস্থ গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকার এবং ‘সাদা সমাজ’-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়ায়ের সমাপ্তিতে তৈরী হল “Truth and Reconciliation Commission”, এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের বিচারসভা। হিংসার শিকার যাঁরা আর হিংসা ঘটিয়েছেন যাঁরা—দুই পক্ষ মুখোমুখি বসলেন। দুই পক্ষই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলি, বিস্তারিতভাবে জানালেন। বলাই বাহুল্য উভয় পক্ষের কাছেই এ এক তীব্র ব্যথাজর্জরিত প্রক্রিয়া, তবে যার পরিণতি আরও তলিয়ে গিয়ে নয়, বরং মানব অস্তিত্বের মর্যাদার পুনরুদ্ধারে। অপরাধীদের শাস্তির বদলে গ্রহণ করতে হল এক বিশেষ দায়িত্ব—তাঁদের হিংসার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা ক্ষতিপূরণের (এ বিষয়ে পরে আবার ফিরে আসব)। ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া TRC’র দারুণ সাফল্য আজ যেকোনো প্রগতিশীল মানুষের, সমাজের কাছে এক গভীর অনুপ্রেরণা।
আমেরিকায় মৃত্যুদণ্ড-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি জেল-বিরোধী আন্দোলনও চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। এই লড়ায়ের অন্যতম নেত্রী এঞ্জেলা ডেভিস আর তাঁর সহকর্মী, সহযোগিরা সরাসরি জেল-ব্যবস্থার অবলুপ্তির প্রশ্ন তুলে বসেছেন। চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রচলিত “শাস্তি-ভিত্তিক ব্যবস্থা”র সঙ্গে সামাজিক অপরাধের “স্বাভাবিক” যোগটিকেই। আইনের মূল বিষয় justice কিংবা ন্যায়বিচার। আর সেই ন্যায়বিচার আমরা ধরে নিয়েছি পূর্ণ হয় অপরাধীর শাস্তির মধ্যে দিয়ে, অপরাধের গুরুত্ব অনুযাযী শাস্তির মাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কারাগার-বাস, শারিরীক-মানসিক অত্যাচার আর গুরুতর হিংসার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড। এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে আমাদের অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। প্রকৃত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ অপরাধ-নিয়ন্ত্রণে সাফল্য দেখা দিক বা নাই দিক এই প্রচলিত ব্যবস্থাই সাধারণ নাগরিকের পূর্ণ ভরসাস্থল। আর এরই উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বিশাল, জটিল আইনী ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের এ এক গভীর অন্তর-দ্বন্দ্ব। “Human rights are innate and inalienable”—এই যদি হয় আধুনিক গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র তবে যে কোনও সাধারণ অপরাধের আইনী বিচার (criminal prosecution) শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর অধিকাংশ মানবিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় কেন?! মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারলেও বন্দী-জীবন, যেখানে তার গোটা অস্তিত্ব লোপাট। শারীরিক-মানসিক নির্যাতন কয়েদিজীবনের প্রত্যেকদিনের অভিজ্ঞতা। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই একটা নিখুঁত ‘ফ্যাসিস্ট’ (fascist) ব্যবস্থার অস্তিত্ব আমরা মেনে নিয়েছি, আর তার ওপরেই আমাদের অগাধ বিশ্বাস। এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে আমরা বিপন্ন বোধ করি। একটা অসম্ভব “repressive system”-এর সাহায্যে সামাজিক অপরাধকে রোখার অর্থহীন অভ্যাস। এই পথে অপরাধ বা হিংসা নিয়ন্ত্রণে কোথাও কী কখনো প্রকৃত সুফল মিলেছে? আমাদের প্রত্যেকদিনের অভিজ্ঞতা তো তা বলছে না! “নাইন ইলেভেন” (‘9/11’) পরবর্তী অধ্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ‘পশ্চিমের’ আন্তর্জাতিক ‘আতঙ্কবাদ” নিয়ন্ত্রণের বিশ্ব-জোড়া প্রয়াসের দিকে তাকালে এই বিষয়ে বোধ হয় আর সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। এ বিষয়ে বরং জাপানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এই সাফল্যের কারণ কোনও বিশেষ পুলিশী বা মিলিটারি ব্যবস্থা নয়, সাফল্যের পিছনে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র বা বন্দুক ব্যাবহারের উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা। তাছাড়া, অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করার প্রয়াস তো আছেই। এঞ্জেলা ডেভিসের দাবী 'জেল’-গুলো বন্ধ হয়ে গেলে ‘সামাজিক অপরাধ’ আপনি কমে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এই আপাত অবাস্তব দাবী দাঁড়িয়ে আছে যুক্তির, গভীর জীবনবোধের শক্ত জমিতে। আমরা সকলেই জানি যে জেলগুলি ভবিষ্যত্ অপরাধী তৈরীর উর্বর ভূমি, যেখানে চরম অবমাননাকর পরিস্থিতির মধ্যে আটকে রেখে অপরাধীর শেষ মনুষ্যত্বটুকু নিংড়ে বার করে নেওয়াই রীতি। একমাত্র আরও হিংসাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই প্রসঙ্গে ‘ফেমিনিস্ট বুদ্ধিজীবি সিলভিয়া ফেদেরিচি (Sylvia Federicci)-র অকাট্য যুক্তি: “...the function of feminist politics as an activity whose task is to call into question all forms of domination, and that must, therefore, denounce the system of ontological apartheid that the death penalty institutes. By "ontological apartheid" I refer to the fact that capital punishment postulates the existence of two, almost ontologically different humanities: on the one side the "rational" citizen, for whose benefit executions are allegedly carried on, on the other, the beastly criminals, to whom anything can be done, since by their actions--we are told--they have placed themselves outside the boundaries of our humanity. There are other reasons, however, why feminists should ... speak in support of a society free from hangings, electric chairs and lethal injections.” অধ্যাপক ফেদেরিচি মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন তা সাধারণ শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা অপরাধীদের মানবিক-বোধ, বিচারের পরিধি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি, ধরে নিই তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ মানবিক-অধিকারের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অপরাধী জগত আর সাধারণ সমাজ—এই দুয়ের মধ্যে যেন একটা দুর্ভেদ্য দেওয়াল রয়েছে। ভুলে যাই যে মানুষ ভুল করে, অনেক মারাত্মক ভুলও করে বসে। সেই ভুলের পেছনে সামাজিক গঠনের অজস্র ত্রুটি দায়ী। তাছাড়া, একই জাতীয় অপরাধের জন্য একজন সাজা পেলেও অন্য ক্ষেত্রে তা অপরাধ বলে স্বীকার করা হয় না। “রেস”, “জাতপাত”, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি-র দ্বারা আইন-আদালতের রায় প্রভাবিত হওয়ার ঘটনাও তো বিরল নয়। রাষ্ট্র প্রধানের সামান্য অঙ্গুলিহেলনে গণনিধনযজ্ঞ বা genocide ঘটলেওতা অনৈতিক হিসেবে গ্রাহ্য করা হয় না, অথচ একটি খুনের জন্য মৃত্যুদণ্ড আমাদের বিচলিত করে না। চার্ল্স চ্যাপলিনের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে না এসে পারে না: “One murder makes a villain, millions a hero. Numbers sanctify, my good fellow." (Charles Chaplin in Monsieur Verdoux)। কোন ক্ষেত্রে কী রকম শাস্তি জুটবে তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেবারেই arbitrary! তাই, এঞ্জেলা ডেভিসের মত একজন মানবতাবাদী ‘প্রাগৈতিহাসিক’ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বর্জন করে সম্পূর্ণ নতুন, সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনের দাবী কেন তোলেন বুঝতে অসুবিধা হয় না।
প্রগতিশীল অপরাধ-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিকল্প অনুসন্ধানে বিশেষ উদ্যোগী হেরমেন বিয়ানসে (Herman Bianchi) তাঁদের অন্যতম। বিয়ানসের বহু অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা ভিত্তিক মডেল-টি Justice as Sanctuary নামে পরিচিত। এই মডেলটি অনেকটাই political asylum-এর আইডিয়ারই প্রয়োগ মাত্র, অর্থাত্ যা প্রায়শই আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—অর্থাত্ যেখানে মূল মন্ত্র conflict resolution, দ্বন্দ্বের সমাধান, শাস্তি নয়। এই বিচারব্যবস্থায় অপরাধকারী এবং অপরাধের শিকার যিনি হয়েছেন–এই দুই পক্ষেরই থাকবে সমান সাংবিধানিক অধিকার, conflict resolution-এর মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান দাবী করার। অর্থাত্, সমস্যার সমাধান হবে প্রত্যক্ষ আলোচনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়োজিত এবং নিয়ন্ত্রিত আইন-বিশেষজ্ঞদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে সরকারকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জেলের পরিবর্তে sanctuary গঠন করতে হবে, নতুন আইনজ্ঞদের এই বিশেষ ব্যবস্থা নতুন নিয়ম কানুন রচনা এবং পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। প্রবক্তার মতে প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশিই এই নতুন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, “কয়েদখানা’ পুরোপুরি তুলে না দিয়ে। অপরাধী এবং বিরোধী পক্ষের সামনে দুটি ব্যবস্থাই বিকল্প হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। এই বিকল্পের মূল ভিত্তি প্রচলিত ব্যবস্থার খানিকটা বিপরীতধর্মী। অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে অপরাধীর শেষ মনুষ্যত্বটুকু নি:শেষ করার পরিবর্তে তার সুপ্ত মানবিক দিকটার পুনরুদ্ধার। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এই ছোট রচনার পরিসরে সম্ভব নয়, কেবল আভাসটুকুই রইল খানিকটা বিতর্ক শুরু করার উদ্দেশ্যে। বলাই বাহুল্য, এই মডেল আমাদের অভ্যস্ত ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন দাবী করে। তবে, আপাত দৃষ্টিতে মস্ত paradigm shift মনে হলেও একেবারে নজিরবিহীন নয়। যেকোনো ধ্রুপদী সভ্যতায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর রেশ খুঁজে পাওয়া যাবে আজও, বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে। এক কথায় প্রাক-ধনতন্ত্রী সমাজের জীবন-অভ্যাস এবং দর্শনে। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুয়ায়ী ধরে নেওয়া হয় ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষের জীবনে স্বাভাবিক অঙ্গ। সেই ভুল বা বিচ্যূতির ফলে ব্যক্তিজীবনে, সমাজ-জীবনে যে ক্ষতি বা ‘ছন্দপতন’(disharmony) ঘটে তাকে পূরণ করাই সভ্যতার লক্ষ্য। তাই, এমন বিধানের প্রয়োজন যা হারিয়ে যাওয়া শান্তি ফিরিয়ে আনবে, ক্ষমার মধ্যে দিয়ে, দুই পক্ষের মধ্যে বিঘ্নিত/ক্ষুণ্ণ সামাজিক সম্পর্কের সুস্থতা ফিরিয়ে আনার মধ্যে দিয়ে। অবশ্যই এখানে শেষ পর্যন্ত ‘ক্ষমা’র একটা বিরাট ভূমিকা। আসলে, ক্ষমা তো কেবল উদারতা নয়, ঘটে যাওয়া অপরাধকে ভুলে যাওয়াও নয়, ক্ষমার মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে সমাজের সুস্থতা--এক অর্থে মানব অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। তাই, সেই ক্ষমাকেই আজ সরকারী নীতি বা policy হিসেবে আমাদের প্রচলিত আইনী কাঠামোয় গেঁথে নিতে হবে। নইলে cycle of violence-এর অন্ধ গলি থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই। অনেকেই অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলবেন এসব utopian ideas। মনে রাখতে হবে কালকে অনেক কিছুই utopian ছিল আজ যা বাস্তব। এর পরেও প্রশ্ন উঠবে: খুনী, ধর্ষণকারীদের কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এঞ্জেলা ডেভিস যে ঘটনাটি তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন সেই উদাহরণটি দিয়েই বর্তমান আলোচনা শেষ করা যাক:
গল্পটি দক্ষিণ আফ্রিকার TRC-র সাফল্যের একটি উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার এক ‘শ্বেতাঙ্গ’ Fulbright ছাত্রী Amy Biehl দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে একদল কালো আফ্রিকান যুবকের ‘শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী’ আক্রমণের শিকার হন। বিচারে অপরাধীদের দণ্ড হিসেবে ১৮ বছরের কারাবাস ঘোষিত হয়। “Truth and Reconciliation Commission”-এর কাছে সাজাপ্রাপ্তরা যখন ক্ষমা চেয়ে মুক্তির আবেদন করেন তখন মৃতা ছাত্রীর মা-বাবা সেই আবেদন মেনে নেন একটি বিশেষ শর্তে। তাঁরা ওই যুবকদের দুজনকে অনুরোধ করেন মৃতা কন্যার স্মৃতিতে গঠিত সংস্থায় যোগ দিতে। আজ তারা সেই সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। ‘নাইন ইলেভেন’-সদ্য ঘটে যাওয়ার পর একটি সভায় নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে Biehl দম্পতি বলেন: কোনও হিংসার ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর প্রতি-আঘাত হানার বদলে আমাদের উচিত একটু ভেবে দেখা এমন ঘটনা ঘটলো কেন। বিশ্বজোড়া সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল কারণ তো আমাদের অজানা নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অধিকার—এই নিয়েই তো চলছে যুদ্ধের পর যুদ্ধ। প্রাক-ধনতন্ত্রী দুনিয়ায় মানুষ জানত যে পৃথিবীর/প্রকৃতির সম্পদ শেষ পর্যন্ত সীমিত, তাই সভ্যতাকে বাঁচতে হলে মানুষকে তা ভাগ করে নিতে হবে পাশের মানুষের সঙ্গে, এমন কী অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গেও। ভোগ-সর্বস্ব ধনতন্ত্রের লাগাম-ছাড়া বিকাশে সেই জীবনবোধ আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল চূড়ান্ত ভারসাম্যহীন, ব্যথায় ভরা এক পৃথিবী।
“হিংসার বদলে হিংসা”-র পথ আঁকড়ে ধরে রেখে মানব সভ্যতা যখন লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে বসেছে তখন “utopia”-কে একটু সুযোগ দেওয়া যাক না, ক্ষতি কী?!
যে বইগুলি এই রচনাটি লিখতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে:
(১) “শিলং জেলের ডায়েরি”; সুরমা ঘটক; ‘অনুষ্টুপ’; ১৯৯০
(২) Bianchi, Herman; Justice as Sanctuary, Wipf and Stock Publishers, 1994
(৩) Davis, Angela Y.; Are Prisons Obselete? Seven Stories Press, 2003
(পরবাস-৫৮, নভেম্বর ২০১৪)
ছবিঃ Times of India, June 22, 2013 থেকে