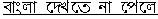Parabaas Moviestore

Parabaas Musicstore

Subscribe to Magazines
পরবাসে রাহুলের
লেখা
ও
বই

Parabaas Bookstore

কেদারনাথ মন্দির
৫ নভেম্বর; ২০১৫
গুপ্তকাশীর GMVN টুরিস্ট লজ থেকে দুজনে বেরোলাম সকাল সাড়ে ছ-টায়। এখানে পৌঁছেই সেরে নিয়েছি বায়োমেট্রিক কার্ড আর স্বাস্থ্যপরীক্ষা পর্ব। কেদার আর চৌখাম্বা মেঘের পাঁচিলের ওপারে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম বাজারে, উঠে বসলাম সোনপ্রয়াগের শেয়ার গাড়িতে। গুপ্তকাশীর বেশিরভাগই এখনও সুপ্ত — তবুও চা ঠিক জুটে গেল। সকালের ঠাণ্ডাকে খানিক ঠাণ্ডা করলাম কাকা আর আমি। গাড়ি, ছাড়ার মতো ভরতি হতে সোয়া সাতটা বাজল। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পথের কালচে ফিতেটা ধরে মসৃণগতিকে ছুটছে গাড়ি। নারায়ণকোটা, পম্পাপুর, হনুমাগঢ়ী ছাড়িয়ে ফাটা চটীর হেলিপ্যাডকে যখন পেরোচ্ছি, ঘড়িতে তখন সাতটা তেত্রিশ। বড়াসু, শেরসী, রামপুর, সীতাপুর পার করে গাড়ি আমাদের সোনপ্রয়াগে নামিয়ে দিল আটটা ন-য়ে। ওখানকার ক্যাম্পে ছাড়পত্রে ছাপ মারিয়ে পা রাখলাম পথে। ধস সারানোর কাজ চলছে, তাই মন্দাকিনীকে পেরোলাম পদব্রজেই। ওপারে ভিড় অপেক্ষমান গৌরীকুণ্ডের গাড়ির। সিজন শেষ হয়ে আসছে, তাই গাড়ির সংখ্যাও কম। আমরা দুই বাঙালি ছাড়া প্রায় সকলেই গুজরাতবাসী। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে গাড়ি আসা মাত্র সকলে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন আয়লার প্রথম ত্রাণ এসেছে। গাড়ির দশ ফুটের মধ্যে ঘেঁষতে পারলাম না। বহনক্ষমতার দেড়গুণ বেশি মানুষ নিয়ে দুলতে দুলতে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁকে। যে করেই হোক এর পরের গাড়িতে সেঁধোতেই হবে। এখন আটটা সাতাশ বাজে, আর ন-টায় শেষ গাড়ি এ-বেলার মতো।
পরের গাড়ি আসতেই অল্পবয়েসে সিনেমার ফ্রন্ট স্টলের লাইনে ঝাঁপাবার বিদ্যেটা কাজে লেগে গেল — দুই বুড়ো সেঁধিয়ে গেলাম গাড়িতে। আটটা চল্লিশে চল্লিশ জন (আসলে বোধহয় পঁচিশ) লোক নিয়ে গাড়ি নড়ল। কুড়ি মিনিট বাদে ঠিক ন-টায় গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিল গৌরীকুণ্ডে। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত রূপ এখন গৌরীকুণ্ডের। দু-পাঁচখানা বাদ দিলে সব বাড়িই ভগ্নস্তূপ। নদীর ধারের কোনও বাড়িরই চিহ্নমাত্র নেই। গৌরীকুণ্ডের উষ্ণকুণ্ডও অদৃশ্য, শুধুমাত্র নল বেয়ে ঝরছে জলের ক্ষীণ ধারা।
মূল পথটা বিধ্বস্ত, তাই সিঁড়ি ভেঙে খাড়া চড়াই চড়তে শুরু করলাম দুই বুড়োতে। গুজরাতিরা ঘোড়ার খোঁজে লেগে পড়লেন।
জি.এম.ভি.এন-এর টুরিস্ট লজকে নিচে ফেলে মূল পথে উঠে আসতে আসতে জিভ হাঁটু ছুঁই ছুঁই। দু-ধারে খাবারের দোকান দেখেই পেটের ছুঁচোগুলো হিপ-হপ শুরু করে দিল। এমনিতেই পথে এখন কোনও চায়ের দোকান নেই। চা-টা জুটবে সে-ই জঙ্গল চটীতে। অতএব শুরু হলো চা আলু-পরোটা পর্ব।
পেটের আন্দোলন শান্ত করতে করতে লক্ষ করলাম দোকানেই দোকানির ঘরসংসার। হাঁড়িকুড়ি, বিছানাপত্তর সবই এমনভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে তোলা হয়েছে যে দিব্বি বাড়তি চারজনের বসার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। খদ্দেররা কেউ আমাদের মতো চা আলু-পরোটার কম্বো নিয়ে ব্যস্ত, কেউ কেউ আবার শুধুই চায়ের চাতক। তবে, একটা ব্যাপারে সবাই এককাট্টা — চায়ের তিন চামচের কম চিনি খেতে কেউ রাজি নয়। দেখেই তো আমার ডায়াবেটিস মাথায় উঠে নাচতে শুরু করে দিয়েছে।
ওদিকে, ঘড়ির কাঁটা তো আর থেমে নেই, সাড়ে ন-টার ঘর ছোঁবার তাল করছে। অগত্যা গাত্রোত্থান করতেই হলো। ‘হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল’, থুড়ি, ‘কদম কদম বঢ়ায়ে যা’ বলে পথে পা রাখলাম। একটা অস্থায়ী লোহার পুল পেরিয়ে পাথর বাঁধানো মসৃণ পথে পা বাড়ালাম। কদম কদম ক-দম বাদেই ঢিকুস ঢিকুস হয়ে গেল। সাড়ে দশটা বাজতে না বাজতে শীত উবে গিয়ে ঘামের আবির্ভাব। ব্যস, জ্যাকেট খোলার নাম করে খানিক বিশ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্রাম পনেরো মিনিট যেতে না যেতে, পাহাড়ী পথে (তা যতই চকচকে আর মসৃণ হোক না কেন) ভুঁড়ি বড় বালাই। ঘোড়ায় চড়া গুজরাতিরা তো বটেই, পায়ে হাঁটারাও আমাদের পেরিয়ে গেল। আবার পনেরো মিনিট যেতে না যেতেই বেঞ্চির আকর্ষণ এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। এভাবেই চলল বিশ্রামের রেকারিং ডেসিমেল। আমাদের কীত্তি দেখে মন্দাকিনী তো হেসে খুন। ফিরতি পথের যাত্রীরা জানিয়ে দিল, ‘চলিয়ে চলিয়ে, আভি বহোত দূর হ্যায়।’ একজোড়া বাঁদর আমাদের বিশ্রামের বহর দেখে বিরক্ত হয়ে পাহাড়ের বাঁকে মুখ লুকোলো।
এই যাত্রার প্রথম মহাবিরতি হলো এগারোটা সাঁইত্রিশে। চড়াইয়ের বাঁকে জঙ্গলচটীর দোকানগুলো দেখা দিল। চায়ের গন্ধ পাবার পর কার সাধ্যি আমাদের নড়ায়! পাক্কা তেইশটা মিনিট চায়ে চুমুক দিয়ে এবং না দিয়ে কাটিয়ে দিলাম ২৩৫০ মি. উঁচু জঙ্গলহীন জঙ্গলচটীর রোদ-ছায়া মেখে।
এতক্ষণে চলার ছন্দ খুঁজে পেয়েছি — শম্বুকগতি ছন্দ। আঁকতে বাঁকতে, চড়তে চড়তে বেলা পৌনে একটায় আবার দোকানের দেখা। তবে হরিষে বিষাদ — চা হবে না। দূর, বাজে জায়গা। অগত্যা রোদ আর ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলেছি। ডানদিকে মন্দাকিনী এখন অদৃশ্য হলেও সশব্দ। সোয়া একটায় একটা বাঁক পেরোতেই নিচে মন্দাকিনী আর সামনে খানিকদূরে বাঁকের মাথায় চায়ের দোকান দেখা দিল — গোটা দুয়েক বাড়িও যেন উঁকি দিল — ভীমবলী। আশ্রয়ের দেখা মিলতেই শরীরের ক্লান্তি এক ধাক্কায় সাতাশ গুণ বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অটল সিদ্ধান্ত — ‘আজ পাদমেকং ন গচ্ছামি’। টেন্ট নয় একেবারে রাজকীয় ‘হাট’-এর বিছানা দখল। মূল রাস্তা থেকে হেলিপ্যাডের গা ঘেঁষে নেমে এলাম কুড়ি পা। তোফা ব্যবস্থা — কয়্যার ম্যাটে ধবধবে চাদর বালিশ কম্বল, গিজার বসানো ঝকঝকে অ্যাটাচড্ বাথ — একেবারে সগ্গোমুখ। তীর্থযাত্রীরা সব এগিয়ে গেল লীনচোলি-র চড়াইয়ের পথে — আমরা খেয়ে দেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে রোদ্দুর পোয়াতে লাগলাম। যে রোদ্দুরকে চলার পথে রীতিমতো শত্তুর মনে হচ্ছিল। সে এখন নরম মনের বন্ধু। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। খানিক উজানে মন্দাকিনী তিন ধাপে লাফিয়ে নেমেছে। তাকে পেরোতে বাঁধা হয়েছে পুল। পুল পেরিয়েই চড়চড়িয়ে উঠেছে পথ। হুই উপরে বহুদূরে লীনচোলির নিশানা। কয়েক পা পিছনের চায়ের দোকানটা অনেকক্ষণ থেকেই টানছিল। সে টান কি এড়ানো যায়! শেষমেশ সেই টানে এসে ঢুকতেই হল দোকানে। চায়ের সঙ্গে পেতে থাকলাম সেই বিধ্বংসী দিনগুলোর খবর। যেদিন কেদারনাথে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা হয়, উনি (দোকানের মালিক) তখন এখানেই। দুর্যোগে, ঘন ঘন ধ্বসের শব্দে সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেননি। মন্দাকিনী তখন রণচণ্ডী — ভীমগর্জনে তার ঘোলাটে জল তাণ্ডবনৃত্য করতে করতে ছুটেছে, চোখের সামনে ধসে পড়ছে পাহাড়; প্রাণ হাতে করে নিচের দিকে ছুটছে মানুষ। অনেকেই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করছে। ভোরে পথের ওপরেই পড়ে মরতে দেখেছেন অনেককে। তারপর আর সাহসে কুলোয়নি — সব ফেলে ছুট মেরেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

ভীমবলী
৬ ই নভেম্বর
সকাল সাড়ে ছ-টায় ঘুম পগার পার। বাইরে উঁকি মেরে দেখি পাহাড়গুলো রাতের আঁধারে সাদা টুপি পরে সাদা মাফলার ঝুলিয়েছে, চা দিয়ে যাচ্ছেতাই ঠাণ্ডাটাকে খানিক চাপা দেওয়া গেল। শুনলাম, এটাই নাকি এ মরসুমের প্রথম তুষারপাত।
সকাল আটটার ঘরে পা দেবার আগেই আমরা পথে পা দিলাম। মহাবলী ভীমের গেরুয়া মূর্তিকে (ওটা ‘দাদা’ হনুমানের মূর্তি বলেও চালানো যায়) দেখে পেরিয়ে এলাম ভীমবলীর ঠিকানা। খানিকদূর যেতেই পথ দিয়েছে থমকে — অনেকটা জুড়ে পাহাড়ের গায়ে সাদাটে ক্ষত — কেউ যেন পাহাড়ের গা-টা খাবলে নিয়েছে। সেখানে যেন কোনওদিন রামওয়াড়া বলে কোনও জায়গা কখনও ছিল না।
পথ এবার নেমেছে নদীর ধারে, নতুন পুলে চড়ে তাকে পার করে চলে এলাম মন্দাকিনীর বাম তীরে। বাঁকা হেসে পথ এবার দৌড়ে দিয়েছে সোজা উপরপানে। এপারে এখনও ছায়া বলে ঠাণ্ডাটা বেশ বেশি। সেই ঠাণ্ডাতেও চড়াই ভাঙতে গিয়ে সাড়ে আটটাতেই গায়ের জ্যাকেট ন্যাপস্যাকে। পাহাড়ের গায়ে তুষারের নকশা — পথের ধারেও বিশ্রাম নিচ্ছে তারা। হাঁফাতে হাঁফাতে দু-জনে উঠে এলাম ছোট্ট লিনচোলি-র চা খাবারের দোকান চত্বরে। দোকানটাকে দেখেই মনে হতে লাগল গত বিশ্বযুদ্ধ থেকে আমরা বুভুক্ষু। চা আলু-পরোটার অর্ডার দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দৃশ্য অবলোকনে মত্ত হলাম। ছাউনির বাইরে থমকে আছে বরফ। দোকানের ছাদে, সেনাবাহিনীর তাঁবুর মাথায় গায়ে সর্বত্র বরফের উপস্থিতি।
সকাল ন-টা পাঁচে বসেছিলাম। পাক্কা কুড়ি মিনিট খেয়ে বসে দেখে কাটিয়ে দিলাম। আমরা থেমে থাকলেও পথ ঘোড়ার খুরের আর মানুষের পায়ের শব্দে মুখর। এবার তাতে যোগ দিলাম আমরাও। আবার চড়াই। পথের ধারের ঝোপগুলো তুষারের পাউডার মেখে সেজেগুজে বসে রয়েছে। উলটোদিকে পাহাড় (আগেকার যাত্রাপথ) রোদ পড়ে ঝলমল করছে। একটা হেলিকপ্টার দামী পুণ্যার্থীদের নিয়ে উড়ে গেল কেদারের উদ্দেশ্যে। কেদারশৃঙ্গের মাথায় মেঘেরা বিশ্রাম করছে। নিচে বাঁধানো পথ ধরে আমাদের মতো কিছু পদাতিক আর অনেক অশ্বারোহী চলেছে কেদার জয়ে। এদের নোংরা করে যাওয়া পথটাকে ঝাঁট দিয়ে, ময়লা সরিয়ে পরিষ্কার করে চলেছেন একদল সাফাইকর্মী — বিকট ঠাণ্ডা সহ্য করেও। তাঁদের কুর্নিশ জানিয়ে মুখে হাসি ফোটাবার ভান করে উঠে চললাম দু-জনে।
বা-বা-বা — মুখে পিঠে রোদ পড়ছে। পুরোনো পথে গরুড় চটি চোখে পড়ছে — একেবারে অক্ষত; শুধু দু-পাশের পথ অদৃশ্য। যেন কোনও জাদুকর মন্ত্রবলে কোলাহলমুখর জনপদকে নিথর স্তব্ধপুরীতে বদলে দিয়েছে। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি আশ্রম বাড়িঘর গুলো ফিরে পাবে জীবনস্পন্দন, হয়ে উঠবে মুখর। একটা বাঁকে এসে এসব স্বপ্নালি ভাবনার জাল ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। পথ এখানে মোচড় মেরে নেমেছে — শেষবেলায় ছ-টা ধাপ। ধাপগুলোর ওপর শক্ত বরফের পুরু আস্তরণ — পপাত চ মমার চ হওয়ার সম্ভাবনা অতীব উজ্জ্বল। পাকা সহিস থাকা সত্ত্বেও ঘোড়ারা বেঁকে বসেছে। ওইটুকু পার করতে পারলেই কিন্তু নির্বিকার নির্বিষ পথ। ... যা হোক, জ্যান্ত অবস্থাতেই পেরিয়ে এলাম — পিছন ফিরে দেখার আর সাহস হলো না। পা হড়কালেও পতন রোধ করা গেছে, মাথার ওপর জমে থাকা ঝরনাটাও ভেঙে পড়েনি — জয় বাবা কেদারনাথ।
বাঁক ঘুরতেই উপরে দেখা মিলল লিনচোলির। চড়াই এখানে প্রায় ঈগলপাখি। কোনওমতে নিজেদের টেনে তুলে গুঁজে দিলাম চায়ের দোকানে। গোটা লিনচোলি সোনালী রোদ্দুর মেখে হাসছে। চালের ওপর জমে থাকা বরফেরা থপ থপ করে লাফিয়ে নামছে মাটিতে। GMVN-এর কটেজগুলো লোভনীয়ভাবে ডাকছে। কিন্তু, এখন তো বেলা এগারোটাও বাজেনি। পঁচিশ মিনিট মনে মনে তর্কবিতর্ক করে এগোনোর সিদ্ধান্তই বহাল রাখলাম আমরা। লিনচোলি ছাড়াতেই পথ আরও ঊর্দ্ধমুখী হলো — চার বাঁকেই উঠে এলাম শ-খানেক ফুট। চড়াইয়ের বহর দেখেই বোধহয় ঘোড়ারা তাদের তিনমনী সওয়ারদের নামিয়ে দিয়ে ঘাড় পিঠের ব্যথা কমাতে রোদ্দুর মেখে ঘাস খেতে লেগেছে। অতএব, সব যাত্রীই এই মুহূর্তে পদাতিক। এখন এই পথকে নির্দ্বিধায় পাকদণ্ডী (আসল শব্দটা ‘পগদণ্ডী’ পায়ে চলা পথ বলে) বলা চলে। আর একটা হেলিকপ্টার কেদারমুখী। হাঁফাতে হাঁফাতে, থামতে থামতে চড়াই ভাঙছি। আস্তে আস্তে চড়াইটা সহনীয় হয়ে আসছে। পৌনে একটায় উঠে এলাম পথের মাথায় — ছোট্ট একটা সেনা পরিচালিত চা-ঘর। চা-টা দেবভোগ্য মনে হলো, যখন জানলাম চায়ের পয়সা লাগবে না। এটা সেনাদের সেবা — গ্লাসটা অবশ্য ধুয়ে রাখতে হোলো।
কয়েক পা এগোতেই চোখ পড়ল, একটা ভাঙা ‘উদ্ধারকারী’ হেলিকপ্টার সেই ভয়ানক বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়ে অসহায়ভাবে ঘাড় গুঁজড়ে উলটোদিকের পাহাড়ের গায়ে পড়ে রয়েছে। তাকে সাক্ষী রেখেই হেলিকপ্টারের যাতায়াত অব্যাহত।
এসে পড়েছি ‘কেদারনাথ বেস ক্যাম্পে’-এ (৩৭৫২মি: )। একে এখনকার দেওদেখনি বলা চলে, কারণ এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি কেদারনাথের মন্দির। বেলা এখন সোয়া একটা। চলার গতি আপনিই বেড়ে গেল; পথও অবশ্য সমতল। একটা হলুদ ঠোঁটের ‘চাফ’ খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডানদিকের ঢালে কিছু ঘোড়া চরছে। বেসক্যাম্পের কটেজগুলোর আহ্বান নস্যাৎ করে ‘বীরদর্পে’ এগিয়ে চললাম। শেষ পথটুকু উৎরাই — ঠিক একটা চল্লিশে হাজির হলাম হেলিপ্যাডের গায়ে কেদারনাথের রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার-এর সামনে। (৩৫৮৯মি: )। ডানদিকে কিছু অস্থায়ী দোকান — চা-খাবার থেকে পূজা সামগ্রী, সব কিছুরই পসরা সাজানো সেখানে। এমনকী পোশাক, গরম পোশাক, জুতোও পাওয়া যাচ্ছে। পাশে ঘোড়া ভাড়ার ব্যবস্থাও আছে। ডানদিকে ওপর দিকে তাকালে মেঘ ছুঁয়ে রক্তিম আর গেরুয়া নিশানে সাজানো ভৈরব শিলা। বাঁদিকে মন্দাকিনীর ওপারে ক্ষতবিক্ষত পুরোনো পথের ওপর পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি। আশ্চর্যজনকভাবে কিছু মানুষের আনাগোনা চোখে পড়ছে — সম্ভবত এখানে কর্মরত মজুরেরা ওই বাড়িগুলোকে আস্তানা হিসাবে বেছে নিয়েছে। হেলিপ্যাড আর ক্যান্টিন পেরোলেই সার সার আধুনিক তাঁবু সাদা ফুলের মতো বিছিয়ে রয়েছে। আরও একটু বিলাসবহুল কটেজও রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখন তথ্যচিত্র বানিয়েদের দখলে; তাই তাঁবুরই দখল নেওয়া গেল। বাঙ্ক-সিস্টেম দশজনের শোবার ব্যবস্থা প্রতি তাঁবুতে। ম্যাট্রেস চাদরের ওপর দুর্দান্ত স্লীপিং ব্যাগ। (১১৭৫৫ ফুটে দারুণ ব্যবস্থা)। মালপত্র রেখে কাকা-ভাইপোতে বেরোলাম কেদার-টহলে। চমৎকার বাঁধানো পথের দু-পাশে পুনর্গঠনের লড়াইয়ের ছবি। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে কেদারকে আবার গড়ে তোলার যজ্ঞ চলছে অবিরাম। মন্দাকিনীতে যেখানে সরস্বতী এসে পড়েছে, সেখানে মজবুত অস্থায়ী পুল তৈরি হয়েছে — নিচ দিয়ে ভীমগর্জনে বয়ে চলেছে সরস্বতী ছিন্নমস্তার মতো মহাবেগে। আজই এর এমন রূপ, সেদিন না জানি সে কেমন প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করেছিল! তার বুকে, দু-ধারে পড়ে থাকা ভীমকায় বোল্ডারগুলো তার সাক্ষ্য বহন করছে। সেই দোতলা সমান মাটি পাথরের স্তূপ সরিয়ে, গুঁড়িয়ে তার ক্রোধকে প্রশমিত করার চেষ্টা চলছে। নদী পেরোতেই ডানদিকে প্রথমেই চোখে পড়ল GMVN-এর টুরিস্ট লজটার কোমরভাঙা চেহারা — তারও চিকিচ্ছে চলছে। সোজা মন্দিরমুখী পথের দুধারে এই দু-বছর পরেও হাড়ভাঙা দ-য়ের মতো অষ্টাবক্র মুনি হয়ে পড়ে রয়েছে অসংখ্য ধর্মশালা — তাদের একতলাটা পুরোপুরি মাটির তলায়। অর্থাৎ পুরোনো কেদারের জমির তুলনায় এখনকার জমি অন্তত দশ ফুট উঁচু। অধিকাংশ বাড়িই পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপ, বেশ কিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন; কিছু কিছু কোমায় — মৃত্যুর প্রহর গুনছে। সব ক-টাতে এখন আঁধার আর তুষারের বাস। দু-তিনটে ধর্মশালা টিমটিম করে তাদের দরজা খুলেছে আর পথের দুধারে কয়েকজন পূজা-সামগ্রীর পসরা নিয়ে বসেছে।

কেদারনাথ মন্দির চত্বর
রাত বাড়ছে, শীতও বাড়ছে। তাপমাত্রা শূন্য ছুঁই ছুঁই। তাই সোয়া সাতটার ‘গভীর রাতে’ ডিনার সুসম্পন্ন করে তাঁবুস্থ হলাম দুজনে। স্লীপিং ব্যাগের আরামে রাতও মন্দ কাটল না। শুধু কত রাতে কে জানে, ঘুম ভেঙে গেলে দেখলাম (অবশ্যই টর্চের আলোয়) মাইনাস দুই — তাঁবুর ভিতরেই!
৭ই নভেম্বর; ২০১৫
ভোররাত পৌনে চারটে — তাঁবুর বাইরে বেরোতেই পা পিছলালো — ভারগ্লাস জমে গেছে কংক্রিটের চত্বরে। মাইনাস তিনের থাপ্পড় খেতে খেতে বায়ো টয়লেটের দিকে এগোলাম। বাইরের পলিথিনের ড্রামে রাখা জলে মগ ডোবাতেই — ঠক্। জল জমে বরফ। অব ক্যয়া হোগা? মান বাঁচালো একটা পাইপের বহতা জলের ধারা। বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা হলেও জল তো!
ফিরে এসে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত স্লীপিংব্যাগে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। তারপর উঠে জোব্বাজাব্বা চাপিয়ে স্লীপিংব্যাগ গুটিয়ে ফেললাম। লোকজন উঠতে শুরু করেছে। মন্দিরের দিকে রওয়ানাও দিয়েছে বেশ কিছু ভক্তিমান। আমরা দুই অভক্তির পাহাড় চায়ের খোঁজে ছোঁকছোঁক করতে লাগলাম। মাইনাস দুইয়ের ঠাণ্ডায় কালিয়ে যাওয়ার আগেই চা জুটল, প্রাণ জুড়োলো। ভোরও রাতকে ঠেলেঠুলে ভাগিয়ে দিল। সাড়ে ছ-টায় সুয্যিমামা কেদার সুমেরুদের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিল। সোয়া সাতটা থেকেই শুরু হয়ে গেল হেলিকপ্টারের আনাগোনা। সূর্যকিরণের উষ্ণ পরশে হেলিপ্যাডের বরফ গলে জল। পায়ে পায়ে আর একবার মন্দির দেখে এসে ঢুকলাম ব্রেকফাস্টের খোঁজে। উদরপূর্তির শেষে আটটা কুড়িতে এবারের মতো কেদারের থেকে বিদায় নিলাম। মন ফিরে চলো ... ইত্যাদি ইত্যাদি।
(পরবাস-৬৪, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)