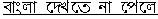যামিনী কলকাতা সংলাপ সঞ্জয় ঘোষ; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৮; অভিযান পাবলিশার্স - কলকাতা; প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস, পৃষ্ঠাঃ ১৯১; ISBN: 978-93-87575-16-5
যামিনী কলকাতা সংলাপ সঞ্জয় ঘোষ; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৮; অভিযান পাবলিশার্স - কলকাতা; প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস, পৃষ্ঠাঃ ১৯১; ISBN: 978-93-87575-16-5
বইয়ের নাম ‘যামিনী কলকাতা সংলাপ’, তার উপরের পঙ্ক্তিটিতে পাঠকের চোখ আটকে যায় ‘যামিনী রায়ের জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস’। শিল্পরসিকমাত্রেই ‘যামিনী রায়’ নামটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, যাঁরা চিত্রশিল্প নিয়ে চর্চা করেন না তাঁদের কাছেও যামিনী রায় নামটি অপরিচিত এমন না-ঘটাটাই স্বাভাবিক যদিও পাশাপাশি এ-কথাটাও বলে দেওয়া ভালো এর অন্যথা ঘটলে তা তেমন বিস্ময় নাও জাগাতে পারে! বইয়ের পিছনে ব্লার্বে লেখা আছে এই কথাগুলি: ‘সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনুগামী কবি নরেশ গুহকে বলেছিলেন, ‘শিল্পী যামিনী রায়ের জীবনী লেখ।‘ তারই ফসল নরেশবাবুর রচনা ‘যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর’। যামিনী রায়ের শিল্প অপেক্ষা তাঁর জীবন অনেক বেশি আকর্ষণ করেছিল বুদ্ধদেব বসুর মতো বিদগ্ধ, মরমী সাহিত্যিককে, সংবেদী মানুষকে।
মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয় উপন্যাসের আয়নায়। সে আয়নার মুখোমুখি দাঁড়ালে পাঠক তথা মানুষের নিজের সঙ্গেই যেন দেখা হয়, তাকে ঘিরে থাকা সামাজিক প্রতিবেশ, নানা চেনা-অচেনা মানুষ, জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সব মিলিয়ে ঔপন্যাসিক বা কথাকারের সৃজিত বিশ্বে পাঠক অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারেন। লেখার জোর পাঠককে টেনে নিয়ে যায় লেখকের কথনবিশ্বে। আসলে উপন্যাসের অন্দরমহলে প্রবেশ করে মানুষ নিজেকেই আস্বাদন করতে চায়। বাংলা কথাসাহিত্যের সেই প্রথম সার্থক কথাকারের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল ‘এই জীবন লইয়া কি করিব? কি করিতে হয়?' – তা আজও নিয়ত তাড়িত করে একজন ঔপন্যাসিককে। জীবন বড়ো রহস্যময়, মানবজীবন-প্রবাহের কতটুকু আমাদের ‘ব্যক্তি আমির’ কাছে স্পষ্ট হয়? সব উপন্যাসই মানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। যা সে দেখায় তা হয়তো তত সহজ নয়। উপন্যাসের কাছে সবচেয়ে বড়ো রহস্য বলা যেতে পারে মানুষের ব্যক্তিত্বের রহস্য। আর সেই ব্যক্তিত্ব যদি হন যামিনী রায়ের মতো সেলিব্রিটি। লেখক সঞ্জয় ঘোষ তাঁর উপন্যাসে পরিচিত শিল্পী যামিনী রায়ের অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা মানুষটিকে আবিষ্কার করতে চান – সে উদ্দেশ্য তিনি গোপন রাখতেও চান না। তাই ব্লার্বে আর-একটি পঙ্ক্তি পাঠকের চোখ টেনে নেয়। সেই পঙ্ক্তিটি হল ‘বাঙালি যামিনী রায়ের ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে, অথচ তাঁর জীবনের আলো-অন্ধকার, উত্থান পতনের, ডাইকোটমির সন্ধান করেনি তেমনভাবে।'
সেই সন্ধানেই এই কথাশিল্পের অভিযাত্রা লেখক শ্রী সঞ্জয় ঘোষের। মোট ষোলোটি অধ্যায়ের পরিসরে অনন্য এক চিত্রশিল্পীর জীবনের জানা-অজানা বৃত্তে আলো ফেলেছেন লেখক, দুটি চরিত্র নগর কলকাতা ও যামিনী রায়ের সংলাপের প্রবাহে কোথাও কোথাও স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি যেন দুটি চরিত্রের জীবনের অজানা অনেক কিছু পাঠকের কাছে এনে হাজির করে যা স্বতন্ত্র এক আঙ্গিকের আস্বাদন যোগায়। তাদের দেখা ঘটনা, নানা স্মৃতি, নানা চরিত্রের উপর সন্ধানী আলো পড়ে যা থেকে পাঠকের মনেও কোথাও কোথাও প্রশ্নের জন্ম নেয়। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমকালীন শিল্পসংস্কৃতিচর্চার আবহ বা এক চালচিত্র যেন এই উপন্যাসের শরীরে রংয়ে-রেখায় আভাসিত হয়ে উঠেছে।
ধারাবাহিকতা উপন্যাসের একটি শর্ত তবে সে ধারা মাঝে মাঝে উজানে যে বইবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফ্ল্যাশব্যাকে উপন্যাসটির সূত্রপাত ঘটেছে। ‘রঙিন কাচলন্ঠন ও মহামানব’ – এই নামে কাহিনির যে মুখপাত ঘটে তাতে পাঠক খানিক এগোলেই জানতে পারেন এই ‘মহামানব’ অন্য কেউ নন, বাংলা সংস্কৃতির অপরিহার্য আইকন রবীন্দ্রনাথ। এই উপন্যাসেও কথনসূত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে, আসাটাই স্বাভাবিক। কেন না সে এমন এক সময় যা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায় ‘সম্মুখে থাকুন ব’সে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর’ – শিল্পসাহিত্যসংস্কৃতির চর্চায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু শিল্পীও তো রক্তমাংসের মানুষ, দোষগুণ নিয়েই তার সম্পূর্ণতা, রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। এই উপন্যাসের দুটি চরিত্রের কথাবার্তার মাঝখানেও এসেছে রবীন্দ্রনাথের নানা স্ববিরোধিতার কথা। এর কারণ হিসেবে কলকাতা চরিত্রটির মুখে সংলাপ শোনা যায় ‘রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না, আমার গুণ ইনকনসিসটেন্সি, আমার দোষ ইনকনসিসটেন্সি’। বস্তুত এই ‘ইনকনসিসটেন্সি’ উনিশ শতকের অনেক মহামানবের ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হয়েছে অনেক পাঠকেরই তা জানা। এরকম ডাইকোটমি যামিনী রায়ের জীবনেও আছে তারও বেশ কিছু ইঙ্গিত উপন্যাসের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে।
পেশায় খ্যাতনামা ত্বক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-লেখক সঞ্জয়বাবু শিল্পের নানা আঙিনায় ভ্রাম্যমাণ একথা কারও কারও জানা। তার পাশাপাশি আর একটা খবরও জরুরি, তা হল চিত্রকর হিসেবেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি আছে। একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি যেমন এই উপন্যাসে যামিনী রায়ের পূর্বাপর শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস আকারে-ইঙ্গিতে, ঘটনার উল্লেখে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই শিল্পচর্চার আড়ালে লুকিয়ে-থাকা সূক্ষ্ম রাজনীতিকে। ছবি আঁকার শিল্পকলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যরীতি, কোথাও এই দুইয়ের মেলবন্ধন, কোথাও বৈচিত্র্যের আস্বাদন--সবকিছু নিজের মতো করে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক নিজেও একজন চিত্রশিল্পী বলে।
নানা প্রতিকূলতায়, জীবনসংগ্রামে একজন শিল্পী কীভাবে বিশিষ্ট শিল্পী হয়ে ওঠেন তার একটি রূপরেখা এই উপন্যাসে এঁকেছেন লেখক। চলমান জীবনের নানা ঘটনামুহূর্ত, সুখ-দুঃখ, অপ্রাপ্তি-বেদনা, গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন, মূল্যবোধ, আদর্শ আরও অনেক কিছুর মুখোমুখি যেমন হয় সাধারণ মানুষ, যামিনী রায়ও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর সময়, সমাজ ও ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ ব্যক্তিগত অনুভবসমেত কথোপকথনে ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসের মধ্যেও ব্যয়িত এক সময় স্তব্ধ হয়ে আছে যার সঙ্গে লেখক সমকালীন কিছু শিল্পীব্যক্তিত্ব, কিছু ঘটনার উল্লেখে চলমান সময়প্রবাহের সঙ্গে অন্বিত করে দেন। যামিনী রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে কান পাতলে আমরা শুনি:
কলকাতা : ট্রামকে যদি তুমি সহ্য করতে না পার আমার এ যুগের যানবাহনকে তুমি সইবে কী করে? ট্যাক্সি, অটো, ওলা, উবের, মেট্রো? মেট্রোতে তো কত আত্মহত্যা হচ্ছে রোজ!যামিনী : আমি পারতাম না ... একেবারেই পারতাম না। তুমি বিশ্বাস করবে না আমি বাড়িতে টেলিফোন অবধি ধরতে পারতাম না, অসহ্য লাগত ... রাখতেই চাইতাম না ... কিছুটা ক্রেতাদের তাড়নায় রাখতে হয়েছিল। (পৃ. ২৯)
অথবা,
কলকাতা : তোমার পরের যুগে গণেশ পাইনেরও হয়তো এই ফ্যাক্টরটা কাজ করেছে?এই উপন্যাসের লেখকের কৃতিত্ব এইখানে যে যামিনী রায়ের মতো সময়ান্বিত ব্যক্তিকে, শিল্পীকে উপন্যাসে প্রতিষ্টিত করার প্রচেষ্টার কোনো বাঁধাধরা পথে চলেন নি, নাটকের মতো সংলাপের মধ্য দিয়েই তিনি বার করে আনতে চেয়েছেন বাইরের পৃথিবীর কাছে অচেনা, অজানা মানুষটিকে। শৈশব-কৈশোর – প্রথম যৌবনের দিনগুলি জন্মস্থান বেলিয়াতোড়ে কাটলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শহর কলকাতার ‘ইভাক্যুয়েশন’-এর সময় মাস ছয়েকের কথা বাদ দিলে বাকি জীবনে শহর কলকাতা ছেড়ে সেখানে যান নি বললেই চলে। তার একটা বড়ো কারণ সেখানে গেলে তিনি কিছু আঁকতে পারতেন না। অথচ শৈশবে সেখানের কুমোরপাড়ায় মূর্তি বানানো দেখা, পটুয়া-পাড়ায় পট আঁকা দেখতে দেখতে শিল্পচর্চায় হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। তাই পাঠশালায় হাতের লেখার খাতায় ছবি আঁকা, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পুকুরপাড়ে বসে ভিজে মাটি দিয়ে মূর্তি বানানো; লাল, হলদে, খয়েরি রঙের গেরিমাটি দিয়ে পুকুরপাড়ে মাটিতে ছবি আঁকা, বাবা রামতারণ রায়ের সঙ্গে বাড়ির কাছেই বৈঠকখানার বাড়িতে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাল সাদা নীল প্রভৃতি নানা রঙের পাথর কুড়িয়ে ঘরের মেঝের ওপর নানা জন্তু জানোয়ারের ছবি এঁকে সেই রঙিন পাথরগুলি দিয়ে তাদের গা-ভরাট করা ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখে ভাবীকালের এক বিরাট শিল্পীর সৃষ্টিরহস্যের প্রথম পাঠপর্বটি পাঠকের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামীণ প্রথায় ছবি আঁকা রপ্ত করে পরবর্তীকালে কলকাতায় আর্ট কলেজে তিনি ইওরোপীয় প্রথায় অ্যাকাডেমিক আর্ট শিক্ষার চর্চা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভিতরে গ্রামীণ সত্তাই পরবর্তীকালে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; লৌকিক পদ্ধতিতেই তিনি ছবি এঁকেছেন। পিকাসো, মাতিস, ভ্যান গঘ-এর মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায়। অথচ শিল্পচর্চার মাধ্যম হিসেবে গ্রামীণ পদ্ধতি প্রাধান্য পেলেও অন্তরে তিনি নাগরিক পরিমণ্ডলেই স্বস্তিবোধ করেছেন।যামিনী : হ্যাঁ গণেশের ছবিতে ভারতীয় শিল্প অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও ও নিজেও তো অ্যাকাডেমিক আর্টের স্টুডেন্ট ছিল। ইন্ডিয়ান আর্ট নিলে হয়তো ওর হাত আর চোখটা ততটা খুলত না। যোগেনের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। ওর রেখা বা ফর্মের যে ভঙ্গি তাতে ভারতীয়তাই মূল চাবিকাঠি, তবুও ইউরোপীয় আর্ট না শিখলে ওই জায়গাটায় পৌঁছতে পারত না। (পৃ. ৬৭)
অথচ এর বিপরীত ঘটেছিল তাঁর বাবার জীবনে। শহরের চাকরি ছেড়ে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন সেই আমলের অজ পাড়া-গাঁ বেলিয়াতোড়ে। সচ্ছলতা থাকলেও স্ব-ইচ্ছায় গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষবাস, তুলোর চাষ করে তা থেকে সুতো তৈরি, গ্রামের তাঁতিদের দিয়ে পরনের কাপড় তৈরি, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারের জন্য সরষে থেকে সরষের তেল, তিল থেকে তিলের তেল তৈরি করে নেওয়া, গবাদি পশুপালন, বাড়ির কাছেই জঙ্গল এবং সেখানে বসবাসকারী হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে গোরু-মোষগুলিকে বাঁচানোর জন্য অস্ত্র হাতে গোয়ালে শুয়ে রাত-কাটানো একটি আশ্চর্য মানুষকে যেমন আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে আবার পাশাপাশি একথা জেনেও আমরা অবাক হয়ে যাই সেই মানুষটাই চাষি-বাউরিদের আঁকা শেখাতেন, পেনসিলের অভাবে নখ দিয়ে ড্রয়িং করাতেন। সেই আমলে সেই মানুষটা বিশ্বাস করতেন ‘আমাদের ভারতীয় সভ্যতা, তাতে আমাদের এক হাতে থাকবে বই, আর-এক হাতে লাঙল’। উপন্যাসে কথা প্রসঙ্গে বই আর লাঙল – এই দুই-ই ধরতে না পারার আক্ষেপ যামিনীর কন্ঠে ঝরে পড়লে লেখক কলকাতা চরিত্রের সংলাপে আশ্চর্য এক পঙ্ক্তি রচনা করেছেন : ‘তুমি লাঙল হাতে নাওনি ঠিক, কিন্তু তোমার হাতের তুলিটাকে তো তুমি লাঙলের মতোই ব্যবহার করেছ।’ জীবন ও শিল্প – দুইকেই কর্ষণ করেছেন যামিনী রায়।
উত্তরাধিকারসূত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার এই মনোভাব হয়তো পিতার কাছ থকে অর্জন করেছিলেন যামিনী রায়। সারাজীবন দারিদ্র্যকে তিনি ভয় পেয়েছেন। পরমুখাপেক্ষী হওয়াটা তাঁর না-পছন্দ ছিল। তাই সে আমলে তাঁর দাদা শৌখিন, সম্পন্ন ব্যবসাদার হয়ে শহর কলকাতায় গাড়ি-বাড়ি করলেও তিনি তাঁর আশ্রয়ে যান নি। দাদার ব্যবসায়ে মজুরির বিনিময়ে কাজ করেছেন। আর্ট কলেজের প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর বাবা আস্থাশীল ছিলেন না সে কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত অনুমতি দেন নি তাঁর শ্যালক (যামিনী রায়ের মামা) চারুচন্দ্র দত্তের অনুরোধেও। ছোটোবেলায় যে মামার উৎসাহ ও স্নেহের আশ্রয় শিল্পী যামিনীকে এগিয়ে দিয়েছিল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনগুলির দিকে তিনি বিশ্বাস করতেন যামিনী একদিন বিরাট বড়ো শিল্পী হবেন। বাঁকুড়ার একটি শিল্প প্রদর্শনীতে ‘সমাজ’ নামে একটি ছবি বাবাকে লুকিয়ে পাঠালে সেই ছবিটি উচ্চ-প্রশংসিত হয় এবং তৎকালীন জেলাশাসকের অনুরোধে যামিনী রায়ের জ্যাঠামশায় তাঁর বাবাকে কলকাতার আর্ট স্কুলে শিক্ষার কথা বললে তিনি নিমরাজি হন। যামিনীর কলকাতায় আসা স্থির হয়।
মানুষের জীবনপথের মাঝখানে কোন্ সঠিক বাঁকটি কোথায় লুকিয়ে থাকে তা মানুষ জানে না। যামিনীরও তা জানা ছিল না। বেলিয়াতোড় থেকে ন্যারোগেজ ট্রেনে, তারপর ব্রডগেজ ট্রেনে নগর কলকাতায় আসার মাঝখানে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের রঙবদল, বিষয়, পটভূমির বদল-- জানালার ফ্রেমের মধ্য দিয়ে বাইরের দৃশ্য যেন ফটোকপি হয়ে মনের মধ্যে চিরকালীন স্থান নেওয়া, আবার সেই বিশাল দৃশ্যের কতখানি ছবি আঁকার সময় ব্যবহার করা যেতে পারে তা স্থির করা-- শিল্পের আভ্যন্তরীণ সূক্ষাত্মিসূক্ষ্ম এইসমস্ত শিল্পকৌশল সেই বয়সেই তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই কলকাতা চরিত্রটি সাদৃশ্য খুঁজে পায় ভাস্কর হেনরি মুরের ইয়র্কশায়ার থেকে লন্ডন যাত্রার ছবির। এইরকম অনেক ছোটোখাটো ঘটনা, অনুভূতির উল্লেখ আছে এই উপন্যাসে যা একজন প্রথিতযশা শিল্পীর প্রতিষ্ঠা পাবার সংগ্রামকে, তাঁর শিল্পভুবনের দর্পণে প্রতিফলিত নানা ভাবনা, খ্যাতির আড়ালে লুকিয়ে-থাকা একটি রক্তমাংসের মানুষকে পাঠকের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।
প্রথাগত উপন্যাসের চলন এই আখ্যানের নয়, সেই চলনে উপন্যাসটিকে লেখক বাঁধতেও চান নি। যামিনী রায়ের মতো একজন শিল্পীর জীবনের নানা খণ্ড-মুহূর্ত উঠে এসেছে এই উপন্যাসে যা ক্যানভাসে আঁকা এক কোলাজের মতো। মানুষ হিসেবে বিভিন্ন সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা, সৃষ্টির প্রেরণা, সীমাহীন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর ভাবনা, পিতা রামতারণ রায়ের জীবনাদর্শ, বিধবা বোন সুজনকুমারীর সে যুগে একা বেলিয়াতোড়ের মতো গ্রামে বসবাস ও বিরুদ্ধ পরিবেশের, প্রতিবেশীর সঙ্গে লড়াই করে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন স্বাবলম্বী মানসিকতার পরিচয়। আর্টের টিচার হওয়া বা চাকরি না করার মনোভাব থেকে শেষ পর্যন্ত আর্ট কলেজের ডিগ্রি না নেওয়া, সমকালীন থিয়েটার ও শিল্পচর্চার সঙ্গে যোগ, আর্ট কলেজ ছাড়ার পরে বিডন স্ট্রিটে হেমেন মুজমদারের বাড়ির আড্ডায় প্রায় নিয়মিত যাওয়া ও শিল্পীবন্ধুদের সঙ্গে শিল্প নিয়ে, ছবি নিয়ে আলোচনা, অবনীন্দ্রনাথের নিউ-বেঙ্গল আর্ট ও হেমেন মুজমদারের অ্যাকাডেমিক পদ্ধতি— দুইয়েরই ছবিতে গল্প বলার প্রচেষ্টা অথচ ছবির নিজস্ব কোয়ালিটি নিয়ে তাঁদের ভাবনার অভাব, পাশাপাশি যামিনী রায়ের ছবি বিষয়ে ভাবনা যা তাঁর ভাষায় ‘সিগনিফিকেন্ট ফর্ম’ বা ছবির বক্তব্যকে ছবির ফর্মের মধ্য দিয়েই তুলে ধরবে, ‘পরিচয়’ পত্রিকায় বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী লেখক-কবি-শিল্পীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ, রবীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে সান্নিধ্য, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীর ধর্মতলার কার্যালয়ে কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে যাতায়াত, অসুস্থ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্য অর্থসংগ্রহে আয়োজিত নাটকে শিল্পনির্দেশনা— এমন বহু ঘটনা, অনুভূতি ভিড় করে এসেছে এই উপন্যাসে যা একটা অদৃশ্য ক্যানভাসের মতো এই উপন্যাসকে জড়িয়ে রেখেছে। ধরে রেখেছে গত শতকের একটা বিশেষ সময়পর্বের রাজনীতি, শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ তাপ যা উপন্যাসটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা যায়। তাই মাত্র দুটি চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপ বয়নে উপন্যাসের নকশি কাঁথাটি বোনা হলেও তাঁদের কথাবার্তাকে ঘিরে রয়েছে অনেক ঘটনা ও চরিত্র যা উপন্যাসোপম খানিক তৃপ্তি দেয়।
পারম্পর্য বজায় রেখে উপন্যাসে যেভাবে আখ্যানভাগ নির্মাণ করা হয়ে থাকে, চরিত্রের পরিস্ফুটন হয়ে থাকে, চরিত্রগুলি যেভাবে ঘটনার সম্মুখীন হয় তাতে তাদের প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত তেমনভাবে এই উপন্যাসে ব্যক্ত হয়নি, সেগুলি রয়ে গেছে লুকোনো হিমশৈলের চূড়ার মতো গোটা আখ্যানটিতে। দুটি চরিত্র উত্তম পুরুষের জবানিতে গোটা উপন্যাসটিতে কথাবার্তা বলে গেছে। একটি মানুষের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অনেক টুকরো টুকরো মানুষ যা সচরাচর অন্যের চোখে ধরা পড়ে না। উপন্যাসের অন্দরমহলের আয়নায় সেই মানুষের ‘আরশিনগরের পড়শি’ মানুষটির দেখা মেলে। পরবর্তীকালে খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে সচ্ছলতা পেলেও আজীবন যামিনী রায় দারিদ্রকে ভয় পেয়েছেন, বাংলা থিয়েটারের প্রবাদপ্রতিম অনেক নট-নটীদের শেষ জীবনে আর্থিক দুরবস্থা, শিল্পী রেমব্রান্টের জীবনের শেষ পরিণতি, আরও নানা অভিজ্ঞতায় মনে জন্ম নেওয়া নিরাপত্তাহীনতাই হয়তো তাঁকে এই অখ্যাতির দোষে দুষ্ট করেছিল। তিনি খুব নিকট বন্ধুদের, পরিচিতদেরও ছবি বিক্রি করে টাকা নিতেন, শেষের দিকে অন্যের আঁকা ছবিতে নিজের নাম সই করে বিক্রি করা— এমন অনেক স্পর্শকাতর অখ্যাতি প্রসঙ্গও এই উপন্যাসে প্রশ্নের আকারে যামিনী রায়ের সামনে এসেছে। তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন।
একসময় বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল যোগেন চৌধুরীর ‘রাবণ’ নাটকের জন্য বড়ো বড়ো সিন এঁকে, তারপর নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের দীর্ঘ সান্নিধ্য ও নিয়মিত বাংলা থিয়েটার দেখা। ‘নাটকের সঙ্গে সঙ্গে’ নামের অধ্যায়টিতে বাংলা থিয়েটারের একদা জনপ্রিয় নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়, অভিনেতা অঘোর রায়, ক্ষেত্র মিত্তির, অভিনেত্রী সুশীলা, কুসুম কুমারী, তারাসুন্দরী, নরিসুন্দরীর স্মৃতিচারণ ও বিখ্যাত সব প্রযোজনার কথা, সর্বোপরি শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারের কথা। আবার এসেছে উদয়শঙ্করের নাচের কথা আবার সে-নাচ প্রথম দিন দেখে মুগ্ধ হলেও পরের দিনই সে নাচ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ‘সাহেবরা যাত্রা শুনতে গিয়েই হাঁক দেয়— ‘হনু-কাঁহা হ্যাঁয়’। এ হচ্ছে তাই’। এর আগে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগঠনের প্রযোজিত ইয়েটস-এর ইংরেজি নাটক থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ ‘পুনরুজ্জীবন’--যা পরিচালনা করেছিলেন বিষ্ণু দে--সেই নাটকে রূপসজ্জায় বিশেষ সহায়তা করেছিলেন যামিনী রায়। আসলে সে সময়ের সংস্কৃতির কুশীলবদের মধ্যে ‘দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে’ এই মনোভাব। সহজ পদ্ধতিতে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার কথা যাত্রা-থিয়েটার-লোকশিল্পীরাই তাঁকে শিখিয়েছিল। বিষ্ণু দে সহ অনেক সমালোচক বলেন মাতিসের ছবি তাঁকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু মাতিসের অনেক আগেই এই প্রাচ্যশিল্পীরাই তাঁকে শিক্ষিত করেছিল। ছবির জটিলতা, পারস্পেকটিভের হেঁয়ালি মুছে দিয়ে ছবিকে বিশুদ্ধ রেখা, ফর্ম আর রঙের সার্থক প্রয়োগে তিনি সাজিয়ে তুললেন। শিল্পী হিসেবে সেদিনের বিখ্যাত অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ‘আমি বেশ্যাদের সাধু বলে মানি’ তার কারণ পেশার ওপর তাদের প্রবল নিষ্ঠা স্বভাবগত বলেই ‘বাবু সামলানোর পাশাপাশি সন্ধ্যায় তারা অভিনয়ের পেশায় লোকের মন ভুলিয়েছে।' নিজের মতো করে ছবি আঁকতে শুরু করার সময় থিয়েটারের জ্ঞান যামিনী রায়কে অনেক সাহায্য করেছে। আবার পাশ্চাত্য-সাহিত্যের জ্ঞানে পারঙ্গম কবি-সাহিত্যিকেরা, যেমন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখের সান্নিধ্য ও আলাপ আলোচনা তাঁকে পাশ্চাত্য শিল্পী, শিল্পকলা বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তিনি মনে করতেন পরিশেষে পৌরাণিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে কেন-না ‘পৌরাণিকের মধ্যে মানুষের কৌমচেতনা গাঁথা হয়ে আছে। ছবিতেও এটা খুব প্রয়োজন’। সেই শিকড়ের সন্ধান তিনি পেয়েছেন যশোদা আর বিন্দুমতীর গানে যাঁরা আদপে পুরুষ কিন্তু নারীকন্ঠে গান গেয়ে বিপুলসংখ্যক শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। তেমনই এক প্রবাদপ্রতিম লোকশিল্পী ছিলেন বর্ধমানের নীলকন্ঠ মুখুজ্জে। খঞ্জ, দন্তহীন হলেও তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে হাজার লোক নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর গান শুনত। এইভাবে এই উপন্যাসে লেখক শ্রী সঞ্জয় ঘোষ বঙ্গসংস্কৃতির এক দীর্ঘ বর্ণোজ্জ্বল লুপ্তপ্রায় ইতিহাসকে পুনরাবৃত্ত করেছেন আজকের পাঠকের কাছে, শ্রোতার কাছে।
প্রথম জীবনে পোর্ট্রেট আঁকায় যামিনী রায়ের বেশ নামডাক হলেও, অর্থোপার্জনের প্রচুর সুযোগ থাকলেও, তিনি পোর্ট্রেট আঁকা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে তিনি শশী হেসের আঁকা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন, এঁকেছেন আরও একাধিক পোর্ট্রেট। সেই মানুষটারই মুখে এই উপন্যাসে শুনতে পাওয়া যায় ‘এই পোর্ট্রেটের ইতিহাস ভুলে যেতে চাই আমি...’। কিছু বাইরের কারণ আর কিছু ভেতরের টানাপোড়েনে এই মাধ্যমে কাজ করা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, চিরাচরিত পোর্ট্রেট আঁকার নিয়ম না মেনে কিছু স্বাধীন ভাবনাও তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সে যন্ত্রণার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে ‘একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে’ নামের অধ্যায়ে। আছে শিল্প বিষয়ে, নানা বিখ্যাত শিল্পীদের কাজ নিয়ে, তাঁর নিজস্ব অনুভব, ব্যাখ্যার কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা শিল্পী প্রসঙ্গে তৃতীয় পথের দিশারি হিসেবে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। শিশুদের ছবি আঁকায় নিজের চার-পাঁচ বছরের ছেলে পটল (অমিয়)-এর ছবির আঁচড়ে মুগ্ধ হয়ে পড়া, পাশ্চাত্যের নানা চিত্রকরের ছবিতেও তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা, বিনোদন-প্রলোভনের হাজার হাতছানি এড়িয়ে দিনভর শিল্পচর্চা যা লক্ষ্য করে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন ‘ব্রত পালনের মতো জীবন’ — একটি মানুষের নিভৃত গোপন সব ভাবনাকে কথোপকথনের মাধ্যমে চমৎকার তুলে ধরেছেন লেখক। এই অধ্যায়টিতে শিল্পী যামিনী রায়, তাঁর শিল্পভাবনা, শিল্পকলা সমালোচনা (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য), বাহ্যিক জীবনের প্রতিকূলতা, অবনীন্দ্রনাথের উপেক্ষা, গগনেন্দ্রনাথের স্বীকৃতি— জানা-অজানা নানা ঘটনা আমাদের বেদনার্ত করে, সে বেদনা ঘুচিয়ে খানিক স্বস্তিও দেয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়েও অনেক কথা আছে এই উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে যামিনী রায়ের বক্তব্য হল ‘সেই ছবি এক অন্য জগতের এবং তার এক ‘সতেজ শিরদাঁড়া’ আছে’।
এই উপন্যাস পড়তে গিয়ে মাঝেমাঝে সদ্যপ্রয়াত বন্ধু, কথাকার রবিশঙ্কর বলের ‘দোজখনামা’-র কথা মনে পড়ছে। যদিও বিস্তৃতির প্রশ্নে রকমফের আছে। দুই বদনসিব আত্মা মির্জা গালিব ও সাদাত হাসান মান্টো পরস্পরের সঙ্গে অনর্গল কথোপকথনে কথা বলে চলেন যেখানে। আখ্যানে ঢুকে পড়ে দুজনের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অপ্রাপ্তি, বেদনা, অসহায়তার দীর্ঘশ্বাস। এই উপন্যাসেও দুটি চরিত্র, কলকাতা ও যামিনী রায়ের ব্যক্তিগত কথোপকথনের সঙ্গে মিশে যায় সমসময়ের আলো-অন্ধকারের কাছে জাফরি-কাটা নকশা। কাল্পনিক সংলাপদষ্ট এই আখ্যান আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় ভারতের শিল্পচর্চার একটি নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের স্পন্দনধ্বনিকে, ব্যক্তিগত একটি মানুষের সুখ-দু:খের পদাবলীকে, তাঁর সীমাবদ্ধতা ও নিজেকে পেরিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে, শিল্পী হিসেবে জীবনের শেষ ছবি ‘লাস্ট সাপার’ বার বার আঁকতে চেয়েও সন্তুষ্ট না-হওয়াকে; মৃত্যুর পরেও আজও এই সময়ে সময়ের কন্ঠস্বরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে যামিনী রায়ের মতো মানুষকে লেখক যে নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকতে চেয়েছেন তাকে সেলাম না জানিয়ে উপায় নেই। এই জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি উৎস হিসেবে যামিনী রায় বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই শ্রমের কোনো বিকল্প নেই, অজস্র সাধুবাদ জানাই লেখককে। এই উপন্যাস যেন আত্মসন্ধানের এক ব্রতকথা, আর তা শুনতে পাঠক বসে পড়েছে কথোপকথনরত দুটি মানুষের মাঝখানে।
এই উপন্যাস নাট্যাত্মক, বিবরণাত্মক নয়। আটপৌরে এক ভাষাভঙ্গির মাঝে যামিনী রায়ের সংলাপে বেশকিছু শব্দ ও ব্যাখ্যা যথেষ্ট গুরুগম্ভীর শোনায় যা একটি মানুষকে খানিকটা যেন দূরের করে তোলে কেন না জীবনের বেশিরভাগ সময় যামিনী রায় নাগরিক পরিমণ্ডলে কাটালেও তাঁর ভিতরে লেগে-থাকা লাল মাটির ধুলো কোনোদিন মুছে যায় নি! এই উপন্যাসেরই ৭০-নং পৃষ্ঠায় যামিনী রায়ের মুখে আমরা শুনি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ, পরবর্তীকালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্সি ব্রাউনের বিদায় সংবর্ধনা সভায় এক পঙ্ক্তির বক্তৃতা ‘আমি ছবি আঁকি, আমি কিছু বলতে পারব নি’। সেই মানুষটিই এই উপন্যাসে অনেক কথা বলেছেন; তা সম্ভবপর হয়েছে এই উপন্যাস কাল্পনিক সংলাপনির্ভর বলেই।
একজন অভিনেতা নিত্যদিন নিজের আত্মকে ভুলে আত্মাকে প্রবিষ্ট করান নানা অভিনেয় চরিত্রের শরীরে, নাটক শেষ হলেই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয় বাহ্যিক জীবনে, আত্ম-র মধ্যে। সঞ্জয়বাবুও নিজেকে বার বার দুটি চরিত্রে প্রবিষ্ট করেছেন-- কখনো যামিনী রায়, আবার পরমুহূর্তেই কলকাতা। চিকিৎসকের নিরাসক্তি, নিরাবেগ চরিত্রনির্মাণে হয়তো কাজে লাগিয়েছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি খানিক সফলও বটে। তবে কথনে কোনো কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি আছে সেটি এড়ানো গেলে খুব ভালো হত। এই ভালো না-লাগাটুকু বাদ দিলে উপন্যাসটি পড়তে বেশ!
(পরবাস-৭০, ৩১ মার্চ ২০১৮)