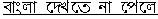Parabaas Moviestore

Parabaas Musicstore

Subscribe to Magazines
পরবাসে
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের
আরো লেখা
জিনিয়া জেনে গেছে, আমি ওকে ভালবাসি। জিনিয়া যে জেনে গেছে, সেটা জানার পর থেকেই আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। এখন কথা হল এই পালিয়ে বেড়ানোটা মোটেই সহজ কাজ নয়। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে জিনিয়াকে দেখেও না দেখার ভান করে দৌড়ে রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলাম। একটা হলুদ ট্যাক্সি ঘাড়ের ওপর ঘ্যাঁচ করে থেমে, জানলা দিয়ে মুখ বার করে কাঁচা খিস্তি দিল... গুঁতিয়েই দিচ্ছিল প্রায়। একটা ট্রাম টং টং করে দু’বার ঘন্টা বাজিয়ে থেমে গেলো। পথ-চলতি দরদ-গেঁড়ে লোকজন এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন কলকাতায় এলিয়েন নেমেছে। আমি কোনোমতে উল্টো ফুটে উঠে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এক এক সময় মনে হয় জিনিয়া আমায় ট্যুয়েন্টি-ফোর-সেভেন ফলো করছে। যেমন আজকে হাওড়া স্টেশনে। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ব্যান্ডেল লোকালে উঠে সবে জানলা ধরে বসেছি, দেখি জিনিয়া ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে। ট্রেনের জানলায় জানলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে কাউকে যেন খুঁজছে। বাধ্য হয়ে পাশের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা তারকেশ্বরের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেলাম। এগারো নম্বর থেকে পাঁশকুড়া লোকাল ছাড়ছিল। চলন্ত ট্রেনে লাফ দিয়ে চড়ে রামরাজাতলায় তন্ময়দার বাড়ি চলে গেলাম। তন্ময়দা আমায় দেখে খুব যে খুশি হল তা নয়। বিরস গলায় বলল, “তোর বৌদি বলছিল ইভনিং শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। তুই কি বসবি?”
আমার বেশ খিদে পাচ্ছিল। সাত-সকালে বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে এসেছিলাম। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কিছু খাওয়া হয়নি। তাছাড়া দিনের আলো পড়ে এলে এমনিতেই আমার কেমন বিষণ্ণ লাগে, খিদে খিদে পায়। আমি বললাম, “না না, আমি বসব না। চা আর অমলেট খেয়েই চলে যাব।”
বৌদি দরজার কাছ থেকে হেসে বলল, “বোসো, করে আনছি।”
আগের বার যখন এসেছিলাম বৌদি ছিল না। শ্রীরামপুরে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আমায় নির্জলা বসিয়ে রেখে তন্ময়দা মেয়েকে নাচের স্কুলে ছাড়তে গিয়েছিল। বইয়ের তাকের নিচে আন-সান কাগজ পত্রর মধ্যে ‘পিকচার অভ ডোরিয়ান গ্রে’ মিছিমিছি ধুলো খাচ্ছিল। সেটা হাতে তুলে উলটে পালটে দেখছিলাম। পড়া বই, তবু আর একবার পড়াই যায়। আধ ঘন্টাটাক বসে, তন্ময়দা ফিরছে না দেখে, বইটা ঝোলায় ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তন্ময়দার বাড়ি এলে আমি দু-একখানা বই প্রতিবারই না-বলে উঠিয়ে নিয়ে যাই। নতুন কিছু নয়। তন্ময়দা বোধ হয় এতদিনে আঁচ করেছে। আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন চোখ ফেরালেই টপ করে একটা বই ঝোলায় ঢুকিয়ে নেব। এত পাহারাদারির কী আছে? আমি নিশ্চিত তন্ময়দাও আমার টেকনিকেই এতগুলো বইয়ের আলমারি ভরেছে। এ বাড়ির অনেক বইতেই অচেনা নাম লেখা দেখেছি।
তন্ময়দাকে পাত্তা দেবার কোনো মানে হয় না। বৌদি অমলেটের সঙ্গে মাখন লাগিয়ে দুটো ব্রেড টোস্ট দিয়েছে। সেগুলো ধ্বংস করে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলতেই মনে পড়ে গেল, চঞ্চলকে বলেছিলাম আজ ওর মাকে নিয়ে একবার সঞ্জয় ডাক্তারের কাছে যাব। নন্দীদের চায়ের দোকানের কাউন্টারে থাকে চঞ্চল। দোকানে ঢুকলেই চা-পাতার গন্ধে মনটা চামেলী চামেলী হয়ে যায়। ক্ষয়া ক্ষয়া চেহারার চঞ্চলকে দেখে মনে হয় নন্দীদের কর্মচারী নয়, চা-বাগানের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যানেজার। রেলার মাথায় খদ্দের সামলাচ্ছে। আমি এক-ধারে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ ফুসফুস ভরে চা-পাতার গন্ধ নেওয়া যায়। চঞ্চল আবডালে ডেকে বলে, একটু দাঁড়াও দাদা, নতুন পেটি খুলেছি...। বেস্পতি বার সন্ধেবেলা নন্দীদের দোকান বন্ধ থাকে, চঞ্চলের ছুটি। আজ নিয়ে না গেলে আবার এক হপ্তা দেরি হয়ে যাবে। চঞ্চলের মা, মানে মাসীমার হাঁপানির টানটা আবার বেড়েছে। চঞ্চল অপেক্ষা করে থাকবে। আমি গেলে সঞ্জয় ডাক্তার ফীজটা নেয় না। বাবার কাছে বিনা পয়সায় টিউশন পড়ত। সেই ঋণ শোধ দেয়, আর কী?
কারো কিছু রোগ-ব্যাধির খবর পেলেই টেনে টেনে সঞ্জয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। আসলে আমার একটা গোপন অভিসন্ধি আছে। আমি সঞ্জয় ডাক্তারের কৃতজ্ঞতার শেষ সীমা দেখতে চাই। আমি জানি, একদিন সঞ্জয় ডাক্তার বলবেই বলবে, “শালা, পেয়েছিস কী? আমি কি চ্যারিটি খুলে বসেছি?” আর আমি তৎক্ষণাৎ ‘ইউরেকা’ বলে হাততালি দিয়ে উঠব। আসলে একটা হাইপোথিসিস প্রোপোজ করতে চাই আমি যার বক্তব্য হল — স্থান-কালের অতিঘনকে প্রতিটি অনুভবের ভিত্তিই সসীম। বাংলায় একটু খটোমটো শোনায় বটে। ইংরিজিতে বললে ব্যাপারটা জলের মত সহজ হয়ে যায় — ইন স্পেস-টাইম হাইপার-কিউব এভ্রি ইমোশান হ্যাজ ফাইনাইট সাপোর্ট। আমি নিশ্চিত কৃতজ্ঞতা এই হাইপোথিসিসের একটা স্পেশাল কেস ছাড়া আর কিছু নয়। মোদ্দা ব্যাপার হল এই যে আমাদের সব ইমোশানই ছোট ছোট ঢেউয়ের মত। আজ ওঠে, কাল ফুরিয়ে যায়। কলকাতার ইমোশান বর্ধমান পৌঁছোতেই জুড়িয়ে ঠান্ডা জল হয়ে যায়।
চা’টা বেশ গরম। প্লেটে ঢেলে ফড়াক ফড়াক করে চুমুক দিয়ে শেষ করলাম। তন্ময়দা আমার দিকে কঠিন চোখে তাকাল। বুঝিয়ে দিল এই ধরণের অসভ্যতা তন্ময়দা অনুমোদন করে না। আমি চোখ নামিয়ে দেখলাম সেন্টার টেবিলের তলায় বাসি খবরের কাগজের মধ্যে ‘ইউলিসিস’ গড়াগড়ি খাচ্ছে। বইটা বেশ ওজনদার। ওটা নিশ্চয়ই বৌদি খবরের কাগজের সঙ্গে রদ্দিওলাকে বিক্রি করে দেবে। তার থেকে বরং আমি নিয়ে যাই। তন্ময়দাকে সামনে থেকে সরানো দরকার। বললাম, “তন্ময়দা, একটা ডিস্পিরিন হবে, মাথাটা ধরেছে।”
তন্ময়দা আমার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে বলল, “না।”
আমি বিমর্ষ হয়ে উঠে পড়লাম। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, আসার সময় খেয়াল করিনি, তন্ময়দাদের বাড়ির পাশের পুকুরটা মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে। প্রোমোটারের সাইনবোর্ডও লেগে গেছে। ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে নিশ্চয়ই। তন্ময়দাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকটা একদম ব্লক হয়ে যাবে। এ হেঃ! তাহলে তো তন্ময়দা আর বৌদি বসন্তকালে সন্ধ্যাবেলা ছাদে মাদুর পেতে আর প্রেম করতে পারবে না। রুজু রুজু হাওয়ার মধ্যে, মৃদু-জ্যোৎস্নার আলোয় দুটি পৃথুল মধ্যবয়স্ক শরীর ধুলো মাখছে। তাদের খোলা ত্বকে মাদুর কাঠির কারুকার্য খচিত হচ্ছে। ভাবতেই আমার রোমহর্ষ হয়। মুশকিল হল, বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে গেলে সেই স্বর্গীয় প্রেম-দৃশ্য সবাই দেখে ফেলবে। মানুষের প্রেম-প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা একটা অত্যন্ত গর্হিত, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রোমটারের জেল হওয়া উচিত। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি কালকেই এই প্রোজেক্ট বন্ধ করে দিতাম।
আপাতত কিছু করার নেই। তবু তন্ময়দা আর বৌদির অবশ্যম্ভাবী বঞ্চনার কথা ভেবে আমার বুক ভারী হয়ে উঠল। নয় নয় করেও তন্ময়দার গোটা পনেরো বই আমি আত্মসাৎ করেছি। তাছাড়া তন্ময়দার বাড়ি এলে বৌদি কখনোই শুকনো মুখে ফেরায় না। সেটাও একটা বিবেচনার বিষয়। এইটুকু সমবেদনা তো ওদের প্রাপ্য। আমি মোড়ের পান-বিড়ির গুমটি থেকে একটা গোল্ড ফ্লেক কিনে ধরালাম। ধোঁয়ার সঙ্গে বুক ফাঁকা করে বেশ খানিকটা সমবেদনা বেরিয়ে গেল। নিজেকে বেশ হালকা হালকা লাগল। ম্যাচবক্সটা ফেরত দিয়ে এক বান্ডিল বিড়ি নিলাম, রাতে লাগবে। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে হাঁটা দিলাম। পেট ভরা বলে মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। ষ্টেশনে পৌঁছতেই প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। যেন আমার জন্যেই। উল্টো দিকের ট্রেন, ভিড় কম। জানলায় বসে হাওয়া খেতে খেতে হাওড়া চলে এলাম।
সন্ধে হয়ে গেছে। স্টেশনে গিজ গিজ করছে লোক। এদের মধ্যে জিনিয়া নেই। শান্তি। এবার মেন লাইনের যে কোনো একটা ট্রেনে শরীরটাকে গুঁজে দিতে পারলেই হল। তারপর ভিড়ই দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দেবে। প্রত্যেক লাইনের ভিড়ের একটা নিজস্ব চরিত্র থাকে। এমনকি ভিড়-ঠেলা হকারদেরও আলাদা আলাদা পদ্ধতি। হাওড়া-বর্ধমান লাইনের কোনও হকার বনগাঁ লাইনে গিয়ে একটা লেবু লজেন্সও বেচতে পারবে না। এন্ড ভাইস ভার্সা। মাঝে মাঝে ভিড়ের একজন হয়ে বেঁচে থাকতে মন্দ লাগে না। কোন্নগরে বেশ কিছু লোক নামল। আমি তিন নম্বর সীটের আধখানায় আড় হয়ে বসতে না বসতেই ঝোলার মধ্যে মোবাইলটা বাজতে শুরু করল। বার করতে করতে কেটে গেল। জিনিয়া ফোন করছিল। ফোনব্যাক করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি মোবাইলটা আবার ঝোলার মধ্যে রেখে দিলাম। এই এক উপদ্রব। সঙ্গে থাকলে খোঁটায় দড়ি বাঁধা ছাগলের ফীলিং আসে। এখানে খোঁটা এবং দড়ি যথাক্রমে মোবাইল টাওয়ার এবং তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। আমি অবভিয়াস্লি রামছাগল। উপায় নেই। মায়ের জন্য রাখতেই হয়। রাত্তিরে ফিরতে একটু দেরি হলেই মায়ের বুকের মধ্যে প্যাল্পিটেশান শুরু হয়ে যায়।
চন্দননগর স্টেশনে নামতে নামতে টুং করে মেসেজ এল। জিনিয়া লিখেছে — পরশু দিন সন্ধেবেলা যদি না আসিস, তোর সঙ্গে সারা জীবন কথা বলব না। আগামী পরশু মানে শনিবার জিনিয়ার জন্মদিন। আমি গিয়ে কী করব? জিনিয়ার বরটা একটা গাম্বার্ট। কোন একটা মাল্টিন্যাশানাল ব্যাঙ্কে চাকরি করে। পার্টি-ফাটি হলেই ঘোঁত ঘোঁত করে মাল খায় আর আলবাল বকে। ক’দিন আগেই ওদের ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, “দুঃখের কথা কী বলব ব্রাদার, তোমার বন্ধু মানুষ নয়, পরী। আমি একজন পরীকে বিয়ে করেছি। দিনের বেলা ও মানুষ সেজে থাকে। রাত্তিরে ওকে ছুঁতে গেলেই জানলা দিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়।”
জিনিয়া যে আসলে একটি পরী — এই সন্দেহ অবশ্য আমার বরাবরই ছিল। আমি ভাবতাম ও উড়তে পারে না, ডানাকাটা হলে যা হয় আর কী? তবে আমি নিশ্চিত জিনিয়ার বর মিথ্যে কথা বলছিল। কারণ আমি সেদিন জিনিয়ার পিঠে মানুষের দাঁতের দাগ দেখেছিলাম। তার মানে জিনিয়া উড়ে যাবার চেষ্টা করেও পারেনি। জিনিয়া শাড়ির আঁচল দিয়ে দাগ ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিল। পারছিল না। ওকে চিরকাল জিনস আর টপেই দেখেছি। অ্যানিভার্সারির দিন বরের গিফট করা ভারি সিল্কের শাড়ি সামলাতে হিমসিম হচ্ছিল। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি ওর দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। জিনিয়া আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, “কী রে কষ্ট হচ্ছে?”
আমি চমকে গেলাম। জিনিয়া জানল কী করে? আমি আমতা আমতা করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম। জিনিয়া আমার পাতে দুটো ফিস ফ্রাই দিয়ে বলল, “গরম গরম খা। মন ভাল হয়ে যাবে।”
সেই শুরু। আচ্ছা, কারো জন্যে কষ্ট পাওয়া মানেই কি তাকে ভালবাসা? নাহলে নয়? অপরিচিত মেয়েদের কথা বাদই দিলাম। দু-এক জন, যারা বলেছে, ‘তাকালে চোখ গেলে দেব’, তাদের ছাড়া আমার পরিচিত নিরানব্বই শতাংশ মেয়েকেই আমি গভীর ভাবে ভালবাসি। বাকি এক শতাংশকে ভালবাসতেও আপত্তি ছিল না। নেহাত চোখ নিয়ে আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর ভালবাসা পেলেও আমি দৃষ্টিহীন হয়ে বেঁচে থাকতে রাজি নই। আমার মনে হয় শুধুমাত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য সকাল সন্ধ্যা দু’চোখ ভরে দেখা ছাড়া আমার কাছে বেঁচে থাকার আর তেমন কোনো সার্থকতা নেই। তাছাড়া জিনিয়া আমার ছোটবেলার বন্ধু, টাউনের ডাকসাইটে সুন্দরী। তাকে না ভালবাসার কোনও যুক্তিসংগত কারণই নেই।
এত সব কথা জিনিয়াকে বোঝানো খুব কঠিন। জিনিয়ার ধারণা হয়েছে আমি তাকে ভালবেসে তুমুল কষ্ট পাচ্ছি। এবং কিছুদিন এই রকম চললে আমি নির্ঘাত ডিপ্রেসানে চলে যাব। আশ্চর্য হল যে এই ব্যাপারটার জন্য সে নিজেকেই দায়ী করছে। বলা যায় — এক ধরণের ভয়ঙ্কর অপরাধবোধে ভুগছে। আমি জিনিয়াকে দু-একবার আকারে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, ব্যাপারটা তত সিরিয়াস নয়। কোনও ফল হয়নি। বরং আমাকে অবসাদের খপ্পর থেকে মুক্ত করার নৈতিক দায়িত্ব জিনিয়া স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চায়, যাতে আমি সাংঘাতিক কিছু না করে বসি। অবশ্য আমার হাইপোথিসিস যদি ঠিক হয় ব্যাপারটা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। ততদিন পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া গতি নেই।
ফুট ওভার ব্রীজ থেকে নেমেই দেখি ঋভু। ঋভু আমার স্কুলের বন্ধু। মোটামুটি একই সময়ে আমরা দু’জনে জিনিয়ার প্রেমে পড়ি। এবং বাবলির, এবং নন্দিনীর, এবং সেই মেয়েটার, ট্যারা মত, কী নাম যেন... লালবাগানের দিকে থাকত। ঋভু একটা সিমেন্টের স্ল্যাবের ওপর একা একা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। অন্যদিন প্ল্যাটফর্মের শেষের দিকে একটা অন্ধকার বেঞ্চ খুঁজে চার-পাঁচজন মিলে নেশাভাঙ করে। সস্তার শুকনো নেশা। আজ সেসব ছেড়ে আলোর নিচে, ব্যাপারটা সন্দেহজনক। আমায় দেখেই বলল, “পঞ্চাশটা টাকা হবে?”
আমি বল্লাম, “না।”
ঋভু মিনতি করে বলল, “আচ্ছা কুড়ি টাকাই দে তবে।”
আমি আবার বললাম, “না।”
এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ঋভু পিছন থেকে বলল, “আমায় দিবি কেন? আমায় দিলে মাগীবাজি করার জন্যে টাকা কম পড়ে যাবে যে!”
আমি অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে বললাম, “কী ফালতু ভাটাচ্ছিস? বাড়ি যা।”
ঋভুর রাগ পড়েনি। জ্বলন্ত চোখে বলল, “সাধু সাজিস না। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস।”
ব্যাপারটার তদন্ত হওয়া দরকার। আমি ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে বললাম, “আহা, রাগছিস কেন? কী হয়েছে খুলে বল।”
ঋভু শান্ত হল। বলল, “একটা বিড়ি দে।”
ঋভুকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজেও একটা ধরালাম। দুটো টান দিয়ে ঋভু যা বলল তার মর্মার্থ হল আজ এস্প্ল্যানেডে হীরেন আমাকে আর জিনিয়াকে মানে জিনিয়াকে আর আমাকে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। শুধু তাই নয় আমি নাকি জিনিয়াকে ইন্দ্রমহলে দহি পাপড়ি চাট খাইয়েছি। ওপরে বীট নুন ছড়িয়ে। আমি যে এই রকম বিশ্বাসহন্তার কাজ করতে পারি তা ঋভুর কল্পনার অতীত। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি। আমি বললাম, “দেখ ঋভু, হয় হীরেন ভুল দেখেছে, নাহলে তোকে পাতি ঢপ দিয়েছে।”
ঋভু মেনে নিল। আমার শার্টের কোণা দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বলল, “তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। প্রমিস কর কোনোদিন জিনিয়ার সঙ্গে প্রেম করবি না।”
সন্দেহটা রয়েই গেল। চঞ্চলের বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামতে নামতে মনে হল, এমন তো নয় যে হীরেন সত্যি বলছে? আচ্ছা আমার কি কোনও যমজ ভাই টাই আছে, আইডেন্টিক্যাল ট্যুইন? থাকলেও তার সঙ্গে জিনিয়ার পরিচয় হবে কি করে? জিনিয়ারও যদি আইডেন্টিক্যাল ট্যুইন থাকে? এঃ, ব্যাপারটা সত্যি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমার আইডেন্টিক্যাল ট্যুইন জিনিয়ার আইডেন্টিক্যাল ট্যুইনের সঙ্গে প্রেম করছে। ভাবা যায়? সঞ্জয় ডাক্তারের কাছে চঞ্চলের মাকে দেখিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম জিনিয়ার জন্মদিনে ডুব মারার একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, “মা, কাল আসানসোল যাব। ছোটমাসী ফোন করেছিল। তিন চার দিনের জন্য মহিলা সমিতির সঙ্গে কাশী যাচ্ছে। মেসোকে পাহারা দিতে যেতে হবে।”
মেসোর গত বছর বাইপাস হয়েছে। মাসী না থাকলেই অনিয়ম করে, সিগারেট-মিগারেট খায়। বন্ধু-বান্ধব ডেকে মোচ্ছব করে। মাসীর ছেলে মন্টু বম্বে আইআইটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। সে সারাবছর সাংঘাতিক ব্যস্ত। ছুটিতেও বাড়ি আসে না, বিদেশে গিয়ে ইন্টার্নশিপ করে। মাসী একা কোথাও গেলে ন্যাচারেলি আমাকেই গিয়ে মেসোর সঙ্গে থাকতে হয়। আমার মত ‘বললেই যাই’ টাইপের ছেলে পাবে কোথায়?
আমার ধারণা ছিল গল্পটা এতটাই নিশ্ছিদ্র মা কিছু সন্দেহ করবে না। যথারীতি মা ধরে ফেলল মিথ্যে বলছি। চোখে সন্দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “অমিয় গতকাল ফোন করেছিল। কিছু বলল না তো!”
আমি বললাম, “আজ সকালেই যাওয়া ঠিক হয়েছে।”
মা আর কথা এগোল না। রাত্তিরের রুটি করার জন্য উঠে গেল।
ভোর রাতে ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম আমার আসানসোল যাওয়া হবে না। গলা নাক জ্বালা জ্বালা করছে, মাথায় যন্ত্রণা। জ্বর আসছে। জ্বর-টর হলে আমি বেশ আওপাতালি হয়ে পড়ি। আওপাতালি শব্দটার মানে সম্ভবত অল্পেই কাতর হয়ে পড়া। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, মা বলে। আসলে মা কপালে ঠাণ্ডা হাত রাখলে মনে হয় জ্বর নেমে গেল। ইচ্ছে করে মা সারাক্ষণ পাশে বসে থাকুক। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটাও বাড়ছিল। একটা ক্যালপল খেয়ে চাদর টেনে শুলাম। মা বলল, “একবার সঞ্জয়কে খবর দিই। দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় দেখে যাবে।”
সঞ্জয় ডাক্তার দেখে টেখে বলল, “মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। এখনি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি না। দু’দিন রেস্ট নিক। জ্বর আড়াই-তিনের ওপর উঠলে এসওএস এই ওষুধটা দিয়ে দেবেন।”
সঞ্জয় ডাক্তারকে বিদায় করে মা ওষুধ আনতে বেরোল। আমি আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে যাচ্ছিলাম, দেখলাম খাটের পাশে জিনিয়া দাঁড়িয়ে। আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, “তোকে দরজা কে খুলে দিল?”
জিনিয়া বলল, “সে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।”
দু’হাত মাথার ওপরে তুলে ডাইনি বুড়িদের মত ব্রহ্মতালুর ঠিক ওপরে খোঁপা বেঁধে বলল, “ভেবেছিস কী? তোর ফন্দি আমি বুঝি না? আমার জন্মদিনে আসবি না বলে জ্বর বাঁধিয়েছিস।”
আমি তীব্র প্রতিবাদ করতে গেলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। জিনিয়া বলল, “বগল তোল তো দেখি, রসুন চেপে রেখেছিস কিনা।”
আমি গলার কাছ পর্যন্ত চাদর টেনে হাত দিয়ে চেপে রাখলাম। জিনিয়াকে বিশ্বাস নেই। বলা যায় না, সত্যি সত্যি যদি চেক করতে আসে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। আমার স্যান্ডো গেঞ্জিটায় গোটা দুই-তিন ফুটো, বগলের নিচটা ফেঁসে গেছে। জিনিয়া আমার গালে গলায় হাত ছুঁইয়ে বলল, “বেশ জ্বর। দাঁড়া, একটা উপায় করি।”
এর পর যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। জিনিয়া ঝুঁকে পড়ে আমার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট নামাল। ও এত কাছে সরে এসেছে যে আমি ওর বুকের থেকে উঠে আসা মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছি। আমি ওর পিঠে হাত রাখতে গেলাম। জিনিয়া তোর পিঠের দাগটা কি মিলিয়ে গেছে? অনেক চেষ্টা করেও আমার হাত উঠল না। পারফিউমের গন্ধটা সম্ভবত হিপ্নোটিক। স্নায়ু অবশ করে দেয়। জিনিয়া তৈরি হয়েই এসেছে। ও কি আফ্রিকার কালা জাদু জানে? জিনিয়া, মুখপুড়ি, করছিস কী তুই? মানছি আমি আর্কিমিডিসের ছাত্র। তাই বলে চুমু এমন স্বাদ-বর্ণ-গন্ধহীন, যৌনতাহীন হবে! প্রথম চুমু নিয়ে আমার কত স্বপ্ন ছিল রে। তুই আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলি! জিনিয়া মুখ তুলছে না। আমার হাঁ-মুখ থেকে সমস্ত উত্তাপ শুষে নিচ্ছে। আমার শরীর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম জিনিয়ার চোখ খোলা। চোখের সাদার মধ্যে লাল লাল রক্ত কণিকা ভাসছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।
ঘুম ভাঙল যখন বিকেল পড়ে এসেছে। জ্বর নেই, মাথার যন্ত্রণা নেই, শরীর ঝরঝরে। খিদে পেয়েছে। মা এক কাপ চা করে এনেছে। একটা টোস্ট বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেলাম। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, “জিনিয়া কখন গেল?”
মা বলল, “জিনিয়া এসেছিল নাকি? জানি না তো। ওষুধ নিয়ে এসে দেখলাম তুই অঘোরে ঘুমোচ্ছিস।”
আমি চা শেষ করে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা মা, আমার কি কোন যমজ ভাই ছিল?”
মা আমার দিকে এমন করে চাইল যেন, র্যা মসের সিনেমা দেখছে। বলল, “কবেকার কথা, তুই কী করে জানলি?”
আমি আধশোয়া থেকে খাড়া হয়ে উঠে বসলাম, “মানে? সত্যিই ছিল?”
মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “তুই জন্মানোর দু-মিনিট পরে সে জন্মেছিল, সাত মিনিটের মাথায় মারা যায়। তোর বাবা, জ্যাঠা ছাড়া আর কেউ জানত না। সেই রাত্তিরেই ওরা ওকে গোর দিয়ে এসেছিল। খুব কেঁদেছিলাম, জানিস।”
মায়ের মনের মধ্যে ছাড়া আমার পাঁচ মিনিট বেঁচে থাকা যমজ ভাইয়ের কোনও অস্তিত্বই নেই। অথচ হীরেন...। রাত্তিরে আর জ্বর এল না। সকালে বেশ দেরি করে ঘুম ভাঙল। চোখ খুলেই মনে হল আজ জিনিয়ার জন্মদিন এবং আমার কাছে ওর জন্মদিনে না যাবার আদৌ কোনো অজুহাত নেই। ভেবে দেখলে আজকের জ্বরহীন সকালটার জন্য আমি জিনিয়ার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে ঋণী। জিনিয়া বলে নয়, যে কোনও কারো জন্মদিনে যাবার কথা হলেই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কী গিফট নিয়ে যাব বুঝতে পারি না বলে আমি সাধারণত কারো জন্মদিনে যাই না। অবশ্য জিনিয়ার জন্মদিনে গিফট না নিয়ে গেলেও চলে।
সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরনোর সময় হাতটা খালি খালি লাগল। পড়ার টেবিলের ওপর রাজ্যের বই ডাঁই হয়ে আছে। চোখ বুজে হাত চালিয়ে তার মধ্যে থেকে একটা বই তুলে আনলাম। পাওলো কোয়েলোর ‘দি অ্যালকেমিস্ট’। জিনিয়াই পড়তে দিয়েছিল। দু-পাতা পড়ে আর পড়িনি। কোয়েলোর গদ্য পড়লেই আমার সলিল চৌধুরীর ওই গানটার কথা মনে পড়ে, পল্লবিনী গো সঞ্চারিণী, মন না দিয়ে আর পারিনি...। ওই বইটার কুড়ি আর একুশ পাতার মধ্যে একটা গোলাপ কুঁড়ি রাখা ছিল। যেমন থাকে আর কী? বইটা তুলতেই ঝুর ঝুর করে শুকনো ফুল ঝরে পড়ল। খুলে দেখলাম দুটো পাতাতেই দাগ ধরে গেছে। তা হোক, হাতে যখন উঠেছে, বইটা একটা গিফট র্যা্পে মুড়ে নিয়ে নিলাম। জিনিয়াদের গলির মুখে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে এল। ঢুকতে যাব, দেখি ঋভু উল্টো দিক থেকে সাইকেল চালিয়ে আসছে। আমার কাছে এসে পায়ের ঠ্যাকনা দিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করাল। বাঘের মত থমথমে মুখ তুলে বলল, “মীরজাফর!”
আমি লজ্জা লজ্জা মুখ করে হাতের বইটা দেখিয়ে বললাম, “এটার কথা বলছিস? এটা জিনিয়ার জন্য নয়...”
ঋভু খিঁচিয়ে উঠল, “তবে কার জন্যে?”
আমি বললাম, “জিনিয়ার বোনের জন্যে...”
ঋভু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, “জিনিয়ার আবার বোন হল কবে? আমি জানলাম না...”
আমি বললাম, “সে কী? তুই জানতিস না? জিনিয়ারা দুই বোন। ছোটবোন জামসেদপুরে ওর মাসীর কাছে থেকে মানুষ।”
ঋভু চোখ সরু করে বলল, “ভোগা দিচ্ছিস না তো?”
আমি বললাম, “তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। তোকে ভোগা দিতে পারি?”
ঋভু আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। আমি জিনিয়াদের বাড়ি ঢুকতেই জিনিয়ার বর হৈ হৈ করে ছুটে এল, “এসো ব্রাদার, এসো। তোমার জন্যেই বসে আছি। শুরু করতে পারছি না।”
ঘরোয়া পার্টি। জিনিয়ার বরের দু-চার জন কেজো টাইপের বন্ধু ছাড়া কাউকে বিশেষ দেখলাম না। সেন্টার টেবিলের ওপর অলরেডি বোতল-টোতল সাজানো হয়ে গেছে। জিনিয়া কোমরে শাড়ি গুঁজে তদারকি করছে। জিনিয়ার বর বলল, “কী গো? মালের সঙ্গে একটু চাট-ফাট দেবে না?”
আমি জিনিয়াকে বইটা দিতে গিয়ে দেখলাম ওর ঠোঁট সাদা, গালের চামড়ায় খড়ি উঠেছে, চোখের নিচে কালি। আমার অসুখ নিরাময় করতে গিয়ে জিনিয়া কি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল? আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে নিস্পৃহ ভাবে বলল, “আবার এসব আনতে গেলি কেন?”
গিফট র্যা প খুলে দেখলও না। বুককেসের ওপর রেখে দিয়ে কিচেনে ঢুকল, সম্ভবত চাট বানাতে।
জিনিয়ার বর আমার হাতে একটা গ্লাস গুঁজে দিল। অন্য বন্ধুদের হাতেও। এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে নিজের গ্লাসটা তুলে বলল, “চীয়ার্স।”
লোকটার এত কীসের খুশি কে জানে? ভ্যাড়ভ্যাড় করে যত হাবিজাবি কথা বলে যাচ্ছে। কারণে অকারণে দাঁত কেলাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঠাস করে একটা বসিয়ে দিই। কিন্তু মালটাকে চড় মারার পর মনে হয় না এখানে আর বসে থাকা যাবে। মাঝখান থেকে ডিনারটা মিস হয়ে যাবে। কিচেন থেকে ভুর ভুর করে বিরিয়ানির গন্ধ আসছে। জিনিয়া প্লেটের ওপর চিকেন পাকোড়া সাজিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের কাছে এসে সেন্টার টেবিলের ওপর প্লেট নামিয়ে রাখল। প্লেটের ওপর ছাঁকা তেলে ভাজা থোকা থোকা হালকা বাদামী রঙের পাকোড়া ফুটে আছে। আমি একটা পাকোড়া তুলে দু-আঙ্গুলে ভেঙে, ফুঁ দিয়ে মুখে দিলাম।
জিনিয়া আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি মুখ তুলে ওকে বলতে গেলাম — ফাটাফাটি বানিয়েছিস, মাইরি। তার আগেই দেখি ও মুখে হাত চাপা দিয়ে ছুটল। জিনিয়ার বর গ্লাস নামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেল। কী হল? লিভিং রুমের লাগোয়া বাথরুম থেকে শব্দ আসছিল। জিনিয়া ওয়াক তুলে বমি করছে। এই তো ঠিক ছিল। হঠাৎ শরীর খারাপ হল কেন? আমার কী একবার উঠে গিয়ে দেখা উচিত নয়? আমি দোনামনা করে উঠলাম। জিনিয়া ওর বরের কাঁধে ভর দিয়ে ওদের বেডরুমের দিকে যাচ্ছে। আমিও সঙ্গে গেলাম। যদি কিছু কাজে আসি। অসুস্থতার সময় অত বেডরুম-টেডরুম মানলে চলে না। জিনিয়ার বর জিনিয়াকে খাটে শুইয়ে মাথার নিচে বালিশ গুঁজে দিল। খাটের পাশে বসে জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “রেস্ট করো একটু, ঠিক হয়ে যাবে।”
আমি আশঙ্কার দৃষ্টি নিয়ে চেয়েছিলাম। জিনিয়ার বর আমাকে বলল, “চিন্তা কোরো না ভায়া, এই সময় এই রকম হয়।”
আমি হাঁদার মত বললাম, “কোন সময়?”
জিনিয়ার বর ঘাঘু লম্পটের মত মিচকে হেসে বলল, “বুঝলে না? তুমি মামু হতে চলেছ হে।”
জিনিয়া নেকু-পুষু বেড়ালের মত গুটিসুটি মেরে বরের বুকের কাছে সরে এল। ছদ্ম কোপে ঘুসি পাকিয়ে বরকে দেখিয়ে বলল, “উঁ-উঁ... যাও!”
ওদের প্রেম দেখে আমার দু-চোখের কূল ছাপিয়ে জল এল। যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান এসেছে, সব লণ্ডভণ্ড করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এসময় আমার হাঁকুপাঁকু করে পাড়ে ওঠার চেষ্টা করা উচিত। ঝামেলা হল আমি কখনোই কোনো উচিত কাজ করে উঠতে পারি না। বলাই বাহুল্য, এখনও পারলাম না। কারণ এই মুহূর্তে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের হর্ষোন্মাদনা আমার মধ্যে ভুড়ভুড়ি কাটছে। আমার হাইপোথিসিসের সপক্ষে জিনিয়ার প্রেগন্যান্সির থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? থ্যাঙ্কস জিনিয়া, তুই গর্ভবতী হয়ে ‘হেন্স প্রুভড’ করে দিলি ইন স্পেস টাইম হাইপার-কিউব ইটিসি... ইটিসি। ফলিত রসায়নের ইতিহাসে তোর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। শুধু আমি নই, এই স্বার্থহীন আত্মগর্ভদানের জন্য সমগ্র মানব সমাজ তোর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। আমার উল্লাস আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না, ‘ভজ গৌরাঙ্গ’ স্টাইলে দু-হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে নাচতে হাততালি দিয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, “ইউরেকা, ইউরেকা...”
জিনিয়া ফিস ফিস করে বলল, “এই বোকা, কাঁদছিস কেন?”
আমি জামার আস্তিনে চোখ মুছে বললাম, “কাঁদলাম কোথায় রে, এ তো আনন্দাশ্রু। এমতাবস্থায় আর্কিমিডিস বাথটব থেকে লাফ দিয়ে নেমে, নাঙ্গু-পাঙ্গু হয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটেছিল। নেহাত তুই বিরিয়ানি বানিয়েছিস, নইলে আমিও দেখতিস...”
জিনিয়া ওর বরের কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। আমার গলার কাছটা আবার জ্বালা জ্বালা করছে। এই মুহূর্তে একটা সিগারেট ধরানো খুব জরুরী।
(পরবাস-৭৩, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮)