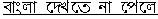সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা;— নলিনী বেরা; প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৮; দে'জ পাবলিশিং - কলকাতা; পৃষ্ঠাঃ ২৮০; ISBN: 978-93-88923-64-4
সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা;— নলিনী বেরা; প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৮; দে'জ পাবলিশিং - কলকাতা; পৃষ্ঠাঃ ২৮০; ISBN: 978-93-88923-64-4
নদীর নাম সুবর্ণরেখা।।
শোনা যায় এ’নদীর বালিতে নাকি কোনো সময় সোনার রেণু মিলতো, সেই থেকেই এই নাম! কোনো মধ্যমানের মালভূমি থেকে বেরিয়ে নানা গ্রাম্য জনপদের পাশ দিয়ে বইতে বইতে এই নদী সাগরে গিয়ে মিশেছে নীরবে। এই অবোলা নদীটির কপালে জোটেনি কোনো হিমবাহ বা তুষারশৃঙ্গের আশীর্বাদ, মাত্র চারটি রাজ্যের মাটি ছুঁয়েই এর যাত্রা শেষ। এ পাড় ভাসায় না, এতে জাহাজও চলে না; পণ্যবাহী নৌকা আর প্রান্তিক মানুষজনকে পারাপার করিয়েই এর দিন কাটে। তবে স্মৃতিতে, গীতিতে, গল্পে-কাহিনীতে থেকে যায় সেই সোনার স্মৃতি। হীরে-জহরত, চূনি-পান্না নয়, সোনা-রূপোর আকরিকও নয় শুধুই গুঁড়োগুঁড়ো সোনা। যা মিশে থাকতো বালিতে। ভাগ্য সহায় থাকলে পরিশ্রমী কোনো কোনো মানুষ খুঁজে পেতো সেই সোনা... ... ... সুবর্ণরেণু।।
শ্রী নলিনী বেরা সাহিত্যর আঙিনায় পা রেখেছেন প্রায় চার-দশক। তেমন করে পাদপ্রদীপের সামনে হয়তো আসেননি। সাম্প্রতিক (১লা বৈশাখ ১৩২৬) ‘আনন্দ-তিলক’ তাঁকে নিয়ে এলো ‘হাজার-টাকার ঝাড়বাতি’র আলোতে। আগ্রহী পাঠক অতঃপর খুঁজে নেবেন তাঁর পূর্বতন সাহিত্যকর্ম।
সুবর্ণরেখা নদীর চলার পথের আশেপাশে গাছপালা-ফুল-ফল-পাখপাখালি-জন্তুজানোয়ার, এবং অবশ্যই মানুষজনকে নিয়ে স্বর্ণসন্ধানী সাহিত্যিক রচনা করলেন একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ! আত্মজীবনী নয়, সেই অর্থে উপন্যাসও নয়, অথচ দু’য়ের মৌলিক উপাদানই স্পষ্ট পাওয়া যাবে গ্রন্থটিতে। লেখকের গদ্য একেকবার মনে করায় ‘আরণ্যক’ এর আত্মগত পটচিত্রকে, বা তার স্রষ্টা নিসর্গপ্রেমী বিভূতিভূষণকে। আবার দেশজ/ভূমিজ উপকরণের প্রাচুর্য বা প্রান্তিক শব্দ-বন্ধের ব্যবহার মনে পড়ায় আবদুল জব্বার-কে, যাঁর ‘বাংলার চালচিত্র’ আজ বিস্মৃতপ্রায় হলেও মলিন নয় কোনোমতেই!
গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলতে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। এ’ বইয়ে কোনো নির্দিষ্ট গল্প বা theme নেই, অথচ আছে অগুণতি ছোট-বড় টুকরো কাহিনীর সমাহার। ফকিরের আলখাল্লার মত বহুবর্ণের নানা টুকরোর এক আকর্ষণীয় কোলাজ, যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে ‘নলিন’ ওরফে ললিন: কিন্তু আদৌ উচ্চকিত নয় তার উপস্থিতি।
গ্রন্থটির মুখবন্ধে আনন্দ-পুরস্কারের সাম্মানিক ভাষণেও নলিনী এতটাই অকপট এবং এতই ঋজু, সরল এবং অকৃতঘ্ন, যে তাঁর সাহিত্যকৃতির উৎস-সন্ধানে ঋণস্বীকারের তালিকায় P.K DeSarkar এর ইংরিজি গ্রামার-এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন গ্রামের পটভূমিকায় ‘বাৎসায়নের কামসূত্র’ বা ‘জীবন-যৌবন’-এর কথা। পাঠকের একটা ঝাঁকুনি লাগে বৈ কি! অন্ত্যজ, অপাংক্তেয় ও ‘সাব-অলটার্ন’ মানুষদের নিয়ে এই লেখা তাই তাদের উৎসর্গ করেছেন তিনি। এইসঙ্গে তাঁর পাতানো এক সাঁওতাল দিদির যে ছোট্ট কাহিনীটি ভাষণে ও মূল পরিসরেও বিবৃত করেছেন, সেটি শুধু মর্মস্পর্শী নয়, তার সামাজিক ব্যাপ্তিও বিরাট।
সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখাকে ঠিকমত আস্বাদন করতে গেলে এর শেষাংশের Glossary বা অর্থ-তালিকাটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তথাকথিত অপরিচিত শব্দাবলীর প্রচলিত বাংলা অর্থ অধ্যায়ানুযায়ী সাজানো আছে। না থাকলে আমরা কি করে জানতাম:
. পদ্মল ঘা মানে কর্কট রোগ, বা Cancer
. কুঁইরাচ্ছে মানে ডাকছে
. গাড়িয়া মানে ছোট পুকুর
. ‘দেড়ইয়া’ মানে সঙ্গম করা
. ‘বুড়ে যাওয়া’ মানে ডুবে যাওয়া ?
'বাহা ঘর’ মানে বিয়ে-বাড়ি বা ‘কাঠ-বিলেই’ অর্থ কাঠবিড়ালি যদি বা আন্দাজ করে নিতে পারি, কিম্বা পাওয়া অর্থে ‘মাগ্নে’, না বলে দিলে কী করে বুঝবো যে ‘কচিকুসুম’ মানে ফুলের কুঁড়ি, কিম্বা ‘মেঘপাতাল’ বোঝায় আকাশ-কে?
হিন্দি কবিতা বা উর্দু শায়রি শুনবার সময় দেখেছি ও শুনেছি কবি-রা একএকটি পংক্তিকে অন্ততঃ দু-দু’বার ফিরে ফিরে পড়েনঃ শ্রোতার রসাস্বাদন যাতে গভীর বা নিবিড়তর হয়। কীর্তনেও আখর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাওয়া হয়। নলিনী বেরার এই ব্যতিক্রমী উপন্যাসেও একএকটি ছোট বাক্যবন্ধকে অত্যন্ত সচেতনভাবে লেখক প্রায়শই দ্বিত্বে ব্যবহার করেছেন, যেগুলি, আমার মতে লেখাটির কাব্যগুণ, কিম্বা গীতিময়তা বাড়িয়েছে অনেকখানি। দেখা যাক্ —
• রাগী বিড়ালের ল্যাজের মতোই ক্রমশঃ ফুলতে থাকে। ফুলতে থাকে, ফুলতে থাকে। (পৃ-৩৫)
• জায়গাটা ছায়াছন্ন, ছায়াছন্ন (পৃ-৩৯)
• গান্ধীর প্রতি আমার অশ্রদ্ধাটাও উধাও। উধাও, উধাও। (পৃ-৪৯)
• আমাকে ভাবিয়ে তুললো। ভাবিয়ে তুললো, ভাবিয়ে তুললো। (পৃ-৯৬)
• পশ্চিম আকাশে তারা জ্বলজ্বল করে, জ্বলজ্বল করে (পৃ-২২১)
• তবু যেন তার মন ভরেনা। মন ভরেনা, মন ভরেনা। (পৃ-২২২)
• বিস্ফারিত চোখে চারধারটা দেখে যাচ্ছি। দেখে যাচ্ছি, দেখে যাচ্ছি!! (পৃ-২২৩)
আমাদের ভদ্র-সভ্য-শালীন বাংলাভাষা যেমন নলিনীর করায়ত্ত, তেমন, বা তার থেকেও বেশি দক্ষতা তাঁর ভূমিজ ভাষার ওপরে। আর এই যুগপৎ কর্তৃত্বই অ-সাধারণত্ব এনে দিয়েছে গ্রন্থটিকে, আগাগোড়া। গ্রামের উলঙ্গ শিশুর দলকে যে সস্নেহ মমতায় তিনি নামাঙ্কিত করেন “ন্যাঙ্টা ভুটুম, সাধের কুটুম” বলে, সে’ মমতাই মন্ত্রবলে রূপান্তরিত হয়ে যায় সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায়, সুবর্ণরেখা নদীর উদ্দেশে। অভিমানী বিস্ময়ে ললিন জিজ্ঞেস করেন হংসী মাঝি বা নাউরিয়াকে “এই যে হাতমুঠোয় জল নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে সুবর্ণরেখাতে দাঁড়িয়েও 'ওঁ গঙ্গা ওঁ গঙ্গা' বলে উচ্চারণ করলেন, কই 'ওঁ সুবর্ণরেখা ওঁ সুবর্ণরেখা' তো বললেন না? এখানে আর গঙ্গা কোথায়?” আপাত-নিরক্ষর অথচ প্রাজ্ঞ মানুষটির মুখে শুনি অমোঘ এক বিচার-নিদান “... আসলে কী জানল ললিন, সবু নদী গঙ্গা, সবু নদীর জল গঙ্গাজল” …..কী বিশাল ব্যাপ্তি এই উক্তিটির!
গ্রন্থটির আত্মজৈবনিক গন্ধেই জানতে পারি "মনে মনে কত কী হতে চেয়েছিলাম--মেজোকাকার মতো কোব্রেজ, নাটুয়াদলে নবীনের মতো ;নাচুয়া', হা-ঘরে যাযাবরীর সঙ্গে ঘর-ছাড়া, অ্যামেরিকো ভেস্পুচ্চী কিংবা ভাস্কোদাগামার মতো দেশ আবিষ্কারক... (পৃ-৩৮), শেষমেশ কি না নদীনালায় খালে মাছ মারা? মাছ ধরা?" এই মাছ-মারা মাছ-ধরা, বা এককথায় হংসী নাউড়িয়ার সঙ্গে নৌকা-বিহারের আনন্দ-কণা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বইটির পাতায় পাতায়। যে বহুমাত্রিক বাসনার বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে, তাই গড়ে দেয় লেখকের সামগ্রিক সাহিত্য-মানস।
নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা সভ্যতা বা জনপদের মতো কিছু নদী-কেন্দ্রিক উপন্যাসও বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রয়ে গেছেঃ ইছামতী (বিভূতিভূষণ), পদ্মানদীর মাঝি (মাণিক বন্দ্যোঃ), হাঁসুলি বাঁকের উপকথা (তারাশঙ্কর), তিতাস একটি নদীর নাম (অদ্বৈত মল্লবর্মণ), তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (দেবেশ রায়)--এই নাতিবৃহৎ কিন্তু উজ্জ্বল তারামণ্ডলীতে 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' নিজের বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর একটি নুতন সংযোজন।
বর্তমান গ্রন্থটির লেখক শ্রী নলিনী বেরার জন্ম মেদিনিপুরের অখ্যাত গ্রাম বাছুরখোঁয়াড়ে । ত্রিশ সদস্যের সংসারে বেড়ে ওঠা কুম্ভকার/কুম্হার পরিবারের ছেলেটির শুধু মাথা পরিষ্কার ছিল তা' নয়, হাতের লেখা ছিল 'মাছের কাঁটার মতই' তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধ করে বড় হয়ে ওঠার পথের দুধার থেকেই সংগ্রহ করেছেন তাঁর লেখার রসদ। অবশ্য গল্প-উপন্যাস রচনার এই প্রতিভা ও প্রবৃত্তি (talent ও tendency) কি কিছুটা তাঁর 'কথক-পিতার' থেকে জিন-বাহিত হয়েও আসেনি তাঁর রক্তে? যেমনটি এসেছিল মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তাঁর পুত্র বিভূতিভূষণে? তবে উৎস-সন্ধানে বিরত হলেও পাঠক রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন না, এটা তো অবিসম্বাদিত সত্য!
‘আনন্দিত’ লেখকের অভিভাষণ থেকেই জানতে পারি: সেই কবে শুরু করেছিলাম সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী ওড়িশা সংলগ্ন লোধা-ভূঁইঞা-ভূমিজ-কাম্হার-কুম্হার-সাঁওতাল অধ্যুষিত একটা গ্রাম থেকে .... ভাষাটাও বাংলা নয় — হাফ-ওড়িয়া হাফ-বাংলা। ... মূলত রাজু তেলি সদ্গোপ করণ কৈবর্ত খণ্ডায়েৎ--সব হা্টুয়া লোকেদের ভাষা। আরও বইয়ের মধ্যে প্রবেশ করে ইস্কুলের [রোহিণী চৌধুরাণী রুক্মিণী দেবী হাইস্কুল] হোস্টেলের বাসিন্দাদের বিবরণ দিতে গিয়ে পারিবারিক পদবীর যে তালিকা তিনি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে দিয়ে চলেন, তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় অনার্য ভারতবর্ষের অবহেলিত অবজ্ঞাত কোন্ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি বুনেছেন তাঁর শিল্পকর্ম: টুডু, হেমব্রম, হাঁসদা, মুর্মু, সোরেন, সিং, বাউড়ি, বিশুই, মুন্ডা, ভুঁইয়া, মাঝি, পানি, বেহেরা, বেরা, রাণা, হাটুই, পৈড়া”... এ তালিকা প্রায় অনিঃশেষ।
একটি কিশোরের বেড়ে ওঠার কাহিনীতে বয়সের ধর্মের ছোঁয়া বা যৌনতার গন্ধ থাকবেনা, তা হয় না বলেই কাঁদরি- চাঁপা-রসনাবালা বা কালিন্দী-র মত কিশোরী/ যুবতী/ মহিলার প্রসঙ্গ আসে। লেখক ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই ছুঁয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান, সুরও কাটে না, তাল-ও ভাঙে না। অথচ স্বাদ বদল হয় বৈ কি!
যে কোলাজের কথা আগে লিখেছি, তার কয়েকটি টুকরোকে আলাদা করে দেখলে পাই: সাঁওতাল দিদির গল্প, রোহিণী হাইস্কুলের ও হোস্টেলের নানান মজাদার এবং রহস্যময় অভিজ্ঞতা, বাড়িতে কালপ্যাঁচা এসে বসা ও তৎপরবর্তী ঘটনা ও দুর্ঘটনা চক্র, ছোটপিসিমার মস্তিষ্কবিকৃতি ও নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, বৈশাখী পালের চর-সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত, বড়দা শ্রীকান্ত-র বিবাহ — ছোট বড় আরো কিছু।
আর আমাকে বিশেষ করে মুগ্ধ করেছে, এইরকম আরো অনেক ঘটনার বিবরণের বহতা ধরার মধ্যে মধ্যে লেখকের নিখুঁতভাবে ব্যবহৃত নানান্ উদ্ধৃতি; এত প্রাসঙ্গিক, এত পরিচিত, যে বাঙালি পাঠক সহজেই নিজেকে জুড়ে নিতে পারেন ঐ সব ঘটনার সঙ্গে। এবং ধীরে ধীরে পুরো কাহিনীর সঙ্গেই কখনও বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কখনও বিভূতিভূষণ বা রাজশেখর বসু, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, একবার জীবনানন্দ; আর অভ্র-কণার মত ছড়িয়ে আছে বাংলা পুরোনো গানের টুকরো, যে সব গান আর কবিতা দশকের পর দশক ধরে বাঙালিকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে, যেমন 'ও সাতভাই চম্পা গো রাজার কুমার ...', কিম্বা 'ঘুমঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত', বা 'মন চলে আগে আগে আমি পড়ে রই ...' অথবা 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ...', কিম্বা 'আহা কী আনন্দ আকাশে' বা 'পথের ক্লান্তি ভুলে/ স্নেহভরা কোলে তুলে'। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে না হোক্, সমান পা-ফেলে চলে আরও অনেকখানি মাটির কাছাকাছি গান, গীত বা গাথা, নিদেনপক্ষে ছড়া: যেমন: 'বারিপদা শহরে গাড়ি চলে রগড়ে — দাদাগো দিদিগো — চল যাব টাটানগরে', কিম্বা 'বিধি যাহা লেখি আছে কপালে। বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে'। বৈশাখীপালের চর নিয়ে এই ‘দোহা’টুকু বারবার ফিরে এসেছে পুরো বই-এ; গ্রাম্য কবি সন্তোষ দাসের লেখা পালাগানের পংক্তিও ঢুকে গিয়েছে এই কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে।
যে কথা না লিখলে আমার এই আলোচনা প্রতিবন্ধী বলে পরিগণিত হতে পারে, সেটা শ্রীবেরার ভাষার ওপর সাবলীল ও সহজাত দক্ষতা। ভূমিজ বা আদিবাসী জনজাতির ব্যবহৃত ভাষা যেমন অবলীলাক্রমে তিনি ব্যবহার করেছেন, তেমনি শুদ্ধ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দকেও সম্পূর্ণ সচেতনভাবে বসিয়েছেন আপন অভিরুচি অনুসারে। নদীর জলে “সমভিব্যাহারে” নেমে আসা নোংরা-জব্রা, শিশির-দুষ্ট শতদলের ব্রীড়াবনত পাপড়িনিচয়ে টুসকি মেরে ঝেড়ে পুঁছে দেখা, বহির্জগত বিবর্জিত খড়ের ওমসংযুক্ত অন্ধকার প্রদেশে কৌশল্যার শরীর খুলে আহ্বান, ক্রীড়ারত চ্যাঙনা-মাঙনাদের নাচ — আমার কাছে বিন্দুমাত্রও গুরুচণ্ডালীর গন্ধ আনেনি।
ধ্বন্যাত্মক শব্দ কমবেশি আমরা সবাই ব্যবহার করি। কিন্তু নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে যে সাহস ও দখল লাগে, সেটা তো সকলের থাকেনা! তাই আমরা যদি বা “হুমদুম” করে আমাদের অন্তর কি “হুদহুদ” করে কখনও? অথবা কোনোদিন “নির্ধূম সে” নাচি? বা “রুম্রুম্ বসি”? “রদবদিয়ে” গাছ বাড়া, বা “ভদভদিয়ে” পায়রা ওড়াও আমরা দেখিনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পসল্প’-খ্যাত বাচস্পতি মশায়ের তত্ত্ব-অনুযায়ী ধ্বনিচরিত্র থেকেই দৃশ্যমানতা জন্ম নেয়, বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না।
তবে ব্যাঙের ডাকের বিশ্লেষণ আর তার প্রত্যয় নিরূপণে লেখকের পাণ্ডিত্য ও রসবোধের যুগল-মিলন পাঠককে অনাবিল আনন্দ দেয়। “ঘ্যাঁ-ঘুঁ”/ “কোয়াক ঘঙ্, কো-য়া-ক ঘঙ্” / “কুঁ-উ-র কঙ্ কুঁ-উ-র কঙ্” এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-অন্বেষণে নিরত লেখক নিপুণ দক্ষতায় ব্যাঙের ডাককে মিলিয়ে দিয়েছেন ‘Gulliver Travels’এ লিলিপুটদের শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে।
গ্রামের এক সাঁওতাল দিদির সঙ্গে সই বা স্যাঙাত পাতানোর সূত্রে পরিচয় ছিল লেখকের, যোগাযোগ ঘন-ঘন না হলেও ঘনিষ্ঠ ছিল। তার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত রক্তক্ষরী দুটি পা দেখে ললিন তাকে এক জোড়া চটি কিনে দিয়ে এলেন পরবার জন্য, সঙ্গে কিছু টাকা। দীর্ঘ সময় পরে আবার সেই দিদির কুঁড়েঘরে পৌঁছে তিনি দেখলেন পদযুগল তেমনই হাজায় ভরা, রক্তাক্ত। “সেই চটি কি ছিঁড়ে গেছে”-- এই লাজুক প্রশ্নের উত্তরে “হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন মেজ্দি। বেরিয়ে এলেন বুকে জড়িয়ে একটা বড়সড় পোঁটলা। তারপর তো পরতের পর পরত ন্যাকড়া খুলে চলেছেন — ন্যাকড়া তো নয়, মনে হচ্ছিল অনার্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা ওল্টাচ্ছেন! অবশেষে সেই চটিজুতা, অবিকল সেই স্টিকার — “তোর দেওয়া চটিজুতা আমি কি পায়ে দিতে পারি রে?” হুবহু না হলেও স্বামী বিবেকানন্দের সেই আহ্বান মনে পড়ে কি যেখানে তিনি পিছড়ে-বর্গের ভারতবাসীকে স্মরণ করেছিলেন? সে আহ্বান বোধহয় শুধু বইয়ের পাতাতেই আটকে রয়ে গিয়েছে আর সাঁওতাল, মুন্ডা, ভুঁইয়া, তেলি, খন্ডায়েৎ, কৈবর্ত, কোরঙ্গা , হাড়ি, ডোম, লোধা, কাঁড়রা রয়ে গেছে একই জায়গায়।
সামাজিক স্তরভেদ-এরই একটি সঙ্কীর্ণতর অথচ গভীরতর খণ্ডদর্শন পাওয়া যায়, অনেকটা গল্পকথার ঢঙে, যদিও খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক — যেখানে বড়দার বিয়েবাড়ির বিবরণের মধ্যে হঠাৎ করে বাল্যস্মৃতির এক ঘটনা উঠে আসে। চারটে বেড়ালের বাচ্চার নাম রাখা হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ছোট্ট করে ছুঁয়ে যাওয়া মজাদার এই অণু-ঘটনা আঙুল দেখিয়ে দেয় বর্ণাশ্রমপ্রথার শূন্যগর্ভতার দিকে।
আর এই শূন্যগর্ভতাই আরও প্রকট হয়ে ওঠে হস্টেলের রান্নার ঠাকুর টুনি মিশ্র বা টুনি ঠাকুরের ঘটনায়। একদিকে হাতা-খুন্তি-ডেকচির কারবারি এই মানুষটিই ৫ টাকা দরে পৈতে বেচেন হাঁসদা, হেমব্রম, মাইতি, মাহাতোদের; নকল বামনাই-এর ভেক ধরাতে। এ’ছাড়া যজমানের ঘরে পুরুতগিরি তো আছেই! এ’হেন বর্ণময় দাপুটে চরিত্রটি যখন একটি গভীররাতে চালের বস্তা চুরি করে নিয়ে যাবার সময় ধরা পড়েন আমাদের ‘ললিন’ বা নলিনের হাতে, তখন তার কাতর অনুনয়-উপরোধ আর্তনাদের মত শোনায় — “মোকে ছাড়ি দে বাপা!” তুই তো জানু, মোর কেতে অভাব রে, ঘরে মোর একগণ্ডা বালবাচ্চা”। নলিনের পাঁচটাকা ধার মকুব করে দিয়ে আজীবন বিনামূল্যে পৈতের আশ্বাস দিয়ে যান টুনিঠাকুর। আর তখনই লেখকের কলমে ঝলসে ওঠে — “দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা”।
"মুহূর্তে কে যেন আমার কানের কাছে কালের মন্দিরাধ্বনি বাজিয়ে দিল। কংসাবতী শিলাবতী ময়ূরাক্ষী দ্বারকেশ্বর টটককুমারী রাড়ু-কঙ্কর ডুলুং সুবর্ণরেখা নদীবিধৌত ঝারিখন্ডের বঢ় বহড়া শাল পিয়াশাল ব আসন কুচলা কইম করম শিমূল মহুল জঙ্গলাকীর্ণ জঙ্গলমহালের আসনবনি কুড়চিবনি জামবনি শালবনি কেঁদবনি বনকাটি মুরাকাটি আমডিহা নিমডিহা বাঘমারি ভালুকঘরা ল্যাকড়াগুড়ি বাঘুয়াশোল বাছুরখোয়াড় গ্রাম অধ্যুষিত কোনো এক গ্রামে ভূমিজ মুণ্ডা কুম্ভার মাল সাঁওতাল হাড়ি বাউড়ি জনগোষ্ঠীর কোনো এক গোষ্ঠীতে আমার জন্ম , আমি জাতিতে বোধকরি আদিবাসী শূদ্রই হব। কিন্তু উৎকল-ব্রাহ্মণ টুনিঠাকুর আজ আমার কানে ফুঁ দিয়ে যেন বলছেন , "তুই আদিবাসী শূদ্র নোস্ নলিন, তুই 'ব্রাহ্মণ', 'ব্রাহ্মণ'।"
আর climax আসে তখন, যখন নলিন আবিষ্কার করে যে টুনিঠাকুরের উদোম গায়ে পৈতে নেই, সেই পৈতে ছিঁড়েই তিনি চোরাই চালের বস্তা বেঁধেছেন! পেটে ভাত না থাকলে যে ধর্ম হয়না, একথা তো সেই বীর সন্ন্যাসী বহুদিন আগেই বলে গিয়েছিলেন, আমরা কেন ভুলে যাই?
শেষ করবার আগে,(মোটামুটি ৮০/৯০ বছরের ব্যবধানে) দু’জন লেখকের দুটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করি, শুধু এইটুকু বোঝাতে, যে পথই পথিকের আশ্রয়। লেখা দুটির সাদৃশ্য কি শুধুই কাকতালীয়? না কি অণুপরমাণুর মৌলিক কাঠামোতেই কোনো বিস্ময়কর মিল রয়ে গিয়েছে?
(ক) পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশবনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? .... পথ আমার চলে গেল সামনে, শুধুই সামনে ... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে ...... মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায় ... পথ আমার তখনও ফুরোয়না ... চলে ... চলে ... চলে .. এগিয়েই চলে...” [পথের পাঁচালী]
(খ) কতদিন ভেবেছি ঐ যারা পশ্চিমে যায় তাদের পিছু পিছু আমিও যদি যাই, যদি চলতেই থাকি, চলতেই থাকি, তারা হয়তো যেতে যেতে ডাইনেবাঁয়ে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে পাশের গাঁয়ে তার পাশের গাঁয়ে, পাতিনা তালডাঙ্গা, ফুলবনী মালতাবনী কী দাঁড়িয়াবান্ধি খাড়বান্ধি রগড়াপদিমা কাঠুয়াপাল চর্চিতায় যে যার ঘরে, কুটুমঘরে ঢুকে যাবে — আমার পথচলা তখনও কিন্তু থামবে না। চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে ...” [সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা]
চতুর্দশ অধ্যায়ে (পৃ-১৪০) লেখক আবার হংসী মাঝির নৌকোতে। মাঝির নাবালক তথা ভবঘুরে মনের সঙ্গে নিজের মনেরও মিল খুঁজে পায় কিশোর লেখক। আর বড় হয়ে তিনিই লেখেন “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ” — অর্থাৎ মন যখনই চেয়েছে, তখনই বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। ভবঘুরে মানুষের স্বভাবই তো তাই, ভবঘুরে শাস্ত্রের বিধানই তো এই”।
আরো কে একজন জানি লিখে গেছিলেন “প্রভাত কি রাত্রির অবসানে? যখনই চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী — এসেছে প্রভাত।”
এই বইয়ের মাধুর্য্য বা চমৎকারিত্ব সেইখানেই: প্রতিপদেই এই বইটি মেখে চলে মাটির গন্ধ, অথচ আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে যায় গোটা আকাশটাকে! আর ধলেশ্বরী না হোক, এর পাশে পাশে বয়ে চলে সুবর্ণরেখা!
(পরবাস-৭৬, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯)