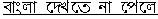রথ্যাঙ্কসগিভিং-এর ছুটি এসে গেছে। কাল, অর্থাৎ শুক্রবার থেকেই হলিডে শপিং সীজনের শুরু ‘ব্ল্যাক ফ্রাইডে-র সেল’ দিয়ে। তার পরেই হুড়মুড় করে এসে যাবে ক্রিস্টমাস। আর ক্রিস্টমাস মানেই কেনাকাটার হুল্লোড়। এই শপিং কমপ্লেক্স-এর দোকান-পাট, রাস্তা-ঘাট সব নতুন বিয়ে হওয়া বৌয়ের মত সেজে পথিকের বা হবু ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখানে আলোর মালা। প্রতি বছরের মত অন্যখানে হোসে ফেলিসিয়ানো-র গলায় শোনা যাচ্ছে চিরকালীন ক্রিস্টমাসী গান--ফেলিস নাভিদাদ/ আই ওয়ানা উইশ ইউ আ মেরী ক্রিস্টমাস/ ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট। আবার অন্যখানে মস্ত ক্রিস্টমাস ট্রির গায়ে নানা রঙের আলো ঝিকমিক করছে। আর সেই ক্রিস্টমাস ট্রির সামনে মস্ত লাল নাক-ওলা রুডল্ফ নামের নকল রেইনডিয়ারের পিঠে চড়ে লাল জামা-কাপড়, মাথায় লাল টুপি পরা, পেটমোটা নকল সেইন্ট ক্লাউস বা স্যান্টা ক্লজ সবে নর্থ পোল থেকে এসে হাজির হয়েছে তার গাড়ি-ভর্তি নানান উপহার নিয়ে। এখন সে হো-হো-হো করে তার স্লেড-লাগানো গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তার সামনে কয়েকটি খুব ছোট বাচ্চাকাচ্চা মা-বাবার হাত ধরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে ভাবছে স্যান্টা তার জন্য কী উপহার এনেছে।
কোন বিশেষ কিছু কেনার জন্য দোকানে যাওয়া ছাড়া উইন্ডো শপিং করা আমার ধাতে একেবারে সহ্য হয় না। বিশেষ করে এই ভিড়ের বাজারে দোকানে গেলেই আমার ঘুম এসে যায়। তাই আমায় দোকানের বাইরে রেখেই তবে নিশ্চিন্তে বাজার করা যায়, সেই সত্যটা আমার বৌ বেশ ভালোভাবে বুঝে গেছে। তাই রত্না, মানে আমার বৌ সীয়ার্স-এর দোকানে ঢোকার মুখে আমায় বসিয়ে রেখে একাই বাজার করতে গেছে।
হাতে বই থাকলে বাইরে বসে সেটা পড়তে পড়তে সময় কেটে যায়। তা না হলে সেলফোন খুলে এটা-সেটা দেখি, পড়ি। সেদিন তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে বই নিতে ভুলে গেছি। তাই হাতে কিছু পড়ার নেই। অতএব চুপচাপ লোক-দেখা ছাড়া কোন উপায় নেই।
এদিকে রত্না সেই যে গেছে আর আসেই না। তাই আমি বসে বসে চারপাশে লোকের ভিড় দেখছি। শুক্রবারের সন্ধের মুখ, তাই পুরো শপিং কমপ্লেক্স-টা একেবারে লোকে লোকারণ্য। তারা নানান দোকানে ঢুকছে, বেরোচ্ছে। কোন দোকানে বড় বড় অক্ষরে ‘সেল’ বিজ্ঞাপন লাগানো। সেখানে বেশ লোকজনের ভিড়। কেউ কেউ সেখান থেকে জিনিস-ভর্তি ব্যাগ হাতে বেরোচ্ছে। মুখে বেশ বিজয়ী-বিজয়ী ভাব, অনেকটা যুদ্ধে-জেতা সেনাপতির মত। বোঝা যাচ্ছে যে তারা বেশ ভালো দাঁও মেরেছে।
আমি যেখানে বসে আছি সেখানে কয়েকটা টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ রাখা আছে শপিং-ক্লান্ত জনগণের জন্য। হয়তো তারা একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে বাজার করতে পারে। আমি বসে বসে দেখছি আর অলসভাবে ভেবে চলেছি। হঠাৎ আমার ভাবনায় যতি পড়ল। দেখি আমার পাশের টেবিলে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে বসেছে। আরো একটি মেয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে। বয়স এদের কারোরই খুব বেশি নয়, টীন-এজার হবে। টেবিলে বসা ছেলেটি যে স্বাভাবিক নয় তা এক পলক চাইলেই বোঝা যায়। গায়ে জামা-কাপড় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চোখে চশমা। কিন্তু সেই চশমার মধ্য দিয়ে একটা উদভ্রান্ত দৃষ্টি ক্রমাগত চারিদিক জরিপ করে চলেছে। মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে লালা ঝরে পড়ছে, কিন্তু তার কোন খেয়ালই নেই। চেয়ারে বসার ভঙ্গিটাও একটু অদ্ভুত। মাঝে মাঝেই উঠে দাঁড়াচ্ছে, বেশ একটু কষ্ট করে। তাতে বুঝলাম যে ছেলেটি শারীরিকভাবেও বেশ অচল। ছেলেটির পাশের চেয়ারে বসা মেয়েটিও স্বাভাবিক নয়। কেমন ফ্যালফ্যাল করে চারিদিক দেখছে। অন্যেরা যে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে তার কোন হুঁশই নেই।
এরা বাদে এদের দলের দাঁড়িয়ে থাকা অন্য মেয়েটিকে দেখে অবশ্য স্বাভাবিক মনে হোল। তার চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে না। স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়েই সে লোকজনের যাতায়াত, দোকানের আলো ইত্যাদি দেখছে। আমি আশ্চর্য হয়ে এই মেয়েটি এদের মধ্যে কেন এইসব ভাবতে ভাবতে তার দিকে তাকিয়ে দেখি সে অতি মমতায় একটা টেডি ভাল্লুক তার কোলের মধ্যে ধরে রয়েছে। আর খানিকক্ষণ অন্তর-অন্তরই তার জাম্প স্যুটের পকেট থেকে হাত বার করে বুড়ো আঙ্গুল মুখে পুরে চুষতে আরম্ভ করছে, একেবারে বেহুঁশ হয়ে। আমার বুঝতে অসুবিধে হল না কেন এই মেয়েটিও এই দলের মধ্যে রয়েছে।
এদের সবায়ের পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা। গলায় একটা আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ সরু দড়ি দিয়ে ঝুলছে। বুঝলাম এ দেশের রীতি অনুযায়ী এই মহিলাই এদের সুপারভাইসার। এটাও বুঝলাম যে কাছেরই কোন মানসিক রোগের আবাস থেকে এই সুপারভাইসার ভদ্রমহিলা এদের মল-এ বেড়াতে নিয়ে এসেছে। সমস্ত শপিং সেন্টারটা যখন হৈ-চৈ, আলো, হাসি দিয়ে আসন্ন ছুটির দিনের আনন্দের অপেক্ষায় গর্ভবতী, তখন এখানে এই মানসিক রোগীদের উপস্থিতি কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর টেনে আনে। কিন্তু এই আনন্দের দিনে সেই খুশির একটু ছোঁয়াচ দেওয়ার তাগিদেই এই মানসিক ভারসাম্য ছেলেমেয়েদের শপিং কমপ্লেক্সে বেড়াতে নিয়ে এসেছে তাদের সুপারভাইসার।
এদের দেখে আমার অনেক ছোটবেলার বন্ধু হাবলুর কথা মনে পড়ে গেল। সেও একটু বড় হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। কে জানে হাবলু এখন কোথায়। তখন বয়স ছিল অল্প। আর হাবলুর সুস্থ জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া আমার মনে একটা স্থায়ী ও গভীর সহানুভুতির ছাপ ফেলে যায়। নিজেকে অনেক প্রশ্ন করেছি কেন এমন হল – কোন উত্তর পাই নি।
হাবলুর জন্যই হয়তো দেশে থাকতে মানসিক অসুখের ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে থাকলেও বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। তাই এ দেশে অর্থাৎ অ্যামেরিকায় আসার পর সুযোগ পেয়েই আমার এক সাইকায়াট্রিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে আমি এ দেশে মানসিক রোগগ্রস্ত লোকজনের চিকিত্সা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কেমন উৎসাহ নিয়ে জেনে নিই। সেই বন্ধুর মাধ্যমেই জানতে পারি যে এই লোকজনের চিকিত্সার নানান স্তর আছে। আর তার ব্যবস্থা স্টেট গভর্নমেন্টই করে। তবে স্টেট অনুযায়ী তার কিছু হেরফেরও হয়। সাধারণভাবে বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়ে, যারা হিংসাত্মক নয় বা যাদের মধ্যে আত্মহননের কোন ইচ্ছা দেখা যায় না, তাদের জন্য গ্রুপ-হোমের ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ তারা এক বাড়িতে থাকে, আর সেখানে স্টেট থেকে নিয়োজিত কেয়ার গিভার বা সোস্যাল ওয়ার্কার তাদের দেখাশুনো করে, মাঝে-মাঝে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যায়, প্রয়োজনে ওষুধ দেয় ইত্যাদি। আমার আজকের দেখা সুপারভাইসার এইরকম একজন কেয়ার গিভার। যাদের মা-বাবা খরচ দিতে পারে, তারা এই ব্যবস্থার বা আয়োজনের খরচ দেয়। আর যারা পারে না, তাদের সহায় স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অফ সোস্যাল সার্ভিসেস ও তার লোকজনেরা। এর পরের স্তরের নারী-পুরুষরা থাকে স্টেট মেন্টাল হসপিটালে। আবার যাদের হিংস্র হয়ে পড়া বা সুইসাইড করার প্রবণতা আছে, তাদের ব্যবস্থা অন্য হাসপাতালে। খরচ ও দেখভালের ব্যবস্থা এই জায়গাগুলোয়ও একই রকম।
আমার সাইকায়াট্রিস্ট বন্ধু ছাড়াও আমার কাজের সুবাদে বেশ কয়েক বছর আমি মানসিক ভারসাম্য-হারিয়ে ফেলা লোকজনদের খুব কাছ থেকে দেখেছি। সে অনেক বছর আগের কথা। আমার অফিস আর রিসার্চ ল্যাবরেটরি ছিল নিউ ইংল্যান্ড ইউনিভার্সিটি মেডিকাল স্কুলের ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা দশ তলা বাড়ির এক্কেবারে ওপরের তলায়। আসলে বাড়িটার মালিক ছিল স্টেট অফ ম্যাসাচুসেটস-এর একটা মানসিক হাসপাতাল, আর আমাদের ইউনিভার্সিটি সেই বাড়ির ওপরের কয়েকটা তলা ভাড়া নিয়ে থাকত, আর বাকি তলায় ছিল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা ‘পেশেন্ট’-দের থাকার জায়গা। বলা বাহুল্য যে এই পেশেন্টরা ছিল 'নিরীহ' পর্যায়ের।
আমার সেই ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া বন্ধু হাবলুর সূত্রে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা লোকেদের প্রতি আমার সহানুভুতি মনের গভীরে লুকিয়ে ছিল। আর এই বিল্ডিং-য়ে কাজ করতে শুরু করার পর থেকেই এই পেশেন্ট-দের প্রতি আমার নরম মনোভাবের কথা সবায়ের জানতে বাকি রইল না। এদিকে আমার সহকর্মীরা এদের সাথে মেলামেশা তো দুরের কথা কোন কোন সময় এলিভেটর বা বিল্ডিং-এর লবী-তে দেখা হলেই অনেক দুর থেকে অন্যদিকে হাঁটা দিত, যেন তারা বাঘ-ভাল্লুক বা অন্য কোন জীব-জন্তু হবে। কাছে গেলে আঁচড়ে-কামড়ে যদি দেয় – এরকম ভাব। কিন্তু আমি প্রায় যেচে যেচেই তাদের সুপারভাইসারের কাছে অনুমতি নিয়ে তাদের সম্বন্ধে জানতে শুরু করলাম, চেষ্টা শুরু করলাম এদের সাথে একটু জানা-চেনা করতে। এরাও তো মানুষ।
শীঘ্রই জানতে পারলাম যে এরা সবাই ইনসটিট্যুসনালাইসড মেন্টাল পেশেন্ট। সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। অনেক চিকিত্সা করার পর এদের মানসিক অবস্থায় একটু স্থিতি এসেছে বটে, কিন্তু তা ‘সুস্থ’ সমাজে ফিরে যাওয়ার মতো নয়। তাই এই হসপিটালটাই এদের দীর্ঘকালের থাকার জায়গা। যদি কেউ চিকিত্সায়, ওষুধবিষুধে ভালো হয়, তাহলে তারা তাদের নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। অবশ্য এটাও জানতে পারলাম যে এদের অধিকাংশই গরিব লোক, আর এদের ফিরে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। যেমন, এদেরই একজনকে একবার কিছুদিন না দেখে তার সোস্যাল ওয়ার্কার বা সুপারভাইসারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল সে কোন আত্মীয়ের কাছে ফিরে গেছে। মাস ঘুরতে না ঘুরতেই দেখি সে ফিরে এসেছে। এদের কারো কারোর জন্মের সময় মা হয় কোকেন-আসক্ত, বাবার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই এদের অনেকেই জন্মায় মানসিক ভারসাম্যের অভাব আর নানারকম অসুখ নিয়ে। আর বয়স যত বাড়ে ততই তাদের মানসিক অসুখ প্রকট হয়। অতএব, প্রথমে গ্রুপ হোম, আর তারপর এই মেন্টাল হসপিটালই এদের ঠিকানা জীবনের শেষ পর্যন্ত। বলা বাহুল্য যে এদের থাকা-খাওয়া, জীবনযাপনের সব খরচা আসে এই স্টেটের অর্থকোষ থেকে, যা আবার ভর্তি হয় ট্যাক্স-পেয়ারের পকেট থেকে।
এই পেশেন্টরা যে আমাদের বিল্ডিঙে নিজেরা ইচ্ছেমত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারে এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই। এদের চলাফেরা সবই থাকত সোস্যাল ওয়ার্কারের রক্ষণাবেক্ষণে। মাঝে মাঝে এদের দেখা মিলত আমাদের বিল্ডিং-এর লবিতে বা এলিভেটরে। দেখতাম তাদের সুপারভাইসার-রা দল বেঁধে এদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ-কেউ সিগারেট খাওয়ার জন্য, আর কেউ-কেউ স্রেফ বাইরের হাওয়া ফুসফুসে টেনে নেওয়ার জন্য। শীত–গ্রীষ্মেও এর কোন পরিবর্তন ছিল না। প্রচণ্ড ঠান্ডায়ও এদের দেখেছি ভারী কোট, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা পরে বাইরে যেতে। আসলে এইটুকু বাইরে যাওয়াই ছিল তাদের বাইরের আলো, বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ।
আমাদের বিল্ডিঙের পেশেন্টদের সবাই ছিল প্রাপ্বয়স্ক, কিন্তু আমি এদের মধ্যেই আমার ছোটবেলার হাবলুকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতাম। ঐ তো--হাবলু। বড় হয়ে সে ওই লোকটার মতনই হয়ে উঠত, ওইরকম রোগা, ঢ্যাঙ্গা চেহারা। এই চেহারা নিয়ে আমরা প্রায় তার পিছনে লাগতাম। বলা বাহুল্য এ সবই আমার অলীক কল্পনা। হাবলু এখানে আসবে কোথা থেকে। সে বেঁচে আছে আমার মনের মধ্যে, যেমন সেই ছেলেবেলায় দেখা।
কলকাতায় আমাদের পাশের বাড়ির হাবলুর সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল খুব ছোটবেলা থেকেই। পাশাপাশি বাড়ি, তাই রোজ দেখা, একই সাথে ওঠা-বসা। তারপর কিন্ডারগার্টেন ছাড়িয়ে একই স্কুলে, একই ক্লাসে ভর্তি হওয়া, স্কুলে যাওয়া-আসা, হোম-ওয়ার্ক করা সবই ছিল একসাথে। খেলা-ধুলো ও করেছি পাড়ার মাঠে। প্রথমে সব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কয়েকটা ক্লাস ওঠার পরেই পরিবর্তনটা এল। আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, কিন্তু আমাদের ক্লাস টীচার একদিন আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন – ‘হাবলু তো তোমার খুব বন্ধু। ইদানীং ওর কী হয়েছে বলো তো? ক্লাসে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। পড়াশুনোয় কোন মন নেই। এবারের হাফ-ইয়ারলী পরীক্ষার খাতায় তো সে কিছুই প্রায় লেখে নি। নম্বর দিই কী করে?’ অবশ্যই আমি কিছু উত্তর দিতে পারি নি। তারপর হাবলু কেমন দ্রুত পাল্টে গেল – চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, কথাবার্তা কেমন যেন অসংলগ্ন, কোন প্রশ্ন করলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে যেন চোখাচোখি করা মহা অপরাধ। আস্তে-আস্তে স্কুলে আসা অনিয়মিত হতে হতে একসময় বন্ধ হয়ে গেল। আমার খারাপ লাগলেও জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে আস্তে আস্তে হাবলুর কথা প্রায় ভুলেই গেছি।
একদিন ওর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাবলুর কথা মনে পড়ে গেল। একসময় কতো এসেছি এই বাড়িতে। কতো হুটোপাটি করেছি। কলিং বেল দিতে মাসিমা, মানে হাবলুর মা দরজা খুলে দিলেন।
–-আরে, এসো এসো খোকন। কতোদিন এ বাড়িতে আসো নি। সব খবর ভালো তো? তোমার মা ভালো আছেন?
--হাঁ মাসিমা, সবাই ভালো আছে। মাসিমা, হাবলু কেমন আছে? ও তো আর স্কুলে যায় না। নানা কারণে আমারও অনেকদিন খোঁজ-খবর করা হয় নি।
আমার প্রশ্নে মাসিমা দৃশ্যতই বিচলিত হলেন। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে বললেন-– তোমার বন্ধুর মানসিক অবস্থার কথা তো তুমি জানোই। ক্রমশ:ই খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শেষের দিকে একটা অদ্ভুত ব্যবহার শুরু করল। ব্লেডটেড যা হাতে পায় তাই দিয়ে নিজের রক্তপাত করতে শুরু করেছিল। কখন যে কী করে বসে কে জানে। শেষে ওর ডাক্তারের পরামর্শে ওকে একটা মেন্টাল অ্যাসাইলামে রাখা হয়েছে। সেখানে ও অনেকটা ভালো আছে। কিন্তু ওকে কোনদিন বাড়ি ফিরিয়ে আনা যাবে কি না কে জানে। মাসিমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।
সেদিন আমি মাথা নিচু করে চলে এসেছি। অনেক-অনেক বছর পর আমাদের এই বিল্ডিং-এর পেশেন্টদের দেখে আমার হাবলুর কথা মনে পড়ে যেত। তাই এখানে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই আমি এদের অনেককেই নাম ধরে চিনতে আরম্ভ করেছি। দেখা হলে সৌজন্যমূলক ‘হাই’ বা একটু মৃদু হাসি দিতে আরম্ভও করেছি, আর তাদের অনেকেই আমার ‘হাই’-এর প্রত্যুত্তর দিত নিজের মত – কেউ উত্তরে ‘হাই’, কেউ আবার একটু মুখ তুলে অল্প হাসি দিয়ে চেনার ভাব করত। কেউ আবার আমায় আদৌ পাত্তা দেয়নি। তাদের সোস্যাল ওয়ার্কাররা প্রথম-প্রথম আপত্তি করলেও পরে কিছু বলত না।
পেশেন্টদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ‘হাই-হ্যালো’-র বাইরে গিয়ে দেখা হলে আমার সঙ্গে বেশ ভাব জমাবার চেষ্টা করত। যেমন উইলিয়াম বা বিল। সে ছিল প্রায় সাত ফুট লম্বা একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে। বয়স কুড়ির বেশি হবে না। কিন্তু লম্বা ছাড়াও এই বয়সেই চেহারায় বেশ বড়সড়। গরমের সময়ে সে যখন শর্টস পরে ঘুরে বেড়াত, তার পা দুটো শর্টস-এর খোলের মধ্য দিয়ে প্রাচীন রোমান স্থাপত্যের টাসকান কলামের মত বেরিয়ে থাকত। তার পায়ের মাপের কাছে হাতির পায়ের উপমাও হার মানে। অনেক দিন ভেবেছি এর পায়ের মাপে জুতো কোথায় পাওয়া যায়।
কি করে যেন তার আমাকে পছন্দ হয়ে গেল। দেখা হলেই সে দুর থেকে তার প্রায় বোমা ফাটার মত গলার আওয়াজে ‘ড্যাড, ড্যাড’ বলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। কতদিন আমি তাকে বলেছি আমায় ‘ড্যাড’ বলে ডেকো না, অস্বস্তি হয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। এদিকে আমার বেইজ্জতির একেবারে একশেষ। আমার সহকর্মীদের কেউ কেউ মুচকি হাসি হাসতে ছাড়ে নি। যেন বলতে চেয়েছে – তোমায় বলিনি, এদের সাথে এত মাখামাখি ভালো নয়। এখন ঠেলা সামলাও। বিল-এর সুপারভাইসারও আমায় বলেছে যে বিল কথা বলতে চাইলে আমি যেন পাত্তা না দিই। কিন্তু আমি বলেছি-–কেন, বিলও তো মানুষ। আর আমি এই বিল্ডিং-এ এতদিন যাতায়াত করছি। এরা আমার তো কোন ক্ষতি করে নি। আমার হাবভাব বুঝে সেই সুপারভাইসার হাল ছেড়ে দিয়েছিল, ও আমাদের কথাবার্তা বা মেলামেশায় কোন বাধা দেয় নি।
কোন এক বছর, সালটা ঠিক মনে নেই, থ্যাঙ্কসগিভিং-এর ঠিক আগে। বিল হঠাৎ আমায় একেবারে ধরে বসল। বেশ আদুরে-আদুরে গলায় বলল- “ড্যাড, আই ওয়ানা কাম ট্যু ইয়োর প্লেস ফর থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনার।”
এ তো ভারি বিপদ। রত্না লোকজন ডাকতে ভালবাসে, তাই আপত্তি করবে না। কিন্তু, ওর এই বিশাল বপু আমার ছোট গাড়িতে ঢুকবে কী করে? আর যদি কোনরকমে ঢোকেও, গাড়ির ট্রান্সমিশন-তো বোধহয় ওর ওজনে ভেঙে পড়বেই পড়বে। তা ছাড়া ওর সুপারভাইসার ওকে বাইরে যাওয়ার সম্মতি দেবে কেন? কিন্তু সে কথা তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। ওর ধারণা আমি যদি ওর সুপারভাইসারকে ভালোভাবে বলি তাহলে আমার সাথে যাওয়ার কোন অসুবিধেই হবে না।
কিছুদিন নানান ভুজুংভাজুং দিয়ে ওকে সামলেছি। শেষে ওর সুপারভাইসারকে বলতে সে বলল কোনমতেই তা সম্ভব নয়। যাক, তাহলে আমার ঘাড় থেকে বিল-কে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ভুত নামল। কিন্তু এ ভবি ভোলার নয়। বিল একেবারে নাছোড়বান্দা। বাড়িতে নাহয় যাওয়া যাবে না। কিন্তু থ্যাঙ্কসগিভিং-এর খাওয়াটাতে তো কোন আপত্তি নেই। সেটা হতেই হবে। অগত্যা ঠিক হল থ্যাঙ্কসগিভিং-এর ঠিক আগের দিন ওর পছন্দমত খাওয়া ওর জন্য আমি কিনে আনব, আর সে এখানে অর্থাৎ ওর নিজের জায়গায়ই সেই খাবার খাবে। এই শুনে বিল একেবারে আনন্দে আত্মহারা। সে বিশ্বাসই করেনি যে ওর ‘ড্যাড’ ওকে সত্যি-সত্যিই থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনার খাওয়াবে। অতএব, তার ফর্দ মতো ম্যাকডনাল্ড রেস্তোরাঁ থেকে কেনা হল চারটে ‘বিগ ম্যাক’, দুটো কুড়ি পীসের ‘ম্যাকনাগেটস’, দুটো লার্জ ফ্রাইস আর দুটো লার্জ কোক। নির্দিষ্ট দিনে আমি খাবারের মস্ত ব্যাগ নিয়ে হাজির। আমাদের বিল্ডিঙের ক্যাফেটারিয়ায় বসে আমি আর ওর সুপারভাইসার। আমাদের সামনে সে খেয়ে গেল, যেন সেই ‘হাপুস-হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপিঁড়া কাঁদিয়া যায় পাতে’। আর খাওয়ার শেষে একটা মস্ত ঢেঁকুর তুলে বলল – ‘‘ড্যাড, আই নেভার হ্যাড আ থ্যাঙ্কসগিভিং দিস গুড।’’
আহা রে, গরীব লোক। হয়তো নিজের বলতে কোন থাকার জায়গাই ওর কোনদিন ছিল না। আমি বসে বসে ওর খাওয়া দেখেছি আর ভেবে চলেছি – হয়তো জন্মের পরেই ওর মা ওকে ফেলে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। কোন অরফ্যান হাউসে বড় হয়েছে। হয়তো একটু বড় হওয়ার পর ডিপার্টমেন্ট অফ সোস্যাল সার্ভিসের লোকেরা ওর দেখাশোনা করে বড় করেছে। কিন্তু অনেকের ভাগ্যে তো তাও জোটে নি।
মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় দেখা বিশুপাগলার কথা। কোথায় যে সে থাকত কে জানে। তবে আমাদের পাড়ায় সে ঘুরে বেড়াত ছেঁড়া জামা-কাপড়, একমুখ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি নিয়ে। পাড়ার ছেলেরা তাকে দেখতে পেলেই ‘পাগলা, পাগলা’ বলে তার পিছনে দল বেঁধে তাড়া করত, আর বিশুপাগলা তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মাঝে এক দুর্বোধ্য ভাষায় তাদের গালাগালি দিত। তাতেও ছেলেগুলোকে দমাতে না পেরে একসময় সে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলত। তখন সেই ছেলের দল ওর পিছু ছাড়ত। তারপর একদিন সে আমাদের পাড়ায় আসা বন্ধ করে দিল। কী হল তার কে জানে।
এদিকে থ্যাঙ্কসগিভিং-এর সেই খাবার খেয়ে বিল কী খুশি। কতবার যে সে--“থ্যাঙ্ক ইয়ু, ড্যাড” বলল তার কোন ইয়ত্তা নেই। তারপর সুপারভাইসরের পিছন পিছন সে নিজের জায়গায় চলে গেল। বেশ কয়েক বছর আগের ব্যাপার এইসব।
আমি মল-এর বেঞ্চে বসে দেখছি আর এইসব ভেবে চলেছি। আর আমার থেকে অল্প একটু দুরে সেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা ছেলেমেয়েগুলি তাদের সুপারভাইসরের সাথে ‘সুস্থ পৃথিবীর স্পর্শ’ নিয়ে চলেছে। এর মধ্যে রত্নার ফোন – ‘আমার কেনাকাটা শেষ। তবে এতোগুলো ব্যাগ নিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছে। তুমি একটু ‘মেসি’-র দোকানের সামনে চলে এসো।’
রত্নার কাছ থেকে কিছু ব্যাগ নিজের কাছে হস্তান্তরিত করে দুজনে সীয়ার্স-এর দোকানের এন্ট্রেন্স-এর দিকে হাঁটা দিলাম, কারণ ওই দোকানের পার্কিং লট-এই আমাদের গাড়ি রাখা আছে। মল-এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বেশ খানিকটা পথ, প্রায় মিনিট দশেকের হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে, লোকজন, দোকানপাট দেখতে দেখতে আমি রত্নাকে ‘ওদের’ কথা বলতে আরম্ভ করলাম। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা লোকেদের কথা ও আমার মুখে আগে অনেক শুনেছে। আর তাদের প্রতি আমার দুর্বলতার কথাও সে জানে। সে জানে আমার ছোটবেলার বন্ধু হাবলুর কথা, আর তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কথা। আর সেই বিশাল-বপু বিল বা উইলিয়াম, সে তো প্রায় এসেই গিয়েছিল আমাদের বাড়ি থ্যাঙ্কসগিভিং-এর ডিনার খেতে।
কথা বলতে বলতে আসছি। আমি সীয়ার্স-এর দোকানের কাছে যেখানটায় বসেছিলাম তার কাছে আসতে বেশ একটু খটকা লাগল। একি! কী ভাবে ভোজবাজির মতো জায়গাটা এক্কেবারে পাল্টে গেছে। প্রথমত, সেই ছেলেমেয়েগুলি ও তাদের সুপারভাইসার কাউকেই চোখে পড়ল না। তা, তারা তো চলে যেতেই পারে। কিন্তু সেই বসার জন্য চেয়ার-টেবিল সেসব কিচ্ছু নেই। তার জায়গায় দেখি একটা আলো-ঝলমল মস্ত ক্রিস্টমাস ট্রি কারা সাজিয়ে রেখে গেছে। আর সেই গাছের সামনেই একটা বেশ সাজানো-গোছানো চেয়ারে সাদা বর্ডার দেওয়া লাল লম্বা জোব্বা, মাথায় সাদা বর্ডার দেওয়া লাল টুপি, হাতে লাল দস্তানা আর পায়ে লাল জুতো-মোজা পরা এক আসল, অর্থাৎ মানুষ স্যান্টা ক্লস বসে। তার লম্বা আলুলায়িত ধবধবে সাদা দাড়ি, আর মুখ ভর্তি সাদা গোঁফ আর জুলফি। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। ঠিক যেমন ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। তার ভুঁড়ো কোলে একটা ছোট্ট বাচ্চা বসে অবাক হয়ে স্যান্টার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আর, তার মা-বাবা নানা দিক থেকে সেই দৃশ্যের ছবি তুলতে ব্যস্ত।
এইতো কয়েক মিনিট আগেও তো এই জায়গাটা অন্যরকম ছিল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। আরে, স্বপ্ন দেখছি না কি? চোখ কচলে আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখি – ও মা, ক্রিস্টমাস ট্রি, স্যান্টা ক্লস - এসবের এক পাশে ‘নেটিভিটি’-র চমত্কার একটা দৃশ্য ফুটে উঠেছে। আমাদের চোখের সামনে দেখি একটা জলজ্যান্ত লাল-সাদা ঘোড়া তার কেশরওলা লম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে সবায়ের দিকে। তার আস্তাবলে খড়-বিচালির ওপর সেই সুপারভাইসার ভদ্রমহিলা মা মেরী সেজে বসে রয়েছেন। আর তার কোলে ছোট্ট যীশু শুয়ে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি যীশুর গায়ের রঙ বেশ ময়লা, মাথায় কৃষ্ণাঙ্গদের মতো ঘন কালো আর কোঁচকানো চুল। আর দেখতে? এ যে আমার সেই অনেক চেনা বিল। সে এখন মায়ের কোলে শুয়ে আছে। সে কি আমার দিকে তাকিয়ে একটা দুষ্টু হাসি দিল, বলে উঠল – হাই, ড্যাড? কে জানে, কিন্তু মনে হল এখন সে মায়ের কোলে শান্তিতে শুয়ে আছে - ড্যাড, ড্যাড বলে চেঁচিয়ে উঠবে না। মলের উঁচু সিলিং-টা হঠাৎ খোলা আকাশের মত লাগছে। আর কী আশ্চর্য সেই আকাশে কয়েকটা তারা জ্বল-জ্বল করে জেগে রয়েছে। আশ্চর্যর পর আশ্চর্য! ভালো করে চোখ কচলে দেখি সেই তিনটে ভারসাম্য-হারানো ছেলেমেয়ে বহুশ্রুত কাহিনীর সেই তিন জ্ঞানী লোকের সাজে যীশু ও মেরীকে ঘিরে নতজানু হয়ে বসে। তাদের মাথা সামনে নামানো, হাত প্রণামের ভঙ্গিতে জড় করা। দ্য সেভিয়র ইস বর্ন।
একপাশে হাতজোড় করে দাঁড়ানো জোসেফ। কী আশ্চর্য! এ যে দেখি আমার সেই ছোটবেলার বিশুপাগলা। আরও আশ্চর্য। যীশুর দিকে হাতজোড় করে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখতে একেবারে অবিকল আমার ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া সেই হাবলু।
(পরবাস-৮৫, ১০ জানুয়ারি, ২০২২)