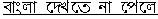[আমাদের নতুন বাড়ির ঠিকানা দেখে বন্ধুদের অনেকেরই ভুরু কুঁচকে গেল: বোলিংব্রুক?! ‘নেপারভিল’ (আভিজাত্য) ছেড়ে ওখানে গেলেন কেন? ওখানে তো ‘কালো’ আর লাটিনোদের ভিড়?!”--এই সব গপ্পে শনিবার সন্ধের বাঙালি আড্ডার পরিবেশ যখন বেশ জমে উঠেছে, চিকেন বটি কাবাব থেকে সর্ষে ইলিশ সবই ‘রেডি’, হঠাত্ দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম, আর তারপরেই ‘পল রবসনীয়’ স্বরে “হ্যালো, মিসেস বোস’—রনখ-এর গলা, আমার পুত্রের পরম বন্ধু, পুরোনো প্রতিবেশী এবং আমাদের পুত্রসম আফ্রো-আমেরিকান ছেলেটির উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলাই বাহুল্য, আমাদের ‘কাণ্ডজ্ঞানহীনতা' সম্বন্ধে জমায়েত ভারতীয় বন্ধুদের সন্দেহের কোনও অবকাশ রইল না আর! শিকাগোর দিশী আড্ডায় যোগ দিতে গিয়ে এমন অজস্র অভিজ্ঞতা জমা হচ্ছে। স্রেফ সামাজিকতার দায়ে বেশিরভাগ সময় অগ্রাহ্য করতে হয় ভেতরের প্রতিক্রিয়াকে, আবার কোনো কোনও সময় যেন সামলানো দায় হয়ে ওঠে—এমনই এক মুহূর্তে বসে এই লেখা। খানিকটা কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টায়। আশাকরি পাঠক সে কথা বুঝবেন।]
“There is a great difference, however, between the optimistic mobility, the intellectual liveliness, and ‘the logic of daring’…..and the massive dislocation and waste, misery and horrors endured in our century’s migrations and mutilated lives”.
---Edward W. Said
(‘Culture and Imperialism’, 332)
আমেরিকার প্রবাসী আড্ডায় যোগ দিতে গিয়ে অনেক সময়েই অস্বস্তি আর বিষাদ বহন করে ফিরতে হয়। ভারতীয় মধ্যবিত্তের একটানা সাফল্যের স্রোতের পরিবেশনে কোথায় যেন লুকনো থাকে এক মস্ত ‘হার’। ব্যক্তিগত নয়, গোটা সমাজটারই। বারবার মনে পড়ে “The Wretched Of The Earth”, Frantz Fanon-এর সেই ধ্রুপদী রচনা, যেখানে তিনি মনোবিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাটাছেঁড়া করে দেখেছেন ঔপনিবেশিক মানসিকতা, তার ক্ষত, তার বিকৃতি। ইউরোপীয় শাসনকে উচ্ছেদ করার সঙ্গে সমাজটার নিজের ভেতরের গভীর ক্ষতকে সরাসরি মোকাবিলা না করতে পারলে মুক্তি অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়—Fanon-এর এই অনুমান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও বোধহয় প্রযোজ্য, গান্ধীজী-পণ্ডিতজীর মতোো প্রগতিশীল নেতৃত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও। সে সময়ের রাজনৈতিক ফলশ্রুতি হিসেবেই ১৯৪৭-এর পরবর্তী অগ্রগতির সুফলের প্রায় সবটুকুই যদিও ধরা থাকে মধ্যবিত্তের ভাণ্ডারে, সমাজ-সংস্কারের মূল কাজগুলি যদিও বা প্রান্তেই পড়ে থাকে, মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক নতুন গণতন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় বেশ খানিকটা সফলতা যে লাভ করেছে তা অনস্বীকার্য, এবং সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা খানিকটা কৃতিত্ব দাবি নিশ্চয়ই করতে পারে। তবুও, আজ মনে হয় আমাদের সেই শিক্ষাব্যবস্থায় খানিকটা ভারসাম্যের অভাব গোড়া থেকেই ছিল। প্রবাসী-ভারতীয়ের চিন্তার দৈন্যতা হয়তো সেই অভাবেরই ইঙ্গিত। সফল ভারতীয় কারিগরী বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের তেমন সচেতনভাবে জানা হয় না পশ্চিমের (নিজের সমাজেরও), বিশেষ করে আমেরিকার শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাস, তাই তাঁরা বুঝতে পারেন না কেন এদেশের আফ্রো-আমেরিকান গোষ্ঠীর পিছিয়ে থাকা আমাদের মতো নবাগত সুবিধাভোগী ভারতীয়ের সাফল্যের মাপকাঠিতে বিচার করতে যাওয়া ভুল। ঠিক যেমন করে তাঁরা মনে রাখেন না হাজার বছরের বর্ণাশ্রমের ক্ষত কত গভীর, কয়েক শতকের ঔপনিবেশিক শাসন সেই সমস্যাকে কেমন করে ব্যবহার করেছে, আর তাই আমাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সাফল্য/ব্যর্থতা কতটা তার দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত। আসলে, ভারতীয় উপমহাদেশে এই গভীর বৈষম্যের দৃঢ়-প্রোথিত কাঠামোকে আমূলে ভেঙে ফেলার প্রয়োজনে দেশব্যাপী সংগঠিত আন্দোলন কখনোই গড়ে ওঠেনি, যেমনটি ঘটেছিল আমেরিকার মাটিতে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, ইতিহাসের হেরফেরেই—মস্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ারে। আমাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তা মূলত ‘রাষ্ট্রদেহের কাঠামোকে স্পর্শ করলেও সমাজদেহের মজ্জায় গিয়ে মেশেনি’ (দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, ১৩)। স্বাধীনতা-উত্তর কালের মধ্যবিত্ত-মুখী/কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাও সেই একই অপুষ্টিতে দুষ্ট। 'গণতান্ত্রিক প্রত্যয় আমরা আন্তরিক অনুসন্ধান থেকে ততটা পাইনি--যতটা পেয়েছি বিদেশী-শিক্ষার আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হিসেবে' (দীপংকর চট্টোপাধ্যায়)। আর যেটুকু রয়েছে সেটুকুও সীমিত একটি ছোট্ট এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে। বলাই বাহুল্য, এই সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল দাঁড়াল বড় অদ্ভুত। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসে সনাতনী সমাজের উঁচু-নীচুর হিসেব সেঁটে রইল অনেকটা সেই মহাভারতের কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো, আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় গণতান্ত্রিক বোধ গড়ে তোলার সক্রিয় উদ্যোগের অভাব সম্ভবত সেই কারণেই। আধুনিক গণতন্ত্রে নাগরিকের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বোধ এখনও তাই বেশ ঝাপসা। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভূমিকা পালনে বেশ খানিকটা ব্যর্থ বলেই বোধ হয়। এই সব সমাজ-সচেতনতা, ইতিহাসবোধ যে বিষয়গুলি চর্চার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে সেগুলি সক্রিয়, সচেতন মন নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ নেই এই বিজ্ঞান-কারিগরী বিভাগের ছাত্রদের, যান্ত্রিক ভাবে কিছু ‘পেপার’ লেখার বাইরে। অথচ এ সব বিভাগেই তো ছাত্রদের ভিড় বেশি। কেবলমাত্র কিছু কারিগরী কলাকৌশল আয়ত্ত করার বিষয়েই মনোনিবেশ করতে হয় জাতীয় এবং ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের কথা মাথায় রেখে, কারণ সিলেবাসগুলির তাই ঝোঁক। কেবল ভারতবর্ষই নয় বেশিরভাগ সমাজেই এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে, আধুনিক চীন হয় তো যার মস্ত উদাহরণ। অথচ, ধনতান্ত্রিক আমেরিকার ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর সমাজ-সচেতনতা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি, কোনো কোনও ক্ষেত্রে বিস্মিত হওয়ার মতো। বর্ণবিদ্বেষ এবং সিভিল রাইটস আন্দোলনের ইতিহাস একেবারে শুরু থেকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত, ‘নতুন বিশ্বের' গোড়াপত্তনে যে ভয়ংকর গণহত্যার বৃত্তান্ত জড়িয়ে আছে এসব সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল, কেবল পুঁথিগত পাঠেই নয়, নানা রকম অভিনয়, নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের সমাজকে/ইতিহাসকে বেশ খানিকটা নিরপেক্ষ চোখে দেখার অভ্যাস তৈরি হযে যায়। তারা চেষ্টা করে এই মাটির হারিয়ে যাওয়া সভ্যতাকে খুঁজে পেতে, আর তারই সঙ্গে পরিচিত হয় পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সম্পর্কে। পাঠ্যসূচির প্রণেতারা বুঝেছিলেন এই শিক্ষাই শেষ পর্যন্ত আধুনিক গণতন্ত্রকে সজীব রাখার অন্যতম হাতিয়ার। বর্ণবিদ্বেষকে মুছে দেওয়া যায়নি, তবে ছেলেমেয়েরা শিখছে এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কেমন করে লড়াই করতে হয়। আক্ষেপের কথা, গান্ধীজী-আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে যে নতুন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ জন্ম নিয়েছিল সেই দেশের ইস্কুল-কলেজের পাঠে আমাদের হাজার-হাজার বছরের বর্ণাশ্রমের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রায় কোনও চেষ্টাই চোখে পড়ে না। জাতপাত, হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা খোলাখুলি আলোচনার বদলে যেন একটা ‘ট্যাবু’ (taboo) হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ-হঠাত্ কিছু ভয়ংকর হিংসার ঘটনা তাত্ক্ষণিক সাড়া জাগায়, আবার সমস্তটা নিমেষে মিলিয়ে যায়। ফলে আজও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স-বর্ণ, অসমবর্ণ হিসেব-নিকেশ মেলানোর রীতি অব্যাহত, কৌলিন্যের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে মস্ত ঘটা করে উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়, আর আমরা, আমন্ত্রিতেরাও দ্বিধাহীন চিত্তে সে ‘আনন্দযজ্ঞে’ যোগ দিতে যাই। কে মনে রাখে প্রগতিশীল ভারতীয়ের কাছে বি.আর. আম্বেদ্করের একান্ত আবেদন ‘হিঁদুয়ানার’ আচার সরাসরি পরিত্যাগের, নইলে জমে থাকা জঞ্জাল জমেই থাকে।
আমাদের দেশে কলেজ-ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান-কারিগরী বিভাগের সিলেবাসের লক্ষ্য ছাত্রদের কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে দক্ষ করে তোলা, ব্যক্তিগত এবং জাতীয় আর্থিক লাভের সীমিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ছাত্রদের সচেতন, সক্রিয় নাগরিক করে তোলার দায় থাকে না IIT কিংবা IIM-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলির, কিছু যান্ত্রিক চেষ্টা ছাড়া। (সাম্প্রতিক কিছু উদ্যোগ নজরে পড়লেও এখনো নিতান্তই ব্যতিক্রম, মূলস্রোতের বাইরে)। বিশ্বজোড়া এই সংকট আরও যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে, সব সমাজই তড়িঘড়ি আর্থিক সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয়ে ওঠায়। এই জটিল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন শিক্ষা-ব্যবস্থার সংকীর্ণতার সঙ্গে আজকের সামাজিক দুর্যোগের যোগাযোগ কতটা নিবিড়।
সুস্থ গণতন্ত্র এবং শিক্ষাব্যবস্থা: আচার-বিচারের পাশাপাশি যুক্তি-বুদ্ধির ঐতিহ্য ভারতবর্ষে নেহাত কমদিনের নয়। “বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়”(for the benefit of many, for the happiness of many)—ভাবলে বিস্মিত হতে হয় ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের গৌতম বুদ্ধের মন্ত্রই আজকের ‘occupy activist’-দের মুখে মূল মানবিক দাবি হিসেবে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কানে ভেসে আসছে। প্রতীচ্যে সক্রেটিস (c. 469 BCE – 399 BCE) এবং প্রাচ্যে গৌতম বুদ্ধ (c. 563 BCE )---এঁদের মিলিত দর্শন একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম শর্ত এবং চ্যালেঞ্জ: যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ, সর্বজনীন কল্যাণ, প্রাকৃতিক সম্পদকে কেবল ভোগের স্বার্থে ধ্বংসের বদলে তাকে রক্ষা করার মধ্যে দিয়ে সামাজিক উন্নয়নকে দীর্ঘস্থায়ী, মজবুত (sustainable) করে তোলা। আমরা জানি কেমন করে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে সচেতন চিন্তাবোধের (critical thinking) প্রশ্ন তোলায় সেসময়ের সমাজ-শাসকের হাতে প্রাণ দিতে হয়। আর প্রাচ্যে আমাদের গৌতম বুদ্ধ, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে অযথা সময় নষ্ট না করে বাস্তব জীবনে যা কিছু ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে তাকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখার কথা বলেন। জাতপাতের, অর্থহীন আচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত আন্দোলনও তাঁরই নেতৃত্বে। বুদ্ধেরও প্রাণসংশয় ঘটেছিল বই কী, ভাগ্যক্রমে তা এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর মতো যৌক্তিক বোধের প্রয়োগে সুস্থ সামাজিক উন্নতির শর্ত হিসেবে সমাজের সমস্ত স্তরের নাগরিকের হিতাকাঙ্ক্ষার প্রশ্নটি মেলানোই মানব সমাজের destiny বা লক্ষ্য। বুদ্ধের ক্ষেত্রে আমরা প্রাণদণ্ডের বদলে আরও মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করলাম--অর্চনার বেদীতে বসিয়ে প্রত্যেকদিনের জীবন-অভ্যাস থেকে দূরে, বহু দূরে ঠেলে দিলাম। মৃত্যুর মুহূর্তে নিকটতম শিষ্য আনন্দের কাছে তাঁর শেষ আবেদন: আমাকে পূজার আসনে বসিও না। তাই মনে হয় আজকের ‘তালিবান’-দের হাতে ‘বামিয়ান বুদ্ধের’ নিগ্রহ ইতিহাসের যেন এক মস্ত ‘আয়রনি’ (irony) হয়ে রইল।
আবার সেই অমিতাভকেই যেন বহু জন্মান্তরে আমরা খানিকটা পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে সচেতন করেছিল আমাদের তত্কালীন শিক্ষাব্যবস্থার চরম অভাব সম্পর্কে। নিজের ভেতরের সেই তাড়া থেকেই জন্ম নিয়েছিল ‘শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী’। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রথম থেকেই স্পষ্ট, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকের প্রধান দায় দুটি: ছাত্রদের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, আর ইস্কুলের পরিবেশকে এমনভাবে সাজানো যা শিশুর নিজস্ব সৃজনশীল দিকগুলির বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে। বীরভুমের ধূ-ধূ প্রান্তরে গিয়ে শিশুদের জন্য পাঠশালা তৈরির তাগিদকে সেইসময় কিন্তু তাঁর নিজের মূলস্রোত সমাজ ‘কবির ক্ষ্যাপামি' ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাঁর ইস্কুলের পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়েছিলেন পূর্ণ বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টিতে। তাঁর মতে ছাত্রকে নিজের সঙ্কীর্ণ জাতীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি সীমারেখার বাইরে গিয়ে গোটা মানব-পরিবারের দায়গ্রহণে দীক্ষিত করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। তিনি বুঝেছিলেন এই চেষ্টাটুকুর সফলতার ওপর নির্ভর করছে মানব সভ্যতার বাঁচা-মরা। আজকের অজস্র খণ্ডে বিভক্ত মানবসত্তা পৃথিবী জুড়ে কী ভয়ংকর প্রলয় ঘনিয়ে তুলেছে। কবির সেই উপলব্ধির গুরুত্ব আজ মানবসংসারকে কী মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই না শিখতে হচ্ছে। সে-সময় নিজের দেশে তেমন সাড়া না মিললেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষাবিদ্রা এসেছেন কবির সেই নিরীক্ষা দেখতে। তাঁর সেই লিবারল আর্টস মডেলের ইস্কুলে ছাত্রছাত্রীরা মুক্তি পেয়েছিল দমবন্ধকরা আবহাওয়া থেকে, শুধু দেওয়াল সরিয়ে দিয়েই নয়, পঠন-পাঠন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। পাঠের সঙ্গে নাচ-গান-ছবি আঁকা, অভিনয়ের সাহায্যে। অভিনয়ে জোর দিয়েছিলেন অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা বুঝতে তা সাহায্য করবে—এমন বিশ্বাস থেকে।
বর্তমান পৃথিবীর নানা অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক হিংসা, অনিশ্চয়তার শেষ পর্যন্ত সমাধান সুস্থ এবং মজবুত গণতন্ত্রের বিকাশে--একথা মেনে নিলে গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে আমাদের প্রধান বাধাগুলি কী--সেই আলোচনা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক নাসবমের ব্যবহৃত উদাহরণটিই উল্লেখ করা যাক--শিশু তার জন্মমুহূর্ত থেকে শেখে কেমন করে তার আশেপাশের মানুষকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে, অন্য মানুষটির প্রয়োজনের মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা বা প্রয়োজন সে বোধ করে না। ধীরে ধীরে সে বুঝতে শেখে তার নিজের বাইরে অন্য মানুষের অস্তিত্ব, তার নিজস্ব প্রয়োজন, দাবি-দাওয়ার বাইরে অপরের সেই একই দাবি/প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ হতে, শেখে কেমন করে অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে আশপাশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। ঠিক শিশুর মতোই মানবসমাজ দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের গণতান্ত্রিক চেহারায় পৌছেছে, এই মডেলটিই বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে গ্রহণযোগ্য, যার মূল শর্ত পারস্পরিক বোঝাপড়া, পারস্পরিক নির্ভরতা। আর তাই অধ্যাপক মার্থা নাসবমের মতে “clashes of civilizations”-টা কোনও বাইরের ঘটনা নয়, মানুষের অন্তরের লড়াই নিজের সঙ্গে নিজের। আধুনিক পৃথিবীতে আমরা আর কিছুতেই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছি না, না চাইলেও একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এক প্রান্তের ছোট ঘটনা পৃথিবীর অন্য প্রান্তের অর্থনীতিকে, সমাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। এই পারস্পরিক নির্ভরতা কেবল সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতেই সীমিত নয়, ধনতন্ত্রের সফলতাও শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে এক ধরনের সমবায়িক ব্যবস্থার ওপর, যার মস্ত নিদর্শন আমেরিকা নিজেই।
আজকের আর্থিক-সামাজিক দুর্যোগের মুহূর্তে সচেতন নাগরিকের দায়-দায়িত্বের প্রশ্নগুলি বিশেষ করে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ১৯২৯ সালে ‘গ্রেট ডিপ্রেশন’-এর সময়, আংশিক সমাধান মিলেছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিখ্যাত ‘নিউ ডীল’('New Deal’) পরিকল্পনার রূপায়নের মধ্যে দিয়ে। আর্থিক দূরাবস্থার সমাধানের নামে সরকারের একাংশ এবং সমাজের সুবিধাভোগী অংশ সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি (প্রবর্তিত হয়েছিল এই রকমের এক সামাজিক দুর্যোগের সময়, ১৯২৯ সালে) আর্থিক বরাদ্দ ছেঁটে ফেলার চেষ্টায় ব্যস্ত। তারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি--কখনো নিউ ইয়র্কের Wall Street-এ, কখনো শিকাগোর রাস্তায়। আর আমেরিকার বাইরে কখনো গ্রীসে কখনো বা মধ্যপ্রাচ্যে। খোদ আমেরিকায গণতন্ত্রের ভেতরের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে বর্তমান নির্বাচনী প্রচারে। গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে প্রায় সব সমাজকেই উন্নতির লক্ষ্যে প্রচলিত পথ কতটা নির্ভরযোগ্য।
‘আমেরিকার ব্যতিক্রমী ঐতিহ্য (American Exceptionalism):
করপোরেট আমেরিকার দাপটের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত, এবং পরিচিত ‘American Exceptionalism’-এর মতো স্থূল দাবির সঙ্গে। আর, যাঁরা আরেকটু বেশি খবর রাখেন তাঁরা জানেন করপোরেট আমেরিকাকে পাকেপাকে জড়িয়ে ধরে বিরাজ করছে এক ধর্মান্ধ আমেরিকা, সাধারণ মানুষের বোধকে আচ্ছন্ন, অসাড় করে। বিজ্ঞান এদের কাছে ‘মিথ’ (myth)। এই দুই ‘আমেরিকার’ পারস্পরিক সম্বন্ধটা ইংরিজিতে যাকে আমরা symbiotic relationship বলে থাকি সেই গোছের। এই ধর্মান্ধ এবং করপোরেট আমেরিকার সঙ্গেই বাস করছে এক তৃতীয় আমেরিকা, সহাবস্থান, কিন্তু ‘শান্তিপূর্ণ’ নয়, বরং ক্রমাগত সংঘাতের। এই অন্য আমেরিকাকেই আমরা আপাতত প্রত্যক্ষ করছি ‘Occupy Wall Street’ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, নিখুঁত না হলেও তারই পরিপূরক হিসেবে ওবামা-নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে। এ সেই আমেরিকা যার যাত্রা শুরু হয়েছিল “We the People” আর তার “Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”-এর মন্ত্রে। আজকের ওবামা এবং তাঁর প্রচেষ্টাও তাই কোনও দৈবযোগ নয়। বরং এক দীর্ঘ গণতান্ত্রিক চেতনার ফল। এই প্রগতিশীল আমেরিকা মিশে রয়েছে এ দেশের সরকার অনুমোদিত শিক্ষাব্যবস্থা বা ‘পাবলিক এডুকেশন’-এ, যে শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলায় দায়বদ্ধ। ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান-কারিগরী আর হিউম্যানিটিস—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ, এদের মধ্যে কোনও লেনদেন নেই। এই প্রবণতার অন্যতম ব্যতিক্রম যুক্তরাষ্ট্র, মনে করিয়ে দিচ্ছেন অধ্যপক নাসবামের মতো শিক্ষাবিদেরা। এই একটি বিষয়ে ‘American Excepionalism’-এর দাবি মেনে না নিয়ে উপায় নেই। মূল ধনতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মেশানো প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিই যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য, এবং আজ যা প্রগতি-বিরোধী জোয়ারে বিপন্ন। জন ডিউই (John Dewey), মারিয়া মোন্টেসারি (Maria Montessori)-দের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের কাজের প্রভাবে গড়ে ওঠা যে শিক্ষাব্যবস্থা। তাছাড়া, এদেশের প্রতিষ্ঠাতারাও তো নানা ব্যক্তিগত ভুল-ত্রুটি, গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়েও গণতন্ত্রের নিরীক্ষাতেই মেতেছিলেন একসময়ে। আমেরিকার পাবলিক স্কুল-এর প্রাথমিক প্রস্তুতি জেফারসন-এর মতো নেতাদের পরিকল্পনায় অবশ্যই স্থান পেয়েছিল। ১৮৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের শেষে আব্রাহাম লিঙ্কন এবং তাঁর সহযোগীরা সেই প্রগতিশীল আদর্শকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। সরকারী উদ্যোগে সাধারণ মানুষের, মূলত সদ্য-মুক্ত আফ্রো-আমেরিকান গোষ্ঠীর প্রয়োজনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন সকলের জন্য ‘লাইফ, লিবার্টি এণ্ড পারস্যুট অফ হ্যাপিনেস’-এর মন্ত্র মাথায় রেখে। সেই ঐতিহ্যেরই বাহক এখনকার পাবলিক স্কুলের পাঠ্যসচি, যেখানে কলম্বাস-এর অভিযানকে গৌরবের বদলে অন্যায় গণহত্যা হিসেবে পড়ানো হয়। হাইস্কুলের ইতিহাস-পাঠে “দুনিয়া-কাঁপানো দশদিন”(Ten Days that Shook the World) স্থান পায়! প্রথম এসে ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলের পাঠ্যসূচি দেখে কারুর তাই মনে হতেও পারে সমাজতন্ত্রটা বুঝি এই মাটিতেই ঘটেছিল! আসলে, ধনতন্ত্রের তুঙ্গে বসেও আমেরিকান সমাজের ভেতরে একটা টানাপোড়েন চলেছে সবসময়েই, ব্যক্তিমানুষের মানবাধিকারের প্রশ্নটি পুরোপুরি ফেলে দেওয়া যায় নি কখনোই। দাসপ্রথার মতো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল শিল্পায়ন আর নতুন ধনতন্ত্রের উথ্থানে, নতুন ধরনের সামাজিক শোষণের ব্যবস্থা হিসেবে। তবুও স্বীকার করতেই হবে সেই ধনতন্ত্রই আবার সেই সময়ের ‘formal democracy’-র বিকাশেও সাহায্য করেছিল। মস্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভেতরে জমে ওঠা ‘অস্বস্তি’ থেকেই গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দাসপ্রথার অবলুপ্তি, suffragist আন্দোলনের সূত্রপাত। ষাটের দশকের সিভিল রাইটস, নারী-আন্দোলন একটু-একটু করে বাঁকাচোরা পথে হলেও এগিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত: গত কয়েক দশকে মূলস্রোত সমাজ অদূরদর্শী এবং মানবিক বোধে দেউলিয়া এক সঙ্কীর্ণ রাজনীতি-সমাজনীতিতে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে, ‘সবার উপরে Wall Street সত্য’-এর মন্ত্রে। ক্রমে সবরকম সুস্থতা উধাও হতে বসেছে, শেষ চক্ষুলজ্জাটুকুও এবার মুছে ফেলে ইস্কুল-কলেজ থেকে ‘critical thinking’ বা সচেতন-চিন্তা চর্চা পদ্ধতিকেই মুছে দেওয়ার নির্লজ্জ দাবি (http://truth-out.org/news/item/10144-texas-gop-declares-no-more-teaching-of-critical-thinking-skills-in-texas-public-schools) উঠতে শুরু করেছে। বিশ্ব-অর্থনীতির সংকটের epicenter আমেরিকা সহ অন্যান্য প্রায় সব সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূলত: জাতীয় আয়মুখী করে তোলায় উদ্যোগী, এবং সেই উদ্যোগের অন্যতম ধাপ humanities, libera larts-এর বিভাগগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থ সরিয়ে নিয়ে কারিগরি আর অর্থনীতি বিভাগগুলিতে বিনিয়োগ করা। এই অদূরদর্শিতার পরিণতি দাঁড়াবে ভয়ানক, খানিকটা সেই apartheid South Africa (Nussbaum, ১৪)-র মতো, যে সমাজে উপচে-পড়া ঐশ্বর্য এক শতাংশ নাগরিকের ভোগে ব্যয়িত, সমাজের বৃহদাংশের নাগালে কেবল তার উচ্ছিষ্টটুকু।
একটি ছোট্ট ‘গপ্পো’ দিয়ে শেষ করা যাক--আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রগতিশীল আমেরিকার মূল আধার এদেশের পাবলিক এডুকেশন, আর তারই একটি চমৎকার নিদর্শন PBS বা পাব্লিক টেলিভিশন। সেই পাব্লিক টিভি-র ‘বিগ বার্ড’-কে চেনে না এমন মানুষ আমেরিকায় পাওয়া ভার। সকলের প্রিয়, অতি আপনজন হলদে পালকের মস্ত, কিন্তু অমায়িক মাপেট পাখিটি আমেরিকার cultural icon। নানা বয়সের শিশুরা এই বিগ বার্ড আর আরও অনেক মাপেট সাথীদের সঙ্গে জড়ো হয় কাল্পনিক ‘সিসেমি স্ট্রিট’ (Sesame Street)-এ। সবাই মিলে খেলতে-খেলতে, abcd শেখার সঙ্গে শিখতে শুরু করে অন্য বন্ধু, সে যে ‘রঙের’ বা চেহারার হোক না কেন, তার সঙ্গে মিলেমিশে খেলতে, শেখে অন্য বন্ধুটির ব্যথায় সহানুভূতি জানাতে—খেলার মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজে বেঁচে থাকার মূল কলা-কৌশলগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। এ হেন বিগ বার্ড-এর নাম হঠাত্ রাজনৈতিক প্রচারের আসরে বারবার কানে আসছিল। আসলে, মৌখিক বিতর্কের সময় করপোরেট আমেরিকার মিট রোমনি নিজের (এবং তাঁর রাজনৈতিক দলের) মানবিক বোধের নিদারুণ অভাবকে নগ্ন করে দিয়ে বলে বসলেন ‘বিগ বার্ড’-এর ‘ডানা’ ছেঁটে দেবেন ক্ষমতায় এলে। রাতারাতি ‘বিগ বার্ড’ তাই হয়ে উঠেছিল গণতান্ত্রিক আমেরিকার অন্যতম ‘কণ্ঠস্বর’।
আজকের অস্থির বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয় শুধু আমেরিকারই নয় গোটা মানবসভ্যতার সামনে খোলা দুটি সম্ভাবনা: সুস্থ গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি আর অল্প কিছু লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্লুটোক্রেসী (plutocracy)। সম্ভাবনা দুটি হলেও আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য (destiny) এবং সার্থকতার পথ তো একটিই: সুস্থ গণতন্ত্র, যেখানে মানবিক বোধ তার পূর্ণতা দাবি করে। আর সেই পূর্ণতায় পৌছনোর অন্যতম শর্ত এমন শিক্ষাব্যস্থা যেখানে সচেতন চিন্তা কেবল আদৃতই নয় আবশ্যকও। অর্থ-সংকোচে কলাশিল্প, মানব-বিদ্যা বিভাগগুলি খুঁড়িয়ে চললে সেই পূর্ণতায় পৌছনও পিছিয়ে যাবে, এমনই আশংকা করছেন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদেরা। এখন প্রশ্ন এই সতর্কবাণী আমরা কতটা গ্রাহ্য করব।
উল্লেখিত বই:
চট্টোপাধায়,দীপংকর; ‘পুরোনো রীতি এবং নতুন যোজনা’, “প্রবন্ধ সংগ্রহ”; আনন্দ পাবলিশার্স, 2003
Nussbaum, Martha C. “Not For Profit: Why Democracy Needs Humanities”, Princeton University Press, 2010
(পরবাস-৫৩, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)