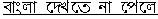এ গলিতে সূর্যের আলো পড়ে। দিকে দিকে ইট-বেরিয়ে-পড়া গগনচুম্বী দালান সত্ত্বেও সূর্য এখানে সরাসরি দেখা দেন কিরণ রূপে অথবা পরোক্ষে আসেন ঋজু ঋজু ছায়ার ছোটো-বড়ো চতুর্ভুজে। তবে সরু গলি ও কানাগলির বিবরণ বাংলাসাহিত্যের গুরুভার সঞ্চয়। তাই সেই embarras de richesse-এর ভিতরে নতুন কিছু যোগ করবার দুরাশা না করে বরং গলিটা যেখানে সমকোণে ঘুরে গেল তার পশ্চিম ও উত্তর বাহুর মধ্যে একটা চকিত আড়াল রচনা করে সেখানটাতে মুহূর্তের দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। সেখানে উচ্ছিষ্টরাশির মধ্যে বসে থাকা বেড়ালটা একবার গা ঝাড়া দিয়ে দৌড়ল উত্তর দিকে; তেইশ ফুট গেলে ডানদিকের যে বাড়িটার আধ-খোলা মুখ, সেখানে একটি সমকোণ কেটে ঢুকে গেল ভিতরে। এই মুখের পাশ থেকে একপাটি দাঁতের মতো উঠে গেছে সিঁড়ি, তার মাথায় কোনো ছাদ বা অন্য আবরণ নেই এবং তার প্রতিটি ধাপের বাম কিনারা ঘেঁষে পাঁজা-পাঁজা বই বেঁধে রাখা। ওপরে কোনো প্রকাশক বা বিক্রেতার তমসাবৃত গুদামঘর যেন একটি অবসন্ন হাত ঝুলিয়ে রেখেছে এদিকে। সেই বেড়ালটি, যার সাদা শরীরে কোনো বিজাতীয় বর্ণের ছোপ, সিঁড়ির দিকটা উপেক্ষা করে বেশ রাজেন্দ্রগমনে হেঁটে এল সোজা। দালানের মুখ থেকে পৌঁছে গেল দালানের আলজিভের কাছটায়। সে জায়গাটা অন্ধকার। একটি বন্ধ দরজার ভিতরে আলো জ্বলছে; দরজার গায়ে মানুষ-সমান উচ্চতায় একটি ঘুলঘুলি। সেই দরজায় একটুখানি গা ঘষে নেবার জন্যে তৈরি হতে লাগল সে, আর ঠিক সেই সময় ঘটে গেল ঘটনাটা। প্রচণ্ড গর্জন হল এক মানবেতর কণ্ঠে, পরক্ষণেই ওপরের সিঁড়ির আল্সে থেকে একটি ছানা-সমেত ঝাঁপিয়ে পড়ল এক বেড়াল-মাতা, একেবারে নিচের বেড়ালটির ঘাড়ে। নিমেষে দাঁতে নখে তুমুল ঝটাপটি বেধে গেল। তারপর রোদনে রোদনে জড়িয়ে এক ভয়ংকর ঝঞ্ঝা চলতে লাগল। কতক্ষণ চলত এ ঝঞ্ঝা কে জানে, যদি-না সেই মুহূর্তে খুলে যেত বন্ধ দরজাটা, এবং একটি কুকুরের ঘুমভাঙা মুখ দেখা না দিত; যদি-না সে কিছু বলবে বলে তার ডাগর চোখ দু’টিকে বড়ো করে তুলত, আর বেরিয়ে এসে শরীরটাকে একটা বক্ররেখায় টানটান করে না ধরত। কারণ সঙ্গে সঙ্গে দুই যোদ্ধা অপমানবোধে উন্মাদ হয়ে নখে-দন্তে লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। সেই জটিল অবস্থায় সারমেয়পুরুষ পিছু হটলেন, এবং যোদ্ধা-যুগলকে শরীরের দু’পাশে বহন করে দরজাটি ঠেলে ভিতরে ঢুকে এলেন।
সেটা ছিল দুপুরবেলা। আর, ছায়াঘন বিকেলে সেই রণক্ষেত্রের পথ দিয়ে যে উদ্ভ্রান্ত মানুষটা হেঁটে গেলেন তার সামনে নিশ্চিত ছিল না কিছুই। ওই দরজাটা - সারস্বত দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগ? সে তো এক অদ্ভুত কৌতুক।
ওই জান্তব যুদ্ধ যখন আছড়ে পড়েছিল বন্ধ দরজায়, সেখান থেকে ঘরের ভিতরে, তখন এই মানবপুত্র শম্ভুনাথ ধাড়া একতাড়া কাগজ থেকে বিরক্ত মুখটি তুলে তাকিয়েছিলেন। টেনে নিয়েছিলেন দরজার লম্বা খিলটি, অব্যবহারে মলিন; এবং লেপ্টে-থাকা ঝুলগুলো নির্মূল করবার অভিলাষে সেটি আলগোছে বুলিয়ে দিয়েছিলেন কুকুরটার লেজে। সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দুই যোদ্ধাকে নিমেষে ঝেড়ে ফেলেছিল। শম্ভুনাথ তখন বলে উঠলেন, ‘চোপ!’ তারপর হেসে বললেন, ‘বিতর্ক জমে উঠেছে’; পরমুহূর্তেই বললেন, ‘চোওপ! এ কি শালা ‘কোমর বেঁধে’ পেয়েছ নাকি? এই রাজু, জলের বোতলটা দাও তো।’ অতঃপর তিনি জল-কামান দ্বারা এক পক্ষকে ভিজে-বেড়াল বানিয়ে তুললেন, আর সারমেয়পুরুষের গুহ্যদ্বারে দিলেন লাঠির সুতীব্র খোঁচা। ঝপ করে যবনিকা পড়ে গেল, যেন বাণিজ্যিক বিরতি। ক্ষুদ্র ছানাটি কোনো অন্তরাল থেকে ‘মিঁউ’ করে উঠল।
‘কোমর বেঁধে’ দূরদর্শনে বিদ্বজ্জনদের তর্কচক্র। আপামর বাঙালি অবাক হয়ে সে অনুষ্ঠান দেখে। শম্ভুকে উদ্দেশ করে রাজু বলল, ‘খুব আঁতেল জিনিস ছাড়লেন মাইরি, শম্ভুদা।’
‘ওরে আমি শম্ভু নই রে আর। আমি শম্বুক।’
‘হ্যাঁ। আপনি যা স্লো।’
শূদ্র তপস্বীর রামায়ণী অনুষঙ্গ ধরতে পারে নি রাজু – শম্ভু বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘থাম্ তো। মেলা বকিস নি। কাজটা করতে দে।’ তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়লেন।
এই একটু রঙ্গের ছোঁয়া লাগল। তারপর আবার সব চুপচাপ আর পাথুরে। শনিবার কিন্তু এমনটা হয় না। গত শনিবারও বইয়ের ভাগ্য নিয়ে নিদারুণ রঙ্গটা জমে উঠেছিল এই দ্বিপ্রহরে, বারবেলা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মূল কপির খোঁজে তোলপাড় চলছিল, কম্পোজ-অন্তে রাজু যথারীতি বলছিল ‘আমি কী জানি’, তোলপাড়ের চোটে কুণ্ডলী-পাকানো কুকুরটা উঠে গিয়েছিল ঘরের কোণ ছেড়ে, আর সেই সন্ধিক্ষণে ‘আমি দেখছি’ বলে নির্ভীকচিত্তে সকলকে আশ্বস্ত করেছিলেন শম্ভুনাথ। কপির খোঁজে তিনি ব্যস্ত নন। তিনি সরাসরি ডুব দিয়েছিলেন প্রুফের রাশিতে। যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজবনে নামে। রচনার কোনো অংশ বাদ পড়লেও খটকা লাগে না তাঁর, অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদভাগের কোনো গোলমাল তাঁর চোখে পড়ে না। তিনি কেবল অফুরান্ আত্মবিশ্বাসে চড়াও হচ্ছিলেন লেখকের ভাষা ও বানানের ওপরে। পরম উৎসাহে তিনি ‘রাগী’-কে করছিলেন ‘রাগি’ (কিন্তু ‘অনুরাগী’-তে এসে ঠেকে যাচ্ছিলেন), ‘পুলিস’-কে করছিলেন ‘পুলিশ’, বিশেষ্য ‘মৌন’-কে ‘মৌনতা’, ‘সুভো ঠাকুর’-কে ‘শুভ ঠাকুর’, ‘অরুণবরন পারিজাত’-কে ‘অরুণ বরুণ পারিজাত’। সারা সপ্তাহের কর্ম তখন ফেনিয়ে গাঁজিয়ে উঠছে। অভীন্দ্রনাথের কানে কানে কিছু বলে যাচ্ছে রাজু, তিনি হাঁক দিচ্ছেন ‘শম্ভু তুমি আজ মীটিঙে থাকবে’, শম্ভু কণ্টকিত হয়ে আরও নিমগ্ন হচ্ছেন প্রুফে, তখন সুবন্ধু এসে হাসিমুখে ঢুকছে, শম্ভুর কাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলছে, ‘সুভো ঠাকুর নিয়ে কী করছেন, শম্ভুদা?’ যেদিন থেকে সে অঙ্গীকার করেছে যথাসাধ্য ‘গৈরিশ’-এর কাজ করে দেবে সেদিন থেকে এটাই সুবন্ধুর আসবার বেলা, এতে তার কামাই নেই। সেই সময় দরজাটা এক হাতে ফাঁক করে অন্য হাতে চটচট শব্দে চপ্পলের স্ট্র্যাপ খুলছিলেন কথাসাহিত্যিক শান্তভাব মিত্র, অভীন্দ্রনাথ সাদরে ডাকছিলেন ‘ওই তো, My Quiet Friend (অস্যার্থ শান্তভাব মিত্র), এসো’। শান্তভাবের কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ, চেহারায় বিনীত ও ব্যস্তসমস্ত ভাব। ‘গৈরিশ’-এর তীর্থক্ষেত্র থেকে শুরু করে, কাছাকাছি আরও অনেক সাহিত্যতীর্থ ছুঁয়ে, তিনি যাবেন কফি হাউসের সঙ্গমে, ও বাড়ি ফিরে ফেসবুকে লিখবেন আজ তিনি কোন্ ঝকঝকে নবোদিত লেখককে দেখে এলেন, শেষ করবেন ‘এর কাছে অনেক আশা রইল’ দিয়ে, এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ১৭৩-টা ‘লাইক’ কুড়িয়ে হৃষ্টচিত্তে ঘুমোতে যাবেন। বিলম্ব না করে তিনি বসে পড়লেন ‘গৈরিশ’-এর প্রকাশিতব্য ‘সমকালীন গল্প – উত্তরপর্ব’ নিয়ে, যে প্রকল্পে অভীন্দ্রনাথ ও তিনি যুগ্মসম্পাদক। অভীন্দ্র প্রথমেই বললেন, ‘আমাকে আবার লোকের কাছে লেখা চাইতে বোলো না কিন্তু।’ শান্তভাব জবাব দিলেন, ‘আপনি অভি ভটচায্যি, লেখা আপনার কাছে আসবে।’ অভীন্দ্র-শান্তভাব যুগ্মপ্রতিভায় এটি চতুর্থ সম্পাদনাকর্ম। অভীন্দ্রের আছে নিজের নামকে যুক্ত করে দেবার প্রশ্নাতীত অধিকার। শান্তভাব তাঁর প্রতিষ্ঠার দ্বারা এনেছেন বিশ্বাসযোগ্যতা, আর অকাতরে জায়গা দিয়েছেন তাঁর স্নেহভাজন তরুণ লেখকদের। দু’একজন অহিন্দু লেখকও আছেন, বিশেষ করে এক তরুণী, কারণ সংখ্যালঘুর সংবেদনশীলতার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না কোনো বিচক্ষণ সম্পাদক। শান্তভাবের কাণ্ডকারখানা চাপা হাসি নিয়ে লক্ষ্য করছিল এখানকার পাঁচ কর্মচারী, সুরসিক ও বহুদর্শী সুবীর তাদের অন্যতম। সে সুবন্ধুকে গোপনে খোঁচা মেরে বলেছিল, ‘শুধু দেখে যান, পরে সব বলব।’ রাজু আবার অভির কানে কিছু বলে গিয়েছিল। অভি তাকালেন সুবন্ধুর দিকে, আর শান্তভাবকে বললেন, ‘চলো, ব্লার্বটা লিখে ফেলি।’ তাঁরা দু’জনেই দু’টি প্রুফের মার্জিন ছিঁড়ে নিয়ে লিখতে বসে গেলেন।
আজ সেই স্পন্দন নেই। সব পাথুরে ও চুপচাপ। তেড়েফুঁড়ে শম্ভুর কাজ চলতে লাগল। তিনি দেখলেন যত নষ্টের গোড়া ওই তদ্ভব আর দেশি শব্দগুলো। আরও সময় নিয়ে ওদের মোকাবিলা করা উচিত ছিল। ওদেরই জন্যে বানানের বিশ্বে এত অনাচার, এত অসাম্য। মনের ওপর চাপ বাড়তে লাগল। ওদের হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ, ও-কার এবং চন্দ্রবিন্দুর অস্তি-নাস্তি, স-শ, র-ড়, ঙ-অনুস্বারের দ্বন্দ্বের কাছে তিনি পদে পদে পরাস্ত হতে লাগলেন। একসময় তিনি ঘড়ি দেখলেন। ঘাম দেখা দিল কপালে। অবেলার মার্জার-যুদ্ধের কথা মনে পড়ল।
একে একে তিনি সমস্যাগুলো লিখতে শুরু করলেন। প্রথমেই লিখলেন – হল/হলো/হোল, করব/করবো – কোন্টা হবে? ও-কারের প্রয়োজন কী? এই শ্রেণির এখানেই শেষ নয়। হসন্তের প্রশ্নটা উঁকি মারল। সেই যাঁরা চাইছেন ‘দেখ্বো/রাখ্বো’, একেবারে হসন্ত সহ। এই দলে স্বয়ং ডঃ স-শ সেনাপতি, রাশিবিজ্ঞানী ও ভাষাতত্ত্ববিদ। ওঁকে চটালে কর্তা রুষ্ট হন। তাই পত্রিকার একই সংখ্যায় প্রচলিত বানান ‘দেখব’-র পাশেই সেনাপতির অতি-বিশিষ্ট ‘দেখ্বো’-কে স্থান দিতে হয়।
‘ও শম্ভুদা, যা লেখার প্রুফের ওপর লিখুন। আলাদা কাগজ আমি দেখতে পারব না কিন্তু।’ রাজুর কণ্ঠে বিদ্রূপ।
শম্ভু জবাব দিলেন না। সব দোষের ভাগী তিনি। যেখানে শুদ্ধতার কোনো সংজ্ঞা নেই, কোনো চাহিদাও নেই, সেখানে তিনি শুদ্ধাশুদ্ধির স্বঘোষিত কাণ্ডারী। একটি বইয়ের নামপত্রে ‘অনুবৃত্তি’ শব্দটা ‘অনাবৃষ্টি’ হয়ে ওঠে, সেই অবস্থায় বই চলে বারো বচ্ছর, নানা পুনর্মুদ্রণের পরম্পরায়। অবশেষে এ বছর নতুন সংস্করণের আয়োজন হলে ওই বেয়াড়া সুবন্ধু সিংহ দ্বিতীয় প্রুফ হাতে নিয়েই বলে, ‘প্রুফ দেখে কী হবে? এই তো নামপত্র। আরও আছে। দেখবেন?’ সে দেখায় সূত্রনির্দেশগুলো – ‘সুকুমার সেন পৃ ৩২৬’, ‘শশিভূষণ দাশগুপ্ত পৃ ২১৫’ – শুধু লেখকের নাম, কোন্ বই তার উল্লেখ নেই কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ সম্পাদক-প্রকাশক অভীন্দ্রনাথ সহ সকলে তাকান শম্ভুর দিকে। শম্ভু অধোবদন হন। একমাত্র সুবন্ধুই বিশ্বাস করে তাঁকে যখন শম্ভু বলেন, ‘কতবার রাজুকে বলেছি, অভিদাকে বলেছি, জানেন?’
রাজুকে ভয় করে চলেন শম্ভু। বস্তুতপক্ষে, সবাইকেই এখন ভয় করে চলতে হয়। ধীরে ধীরে পায়ের তলা থেকে সরে গেছে মাটি। তাঁর কিছুই সম্বল নেই। তাঁর মনে হত কাজের দাঁড়ে তিনি মাথা উঁচু করে বসে থাকবেন। কর্তামশায়ের নেকনজর যে পৃথিবীর দৃঢ়তম অবলম্বন তা তিনি জানেন না।
সেদিন শান্তভাব মিত্র চলে যাবার পরও অভি লিখে যাচ্ছিলেন। সুবন্ধু শম্ভুর পাশে বসে চেয়ে দেখছিল। অভি হঠাৎ বললেন, ‘আপনি তো শম্ভুকে নিয়েই পড়ে আছেন। এই প্রাণীটাকেও একটু দেখুন। আচ্ছা, বইমেলার অডিটোরিয়ামটা ভাড়া নেব। গিল্ডকে ইংরেজিতে একটা চিঠি লিখে দিতে পারবেন?’ অতঃপর চিঠির ভাষায় দু’একটা অকারণ পরিবর্তন করে তিনি বলেন, ‘বইয়ের ব্লার্ব লিখতে জানেন?’
প্রশ্নটা অবান্তর, কারণ এর মধ্যেই সুবন্ধু লিখে দিয়েছে দু’টি ইংরেজি ও একটা বাংলা বইয়ের ব্লার্ব। কিন্তু অভির কি অত মনে রাখার সময় আছে? সুবন্ধু তার মুখের স্থায়ী কুলুপটা খুলে নিয়ে বলে, ‘কীরকম লেখা, পড়ে না না-পড়ে?’
‘না-পড়ে হতে যাবে কেন?’
‘কেন, না-পড়ে কি ভালো ব্লার্ব লেখা যায় না?’
অভি হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে যান - ‘হ্যাঁ শুনুন - রবীন্দ্রনাথ সংকলনের যে ভূমিকাটা আপনি লিখেছিলেন, খারাপ হয় নি। ওটাতে আমার সঙ্গে আপনার নামও যেতে পারে।’
নির্বিকার সুবন্ধু বলেছিল, ‘আপনারটাই যাক। আমার নাম অপ্রাসঙ্গিক হবে।’
অভির একটু গুলিয়ে যায়। স্বভাবত নিশ্চুপ লোককে নিরীহ ও দাক্ষিণ্যপ্রার্থী বলেই ভাবতে অভ্যস্ত তিনি। এবার আরও অবান্তর ভাবে বলেন, ‘জানেন, লেখককে অ্যাডভান্স দিয়ে বা চুক্তি করে ‘গৈরিশ’ কোনোদিন বই ছাপে নি। এটা এ পাড়ায় রেকর্ড।’
সুবন্ধু বলল, ‘ঠিকই তো। অমরত্ব দিচ্ছেন, আবার অ্যাডভান্স কীসের?’
আরক্ত হলেন অভীন্দ্র। এক বিশ্বাসঘাতক লেখক রয়্যালটি নিয়ে মামলা ঠুকে দিয়েছেন। তাতে অভীন্দ্রকে হাজিরা দিতে হচ্ছে তিন বছর ধরে। তিনি বিষয়ান্তর খুঁজে না পেয়ে বললেন, ‘এই - কর্পোরেশনের ব্যাপারটা ফলো-আপ করলেন না কিন্তু।’
এখন পরিবেশটা আরও শীতল ও পাথুরে লাগছে। আজ সুবন্ধু এলে ভালো হত। এই ব্যক্তিটিকে অভীন্দ্র আজকাল ভুঁইফোঁড় মনে করেন, কিন্তু নিজের বিপর্যস্ত দশায় তাকেই নোঙরের মতো মনে হয় শম্ভুর।
এখন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন শম্ভু। বিব্রত, অস্থির। আর বুঝি হল না। তাঁর পকেট থেকে গোছা গোছা বেরিয়ে আসে দীর্ঘ গবেষণার সঞ্চয় – রাশি রাশি চিরকুট। বুক-পকেট উজাড় হলে প্যান্টের দু’পাশের পকেট, তারপর পিছনের একটি। চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ, যে-কোনো বহুভুজ, অথবা অবর্ণনীয় কোনো আকৃতি। প্রুফের কিনারা থেকে, লেখকের কপির কোনা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া খণ্ড। কোনোটা লেখকের কপির একেবারে মাঝখান থেকে উপড়ে নেওয়া। এখানে কপির সংরক্ষণ হয় না। চল্লিশ বছরের ঐতিহ্যশালী সাময়িক পত্র ‘গৈরিশ’, বাঙালির মননশীলতার তিমিরবিদার জ্যোতিষ্ক; এখানে সবই আমন্ত্রিত লেখা। কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। অনামন্ত্রিত লেখা তার জন্মলগ্নেই আবর্জনা। সে লেখা অভিজ্ঞান হারিয়ে-ফেলা শকুন্তলার মতো বিবর্জিতা। এখানে আমন্ত্রণের গৌরবচিহ্ন নিয়ে লেখা আসে, এবং সোজা চলে যায় যন্ত্রে। দৌবারিকেরা সভয়ে সরে দাঁড়ায়। তাদের ওপর কোনো নির্দিষ্ট হুকুমনামা নেই, কেবল মাঝে মাঝে দৈববাণীর মতো শোনা যায়, ‘কপি ফলো করবে, কপি ফলো করবে।’ দৌবারিক আর কে? একমাত্র শম্ভুই ভেবেছিলেন দৌবারিকের কিছু দায়িত্ব আছে। কপি অনুসারেই সব কম্পোজ হয়। তারপর কপি উধাও হয়ে যায়; রাজু শুধু বলে ‘আমি কী জানি’। তারপর সেই বিচিত্র বানান, বিচিত্রতর তথ্য ও সংবাদের গন্ধমাদন এসে পড়ে শম্ভুর ঘাড়ে। তিনি বাইরে গিয়ে বিড়ি খেয়ে আসেন, সঙ্গে দোক্তা পান।
শম্ভু ফিরে এলে অভির সঙ্গে প্রায়ই একটা সংলাপ জমে ওঠে।
‘ও অভিদা, কোন্ বানান ধরে চলব?’
‘আকাদেমি।’
‘বরেনবাবু শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে শৈলজানন্দ লিখেছেন। কী করব?’
‘বরেনবাবু? ওসবে হাত দিতে যেয়ো না।’
‘সোহিনীদি ‘বিদুষী’-তে দীর্ঘ-ঊ দিয়েছেন। কী রাখব?’
‘সোহিনী রোড্স্ স্কলার। তোমার অত ভাবতে হবে না।’
‘ধরন-এ দন্ত্য-ন না মূর্ধন্য-ণ, কী দেব?’
‘শুভেশ কী লেখে?’
‘মূর্ধন্য-ণ। চলন্তিকা কিন্তু দন্ত্য-ন বলছে।’
‘ওসব আউটডেটেড। রাজশেখরবাবু কেমিস্ট্রির বিএসসি। শুভেশ ওহায়োতে ইণ্ডিয়ান ফিলসফি পড়ায়।’
‘বাঞ্চৎ-এ ঞ্চ-য় ও-কার হবে, না হবে না?’
‘বাঞ্চৎদের জিজ্ঞেস করো।’
এরপর শম্ভু যদি জানাতেন, ‘রাজু ‘আর্নল্ড বাকে’-কে ‘আনলোড বেক’ করে দিয়েছে, কিছুতে শুনছে না’, অভীন্দ্রনাথ নিশ্চিত বলতেন, ‘কেন, তুমি কি ডাচ জানো?’ অতএব, শম্ভু প্রুফে ডুব দেন, ও ‘উচিত’ বনাম ‘উচিৎ’, ‘ঊর্ধ্ব’ বনাম ‘ঊর্দ্ধ’, ইত্যাদিতে হোঁচট খেতে থাকেন। এমন লেখকের দেখা মেলে যিনি ‘চমৎকৃত’-কে লেখেন ‘চমকৃত’, ‘বিতাড়িত’-কে ‘বিতারিত’। এমন সমাজ-ভাবুককে পাওয়া যায় যিনি ধর্মান্তর করানো অর্থে লেখেন ‘ধর্মান্ত’-করণ। এঁরা অনেকেই বিগ্রহকল্প, আর ফেসবুকে সমাদৃত। কিন্তু তাঁদের নিয়ে অভিকে কী বলবেন তিনি?
কারণ, ‘গৈরিশ’-কে গড়ে তোলার দীর্ঘ সাধনায় অভীন্দ্রনাথ চালিত হয়েছেন একদিকে বিষয়বুদ্ধি অন্যদিকে তাঁর সামাজিক সংস্কারের দ্বারা। ‘গৈরিশ’-কে কোনো নবীন প্রতিভার আঁতুড়ঘর বানিয়ে তুলতে তিনি চান নি। নবীন প্রতিভা ও অপ্রকাশিত জাত-লেখকের দায়টা তাঁর নয়; এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট দুর্ভেদ্য তিনি, কারণ তাঁকে আজ অবধি টলাতে পারে নি কোনো নবীনাও। তাঁর আগ্রহ লব্ধপ্রতিষ্ঠদের নিয়ে, যাঁরা হয়তো রচনাকর্মে ততটা পরিব্যাপ্ত নন কিন্তু বিদ্যায়তনিক পরিচিতিতে ভাস্বর। তিনি নিজেও একদা লেকচারার ছিলেন, তিনি জানেন এঁদের বাগ্ধারা, এঁদের সূক্ষ্ম অভীপ্সা, এঁরাও সহজেই সৌভ্রাতৃত্ব বোধ করেন এ-হেন প্রকাশকের প্রতি। এঁরা প্রধানত নিবন্ধকার অথবা অবকাশ-মতো রম্যরচনা লেখক, কথাসাহিত্য এঁদের ক্ষেত্র নয়। কথাসাহিত্য ও কবিতার অন্তর্গত অনিশ্চয়তা খুব ভালো করে বোঝেন অভীন্দ্র, তারা ‘গৈরিশ’-এ দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তাঁর পরাক্রান্ত ও বিদগ্ধ লেখকেরা, যাঁদের সঙ্গে তাঁর গুণ ও বৃদ্ধি চলতে থাকে নিরন্তর, তাঁরা যুক্তিবাদী উদার ও বিশ্বনাগরিক, অর্থাৎ তাঁদের অভিধা সেই অনুবাদের অতীত ‘র্যাডিক্যাল’ শব্দে। এঁরা মূলত প্রণব বর্ধন-কথিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত বামপন্থী, তাঁরা বয়সে প্রৌঢ় ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সেই ঐন্দ্রজালিক শ্রেণি, জীবনের বহু বিপরীতকে যাঁরা নিজহিতার্থে আশ্চর্য ভারসাম্যে ধারণ করতে পেরেছেন। এঁদের সংসর্গেই সব থেকে তৃপ্ত হন অভীন্দ্রনাথ, আরাম পায় তাঁর বিবেক, স্ফীত হয় তাঁর গৌরববোধ, এবং তাঁরাও প্রকাশপথ খুঁজে পান তাঁর মধ্য দিয়ে।
কথায় বলে, ‘ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝব ক্যাম্নে?’ কৌলীন্য যেখানে প্রশ্নাতীত সেখানে অভীন্দ্রনাথের আর দুশ্চিন্তা থাকে না। তা নইলে আন্কোরা লেখা পড়ে বাছাই করা তাঁর পক্ষে বড্ড মেহন্নত হয়ে যেত। সেদিন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে তিনি শম্ভুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তোমার ‘বাঙালির ভাষা’-র প্রুফটা কী হল?’
‘সমস্যা আছে।’
‘উফ্ফ্!’
আগে কথা চলছিল ‘গৈরিশ’-এর প্রকাশিতব্য সংখ্যা নিয়ে। বর্তমান প্রসঙ্গ বাংলাভাষাবিষয়ক ‘বাঙালির ভাষা বাঙালির দশা’ বইটি। লেখক ডঃ সবুজশংকর (বা স-শ) সেনাপতি রাশিবিজ্ঞানী তথা ভাষাতাত্ত্বিক। রাশিবিজ্ঞানে তাঁর মার্কিনি ডিগ্রী আছে; ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে সেটি তাঁকে ‘মহাশয়ের কী করা হয়’ জাতীয় প্রশ্ন থেকে রক্ষা করে। সবুজশংকর একজন বানান সংস্কারক, এবং বাংলাভাষার সমস্ত সংস্কারকের মতোই লিপিসংস্কারে উৎসাহী। হ্রস্ব ই-কার চিহ্নের তিনি পরিবর্তন চান; স্বরবর্ণ এ বা এ-কারের যেখানে ধ্বনিবিকৃতি ঘটে সেখানে অ্যা-ধ্বনির জন্য তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত নতুন চিহ্ন আছে, যদিও অ-এর বিকৃতি ও-কে তিনি রেহাই দিয়েছেন। তেমনি রেয়াত করেছেন ‘ত্ত’ যুক্তাক্ষরটিকে, কিন্তু ষ্ণ হ্ম ইত্যাদি চিহ্নের সরলীকরণে তিনি প্রতিদিন নতুন নকশা আঁকছেন। প্রুফরীডার শম্ভুনাথ ধাড়ার সমস্যা অবশ্য এসব নিয়ে নয়। প্রাথমিক দৃষ্টিপাতে শম্ভু লক্ষ্য করেছেন এই পণ্ডিত কেবল ‘নি’-কে ক্রিয়াপদের সঙ্গে জুড়েই ক্ষান্ত নন, তিনি ‘না’-কেও জোড়া লাগাতে চান। ক্রিয়াটি একটু বড়ো হলে না-সুদ্ধ তার চেহারাটা, যেমন ‘বদলাচ্ছিলামনা’, বেশ ভারি মনে হয়েছে শম্ভুর।
এ বিষয়ে অভিকে বলা মাত্রই দপ করে জ্বলে উঠেছেন তিনি। বেরিয়ে গেছেন ‘গৈরিশ’-এর দপ্তর থেকে। শম্ভুর বলা হয় নি যে তিনি নস্যাৎ করেন নি সবুজশংকরের পাণ্ডিত্যকে, ‘বদলাচ্ছিলামনা’-র সঙ্গে সমতার খাতিরে তিনি ‘যত না’ ‘মন্দ না’-র ক্ষেত্রেও ‘যতনা’ ‘মন্দনা’ করতে চাইছেন।
তবু আজকাল একটা রোখ চেপে গেছে শম্ভুর। ক’দিন আগের একটা কৃতকর্মের কথা মনে পড়ছে যা এখনও গোপন। তিনি সেদিন নামিয়ে বসেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রন্থিত প্রবন্ধের গুচ্ছ, যেগুলি নানা উপায়ে অভি সংগ্রহ করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত অনেক লুপ্ত পত্রিকার পাতা থেকে। সেই সংকলনের তৃতীয় ও চূড়ান্ত প্রুফ থেকে কাল ট্রেসিং হবার কথা। কেউ জানে না, শম্ভু সেদিন বসে বসে হীরেন্দ্রনাথের সব ক’টি নিবন্ধকে ‘শ্রেণী’-হীন করেছেন। বহুলব্যবহৃত এই শব্দটিকে ‘শ্রেণি’-তে রূপান্তরে তিনি ব্যয় করেছেন তিনটি ঘণ্টা। সেই সঙ্গে প্রতিটি ‘ভারি’-কে করেছেন ‘ভারী’, ‘গান্ধীজী’-কে ‘গাঁধিজি’, ‘মহাভাগ’-কে ‘মহাশয়’। এর ফলাফল কিছুটা তাঁর জানা। চরম মুহূর্তে রাজু মার্জারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁর ঘাড়ে, ট্রেসিং-এর লগ্ন পিছিয়ে যাবে আরও ক’টি দিন; আর অভিদা কী বলবেন তা অবশ্য জানা নেই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, কাউকে ভয় পাবার নেই। হীরেনবাবু তো কোন্ ছার, রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়ব না।
মাঝে মাঝে শম্ভুর মনে হয়, কেন খাটছি এত? কেউ তো কদর করবার নেই। অভিদার মাথাব্যথা নেই, লেখকেরা যা-খুশি লেখেন, তবু তাঁদের তত্ত্বকথা থামে না। কিন্তু অচিরেই এসে যায় নতুন প্রুফ এবং এমন লেখক যাঁকে তিনি অর্বাচীন ভাবতে পারেন – দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি মেতে ওঠেন সংশোধনের নেশায়।
তবে প্রথম থেকেই হয়তো এমনটা ছিল না। সেই যখন বেনারসী ঘোষ স্ট্রীটে ওই বাড়িটার সিঁড়ির নিচে সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে ছিল ‘গৈরিশ’-এর প্রথম কার্যালয়, যার পিছন দিকের অন্ধকারে ছিল তাঁর প্রুফ দেখার ছোট্ট টুল। সেখানে খাড়া হয়ে বসলে মাথার চুলে সিঁড়ির চুনকাম লেগে যেত। নাবালক সেই প্রতিষ্ঠানে কেবল তিনি আর অভিদা। প্রথম বইটি কী ছিল? বোধহয় সদ্য শেষ-হওয়া নকশাল আন্দোলন নিয়ে। পরের বই? বোধহয় দোর্দণ্ড বিশ্বাসের লেখা একটি। রবীন্দ্ররচনায় চুরি-বিদ্যে সংক্রান্ত। শম্ভু তখনও ছিলেন বিনীত প্রুফরীডার, দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল। দৌবারিকের স্পৃহা তাঁকে তখনও স্পর্শ করে নি। কিন্তু সেই দশকটাতেই চল্লিশ বছরের সুপ্তির পর বাংলা বানান নিয়ে শুরু হল তোলপাড়। ঘোষিত হল দীর্ঘ ঈ আর ঊ-এর বিরুদ্ধে জেহাদ (কোথাওবা ঘটল দীর্ঘ স্বরের প্রত্যাবর্তন), ও-কারের লুপ্তি অথবা উৎপত্তি, এবং ক্রমশ ঘটে গেল ‘ন্ড’ (ন্+ড্)-এর আবির্ভাব ও সর্বগ্রাসী বিস্তার। ব্যুৎপত্তির ছোটো ছোটো প্রভেদের ওপর দাঁড়াবে স্বরের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা, ন-এর দন্ত্য ও মূর্ধন্য চরিত্র, এই সূক্ষ্ম প্রভেদমূলক নিয়মগুলো দিনে দিনে বাড়তে লাগল। জেলায় জেলায় পরীক্ষা পাসের হার বাড়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ও কতটুকু তা বলা মুশকিল, কিন্তু অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে কেবল বানান দেখেই বলে দেওয়া যাবে কোন্ কালে কোন্ রাজার রাজত্বে কোনো-একটি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল, যাকে ঐতিহাসিকেরা হয়তো বলবেন orthographic evidence. শম্ভু ছিলেন সজাগ ও গ্রহিষ্ণু, অভি সততই তাঁকে মনে করিয়ে দিতেন ‘তুমি এইট-পাস’। কাজেই বানান সংস্কারের প্রতিটি বাতাস তাঁর মনে ঢেউ তুলতে লাগল।
আটত্রিশ বছরের স্মৃতি সহসা-সচকিত হাজার হাজার পাখির মতো ডানা ঝাপটায়। বিমূঢ় বোধ করেন শম্ভু। এই অতল আলোড়নে সমস্ত ধূসর ও অস্পষ্ট হয়ে যায়।
আশির দশকে এসে অভিদা হালে পানি পেলেন। তাঁর প্রকাশনার পছন্দ বদলাল। তার মধ্যে শম্ভুর বিস্তর পরামর্শ ছিল। সম্প্রতি ‘গৈরিশ’ পত্রিকা ও প্রকাশনার একটা বিশদ কালানুক্রমিক সূচি রচনায় হাত দিয়েছেন শম্ভু। কবে শেষ হবে জানা নেই। আজ এ বিষয়ে অনাগ্রহী অভীন্দ্রনাথ কাজ সম্পূর্ণ হলে সেটা নিয়েই নিশ্চিত তৈরি করে ফেলবেন ‘গৈরিশ’-এর বিশেষ সংখ্যা, যার নাম অবশ্যই হবে ‘ফিরে দেখা’ বা ‘অন্তবিহীন পথ’।
তবে ‘বাঙালির ভাষা বাঙালির দশা’ নিয়ে একটা আপদ ঘনিয়ে উঠছে চারদিক থেকে। এ বই আকাদেমি আনবে, নিশ্চিত ছিলেন অভি। সেদিন প্রচ্ছদ নিয়ে প্রথম কাণ্ডটা ঘটে গেল। প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন লেখক নিজে। হঠাৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন দপ্তরে। তাঁকে সত্যজিৎ রায় হতে কে বলল? এ প্রশ্নটা জাগে স্বয়ং অভিরই মনে। ওদিকে শিল্পী শরণ সরকারের প্রচ্ছদও হাজির তার এক দিন আগে। অনেক বেশি দৃষ্টিনন্দন, পেশাদারি হাতের সেই কাজ। কিন্তু এই অহংকৃত লেখককে এখন কে বোঝাবে? উপরন্তু, সম্ভবত বাংলা বানানের বিভ্রান্তি বোঝাবার তাগিদে তিনি নিজের নামের মধ্য অংশটিকে লিখেছেন দু’ভাবে, একবার ‘শঙ্কর’ অন্যবার ‘শংকর’; একবার ‘শঙ্কর’-কে জুড়েছেন প্রথম অংশ ‘সবুজ’-এর সঙ্গে, একবার জোড়েন নি, ও এই দুই বিকল্পের ওপরের পঙ্ক্তিতে লিখেছেন ‘সবুজশংকর’, যে রূপটি তিনি ব্যবহার করেন। লেখকের নাম নিয়ে এই খেলাটা প্রথম চোখে পড়ল শম্ভুর। অভি শুনে বিমূঢ় হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, ‘সবুজকে বলো তো, যদি চায় তো নিজের নামটা ছেড়ে ‘বাঙালি’-কে ‘বাঙালী’ ‘বাঙ্গালী’ করে দশ বার লিখতে থাকুক।’ কিন্তু লেখক মোবাইল ব্যবহার করেন না – তাঁকে না পেয়ে অভির দিশাহীন ক্রোধ আছড়ে পড়ল শম্ভুর ওপর।
শরণ সরকারকেই বা বোঝাবে কে?
অভীন্দ্রনাথের মহাবিশ্বের একেবারে কেন্দ্রস্থলে এই ‘গৈরিশ’। আর তারও কেন্দ্রে ত্রৈমাসিকের মলাট আর বইয়ের প্রচ্ছদ। দুই-ই বছরের পর বছর এঁকে দিচ্ছেন শরণ সরকার। সহজাত নেতৃত্বগুণে যে-কোনো কাউকেই নিজের স্নেহধন্য করে তুলতে পারেন অভীন্দ্রনাথ, বিশেষ কোনো কৃতজ্ঞতার বোধ ছাড়াই। সেই স্নেহের সূত্রেই এই বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, যিনি ঘন ঘন প্যারিস যাতায়াত করেন, তাঁর শিল্পকর্ম উপহার দিয়ে চলেছেন বিনামূল্যে। এ নিয়ে আর কোনো দুর্ভাবনা নেই অভীন্দ্রনাথের। কেবল সেটি উন্নত প্রযুক্তিতে ছাপাবার জন্যে কিছু খরচ করতে হয়। অবশেষে পরিণত বস্তুটিতে হাত বুলিয়ে তাঁর গর্বেরও শেষ নেই। বহিরবয়বের পাশে পাঠশুদ্ধি যে এখানে বাহুল্যমাত্র সেকথা না বললেও চলে। তিনি বাছাই করেছেন ভারিক্কি লেখক, দিয়েছেন উচ্চমানের কাগজ, রুচিসম্মত মুদ্রণলিপি, এবং পরিয়েছেন এই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ; অতএব তিনি নিজের চোখেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। কখনও, এইসব ভাবনার অলস প্রহরে, শনিবার অপরাহ্ণে উপস্থিত হয় যাযাবর ক্রেতা; একটা ক্যাটালগ পেতে পারি কিনা জানতে চায়। অভি দু’একটা কথা বলেন যা মননশীলতায় চমৎকার, ক্রেতা সম্মানিত বোধ করেন। অভি তাঁর হাতে তুলে দেন নূতনতম বইটি; ক্রেতা কম্পিত হস্তে নেড়েচেড়ে বলেন ‘আজ টাকা নিয়ে আসি নি’।
এই অলস অপরাহ্ণিক বেলাগুলো বড়ো মায়াময়। গত শনিবার, সেই অভীন্দ্র-সুবন্ধু সংবাদের পর কয়েকটা মুহূর্ত ছিল নীরব। এই খাপছাড়া যুবক সুবন্ধু সিংহকে জাতে তুলেছিলেন অভীন্দ্র। কারণ সে তো কুলীন না হলেও সেই প্রজাতি যাকে বিলক্ষণ চেনেন তিনি, এদের না পেলেও যে তাঁর চলে না। এই মানুষগুলির কোনো বিশেষ গোষ্ঠীলক্ষণ নেই, নেই কোনো অবয়ব; এদেরকে চিনে নিতে হয় হাজার জনতার মধ্য থেকে। অভীন্দ্রনাথ দেখতে পান এদেরকে খুঁজে নিতে কোনো ক্লেশও নেই তাঁর, এরা তাদের নিয়তির অমোঘ টানে আপনিই এসে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে। কোনো সমাবেশে, মধ্যাহ্নভোজ কি ধূমপানের অবকাশে, তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে এদের নীরব পুস্তকপ্রীতি, এদের বিদ্যানুরাগ। তিনি বুঝতে পারেন এদের মধ্যে প্রাপ্তির কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, পুস্তকের উৎপাদনশালাই তাদের কাছে পুণ্যতীর্থ, তার জন্য তারা দিয়ে ফেলতে পারে সময় শ্রম ও অনেক কিছু। কোনো শুভমুহূর্তে তিনি বলে ফেলেন, ‘চলে আসুন ‘গৈরিশ’-এ’, এবং সঙ্গে সঙ্গে জিতে নেন তাদের আরক্তিম আনুগত্য। এরা তাঁর বিচারে শ্রুতকীর্তি নয়, তিনি জানেন এদেরকে গুরুত্বের যোগ্য মনে করবার দায় তাঁর নেই। এদেরকে পারিশ্রমিক দেবার চাপও নেই যেহেতু এরা শ্রমের জন্য প্রত্যাশা করে না কোনো অর্থমূল্য। এদেরকে একটুখানি জাতে তুলে দিয়ে, অথবা জাতে তোলার কুহকটুকু তৈরি করেই, তিনি নিশ্চিন্ত; এর বেশি উদ্বেগের কারণ নেই তাদের নিয়ে।
অতএব, সুবন্ধু সিংহকেও এভাবেই তিনি জাতে তুলেছিলেন। কোনো সেমিনারে ইংরেজিভাষায় তার প্রশ্ন শুনে ভেবেছিলেন সে অধ্যাপক। কিন্তু সেই ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে সে জানায়, ‘আরে না না, আমি শিক্ষিত লোকই নই। ইংলিশে কোশ্চেন করেছি বলে আপনি ওসব ভেবেছেন।’ ইচ্ছে করে সে উচ্চারণ করল ‘কোশ্চেন’, এবং এক ঢিলে অনেক ধারণাকে আঘাত করল। তবে সেদিকে মন না দিয়ে অভি তাকে নিজের দরবারে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তার একটি লেখাও তিনি ছেপেছেন। আর, তার হাতে প্রথম দিনেই তুলে দিয়েছেন সাতশো পৃষ্ঠার প্রুফ, ‘গৈরিশ’-এর উচ্চবর্গীয় বামপন্থীদের রচনায় নানামাত্রিক রবীন্দ্রচর্চা। ‘এক্ষুণি না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে’, অভীন্দ্রের ওই তাগাদায় সে সেটা দেখে দিয়েছিল আড়াই দিনে; তারপর তা অস্পৃষ্ট পড়ে থেকেছে চার মাস, রাজু কঠিন চাহনিতে দেখেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংশোধনগুলো, সুবন্ধুর পরিকল্পিত নির্ঘণ্ট (‘গৈরিশ’-এ প্রথমবার); শেষে কখন তা হারিয়ে গেছে। এর পরে পরে সুবন্ধু ভার নিয়েছে পত্রিকার শীতসংখ্যা, আরেকটি বাংলা ও দু’টি ইংরেজি সংকলনের প্রুফের। সুবন্ধুর দিক থেকে এ কাজে উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। তা দেখে অভীন্দ্র আশ্বস্ত হয়েছেন সে বুঝি ধন্য হয়ে গেল। আর, এই অবকাশে, নিজের অগোচরে তিনি সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে গেছেন সুবন্ধুর কাছে।
এই সময় প্রবেশ করেছিল অমিয় সেন। অভি তখন মৌন ভেঙে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলছেন, ‘চল্লিশ বছর!’ তাঁর চোখে আত্মতুষ্টির বিধুরতা, বিকেলের এলানো ছায়ার মতো গভীর। তাহলে চল্লিশ বছরে ‘গৈরিশ’ কয় প্রজন্মের মননশীলতার প্রতিপালক হয়ে রইল? সুবন্ধুর হিসেব, তিন। অভির বিস্ময়োক্তি, মাত্র তিন! সুবন্ধু ব্যাখ্যা করে, মানুষ প্রজননক্ষম হয় তার ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বছরে। তার আগে পরবর্তী প্রজন্ম আসতে পারে না। তাই ‘গৈরিশ’-এর সূচনাকালকে যদি একটি প্রজন্মের জন্মলগ্ন ধরা যায় তাহলে চল্লিশ বছরে তিন প্রজন্ম। অভির মতে, প্রতি দু’বছরে একটি প্রজন্ম। জৈবিক প্রজন্ম নয়, মানসিক প্রজন্ম। সেই হিসেবে কত হল? কুড়িটি প্রজন্ম। ভাবতে পারেন! কত বই, কত লেখা। ‘গৈরিশ’ একটি আগ্নেয়গিরির কেন্দ্র। নিত্য দহনশীল। - ‘এই কথাগুলো আমাদের ফেসবুকে দিতে পারেন না?’ শুনে সুবন্ধু হাসে। ‘পারি। কিন্তু ‘গৈরিশ’-এর আর নতুন ঢাকের প্রয়োজন কী?’ তার উক্তিতে কোনো হুল নেই। অভি অপ্রস্তুত হন। আলাপের তাল কেটে যায়। অভি সুবন্ধুকে বলেন, ‘এই, আপনার লেখায় কিন্তু বানান ঠিক নেই... এখন মনে পড়ছে না। পরে দেখিয়ে দেব। আছে। যা বলছি শুনুন না।’
অমিয় বলে, ‘হুঁ, র-ড় অনেকেরই সমস্যা।'
সুবীর খুক করে কাশে। বাইরে ক’টা কাক মাটিতে নেমে এসে খেয়োখেয়ি করছিল। সুবীর কাগজের দলা পাকিয়ে সেদিকে ছুঁড়ে দেয়।
সুবন্ধু বেরিয়ে যায়, তার পিছু পিছু শম্ভু। পত্রিকার মহতী মীটিং শুরু হয়ে যায় ঘরের ভিতরে।
… আজকের পাথুরে বাতাসটা আর ভালো লাগছে না শম্ভুর। রাজু কোনো কথা বলছে না কেন, বকবকে রাজু?
ও ঘরে সুবীর আর অমিয় সেন বসে আছে। প্রবীর গেছে পাশেই শ্রীপত্র-এর কার্যালয়ে। এক্ষুণি আসবে। সুবন্ধুকেও ডাকা হয়েছিল। সে অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে দিয়েছে ডাক, যেন কোনো অপকর্মে যোগ দেবার প্রস্তাব এসেছিল তার কাছে। এখন অভি এসে গেলেই হয়। তিনি আজই ফিরেছেন বাংলাদেশ থেকে। কাঁকুড়গাছি থেকে এদিকে রওনা দিয়েছে তাঁর গাড়ি।
... অমিয় সেনের নাম নির্বাহী সম্পাদক রূপে চিহ্নিত হয়েছে গত তিনটি সংখ্যায়। সে কোথা থেকে উদিত হল? সে হঠাৎ একদিন এল বইমেলার স্টলে, নিঃশর্ত ক্ষমা চাইল অতীতের কোনো কৃতকর্মের জন্যে, জানাল বড়ো চাকরি সে হেলায় ত্যাগ করেছে কোনো নৈতিক বিরোধের ফলে, এবং এখন তার স্বাধীন অবকাশ ও ভারবতী অভিজ্ঞতার পুরোটাই সে দিতে চায় ‘গৈরিশ’-কে; তার নম্র বাসনা যেন মঞ্জুর হয়। চিবিয়ে চিবিয়ে (অথবা ৎচিবিয়ে ৎচিবিয়ে) সে যা বলে তাতে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে যান অভি। তার মন্থর বাচনভঙ্গি, তার চ-ছ-জ-ঝ-এর ঈষৎ-ঘর্ষণজাত বিশিষ্ট ধ্বনি, so, but ও even খচিত বাংলা বাক্য, ভরসা জাগায়। সহযোগী বলে কোনো ধারণা যদি কোনোদিন লালন করে থাকেন অভি তার একটা আস্ত চেহারা তিনি আজ চোখের সামনে দেখতে পান। হাতে হাত ঘষে বলতে থাকেন, ‘গডসেণ্ড!’ চেয়ার টেনে গভীর ভাবে আলোচনায় বসে পড়েন। বিষয় – ‘গৈরিশ: নতুন ভাবনা’। অমিয় প্রস্তাব দেয় একদিনের আলোচনাসভার, যার নাম হবে ‘গৈরিশ: নতুন বীক্ষণ নতুন প্রত্যয়’। উপযুক্ত নামটাতে খুব খুশি হন অভি। সভাস্থল? – ‘আকাদেমি, জীবনানন্দ, মহাবোধি – কোন্টা চাইছেন?’ – প্রধান অতিথি? আরাত্রিকা ভাদুড়ী অস্লভ্স্কি (অথবা অস্লভ্স্কায়া), যিনি শীতকালটা কাটান কোলকাতায়, তাঁকে স্কাইপ-যোগে রাজি করাবার দায়িত্ব নিচ্ছে অমিয়। উপস্থিত কর্মচারীদের সহাস্য কটাক্ষের মাঝখানে অভি নির্দেশ দেন: ‘সুবীর, ফ্লেক্স রেডি করো।’
এবং সাতাশ দিনের মাথায় সেই সভায় তড়বড় করে মঞ্চে উঠে যান শম্ভু। সেলোটেপ দিয়ে ফ্লেক্স লাগাতে গিয়ে সেলোটেপের সঙ্গে ফ্লেক্সটাকেও কেটে ফেলেন। অভির আহ্বানে সে সভার সূত্রধর সুবন্ধু। তার পাঁচ মিনিটের মৌখিক প্রস্তাবনায় পঞ্চাশ মিনিটের ঘনত্ব জমে ওঠে। কী ধৃষ্টতা! অভিকে খোঁচা মারে অমিয়। অভিকে বলতে শোনেন শম্ভু, ‘এত বেশি বলছে কেন!’ সুবন্ধুও শুনতে পায়। তখন সপ্ততিবর্ষীয়া আরাত্রিকা ভাদুড়ী অস্লভ্স্কি (বা অস্লভ্স্কায়া) তাঁর চশমার একগজি কর্ডজোড়ার একটিকে আঙুলে জড়িয়ে অপাঙ্গে দেখেন সুবন্ধুকে। ভাবলেশহীনতায় ইস্পাত-কঠিন তাঁর মুখটাতে একটু কি আগ্রহের লঘুতা দেখা যায়? তৎক্ষণাৎ ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়ে একটি গাঢ় লিপস্টিক বার করে আত্মমগ্নতার আড়াল তুলে ফেলেন তিনি।
… ক্রিয়াপদগুলো শেষ করে শম্ভু নতুন কাগজ নিলেন। শিরোনাম লিখলেন ‘বিশেষণ’। ‘ছোটো’ না ‘ছোট’, ‘মেজো’ না ‘মেজ’, ‘ভালো’ না ‘ভাল’? কিন্তু আর মন বসছে না। অভিদার ফোন এসেছে দু’বার। তিনি জানতে চেয়েছেন শম্ভু আছে কি না। সেদিন বিশেষণগুলো নিয়ে সুবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করলে ভালো হত। তার বদলে তাঁর মনে পড়েছিল খবরের কাগজের কর্তিকাগুলোর কথা। হরিচরণ ও জ্ঞানেন্দ্র এই দুই অভিধানকার শব্দার্থ ও প্রয়োগের বিচিত্রতা ঐতিহাসিক শৃঙ্খলায় অনুসরণ করতে চেয়েছেন। প্রতিটি শব্দের ঘরে তাঁদের যে উদ্ধৃতির সঞ্চয় তাতে সাহিত্য আছে, অথচ সংবাদপত্র থেকে বিশেষ আহরণ নেই। কিন্তু সংবাদপত্রকবলিত এই কালে কারও পক্ষেই সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের ভাষাকে উপেক্ষা করা কি সম্ভব? তাই বানান গবেষণার নিষ্ঠায় শম্ভুনাথ ধাড়া নগর কোলকাতার চারটি দৈনিক ও তাদের সাময়িকপত্রাদি থেকে বিস্তর নমুনা সংগ্রহ করেছেন।
তখন সুবন্ধুর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। ভবঘুরে কুকুরটাও তাদের পিছু নিয়েছে। শম্ভু বেরিয়ে এসেই বলেছেন, ‘শিগগির একটা ঝামেলা বাধবে - দেখবেন।’
‘কী নিয়ে?’
‘ওই অমিয় সেন। আর আমাকেও ওরা জড়াবার চেষ্টা করবে।’
সুবন্ধুর মতো কাউকে কোনোদিন পান নি শম্ভু যে তাঁর কাজকে এতটা মনোযোগ দিয়ে দেখেছে। তিনি খুলে ধরেন চিরশ্রী প্রকাশনীর প্রুফ, পৃষ্ঠা-পিছু ছ’টাকা দরে যা তিনি দেখে দেন। ‘বলুন তো, এটা কী হবে? ‘সব চেয়ে’, একসঙ্গে না আলাদা?’
সুবন্ধু বলে, ‘আপনি রবীন্দ্রনাথের ‘নামঞ্জুর গল্প’ পড়েছেন, রচনাবলী শতবার্ষিক সংস্করণে? ওতে দেখবেন একসঙ্গে ‘সবচেয়ে’ আবার হাইফেন দিয়ে ‘সব-চেয়ে’ দুই-ই আছে। জোড়টা যদিও ভাঙে নি। কী বলবেন? অসমতা? সমতার বড়ো দায়। কিন্তু আবার, ‘সব কিছু’ যদি জুড়ে লেখেন তো ‘সব জিনিসে’ কী করবেন?’
তারপর শম্ভু হঠাৎ বার করেছেন সেই কাটিংগুলো, যেগুলো ইউক্লিড-বর্ণিত যাবতীয় দ্বিমাত্রিক আকৃতির মেলা। ঝোলাটাকে হাতড়ে হাতড়ে নিঃশেষ করে চিরকুটের ঢিপির ঠিক সামনে বসে তিনি গর্বিত হয়ে উঠেছিলেন।
সুবন্ধু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘এগুলো কেন করছেন?’
‘না, ‘গৈরিশ’-এর একটা বানান নীতি হোক।’
অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক সংশয় শম্ভুর। সব জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন তূর্য সেনগুপ্তকে, যাঁকে সকলে মানে। তূর্যবাবু তাঁর অভ্যাসমতো জবাব দেন নি। শম্ভু দেখান বাংলাভাষার পিতামহকে লেখা তাঁর চিঠির ফোটোকপি।
সুবন্ধু বলে, ‘রবীন্দ্রনাথ হলে জবাব দিতেন। আপনার ব্যাগে ওগুলো কী, শম্ভুদা? ব্যাগটা এবার একটু কাচুন ভালো করে।’
‘এই তো, ‘বাঙালির দশা’ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। কী যে করি বইটা নিয়ে?’
তখন এই আশ্চর্য বইটা নিয়ে তিনি কথা বলেন। এ বইয়ের প্রুফ দেখার অনুমতি ছিল না। লেখক নিজেই কম্পোজ করে পেন-ড্রাইভ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারণ-নির্দেশক বিচিত্র চিহ্ন, অসংখ্য ঊর্ধ্ব-কমা, যুক্তাক্ষরের আজগুবি সব চেহারা পীড়া দিচ্ছে শম্ভুকে। সেই সঙ্গে বুঝতে পারছেন না, এই লেখক, প্রতিটি ব্যাপারে যাঁর জবরদস্ত্ বক্তব্য আছে, কেন ‘ধারণা’ স্থলে লেখেন ‘ধারনা’, ‘এখন’ ‘কখন’-কে লেখেন ‘এখোন’ ‘কখোন’। কেনই বা ‘কিছুজনে’ বলে একটা শব্দের প্রতি তাঁর বিশেষ টান?
সুবন্ধু প্রথমে এড়িয়ে যেতে চায়। শেষে মানতেই হয়, এত নতুন নতুন চিহ্ন কেন, এত ইলেক-চিহ্ন কেন? এটা তো উচ্চারণের অভিধান নয়। পরিচিত যুক্তাক্ষর নিয়ে এত কসরৎ কেন? এখন তো সেই ভঙ্গুর টাইপের যুগ নয়। সে হাসে, ‘ইনি তো দেখছি যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।’
‘তো কী করব বলুন। আর বইয়ের কী দাম করেছে জানেন?’
‘এত ভেবে কী করবেন? শুনুন, কাঞ্চনমূল্যে বাংলা বই কিনে যে পাঠক শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করবে সে অবিশ্বাসী ও ঘোর নাস্তিক, তার কথা কানে নিতে নেই। বুঝলেন?’
সুবন্ধুর তিক্ত কৌতুকটা শম্ভুর মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে। তিনি বলেন, ‘দেখুন, আগে এত ভাবতাম না। আপনি বয়সে অনেক ছোটো, তবু বলতে বাধা নেই, আপনি আসার পরে আজকাল অনেক কিছু ভাবতে চেষ্টা করি। তো আপনি কি বলছেন কিছুই করার নেই?’
‘শুধু দেখুন কিছু বাদ-টাদ পড়ল কি না।’
‘আর কিছু?’
‘নাঃ। আপনি বরং ‘গৈরিশ’-এ নিজের জায়গাটাকে শক্ত করুন। আর খুব যদি কিছু করতে ইচ্ছে হয় তো লেখকের ‘পণ্ডিত’ ‘ঘণ্টা’ ইত্যাদি তৎসম শব্দে মূর্ধন্য-ণ ফিরিয়ে আনুন।’
‘আচ্ছা, এত বুঝব কী করে বলুন তো। ‘ঘণ্টা’ তৎসম, ‘ঘণ্ট’ কি তৎসম?’
সুবন্ধুর খুব মায়া হয় মানুষটার ওপর। তাঁর সদিচ্ছা সাধ্য বাতিক ও সংকটের কথা ভাবতে ভাবতে সে বিদায় নেয়।
... এর পরেও শম্ভু খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়েছিলেন কি না তা জানা নেই সুবন্ধুর।
পরের ক’টা দিন কেবল একটা অস্বস্তি পাথরের মতো জমে উঠেছে শম্ভুর বুকে। কীসের মীটিং? ওরা যে বলল যন্ত্রস্থ বইগুলোর প্রচ্ছদ নিয়ে মীটিং হবে। তো আমাকে ডেকেছে কেন? শম্ভু ভাবতে থাকেন কবে কবে অভিদার মুখের ওপর কথা বলেছেন তিনি। ওরা যদি বইয়ের দাম নিয়ে কিছু বলে? এ নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন তোলেন শম্ভুনাথ। ‘গৈরিশ’-এর অধিকাংশ প্রকাশনার পিছনে থাকে কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদান, এবং তা জোগাড় করবার কাজে আশ্চর্য নৈপুণ্য অভীন্দ্রনাথের। বিশেষ করে যদি প্রস্তাবিত গ্রন্থটি হয় কোনো সংকলন, কারণ সংকলনমাত্রেই একটি প্রজেক্ট। তাই সাহিত্যবিষয়ক সংকলনে অর্থ মঞ্জুর করে কোনো পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র, বিজ্ঞান সংকলনে সাহায্য করে ইতিহাসচর্চার প্রতিষ্ঠান। অভি একে বলেন ক্রস-ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। তাঁর এই দক্ষতা ছাড়া বাংলাসাহিত্য কিম্বা বাঙালির মননশীলতার কী দশা হত? তবু যখন আকাশছোঁয়া দাম ঠিক করা হয় শম্ভু চুপ থাকতে পারেন না। কর্মচারী হয়ে সেটাও কি সীমালঙ্ঘন নয়?
কত যে পাপবোধ তাঁর মনে; তার মধ্যে জেগে ওঠে একটা অস্ফুট প্রতিজ্ঞা। এখন বানানবিষয়ক খসড়াটা শেষ করতেই হবে। অভিদা এলেই শম্ভু সেটা নিবেদন করবেন তাঁর হাতে।
অমিয় সেনের উপস্থিতিটা খুব কুটিল মনে হচ্ছে আজ। বেড়ালছানাটা আবার ডাকছে। আদুরে ডাক।
ওই আসছে। অভিদা আসছেন। সঙ্গে ডঃ সেনাপতি। আকাশ ভেঙে পড়ল শম্ভুর মাথায়। সেনাপতিকে কে নিয়ে এল? শম্ভু কী শুনলেন কে জানে; বলতে লাগলেন, ‘কী? অভিদার স্ট্রোক হয়েছে!’ তিনি অস্থির হয়ে বিস্কুট খাওয়ালেন কুকুরটাকে।
অভীন্দ্র যখন ঘরে প্রবেশ করে ফেলে দিতে বললেন ‘ওই কাগজগুলো’, সরস্বতীর পলাতক পুত্র শম্ভুর শ্রেষ্ঠ দান, শম্ভু তখন ছটফট করছেন বাস স্টপে, আর খুব মনে পড়ছে সুবন্ধুর কথা।
(পরবাস-৬০, অগস্ট ২০১৫)