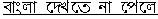সে এক বিশাল বটগাছ। বিশাল বেড়ের গুঁড়ি মাঝখানে। অনেকটা জায়গা জুড়ে চারপাশে অজস্র ঝুরি নামিয়ে বেশ সবল অধিষ্ঠান। মাথার ওপর সতেজ পাতার নিটোল আচ্ছাদন। জ্বলন্ত গ্রীষ্মেও স্নিগ্ধ ছায়ার অনাবিল আশ্বাস। আশ্রিত পক্ষীকুলের কলকাকলিতে প্রাণবন্ত সারাটা দিন।
পরশের মনে হয় এমন একটা গাছ আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই থাকা দরকার—কাছে হোক বা দূরে। কিছুটা বিশ্রাম, কিছুটা শান্তির জন্যে। নিরাপদে, নিশ্চিন্তে ভাবার জন্যে। আর সবচেয়ে বেশি দরকার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে। যেখানে বার বার এক দৌড়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে অল্প আয়াসে। চোর চোর খেলায় বার বার বুড়ি ছুঁয়ে ফেলার মতো।
এমন একটা গাছ সত্যিই ছিল। আজও হয়তো আছে স্বমহিমায়। সেখানে যেতেই হবে একদিন। পথ যদিও আগের চেয়ে সুগম হয়েছে। তবু মনে হয় অনেক দূরের সে পথ, এ জীবনে পার হওয়া সম্ভব হবে না আর। চেষ্টা করে যেতে হবে বারবার। অন্ততঃ আরেকবার সেই গাছটার কাছে পৌঁছে যেতে চায় পরশ। সে উপলব্ধি করে যেদিন পৌঁছে যাবে সেদিন সেও গাছই হয়ে যাবে। সুদীর্ঘ কালের নীরব এবং নিরপেক্ষ সাক্ষী হয়ে সে তাকিয়ে থাকবে কখনো মাটির দিকে—কখনো আকাশের দিকে।
পরশের দেশের বাড়ি খুব দূর নয় কলকাতা থেকে। ভোরে হাওড়া থেকে ট্রেন। স্টেশনে নেমে বাস। সওয়া নটা নাগাদ বাস থেকে নেমে বাসস্টপের পাশেই নারাণ ময়রার দোকানে মণ্ডা আর রসগোল্লা খেয়ে পথচলা শুরু। বাসস্টপ থেকে একটু এগোলেই বড় একটা গ্রাম—একটা মসজিদ, দুটো মন্দিরের পাশ কাটিয়ে...।
বাবার যে একটা ডাকনাম আছে সেটা প্রায় ভুলেই গেছিল পরশ। বাড়িতে বাবার পরিচিত যাঁরা আসেন—পাড়ার বা অফিসের কলিগ, কেউ জীবনবাবু বা জীবনদা ডাকেন। বাবা সবার বড় বলে কাকা ও পিসিমারা ডাকেন বড়দা। দিদিমা, বড়মামা ডাকেন জীবন বলে, বাকিরা সবাই ছোট—তাই জামাইবাবু। একমাত্র ঠাকুমা ডাকতেন মান্তু বলে। দাদুকে পরশ দেখেনি, আর ঠাকুমাও চলে গেলেন বেশ কবছর হল। কাজেই বাবার ডাকনামটা প্রায় ভুলতেই বসেছিল।
পথে বাবার পরিচিত নানা বয়সের মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। চলছিল প্রণাম দেওয়া এবং নেওয়া। সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ। পাশে থেকে পরশ দেখছিল, শুনছিল। বাবাও যে কোনসময় ছোট ছিলেন, স্কুলে গেছেন, দৌরাত্ম্য করেছেন স্কুলে, পাড়ায়, গ্রামে। কানমলা, গাঁট্টা খাওয়ার মতো অপরাধ যে বাবাও কোনদিন করতে পারেন, এটা কোনদিন মনেই হয়নি পরশের। এইসব গ্রামগুলির মাঠে ঘাটে রাস্তার ধুলোয়, পুকুরের জলে তার ছোট্ট বাবার বড়ো হয়ে ওঠার কাহিনী মিশে আছে। বাস্তবিক এখানে না এলে, পরশের কাছে এইসব অভিনব সংবাদ অধরা থেকে যেত চিরদিন।
গ্রামটা পার হয়ে বেশ কিছুটা আবাদি জমি। তারপর ডাঙা জমির ওপর সেই বটগাছটা। অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। পড়বেই—না পড়ে উপায় নেই, এমনই অমোঘ তার উপস্থিতি।
“এই গাছটার নীচে আয় একটু বসি।”
“আর কদ্দুর বাবা, এখান থেকে?”
“অনেকখানি, ধর যতটা এলাম এতক্ষণ, ততটাই হবে প্রায়। সামনের এই মাঠটা পার হয়ে, ওইযে অনেক গাছপালা—ওইটে আমাদের গ্রাম।”
পরশ দূরের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করে দূরত্বটা।
“এই গাছটা আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখছি। একইরকম বিশাল। যে গ্রামটা পার হয়ে এইমাত্র এলাম ওখানেই আমরা পড়তে আসতাম। পাঠশালা থেকে ফেরার পথে এইখানে হয়ে যেতাম।”
“কি করতে এখানে?”
“তোরা কি করিস স্কুল ছুটির পর।” বাবার চোখে দুষ্টু দুষ্টু মজার আলো।
“খেলি।”
“আমরাও খেলতাম। তোদের স্কুলে ছোটদের জন্যে দোলনা, সি-স, বানিয়ে রাখা আছে। আমাদের ছোটবেলায় এটাই আমাদের খেলার জায়গা ছিল। ঝুলে থাকা এই ঝুরি থেকে ঝুলতাম—দুলতাম। হাত পা ছড়ে যেত। বাড়িতে ধরা পড়লে মা পেটাত খুব। বলত দস্যি ছেলে কোনদিন পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবি।”
“ঠাকুমা মারত তোমাকে? দেখে তো মনে হয়নি কোনদিন। আমাদের তো কোনদিন বকেছেন বলেও মনে পড়ে না।”
“তোরা তো নাতি। তোদেরকে তো ভালবাসবেই। আর বয়েস হলে মানুষ অনেক শান্ত হয়ে যায় না? আমি, তোর মা তোকে কম পিটিয়েছি ছোটবেলায়।” বাবা লাজুক হাসেন। “দেখবি, তোর যখন ছেলেমেয়ে হবে, ভীষণ আদর করব। তোরা শাসন করতে গেলে, মারধোর করতে গেলে, দেখবি বাধা দেব। উপদেশ দেব বাচ্চারা অমন একটু আধটু করতেই পারে।”
বাবার চোখের দৃষ্টি ভীষণ নরম আর মায়াময়। এই বটগাছের মতোই যেন। ভীষণ মায়াবি ছায়াঘেরা।
“এতটা পথ হেঁটে আসতে কষ্ট হয়নি তো তোর? এই গরমে।”
“নাঃ, কষ্ট হয় নি, বাবা।”
“তোদের তো অব্যেস নেই।”
“তোমার যেন আছে। তুমিও তো কলকাতাতে ট্রাম বাস ট্যাক্সিতেই অভ্যস্ত বহুকাল।”
“তা ঠিক। তবে কি জানিস, আমাদের বনেদটা তৈরি হয়েছিল এই কষ্ট দিয়েই। নাঃ, ভুল বললাম। তখনকার দিনে এগুলোকে কেউ কষ্ট বলে ভাবতাম না। ভাবনা তো দূরের কথা, মাথাতেই আসত না। এছাড়া যে অন্য কিছু হওয়া সম্ভব, সেই চেতনাটাই ছিল না যে! পাঠশালা ছেড়ে আমরা যে হাইস্কুলে পড়তাম, সেটা এই তল্লাটের একমাত্র হাইস্কুল। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। রোজ হেঁটেই তো যেতাম। সবাই, সে যত ধনীই হোক বা দরিদ্র, একই ভাবে রোজ মাইল দশেক হাঁটতাম। সত্যিকার কষ্টটা হত বর্ষাকালে। যখন মাঠ ঘাট প্রায়ই ডুবে থাকত জলে, আর মাঝে মাঝে বান আসত নদীতে।”
কিছুক্ষণ থেমে বাবা আবার বললেন,
“আমরা গেছি, আমাদের আগেও বাবা কাকারা গেছেন, আমাদের পরেও বহুদিন চলেছে এইভাবে। স্কুল থেকে ফিরে মাঠে দৌড়িদৌড়ি করেছি বল নিয়ে। এই ভাবেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল আমাদের সেই জীবনযাত্রা। একসঙ্গে যাওয়া আসা করতাম এক গাঁয়ের ছেলেরা। ফাজলামি, পেছনে লাগা, মাঝে মাঝে বদমায়েসি সবই ঘটত চলার পথেই। সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠত এক একটা সম্পর্ক। অনেককে মেনে নেওয়ার, অনেকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠত নিত্য পথ চলায়।”
“আমরা যারা শহরে থাকি, আরামে যাওয়া আসা করি, আমরা কি এই সম্পর্কটা মিস করি?”
“ডেফিনিটলি। ক্লাসে কতটুকু সময় পাস বন্ধুত্ব করার—টিফিনের সময়টুকু ছাড়া? স্কুল ছুটি হলেই সবাই বেরিয়ে পড়িস কেউ স্কুল বাসে, কেউ ভাড়ার গাড়ি, কেউ নিজের গাড়ি। কেউ কেউ ট্রামে, বাসে বা পায়ে হেঁটে। যাই বলিস আমরা যে স্মৃতি বয়ে চলেছি—তোরা তার ভগ্নাংশও কল্পনা করতে পারবি না। সব স্মৃতিই আনন্দের বা সুখের নয়। স্মৃতিও গাছের মতোই। কেউ ফল দেয়, ফুল দেয়। কেউ কাঁটা দেয়। কেউ কিচ্ছু দেয় না—দেয় শুধু শান্তি। এই বটগাছটার মতো।”
বাবা চুপ করে গিয়েছিলেন। চোখ বন্ধ। মনে হয় গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন। পরশ কলকাতায় বাবাকে এত কথা বলতে শোনেনি কোনদিন। বাবা বরাবরই গম্ভীর এবং বাংলা সিনেমার বাবাদের মতো ভয়ংকর না হলেও, সমীহ-কাড়া দূরত্ব বজায় রাখতেন সবসময়েই।
এই গ্রাম, এই মহীরুহ বট, দীর্ঘ অদর্শনের পর এত পরিচিত জন, বাবাকে বিচলিত করেছে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরে আসছে চোখের সামনে ফ্ল্যাশব্যাক হয়ে, আবেগে ভাসিয়ে দিয়ে।
অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা তাকালেন, মুখে লাজুক হাসি, বললেন,
“তোদের ভাষায় বললে, বোর হলি তো?”
“নাঃ, একদম না।” পরশ হাসে। “বরং ভীষণ ভাল লাগছে। আসার সময় বহুদূর থেকে এই জায়গাটা দেখে সত্যি দারুণ লাগছিল। চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত মাঠ, জমি, আশেপাশে কিছু এলেবেলে তালগাছ। তার মধ্যে এই গাছটির সুপ্রাচীন অস্তিত্ব। নিমেষে মন ভাল হয়ে গেল। কিন্তু এতক্ষণ বসার পর মনে হচ্ছে—এই গাছটার বোধহয় কোন জাদু আছে। অনেস্টলি বাবা, এখানে না এলে, তোমাকে এভাবে হয়তো চিনতামই না। তোমাকে এত কথা আমি অন্ততঃ কোনদিন বলতে শুনিনি। অনেক না বলা কথা তোমার ভেতরে জমা ছিল। আজ তুমি প্রকাশ করলে। তুমি আজ যখন বলছিলে বাবা, আমার চোখের সামনে থেকে পর্দাটা যেন সরে গেল। তোমাদের সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ ফেলে আসা দিনগুলো যেন ফুটে ঊঠল চোখের সামনে। রিয়েলি, এই গাছটা জাস্ট গাছ নয়, যেন—যেন—কি বলব—যেন একটা ব্যক্তিত্ব।” বাবা মুচকি মুচকি হাসছিলেন। লজ্জা পেয়ে পরশ বলে,
“হেসো না, বাবা। আমার মনে হল—তাই বলে ফেললাম, ব্যস।”
“হাসছিলাম তোর কথা শুনে নয়”—হাসি মুখেই বাবা বললেন—“ভাল লাগল তোর ফিলিংসটা। বুঝলাম আমার ছেলে হিসেবে তুই খুব একটা খারাপ নোস।”
“দেখলে তো বাবা, তোমার রবি ঠাকুরের ভাষায়, এতদিন আমাদের ‘চেনাশোনা’ ছিল, আজ থেকে ‘জানাশোনা”র সূত্রপাত হল।” পরশের মুখে ফাজিল হাসি।
“তোর মুখে রবীন্দ্রনাথ! কবে পড়লি ‘শেষের কবিতা’?”
“না না অতটা আশাবাদী হয়ো না, ক্যাসেটটা শুনছিলাম একদিন।”
“পড়িস, সুযোগ পেলেই পড়িস। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জীবনটাকে চিনতে বেশ অসুবিধে হয়।”
“অ্যাই, তোমার আবার শুরু হল। রবি ঠাকুরে অবসেসন তোমার আর পাল্টাবার নয।”
“কী এমন ঘটল যে—যার জন্যে নিজেকে পাল্টে ফেলতে হবে!”
“তোমার ঘটেনি, কিন্তু আমার ঘটেছে।” গম্ভীর মুখে পরশ ব্যক্ত করে।
“কি?” বাবার চোখে বিস্ময়।
“এতদিন তোমার গাম্ভীর্যের ধাক্কায় তোমাকে ‘ওরে বাব্বা’ ভাবতাম। আজ থেকে শুধু বাবা—খুব ভালোবাসার প্রিয়জন বাবা ভাবব।”
“এতটা পেকেও গেছিস তুই বুঝিনি তো—একটি গাঁট্টায় মাথা ফুলিয়ে দোবো...।”
বাবা রাগের ভঙ্গিতে হাত তুলতেই—পরশ মাথা বাঁচানোর ভঙ্গিতে মাথা ঢাকে, মুখে তার ফিচেল হাসি। বাবাও হেসে ফেললেন। বললেন,
“নে ওঠ, এখনো অনেকটা পথ যেতে হবে।”
অনেকটা পথ যেতে হবে। তাই আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বের হল পরশ। তার গন্তব্য অনেকটাই দূর—জোকা পার হয়েও বেশ কিছুটা। রাজারহাট থেকে তিনটে নাগাদ বেরিয়েও ‘ফোর্থ স্টেজ’ ওল্ডএজ হোমের গেট অব্দি পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বাজিয়ে ফেলল পরশ। পার্কিংয়ে গাড়ি লক করতে করতে লক্ষ্য করল বাবা বারান্দায় বসে আছেন। পরশ হাত নাড়ল। বাবা কোন রেসপন্স করলেন না। হয়তো খেয়াল করেন নি। আজ তো তার আসার কথা ছিল না, কাজেই পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় থাকবেন এমনটাও নয়।
একটু দূর পরে বটে, কিন্তু বেশ ভাল এই হোমটা। অনেকটা জায়গা জুড়ে ক্যাম্পাস। বাড়িটাও বেশ বড়। অনেক গাছপালা, বড় বাগান, সুন্দর সাজানো। ব্যবস্থাপত্রও ভালোই। পরশ এদিক ওদিক অন্যান্য বৃদ্ধাবাস সম্পর্কে যা শুনেছে, তার তুলনায় এটা ওয়েল ম্যানেজড আর ওয়েল মেন্টেন্ড।
নীচের কাউন্টারের রেজিস্টারে নাম ধাম লিখে পরশ জোড়া জোড়া সিঁড়ি পার হয়ে দোতলায় উঠল। লম্বা করিডর ও দীর্ঘ বারান্দা পার হয়ে বাবার পিছনে দাঁড়াল পরশ। বাবা একই ভাবে বসে আছেন সামনের বড় গাছটার দিকে তাকিয়ে। পরশ গাছ টাছ তেমন চেনে না, তবে গাছটা ঋজু, সুঠাম আর শাখাপ্রশাখা সমেত বেশ ঝাঁকালো জম্পেশ গাছ। বাবা সেটার দিকেই নিবিষ্ট তাকিয়ে আছেন।
“বাবা, কেমন আছ?” খুব নরম গলায় ডাকতে পারল পরশ। বাবা কোনমতেই যেন চমকে না ওঠেন। অথবা বাবার এই নিবিড় একাকিত্বটুকু ভাঙতে তার যেন দ্বিধা।
“ঘরে চেয়ার আছে, টেনে নিয়ে বোস।” বাবা নির্দেশ দিলেন। ঘাড় ঘোরালেন না। মাথা তুললেন না। একইভাবে বসে রইলেন সামনের দিকে চেয়ে। পরশ বাবার ঘর থেকে চেয়ার এনে বাবার পাশে বসল।
“কেমন আছ, বললে না তো?”
“তোরা কেমন আছিস। বৌমা, ঊশ্রী। ভাল আছে সবাই?”
“হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে।”
“ঊশ্রীর স্কুল এখন ছুটি না? নিয়ে আসতে পারতিস। অনেকদিন দেখিনি মেয়েটাকে।”
“টিউশন, নাচের ক্লাস। পড়ার প্রচণ্ড চাপ...।”
অস্বস্তি হচ্ছিল পরশের কথাগুলো বলতে। আজ সকালে এই নিয়ে অশান্তি হয়ে গেল খানিকটা। পরশের কন্যা ঊশ্রী আসতে চেয়ে মায়াবী চোখে বার বার দেখছিল পরশের দিকে। ওর মা প্রীতি কিছুতেই আসতে দিল না। একই অজুহাতে—যেগুলো একটু আগে পরশ বাবাকে বলল। পরশ জানে, ঊশ্রী এলে বাবা এমন উদাসীন বসে থাকতে পারতেন না। ছোট্ট চঞ্চল পাখির মতো সে উড়ে আসত, দাদুর গলা জড়িয়ে ধরত। বাবার এই নিবির্কার বসার ভঙ্গি টুটে এলোমেলো হয়ে যেত—অন্ততঃ এই সময়টুকুর জন্যে। পরশকেও ভাবতে হতো না কিভাবে সামাল দেবে বাবার এই উদাসীনতা।
আজন্মই ঊশ্রী ভীষণ দাদু ন্যাওটা। স্কুল থেকে ফিরে জুতো খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত দাদুর কোলে। গলা জড়িয়ে পিঠে চেপে পড়ত। স্কুলের কথা—কোন বন্ধু কি বলল, কোন আন্টি কি বলল—কল কল করে বলে যেত অনর্গল। ওর মা বকত। বলত দাদুকে বিরক্ত না করতে। বাবা আপত্তি করলে বলত, বাবা নাকি আদিখ্যেতা দেখিয়ে নাতনীর বারোটা বাজাচ্ছেন! আর রাগটা গিয়ে পড়ত ঊশ্রীর ওপর। চড়চাপড় মারধোর খেয়েছে কত, তবু ঊশ্রী সুযোগ পেলেই চলে যেত তার দাদুর কাছে।
আজও মেয়েটা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে দাদুর জন্যে। পরশের মনে হয়। আজ সকালে প্রীতি যখন ঊশ্রীর আসাটা নাকচ করে দিল, মেয়েটার মুখটা ব্যথায় পাথর হয়ে গেল। পরশ ঠিক করল খুব শীগ্গির সে আবার আসবে এবং ঊশ্রীকে নিয়ে আসবে সঙ্গে। প্রয়োজন হলে জোর করেই।
মুখোমুখি দুজনেই বসে চুপচাপ। অস্বস্তির পাহাড় সরিয়ে পরশ আবার জিগ্গেস করে,
“তুমি কিন্তু বললে না, বাবা, কেমন আছ?” বাবা কোন উত্তর দিলেন না। মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললেন,
“রোববার ছেড়ে আজকে হঠাৎ চলে এলি, অফিসে ছুটি নিয়ে? অফিসে কাজকর্ম সব ঠিকঠাক চলছে?” বাবা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন পরশের দিকে।
“হুঁ, চলছে, ঠিকঠাক চলছে সব।”
পরশ বলল কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হল না যেন। বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে পরশের ফাঁকটুকু যেন ধরা পড়ে গেল। স্নেহ, ভালোবাসা এবং সমস্ত সম্পর্কের টান থেকে উপড়ে নিজের বাবাকে ঠেলে দিয়েছে একাকিত্বের নিশ্ছিদ্র জগতে। কতোটুকুই বা দূর তার বাসা থেকে এই হোম—তবু যেন মনে হয় সীমাহীন দূরত্ব। অনন্ত সময় যেন পার হয়ে যায় এখানে পৌঁছতে। এ নিয়ে অফিসে, পাড়ায় আড়ালে আলোচনা হয় কানে আসে তারও। শীতল সম্পর্কের ঘেরাটোপে আবদ্ধ পরশ লজ্জায় মাথা নত করে। মনে মনে বলে—কিছুই ঠিক নেই, বাবা, কিচ্ছু ঠিক নেই।
“এই গাড়িটা কবে নিলি। গতবার তো এটা দেখিনি।”
“তুমি দেখেছ? তখন নীচে থেকে হাত নাড়লাম, ভাবলাম তুমি খেয়াল কর নি। রিসেন্টলি নিয়েছি। মাস তিনেক হল।”
কিছুটা উজ্জ্বল হয় পরশ, পুত্রের সাফল্যে কোন পিতা না গবির্ত হয়?
“আগেরটা কি গোলমাল করছিল কিছু?”
“না তেমন কিছু নয়। নতুন মডেল। অনেক ফেসিলিটি। বেটার মাইলেজ। তাই পাল্টে ফেললাম।”
“ভেরি গুড।”
পরশ নিশ্চিত কথাটা আর যাই হোক নিছক প্রশংসা নয়। একটু যেন শ্লেষ মিশে আছে স্বরে। প্রসঙ্গটা এড়াতে, অবান্তর জেনেও পরশ আচমকা জিগ্যেস করে ফেলল,
“বাবা, একবার দেশের বাড়ি যাবে?”
“হঠাৎ?”
“অনেকদিন যাওয়া হয় না। বহুদিন, তাই না? তাছাড়া ঊশ্রীও তো দেখল না আমাদের গ্রাম। ঘরবাড়ি।”
“বেশ তো যাও না, ঘুরে এসো। আজকাল তো হাঁটতেও হয় না, গাড়ি যাবার মতো রাস্তা হয়ে গেছে শুনেছি। তবে গেলে শীতের সময় যেও। গরমে ঊশ্রীর বড় কষ্ট হবে।”
“তুমি যাবে না।” দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা উত্তর দিলেন,
“নাঃ, কী হবে আর ওসবে, যাবার কোন মানে হয় না।”
“তোমার সেই বটগাছটার কথা মনে আছে, বাবা।?”
“কোনটা? তোর সেই ব্যক্তিত্ববান বটগাছটি?”
বাবার মুখে মৃদু হাসি। হাসিটা পুরোন কথা মনে পড়ে যাওয়ার জন্যে। নাকি পরশের প্রতি সামান্য বিদ্রূপ। পরশ ঠিক বুঝল না।
“চলো না, বাবা, একবার। শুধু তুমি আর আমি। আর কেউ না। দুজনে অনেকক্ষণ বসে থাকব সেই গাছের নীচে। কোন কথা বলার ইচ্ছে হলে বলব। না, তো না।”
পরশের কণ্ঠে মিনতির সুর। বাবা পরশের দিকে তাকালেন। তারপর পরশের কাঁধে হাত রাখলেন। কাঁধে বাবার স্পর্শ নিরাপত্তার এক অদ্ভুত বোধ সঞ্চার করল পরশের মনে। বাবা কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন সামনের গাছটার দিকে। পরশের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। নিজের কোলের ওপর জড়ো করে রাখলেন হাতদুটি। খুব জোরে শ্বাস নিলেন।
“সে আর হয় না। আর কখনো হবার নয়।” বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।
“কেন বাবা, দেখ গেলে ভালোই লাগবে।”
“না রে, এই বেশ আছি আমি। এই বারান্দায় এই ভাবেই বসে থাকি সারাটা দিন। মাঝে মাঝে গান চালিয়ে দিয়ে আসি। রবীন্দ্রনাথ শুনি। এই ছোট্ট গণ্ডিটুকুর বাইরে কী আছে, কী ঘটছে সে সব জেনে, আমার আর কী যাবে আসবে, বলতে পারিস? পেছনে ছেড়ে এসেছি যে সব সম্পর্ক, তাদের থেকে না পারব মন খুলে কিছু নিতে, না পারব দিতে।
আজ আমরা যে যেখানে দাঁড়িয়ে, তার সব দায় তোর, এমন ভাবিস না। এটা ভালো নয়। এই ভাবনা তোকে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে দেবে না, অথচ মানসিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবি ধীরে ধীরে। কাছে থেকেও তুই যে এত কম আসিস। তুই কি আসতে পারিস না? পারিস, কিন্তু আসিস না সঙ্কোচে। কোন মুখে দাঁড়াব বাবার সামনে? কোন সান্ত্বনার কথা শোনাব এই ভাবনায়। সবই বুঝি।
নিজেকে বিপন্ন করি এই চিন্তায় যে, তুই নিজেকে কোথাও জুড়তে পারছিস না অন্তর থেকে। না আমার সঙ্গে। না বৌমার সঙ্গে। এমনকি তোর সন্তান ঊশ্রীও বঞ্চিত হচ্ছে তার প্রকৃত পাওনা থেকে। বোঝা যাক বা না যাক, তোর কোলিগ, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া–প্রতিবেশী কেউ মেনে নিচ্ছে না তোর এই ছেঁড়াখোঁড়া সম্পর্কের টানাপোড়েন। মেনে নেওয়া সম্পর্ক আর মনে নেওয়া সম্পর্কের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সে সম্পর্ক যত কাছের বা দূরেরই হোক না কেন।”
সন্ধে হয়ে এল। হোমের গাছে গাছে বাসা বাঁধা পাখিরা ফিরে এসে ব্যাপক কিচির মিচির করছে। শাঁখের আওয়াজ পাওয়া গেল না। প্রদীপ জ্বালালো না কেউ। ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠছে সব জায়গায়। ধূপের মৃদু গন্ধ এসে লাগল নাকে, কেউ জ্বালিয়েছে হয়তো কোন ঘরে বা রিসেপশনে। বাবা অনেক কথা বলার পর চুপচাপ বসে রইলেন। পরশ একবার উঠে বাবার ঘরের লাইটটা অন করে দিয়ে এল। করিডোর আর বারান্দার লাইট এসে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল হোমের একজন, কাছাকাছি এল। ওদের দুজনকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে কিছু বলল না। চলে গেল।
“ঊশ্রীর কোন ক্লাস হল যেন, আজকাল এইসব ব্যাপারগুলো আর মনে রাখতে পারি না।”
“সেভেন।”
“কেমন করছে পড়াশোনা?”
“ওই একরকম। পড়তে চায় না। পড়ায় মন নেই।”
“মারধোর করিস নাকি খুব?” “নাঃ—ওর মা করে, একটু আধটু। খুব জেদি মেয়েটা—কিছুটা স্টাবোর্ন।”
বাবা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মাথা নাড়লেন বার বার। বললেন,
“এমনটা কি হবার কথা ছিল? বৌমাও চান নি। তুমিও না। কেউ না। কিন্তু ঘটে যাচ্ছে এইসব। অনিবার্য্ পরিণতির দিকে চলছে সব কিছু। অমোঘ নিয়তির মতো।”
খুব চঞ্চল আর বিভ্রান্ত লাগছে বাবাকে। যেন অতিষ্ঠ। উঠে দাঁড়ালেন। হতাশায় বিবর্ণ মুখ। কিছুটা রূঢ় ভাবে বললেন—
“তুমি এসো। আর থেকো না এখানে। তোমার দেরি হয়ে যাবে ফিরতে। আবার অশান্তি হবে। ভীষণ কষ্ট পাবে মেয়েটা।”
পরশ উঠে দাঁড়াল। কিছু বলতে পারল না। কথাগুলো কতটা সত্যি তার চেয়ে বেশি আর কে জানে?
“আসছি, বাবা।”
“এসো। আবার এসো। খুব অসুবিধে না হলে ঊশ্রীকে আনবে পরেরবার।”
পরশ এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে। প্রণাম করে বাবাকে। সমস্ত অন্তর নত হয়ে আসে তার এই সমর্পণে। বাবা কাঁধে হাত রাখেন একবার। অস্ফুটে বললেন,
“এস। সাবধানে যেও।”
পরশ নীচে নেমে এল। খুব ধীরে ধীরে। তার শরীরে শক্তি আর নেই যেন। নীচে পার্কিং লটে গাড়ির দরজা খুলে তাকাল দোতলার বারান্দায়। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। পরশ হাত তুলতে গিয়েও নিরস্ত হল। মাথা নিচু করে কিছু ভাবল। তারপর উঠে গাড়ি স্টার্ট করল।
নীরব উদাসীনতায় ঋজু এক মহীরুহের মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন তার বাবা। আশে পাশে স্নিগ্ধ ছায়া মেলে। পরশ আসবে, বার বার আসবে, তাঁর স্নিগ্ধ ছায়ায় কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে বসার আশ্বাসে।
(পরবাস-৬৪, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)