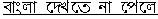Parabaas Moviestore

Parabaas Moviestore

Subscribe to Magazines
পরবাসে দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের আরো
লেখা
ও বই

সত্তর আশির দশকে দেশের প্রগতির লোগো হিসেবে একটা ছবি ব্যবহার করা হত খুব। হাসিমুখ চাষীদম্পতি আর তার পাশে ডিপ টিউবওয়েল থেকে পাম্পসেটে তোলা জলের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষেতের ওপর। আসলে, ষাটের দশকের শেষের দিক থেকেই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাটির তলার জল উত্তোলনের পদ্ধতি এদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার পর, মাটির তলার জলকে চাষের ও গার্হস্থক্ষেত্রে কাজে লাগাবার হার খুব দ্রুতবেগে নদী ও জলাশয়ভিত্তিক জল ব্যবহারকে ছাপিয়ে যেতে শুরু করে। কারণটা বোঝা খুব কঠিন নয়। প্রথমটা অনেক কম খরচসাপেক্ষ। বেশি পরিকল্পনা লাগে না। ভোটভিত্তিক রাজনৈতিক বাতাবরণে এলাকাবাসীকে খুশি করবার জন্য সহজেই জোড়াতালি সমাধানের কাজে লাগানো যায়। নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আর বিপুল খরচের দায়ভার তাতে নেই।
এই ছবিটার পেছনে যে রূঢ় বাস্তবগুলো রয়েছে আসুন সেদিকে একনজর চোখ বোলানো যাক।
১৫ মিটার উঁচু আর অন্তত দশ লক্ষ ঘনমিটার জলধারণের ক্ষমতাযুক্ত বাঁধকে সরকারী পরিভাষায় লার্জ ড্যাম বলা হয়। সত্তরের দশকের শুরুতে এ দেশে তেমন বাঁধের সংখ্যা ছিল ১১১৪টা। একুশ শতকের শুরুতে সে সংখ্যাটা নির্মীত ও নির্মীয়মাণ মিলিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ৫১৯৩তে। (উৎসঃ ন্যাশনাল রেজিস্টার অব লার্জ ড্যামস [NRLD]) এত দ্রুতহারে বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই তিন দশকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেচের ক্ষেত্রে নদীবাঁধভিত্তিক জলের উৎসকে প্রবল গতিতে ছাপিয়ে যাচ্ছে ভূমিগত জলের উৎসের ব্যবহার। কতটা? সঙ্গের ছবিটা সে চিত্র দেখাবে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে ইন্টারমিনিস্টেরিয়াল গ্রুপের রিপোর্ট দেখাচ্ছে, এই মুহূর্তে দেশের শতকরা ৬৫ ভাগ সেচ পাওয়া জমি ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে ফসল ফলাচ্ছে।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখছি, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকেই দেশে বড়ো বাঁধ তৈরির হার দ্রুতবেগে কমতে শুরু করেছে। সত্তর, আশি, নব্বই এবং নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে তৈরি এমন বাঁধের সংখ্যাটা যথাক্রমে ১২৯৪, ১২৫৫, ৬২৫ ও ৩৩৪।
এইখানে একটা সমাপতনের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। খেয়াল করে দেখুন, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে এদেশে বড়ো বাঁধের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের সূচনা। তার চূড়ান্ত রূপে পৌঁছোবার সঙ্গে বড়ো বাঁধ তৈরির গতি শ্লথ হবার সময়টা একেবারে মিলে যায়। ১৯৯৫ সালে সর্দার সরোবর প্রজেক্টে বিশ্বব্যাঙ্কের অংশগ্রহণ বাতিল হবার ঠিক পরের বছর কৃষিক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বেড়ে নদীবাঁধভিত্তিক সেচকে ছাপিয়ে যাওয়াটা এক অর্থে প্রতীকী।
বৃহৎ নদীপরিকল্পনার দুর্দিনের সময় যে সেচপদ্ধতি বিপুলভাবে বেড়ে উঠে কৃষিক্ষেত্রের জলের চাহিদা মেটাতে শুরু করে সেটা হল ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প। ২০০০ হেক্টর অবধি সেচ হয় এমন প্রকল্প “ক্ষুদ্র সেচ”-এর আওতায় আসে। কৃষিমন্ত্রকের হিসেব দেখাচ্ছে, ১৯৯৩-৯৪তে দেশে ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প ছিল ৮.২৪ মিলিয়ন। এর পরেই তা বাড়তে শুরু করে দ্রুতগতিতে। ২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯.৭৫ মিলিয়নে, আর ২০০৬-০৭ এসে দাঁড়ায় ২১ মিলিয়নে।
ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পে ভূমধ্যস্থ জলের ব্যবহার আর মাটির ওপরের জলের ব্যবহার দু-ই হয়। বড়ো বাঁধ তৈরির সামাজিক ও প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো, যা কিনা বড়োবাঁধবিরোধী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, সেগুলো জ্বলন্ত সত্য — তবে ছোটো ছোটো প্রকল্পে, ছোট ছোটো চেক ড্যাম ও জলাধার সৃষ্টি করে ভূতলস্থ জলের ব্যবহার বাড়িয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প গড়ে তুললে তাতে সে সমস্যাগুলো থাকবার কথা নয়। সেটা যদি বাস্তবে ঘটত তাহলে হয়ত ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার এত দ্রুতবেগে ভূতলস্থ জলের ব্যবহারকে ছাপিয়ে যেতে পারত না।
কিন্তু বাস্তবের ছবিটা অন্য। দেখা গেল ক্ষুদ্রসেচপ্রকল্পগুলোও সেদিকে না এগিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার করবার দিকেই ঝুঁকেছে। কতটা? ২০০০-০১ সময়ে ভারতবর্ষের তেত্রিশটা রাজ্য মিলে ১৯.৭৫ মিলিয়ন সেচপ্রকল্পের মধ্যে ১৮.৫ মিলিয়ন, বা সাতানব্বই শতাংশই দেখা গিয়েছিল ভূগর্ভস্থ জলনির্ভর। এর শতকরা সাতানব্বই ভাগ আবার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

এর ফলাফল যা ঘটেছে তা বেশ ভীতিপ্রদ। ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অবস্থার সঙ্গে ২০১৩র নভেম্বর মাসের অবস্থাটার তুলনা করলে এই ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে। এ ছবির লাল বা লালাভ এলাকাগুলোতে জলস্তর অনেকটাই কমে এসেছে এই দশ বছরে। বিপদটা ক্রমাগতই একটা রোগের মত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশের বুকে।
অংকের হিসেবে বিপদটার একটা আন্দাজ পেতে ২০১২র গ্রীষ্মের জলস্তরের সঙ্গে ২০১৩র গ্রীষ্মের জলস্তরের তুলনামূলক চেহারাটা দেখুনঃ
২০১২ সালের বর্ষায় দেশে বৃষ্টি মোটামুটি স্বাভাবিক পরিমাণে হয়েছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, দেখা যাচ্ছে তৎসত্ত্বেও দেশের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, পুব, কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণাঞ্চলে, প্রধানত দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, কর্নাটক, কেরালা, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু আর গুজরাটের বিভিন্ন জায়গায় এই এক বছর সময়ের মধ্যেই জলস্তর ভালোরকমভাবে নেমে গিয়েছে। যতগুলো নমুনা সমীক্ষা করানো হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৫৬ ভাগ ক্ষেত্রেই ফলাফল জলস্তর নেমে যাবার দিকে ইঙ্গিত করছে।
২০০৩-১২ এই দশকের গড় জলস্তরের সঙ্গে ২০১৩র জলস্তরের তুলনায় দেখা যাচ্ছে, দেশের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব এবং পূর্বোত্তর অংশে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে চলেছে। সে রেসে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে রাজধানী দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চল এবং রাজস্থান। জলস্তর বৃদ্ধি হয়েছে মধ্যভারত, গুজরাট আর তামিলনাড়ুর কিছু বিচ্ছিন্ন টুকরোতে কেবল।
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই একই সময়ের তুলনায় দেখা যাচ্ছে মোট নমুনা সমীক্ষার শতকরা ৬৫ ভাগ ক্ষেত্রেই জলস্তর নিম্নমুখী এবং এর বেশিরভাগটাই রয়েছে অধিকতর জনবসতিযুক্ত দক্ষিণবঙ্গে। অন্যান্য ক্ষেত্রে না পারলেও ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে নিম্নগামী করবার ক্ষেত্রে জাতীয় গড়কে সাফল্যের সঙ্গেই পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।
ভূগর্ভে যে জল থাকে তা কিন্তু সেখানেই স্থির হয়ে থাকে না। তাতে ক্রমাগত বাইরে থেকে জল ঢোকে এবং সে জল আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক পথে বাইরে বের হয়ে এসে নদীনালা, জলাভূমিতে জলের জোগান দেয়, যার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় এই ঢোকা আর বের হওয়াটা একটা সাম্যের অবস্থায় থেকে যায়।
কৃত্রিমভাবে সেখান থেকে জল বের করে নেবার অর্থ হল প্রাকৃতিক নিষ্কাশনের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা। এর ফল হয় এই যে সেই জলসম্পদ যে প্রাকৃতিক ধারাদের জল সরবরাহ করছিল সেগুলোতে টান পড়ে। শুকিয়ে যায় কুয়ো, পুকুর, হ্রদ, ছোটো ছোটো নদী, জলাভূমি। ফলে ধীরে ধীরে খারাপের দিকে বদলে যায় একটা এলাকার সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রটাই। গত শতকের শুরু থেকেই এ নিয়ে উন্নত দেশের বিজ্ঞানিরা কাজ করে চলেছেন। সমাধানের পথ হিসেবে বলা হচ্ছে, যেকোন ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেই তার স্থানীয় প্রভাবকে বোঝা, এলাকানির্ভর জল বাজেট তৈরি করা, কৃত্রিমভাবে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বাড়ানো এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে তৈরি করতে হবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের রূপরেখা। এর ওপরেই নির্ভর করবে ঠিক কতটা ভূগর্ভস্থ জল টেনে নিলে তা পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতির ওপরে দীর্ঘস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিপদ ডেকে আনবে না, তার পরিমাণ।
এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে, ভূগর্ভে প্রাকৃতিকভাবে বছরে যতটা জল ঢোকে তার শতকরা ৪২ ভাগ উত্তোলন করা হয়ে চলেছে। সারা ভারতবর্ষের মত এখানেও তার প্রায় সবটাই ব্যক্তিগত মালিকানানির্ভর। স্বাভাবিকভাবেই এই নিষ্কাশন ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডারের সুস্থিত অবস্থাকে ঘা দিয়ে ক্রমাগত কমিয়ে আনছে তার সঞ্চয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ না করবার ফলে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি তারই ইঙ্গিত এ রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের এই দ্রুত নিম্নগমন।
সমস্যাটা শুধু ভারত বা পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নেই। পৃথিবীর তিনটে প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদক দেশ, ভারত, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই দ্রুত নেমে চলেছে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ। ২০১২ সালে আর্থ পলিসি ইনস্টিট্যুট, বিপজ্জনকভাবে নেমে যেতে থাকা জলস্তরের যে এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করেছে তাতে রয়েছে এই তিনটে সহ আঠারোটা দেশ, যেখানে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি লোকের বাস।

মূল কারণটা সর্বত্রই প্রধানত এক — অর্থাৎ চাষজমিতে জল সরবরাহ। কিন্তু তার ঘটবার পদ্ধতি দেশে দেশে ভিন্ন হবে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ওপরের ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে দেখলে একটা ছবি চোখে পড়ছে—
এদেশে যখন সবুজ বিপ্লব এসেছিল তখন কিন্তু ভূতলস্থ জলের ব্যবহার ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারের চেয়ে বেশি ছিল। তার পেছনে একটা কারণ ছিল বিভিন্ন বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলোর সাফল্য। সত্তর আর আশির দশকে লার্জ ড্যাম তৈরি হয়েছিল ২৫৪৯টি। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলোর যে আর্থসামাজিক ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো ছিল, সেগুলোর দিকে যখন মানুষের চোখ ঘুরল এবং ফলত বড়ো বাঁধের বিরুদ্ধে তীব্র, জনমুখী আন্দোলন তৈরি হল, তখন ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের কার্যকরী পথ খুঁজে পরবর্তী প্রকল্পগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে সেগুলোকে প্রয়োগ করে জনমতকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টাটা ভালো করে করলে হয়ত তাতে সবদিকই রক্ষা পাবার একটা সুযোগ থাকত।
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আন্দোলন বাঁধ নির্মাণে স্থানীয় মানুষের ক্ষতির দিকটাকে যথার্থভাবেই ভেবেছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রকল্পটা নেয়া সেটা কীভাবে বিকল্প পদ্ধতিতে নিরাপদ পথে ঘটতে পারে তার দিশা দেখানো তার কর্তব্য ছিল না। তা সে করেওনি। সে দায়িত্বটা ছিল দেশের কর্তাদের। কোন মানুষের ক্ষতি না করে কীভাবে এ প্রকল্পগুলোতে পরিবর্তন এনে রূপায়ন করা যায়, বা নিরাপদ কী বিকল্প খোঁজা যায়, সরকারী স্তরে সে নিয়ে সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির জন্ম দিতে পারত এই আন্দোলন। কিন্তু বাস্তবে তেমন কার্যকরীভাবে তা ঘটেনি। পরিবর্তে বেছে নেয়া হয় সহজ একটা গোঁজামিলের রাস্তা। সরাসরি সরিয়ে দেয়া হল জনরোষের কারণটাকে। দ্রুত কমে এল বৃহৎ বাঁধ প্রকল্পের ও সে-জাতীয় পরিকল্পনার সংখ্যা। জনতা খুশ। ভোটব্যাংক বাঁচিয়ে সরকারও খুশ।
কিন্তু এর বিকল্প হিসেবে, কৃষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদাকে মেটাবার জন্য কোন কার্যকরী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। আমাদের দেশজোড়া ছড়িয়ে থাকা নদীর যে বিরাট নেটওয়ার্ক, ১৯৮৮ সালে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন তার মধ্যে সেচের উৎস হিসেবে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল ১৮৮০ ঘন কিলোমিটার জলকে। ১৯৯৩ সালে ফের বিস্তারিত গবেষণার পর সে হিসেবটা দাঁড়ায় ১৮৬৯ ঘন কিলোমিটারে।
প্রয়োজনে বড়ো নদী পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে অজস্র ছোটো ছোটো নদীভিত্তিক ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প গড়ে দেশ জুড়ে এই বিপুল জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা কেন্দ্রীয় কর্মপদ্ধতি তৈরি করে তাকে কাজে লাগানো হয়ত অসম্ভব ছিল না।
বাস্তবে তা ঘটেনি। বড়ো বাঁধভিত্তিক সেচপ্রকল্প গড়বার রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর “সংবিধানে জল একটি স্টেট সাবজেক্ট” এই অকাট্য যুক্তিতে নিজের নিজের জলের চাহিদা মেটাবার দায় ছেড়ে দেয়া হল রাজ্য সরকারদের হাতে। রাজ্য সরকারেরা সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র সেচভিত্তিক ছোটো ছোটো নদীপ্রকল্পকে গুরুত্ব দেবার বদলে বেছে নিল মাটিতে নল পুঁতে সহজে জল বের করে নেবার অদূরদর্শী কিন্তু কার্যকর রাস্তাটাকেই। তাতে সরকারের দায় কম। সাধারণ মানুষকে যা খুশি তাই করবার স্বাধীনতাটা দিয়ে দিলেই হল।
সেক্ষেত্রেও, একেকটা এলাকার নিবিড় অধ্যয়ন করে সে এলাকার ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের নিরাপদ সীমাকে বেঁধে দিয়ে ব্যবহারের সুষ্ঠু গাইডলাইন তৈরি করে দিলেও হয়ত এতটা অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ঘটত না। কিন্তু সেটাও ঘটেনি বিভিন্ন রাজ্য সরকারের এলাকায়। রাজ্যগুলোতে অজস্র রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও কোন ছাপ ফেলতে পারেনি এতে।
হাতে দায়িত্ব পেয়ে সাধারণ কৃষক তখন জল লাগলেই নল পুঁতি নীতিতে মহানন্দে সেচ বাড়িয়ে গেল। গভীর নলকূপ থেকে উঠে আসা জলের অমৃতধারা হয়ে উঠল দেশের উন্নয়নের লোগো। সমাজসচেতন আন্দোলনকারীরা তখন বড়ো বাঁধের অভিশাপ থেকে জনতাকে রক্ষা করে ঘুমোতে গেছেন। ফলে, একটা একটা করে অপরিকল্পিত নলকূপ কীভাবে গোটা দেশকে একটা পয়েন্ট অব নো রিটার্নের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে সার্বিকভাবে অনুধাবন করবার ও সেই ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেবার জন্য না রইল কেউ সরকার পক্ষে, না রইল সমাজ সচেতন আন্দোলনকারীদের পক্ষে।
অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের একটা ফল জলদূষণ। আর্সেনিক দূষণের যে ছবিটা আমরা দেখছি তাতে ২০০৮ সালের হিসেব অনুযায়ী আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড়, মনিপুর, বিহার, উত্তর প্রদেশ এই সাতটা রাজ্যে আর্সেনিক দূষণ গুরুতর রূপ ধরেছিল। ২০১৪ সালে এসে তাতে যোগ দিয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও কর্নাটক। ২০১৫ সালের হিসেব অনুযায়ী এই রাজ্যগুলোর ৮৬টি জেলা এই মুহূর্তে আর্সেনিক প্রদূষণের শিকার। এর সমাধানে মাঝেমধ্যেই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে আর্সেনিকদূষিত নলকূপের মুখে লাগাবার জন্য শোধক যন্ত্রের খবর। কিন্তু সেই লক্ষণভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রোগের মূল কারণটাকে ধরে না এবং ফলত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের মডেল হতে পারে না।
কিন্তু এই ভয়াবহ সমস্যাটাও ভূগর্ভস্থ জল কমে আসবার আসল প্রতিক্রিয়ার কাছে তুচ্ছ। ওয়াশিংটনের আর্থ পলিসি ইনসটিটিউটের লেস্টার ব্রাউন সাহেবের ২০১২ সালের গবেষণাপত্রটা দেখাচ্ছে ওপরে বলা আঠারোটা দেশে চূড়ান্তভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন এবং তা প্রাকৃতিক পথে পূরণ না হবার ফলে প্রতি বছরেই ফসল উৎপাদন নিম্নগামী হচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে ভূগর্ভস্থ জলের বিপুল উত্তোলনের কারণে। ওদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে তীব্রবেগে। ২১ মিলিয়ন নলকূপের সমবেত, ক্রমর্ধমান চাপ দ্রুত অবনমনের পথে নিয়ে চলেছে জলস্তরকে।
জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো কমবে না। মাটির তলার জলকে তুলে তাদের মুখের অন্ন জোগাবার এই মায়োপিক নীতি এইভাবে চালিয়ে গেলে কদিন বাদে দেশের লোক খাবে কী? অসুখ হলে তার ওষুধ হয়। কিন্তু খিদের ওষুধ যে খাবার, তাকে বানাবার জন্য কৃষি এভাবে ভূগর্ভস্থ জলনির্ভর থেকে যায় যদি, তাহলে সে সঞ্চয় ফুরোলে সে রাতারাতি কোন পথে যাবে? ভারতের আকাশে সে অশনিসংকেত দেখা দিয়েছে এখনই। কয়েক দশক বাদে কী হবে আমাদের? জাদুমন্ত্রের ভেলকি দেখিয়ে এক মুহূর্তে টুপি থেকে খরগোশ বের করা যায়, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে জলের ব্যবহারকে আমূল বদলাতে গেলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আর দৃঢ়হাতে তার সঠিক প্রয়োগ লাগে। সে ক্ষমতার প্রয়োগ এখনই শুরু না করলে এরপর দেরি হয়ে যাবে।
বড়োলোকের অলস ছেলেটা যখন ঘটির জল গড়িয়ে খায় তখন প্রথম প্রথম তার জুলুশ থাকে অনেক। পিঠ চাপড়ানো মোসাহেবেরও অভাব হয় না। কিন্তু সঞ্চিত ধন ফুরিয়ে এলে যখন তার পথে বসবার দশা হয় তখন তার আর কিছু করবার থাকে না। সময় এখনো আছে। ওপরের হিসেবগুলো একটাই দিকে ইঙ্গিত করছে — ক্ষতি এখনও সামলানো যেতে পারে। উপযুক্ত পরিকল্পনা এখনও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে অবস্থাটাকে। কিন্তু প্রশ্ন সেই একটাই — লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে?
(পরবাস-৬৪, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)