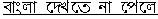শীতকালে নতুন ফসল ওঠার পর অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু হত নানারকম পিঠেপুলির ব্রত অনুষ্ঠান, চলত গোটা মাঘ মাস। এই ব্রতের মধ্যে ছিল নবান্ন, নতুন চালের পিঠেপুলির ব্রত, রান্না ভোগের লক্ষ্মীব্রত, উপায়চণ্ডী ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে বাড়িতে হত নাটাই পাটাই ব্রত। আবার মাঘ মাসে আরেকটি পূণ্য স্নানযাত্রা হত। সেটাতে রান্নাভোগের কোন অনুষ্ঠান ছিল না। তবে আমাদের খুব মজা হত। মকর সংক্রান্তির মত একেও বলত ‘মকরি সপ্তমী’। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে অরুণোদয়ের প্রাক্কালেই হত এই স্নান। এই স্নানের আনুষঙ্গিক কিছু নিয়ম ছিল। সাতখানা আকন্দ পাতা সাতটি বড়ই (কুল) এবং সাতটি কুলের পাতা মাথায় নিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে স্নান করতে হত।
মকর সপ্তমীর পরে মাঘের পূর্ণিমাতে হত ‘মাঘীপূর্ণিমা’ব্রত। মাঘীপূর্ণিমার মূখ্য পূজিত দেবতা হলেন চন্দ্র। সন্তানবতী মহিলারা সারাদিন উপোসের পর চন্দ্রোদয়ের প্রাক্কালে নিষ্ঠামত নিরামিষ ভাত, তরকারী, পিঠে, পায়েস সহকারে কলার আগপাতায় করে, পুবাকাশে উদিত চাঁদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র আউড়ে চন্দ্রার্ঘ্য প্রদান করে, তবেই জলগ্রহণ করতেন। এই ব্রত পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও জেলায়, কোনও গ্রামের কোনও কোনও পরিবারে, বাঘের উৎপাতে বন্ধ হয়েছিল। শ্রুতিকথা এই যে কোন এক গ্রামের এক পরিবারের গিন্নিকে আলোআঁধারী সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় চন্দ্রার্ঘ্য প্রদানকালে অতর্কিতে বাঘের থাবায় প্রাণ দিতে হয়েছিল। এরকম কিছু ঘটনার খবরে মাঘীপূর্ণিমা ব্রতের নিয়ম অনেক পরিবার থেকে উঠে গিয়েছিল।
মনুষ্যজাতির প্রথম জ্ঞান উন্মেষের কালে সুন্দর এ পৃথিবীর রূপে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মানুষ জানতে চাইল অজানাকে। জয় করতে চাইল অজেয়কে। অধরাকে ধরার বাসনায় সৃষ্টি হল দেবতাজ্ঞানে অসীমের নানারকম স্তুতি বন্দনা। চন্দ্র সূর্য বসলেন দেবতার আসনে। আকাশ, বাতাস, জল, বৃক্ষ, কতিপয় জীবকুলও ভূষিত হল দেবমহিমায়, পূজিত হল দেবতাজ্ঞানে। যেমন--তুলসী, শেওড়া, বট, ইত্যাদি উদ্ভিদের সঙ্গে জীবকুলের মধ্যে সাপ হল প্রধান এক দেবতা, মনসা হলেন সর্পদেবী নামে পূজিতা। দেশে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে ধূমধাম করে হত মনসা পূজা।
ছোটবেলায় আমরা কোনদিন বিজলিবাতি দেখিনি। অন্ধকার রাতে পূর্ণিমায় চাঁদ উন্মুক্ত খোলা আকাশে দেখা দিত স্পষ্ট হয়ে। আধুনিককালে যত্রতত্র বিজলি বাতির দৌলতে বাড়ির উঠোন থেকেও চাঁদের সে স্নিগ্ধ আলো আর সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায় না। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান আর গবেষকদের চন্দ্রবিজয়ের পর পত্রপত্রিকায় চন্দ্রবিষয়ক নানা খবর জেনে, বই-পুস্তক পড়ে ও টেলিভিশানের বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ দেখেশুনে চাঁদকে আর দেবতা বলে অন্ধবিশ্বাস করে না মানুষ। আজকের দিনে যে কোনও পরিবারের ছোট্ট ছেলেটিও আর চাঁদের মা বুড়ির গল্প বিশ্বাস করে না। আমরা ছেলেবেলায় সরল বিশ্বাসে চাঁদের মা বুড়িকে দেখতাম। চাঁদের মধ্যে প্রকাণ্ড বটের তলায় পা ছড়িয়ে বসে চাঁদের মা বুড়ির চরকায় সুতা কাটার রূপকথাটি বর্তমান যুগে ছোটদের কাছে নেহাতই ছেলেভুলানো গল্পকথা। যাই হোক এই চন্দ্রবিজয়ের খবর আসবার পর কিছু বুদ্ধিমতী পূর্ববঙ্গীয় মহিলাকে দেখেছি চন্দ্রার্ঘ্য প্রদানে বিরত থাকতে।
মনে পড়ে একবার শ্বশুরবাড়ি থেকে আমার এক দিদি এসেছে আমাদের বাড়ি। সেটা ছিল মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত। সেদিন ছিল হাটবার, রাতে হাট থেকে বড় মাছ এসেছে। রান্নাবান্না হয়ে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সব ঘুমিয়েছে। আমরা ছোটরা সবাই এক থালায় মাখা ভাত সন্ধের আগেই খেয়ে শুয়ে পড়তাম।
শীতের লম্বা রাত। শেষরাতেই আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। বিছানায় শুয়ে শুনছি ঘরের পিছনে শেয়ালের কাঁকড়া খাওয়ার কট্কট্ শব্দ। নদীর জলধারার পাশে শুকনো জায়গায় অসংখ্য কাঁকড়ার গর্ত থাকত। সেই গর্তে চালাক শিয়াল লেজ ঢুকিয়ে বসে থাকত, কাঁকড়ারা বুঝতে না পেরে দাঁড়া দিয়ে শেয়ালের রোমশ লেজটি ধরত অমনি শিয়াল তার কাঁকড়াশুদ্ধ লেজকে টেনে তুলে কাঁকড়ার গর্তের থেকে দূরে চলে আসত। এই কাঁকড়া খাওয়ার শব্দই ঘুম ভেঙে শুনছি। আমাদের ঘরের পেছনেই ছিল একটি প্রকাণ্ড নোনা গাছ। নোনা পেকেছে। দুটো ভোঁদড় এই নোনা গাছের পাকা নোনা খেতে গিয়ে জোর মারামারি করছে। টিনের চালে, গাছ থেকে ঝরে পড়া শিশিরের টপটপ আওয়াজ শুনছি। বাঁশের বেড়ার ছোট ছোট ফাঁক দিয়ে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া চাঁদের অসংখ্য বিন্দু বিন্দু আলোর ফুট্কি এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। উদ্ভাসিত চন্দ্রকিরণে আত্মহারা ‘বউ কথা কও’ পাখি একঘেয়ে ডেকে চলেছে। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রিশেষে আমি একা জেগে আছি।
খানিক বাদে আসন্ন ভোর জেনে চুপিচুপি আমার বিবাহিত দিদিকে ডেকে তুললাম। নিয়ে গেলাম বাড়ির পিছনের সেই পুকুরপাড়ের কুলতলায়। এই কুলগাছের লাগোয়া ছিল একটি কাঠঘর, বারো মাসের রান্নার শুকনো চেলা কাঠ আর পাটকাঠি এই ঘরে জমা করা থাকত। বাড়ির পিছনে এই পুকুরটি ছিল বিশাল আকৃতির, পুকুরের দুই পাশ দিয়ে দুটো সরু রাস্তা গিয়েছে নদীর ঘাটে যাওয়ার। পুকুরের পশ্চিম দিকে ছিল বিরাট জঙ্গল, ছোট বড় বিভিন্ন রকমের গাছ আর বাঁশগাছ ছিল। পাতাবাহারে ঘেরা কুলগাছের তলায় ঢুকে, রাতের শিশিরের আঘাতে এবং ভোঁদড় বাদুড়ের ঝাপটায় ঝরে পড়া কুল শিশিরে ভেজা শুকনো বালিতে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকত। শুকনো পাতা সরিয়ে কুলগুলো কুড়িয়ে কোঁচড় ভর্তি করে বেরিয়ে এসে দেখি আমার দিদি নিশান্তের বিদায়ী চাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুকুরের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। শ্বশুরবাড়ির বদ্ধ পরিবেশ থেকে ক’দিনের মুক্তি দিদিকে এনে দিয়েছে ক্ষণিকের আনন্দ। চারিদিকের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ তাঁকে করে দিয়েছে স্থান-কাল আর সময়হারা।
নদীর লাগোয়া চতুর্দিক ঘনকালো গাছপালায় বেষ্টিত বিরাট পুকুরের উপর, রাত্রিশেষের হলদেটে চন্দ্রকিরণে চারিদিকে এক অদ্ভুত মায়াজালের সৃষ্টি করেছিল। পুকুরপাড়, আর জঙ্গলের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে এবার মনে ভয় এল। নিস্তব্ধ রাত, মাঘের শীত আর ভূতের ভয় সব মিলিয়ে এক কাঁপুনি শুরু হল। খপ করে দিদির আঁচল ধরে টানলাম। দিদি চেতনা ফিরে পেল। আমার হাত ধরে বাড়ির দিকে ফিরে চলল। পিছন থেকে এক নজর দেখলাম, নির্মল আকাশের ভাসমান চাঁদকে। সে রাতের কথা বা সে দৃশ্য জীবনেও ভুলিনি। জীবনের এ অবসর সময়ে যেন এই সব দৃশ্য বা স্মৃতি একে একে বাস্তবে ফিরে আসে। চিন্তার স্রোত ক্ষণিকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় পিছনে ফেলে আসা সেই স্মৃতির পটভূমিতে।
ফাল্গুন মাসে হত শিবরাত্রি, ঘরে ঘরে সবাই উপোস (অসমর্থ শিশু, বৃদ্ধ বাদে) করত, ছোটরাও উপোস করত। সারা গাঁয়ে এক উৎসব শুরু হত। আমার মনে পড়ে, একবার আমাদের বাড়িতে সবাই উপোস, আমার একটি ছোট্ট বছরছয়েকের ভাইপো, সেও আমাদের সঙ্গে উপোসে সামিল হয়েছে। সারা সকাল আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, বেলা দুটো আড়াইটায় দলবল নিয়ে স্নান করতে গেছি দীঘিতে, সেও গেছে আমাদের সাথে। স্নান সেরে যে যার বাড়ি ফিরল। ফাল্গুন মাস--দিনের তাপমাত্রা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হয়েছে। উপোস করে সকলেই কিছুটা ক্লান্ত। রাতে শিবপূজার পর জলযোগের জন্য, সাগরগঞ্জ আলু (রাঙাআলু) সেদ্ধ, খোসা ছাড়িয়ে একটি গামলায় ঢাকা দিয়ে রেখেছে মা।
ঘরে কেউ নেই। দরজাটি বন্ধ, এই নীরবতার সুযোগে আর খিদের ঠেলায়, উপোসের কথা ভুলে গিয়ে আমার ছোট্ট ভাইপোটি, গামলা থেকে একখানা সেদ্ধ করা রাঙাআলু তুলে নিয়ে এক কামড় দিয়েই মনে পড়েছে উপোসের কথা, সঙ্গে সঙ্গে উপর পাটির দুটো দাঁতের দাগ সহ আস্ত সেদ্ধ রাঙাআলুটি মাটিতে নামিয়ে রেখে ভিজে গামছা পরা অবস্থাতেই উধাও।
আমি ছিলাম আমার এই ভাইপোর থেকে ছ’বছরের বড়। আমার উদ্দেশ্য ছিল মাঝপথে ওর উপোস ভঙ্গ হল কি না সেই খুঁত খুঁজে বেড়ানো। উপোসে গলা শুকিয়ে গেলেও, ঢোক না গিলে অনবরত আমার ভয়ে থুতু ফেলে যেত। যাই হোক, নীরব নিস্তব্ধ বাড়িতে ঘরের দরজা ঈষৎ ফাঁক দেখে ঘরে ঢুকে মাটিতে দাঁতের দাগ শুদ্ধ একটি সেদ্ধ আলু দেখে চট্জলদি বুঝে নিলাম এটা কার কাজ। বিপ্লবী,দেশত্যাগী আমার গোড়াদা অর্থাৎ বড়দার ছেলে এই ভাইপোটি ছিল আমাদের সংসারের চোখের মণি। ঘর থেকে বেরিয়ে ওকে কোথাও দেখতে না পেয়ে নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম। বাড়ির আশপাশ, এঘর ওঘর, এবাড়ি, সেবাড়ি খুঁজে দেখলাম। কোথাও না পেয়ে ছুটে গেলাম ঘাটের দিকে। দিদি আর আমি ছুটছি ঘাটের দিকে। আমাদের হাঁকাহাঁকি শুনে সঙ্গী হল অনেকেই। ঘাটের দিকে ছোটার কারণ সবারই জানা ছিল, কারণ আমার এই ভাইপোটিকে খুঁজতে মাঝেমধ্যেই পুকুরে জালও ফেলতে হত।

ভাগ্যক্রমে আমার এই উপোস ভঙ্গকারী ভাইপোটিকে পাওয়া গেল ঐ কড়ই গাছের তলায়, ছায়ায় বিশ্রামরত কিছু রাখাল ছেলের মাঝখানে বসে আছে। তখন নায়েবমশায় গ্রামে ছিলেন না, তাই হাতিও ছিল না সেখানে। আমাদের আসার আঁচ পেয়েই ভাইপো পলায়নোদ্যত হল। চোখে চোখ পড়ামাত্রই ইশারায় ডাকলাম। কাছে এলে বললাম ‘বাড়ি চল, কাউকে বলব না।’ বাকি বেলাটুকু আমার খুব অনুগত সুবোধ বালক হয়ে রইল। সন্ধে হওয়ার পর সাবুমাখা, আর রাঙাআলু সেদ্ধ খেয়ে সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল। এই ঘটনার কথা মাকে ছাড়া কাউকে বলিনি।
ফাগুন মাসের হোলির বিবরণ মনের ভুলে বাদ পড়ে গিয়েছিল বলে সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লেখার প্রয়াস করলাম।
ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমা— এই দোল পূর্ণিমায় সম্প্রদায় বিশেষে (যেমন--শাক্ত, বৈষ্ণব) উৎসবের কিছুটা হেরফের ঘটলেও ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ তারতম্য হত না। প্রত্যেক পরিবারে পারিবারিক নিয়ম অনুসারে পূজানুষ্ঠান, ভোগ, নৈবেদ্য নিবেদন সাধ্যানুসারে পালিত হত। গৃহদেবতাকে ফাগ বা আবীর দেওয়া হত। তবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাণ্ডব নৃত্যে যত্রতত্র হোলি খেলা, আমরা ছোটবেলায় কোনদিন দেখিনি। আমরা হোলির রং--আবীর বা ফাগ দিয়েছি গুরুজনদের পায়ে। তাছাড়া বয়সে বড় নতুন বৌদি হলেও তাঁর সম্মতি নিয়ে তাঁর গায়ে পায়ে আবীর মাখিয়েছি।
এ-বয়সে কত কথাই মনে পড়ে। আজকের সমাজের ইট, কাঠ, লোহার জঙ্গলের পরিবেশে শিশুদের যে আনন্দময় শৈশবটা হারিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমাদের ছিল না। আমাদের একটা নির্মল আনন্দময় শৈশব ছিল। একবারের কথা মনে পড়ে। শিবরাত্রির উপোসে সারাদিনের ক্ষিদে তেষ্টায় ক্লান্ত। সন্ধে হতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ক্ষিদে পেটে থাকলে কি ঘুম হয়? তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হয়ে স্বপ্ন দেখছি, মস্ত বড় একখানা কাঁঠাল ভেঙে তার বড় বড় খাজা কোয়া, মনের আনন্দে খাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেছি। জেগে গিয়েও যেন নাকে মুখে কাঁঠালের গন্ধ টের পাচ্ছি। এখন এসব হাসির গল্প, মনে পড়লে একা একাই হাসি।
বছরের শেষ মাস চৈত্রমাসটি এগিয়ে আসে গুটি গুটি পায়ে। এই চৈত্রমাসে হত, পূর্বকথিত সর্বজনীন বা বারোয়ারি পূজা। সারা গ্রামের মানুষের মঙ্গলকামনায় এই পূজা করা হত। বসন্ত কলেরা ইত্যাদি ছোঁয়াচে মারণ রোগব্যাধির দেবতা বলে পরিচিত ছিলেন বসন্ত রায়। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এই পূজো করা হত। প্রত্যেক হিন্দুবাড়ি থেকে চাঁদা তুলে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় এই পূজো হত। পূজার তিন দিন আগে থেকে নানারকম নিয়মকানুন, অনুষ্ঠানের পর পূজা হত তবে তা হত গ্রামের জনবহুল এলাকা ছাড়িয়ে নদীর তীরে ভাটি জায়গায়। পড়ন্ত বেলায় হতো এই পূজা। গ্রামের যে কোন অমঙ্গলকে নদীর ভাঁটার স্রোতে ভাসিয়ে দূর করে দেওয়ার জন্য, গ্রামের আপদ বিপদের শেষ করার জন্যই হত শেষবেলায় পূজো।
মনে পড়ে একবার চৈত্র মাসে বসন্ত ঠাকুরের (চলতি কথা বসন্দ্রায়) পূজোয় গ্রামের সব মানুষ পূজার সরঞ্জাম নিয়ে গ্রামের শেষপ্রান্তে নদীর ভাটি চরায় গেলেন। গিন্নিবান্নি বয়স্ক মহিলারা পূজোর জোগাড় করছেন। এই পূজার বলি দেওয়া হত পাঁঠা, আখ, চালকুমড়ো এবং পায়রা। যদি কারও মানত থাকত তবে একাধিক পাঁঠাও বলি হত। যে জায়গাটি পুজোর জন্য নির্ধারিত হয়েছিল সে জায়গাটি এতই ফাঁকা ছিল যে নদীর পশ্চিম দিকে তাকালে ফসল জমি ছাড়া কোন গাছপালা কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। বর্ষাকালে এই সমস্ত বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা জলে পরিপূর্ণ হয়ে সমুদ্রের রূপ ধারণ করত। ভরা বর্ষায় অবশ্য একবার জোৎস্না রাতে নৌকা চেপে নদীর এই ফাঁকা জায়গার অপরূপ শোভা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে কথায় পরে আসছি।
সেবার বসন্ত রায়ের পুজোয় একটা ঘটনা ঘটেছিল। পূজা যখন শেষ প্রায়। পাঁঠা বলি হয়েছে। অন্যান্য জিনিস বলি এখনও বাকি রয়ে গেছে। এমন সময় বায়ুকোণ থেকে কালো মেঘ উঠে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে এল এক কালবৈশাখী। চর্তুদিক চষা ক্ষেতের ধুলোয় অন্ধকার। আমরা ছোট বড় যত মেয়েরা সেজেগুজে পুজোতলায় গিয়েছিলাম আনন্দ করতে, ঝড়ের বীভৎস শব্দে আর এলোমেলো ঘূর্ণি হাওয়ার দাপটে, ধূলিধূসরিত হয়ে দিলাম সম্মিলিত দৌড়। দৌড়ে এসে উঠলাম গ্রামে। আমাদের সম্মিলিত দৌড়ের সময় এক মজা হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে পুরোহিতমশাইও হাতে শালগ্রাম শিলা নিয়ে দৌড়চ্ছিলেন। বয়স্কা মহিলা যাঁরা গিয়েছিলেন পূজার যোগাড় করতে, তাঁরাও পূজার বাসনপত্র, শঙ্খ, ঘন্টা যে যা পারলেন, তাই হাতে নিয়ে দিলেন দৌড়। এসে উঠলেন কাছের লোকালয়ে। পূজা মাথায় উঠল। পরদিন ভোরে পুজোতলায় গিয়ে বাঁশঝাড়ের মাথায় পায়রার বকম বকম আওয়াজ শোনা গেল। কাছে গিয়ে দেখা গেল যে কালবৈশাখীর দাপটে খাঁচা শুদ্ধ পায়রা উড়ে গিয়ে বাঁশবনের মাথায় আটকে রয়েছে। গৃহপালিত পায়রা লোকালয়ে থেকে অভ্যস্ত। জনমানবশূন্য এলাকায় বাঁশগাছের শীর্ষে খাঁচাশুদ্ধ বসে ভয়ে ত্রাসে তারস্বরে বক-বকম শুরু করেছিল সমস্বরে।
সকলের চেষ্টায় বাঁশগাছের মাথা থেকে খাঁচাগুলি নামিয়ে আনা হল। পায়রাদের পেয়ে আমাদের মনটা একটু খুশিই হয়েছিল। খাঁচা থেকে বের করে গায়েমাথায় আদর করে একটু হাত বুলোলাম। কিন্তু ওদের এদিক ওদিক ভয়বিহ্বল ছট্ফটে চাউনি দেখে মনে হয়েছিল, অন্ধকার রাতে বনবাসের ভয় এদের মন থেকে তখনও মুছে যায়নি। যাই হোক, বাৎসল্য আবেগে ওদের মন থেকে ভয় দূর করতে মনোনিবেশ করলাম। ভাবলাম নিরীহ প্রাণীগুলো বেঁচে তো গেল। তবে এরকম বলির জন্য নির্দিষ্ট পায়রার খাঁচা অনেকেরই ছিল। যে যার খাঁচা চিনে নিয়ে গেল। কিছু খাঁচা খুঁজে পাওয়া গেল না, বোধ হয় প্রবল ঝড়ে ছিটকে দূরে কোথাও গিয়ে পড়েছিল।
চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বারুণী স্নানের কথা আগেও বলেছি। বারুণী স্নানে ছোটদের আনন্দের বিষয় ছিল পরবী পাওয়া। এক আনা, দু আনা, এক পয়সা, দু পয়সা, পাড়াশুদ্ধ প্রত্যেকেই ছোটদের পরবী দিত। পরবীর খুচরো পয়সায় টিনের ছোট কৌটো ভর্তি হয়ে যেত। সেই পয়সায় বিকালে বারুণী মেলা থেকে ছেলেমেয়েদের কেনাকাটা চলত।
তখনকার দিনে একটু বড় মেয়েদের হাটে, বাজারে যাওয়া নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। বেয়াড়াপনা করলে, হাটে যেতে চাইলে, সেই মেয়েকে ‘বাজারে মেয়ে’ বলে গাল দিত সকলে। তাদের মনের দুঃখের খোঁজ কেউ রাখত না। আমার সময় অবশ্য ছোট ছোট মেয়েদের বেলাতে এই নিন্দনীয় বজ্রআঁটুনিতে কিছুটা শিথিলতা এসেছিল। তাই অনেক বায়না ধরাতে, নানান ওজর আপত্তি করে তারপর বাবা আমাকে বারুণী মেলায় নিয়ে যেতে রাজি হলেন। গ্রাম থেকে দুই ক্রোশ দূরে বসত বারুণীর মেলা। আমরা দুই বোনের (দিদির আর আমার) পরবীর পয়সা সব তুলে দিলাম বাবার হাতে। বিকালে সাজগোজ করলাম। কারবুলী সাবান (লাল রঙের কারবলিক সাবান) দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে, মাথার ছোট ছোট চুলে তেল মেখে আঁচড়িয়ে, ঘরোয়া পদ্ধতিতে হাতে তৈরি (অর্থাৎ কাঁচির অভাবে বঁটি দিয়ে কাপড় কেটে হাতে সেলাই করা) শালুর জামা (ফ্রক) পরে চললাম বাবার পিছন পিছন হেঁটে বারুণী মেলায়। আমার দিদি আমার থেকে তিন বৎসরের বড়। অতএব বড় হয়ে গেছে। সে মেলায় যেতে পারবে না। করুণ মুখে চেয়ে আছে আমার দিকে। আর মনে মনে হয়ত আপশোস করছে বড় হয়ে গেছে বলে। সর্বক্ষণের সঙ্গী দিদিকে বিমর্ষ দেখে জুটি ভাঙার দুঃখে আমার মনে একটু সঙ্গীহারার শূন্যতা উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বললে তো আমারও যাওয়া হবে না। দিদিকে আশ্বস্ত করে কানে কানে বলে গেলাম, ‘দিদি তোর জন্য মাছ সাবান আর প্রজাপতি ক্লিপ আনব।’
বাবার সাথে চললাম মেলার উদ্দেশ্যে। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে উঠলাম সরকারি সড়কে। বাবা আগে আগে চলছেন। আমি চলছি পিছন পিছন। উঁচু সড়ক, ফাঁকা রাস্তার দুই ধারে সবুজ আর সবুজ ক্ষেত। দক্ষিণমুখো চলতে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে রাস্তার পাশ থেকে সরু সরু পথ নেমে গেছে ঢালু বিলজমিতে। দক্ষিণদিক থেকে ফুরফুরে বাতাস বইছে। হেঁটে চলেছি দক্ষিণমুখো। কখনও রাস্তার পাশে মাঠের মাঝে একটি মসজিদ। গ্রাম থেকে দেখতাম দিগন্ত জুড়ে মরীচিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এই মসজিদকে। গ্রাম থেকে একটি বিন্দু আকারে দেখাত। গ্রীষ্মের খরতাপে উত্তপ্ত প্রান্তরে মরীচিকার কাঁপুনি দেখতাম। সীমাবদ্ধ গ্রাম এলাকায় থেকে এত দিন যাকে (মসজিদ) ছোট আকারে, অস্পষ্ট দেখতাম আজ সেই দূরকে কাছে পেয়ে মনের পুলকে চলার গতি মন্থর হয়ে এল। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখে বাবা তাড়া দিলেন। আবার সচল হলাম। এইভাবে গিয়ে পৌঁছলাম বারুণী মেলার সামনে, নদীর এপারে। গরমের দিন, খরস্রোতা নদীতে এখন হাঁটুজল। জলের তলায় সাদা বালি দেখা যাচ্ছে, হেঁটেই পারাপার হওয়া যায়।
নদী পার হয়ে বাবা উঠে গেলেন ওপারে। আমার চলার গতি ফের মন্থর হয়ে গেল কারণ জলে নেমে এক পায় দাঁড়িয়ে আরেক পা স্রোতে ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা পিছন ফিরে তাকিয়ে, ফের তাড়া দিলেন। আবার তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি বাবার পেছন পেছন চললাম।
মেলায় ঢুকে চারদিকে চেয়ে মনটা পুলকে নেচে উঠল। যেদিকে তাকাই কত রংবেরং এর পালকি, পুতুল, হাতি, ঘোড়া, ফিতে, কিলিপ আয়না চিরুনী। কী নেই?
বেশিক্ষণ দেখার সৌভাগ্য হয়নি অবশ্য। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে মেলা বাজারে আসা। মেলায় একটি ঘরে আমাদের গ্রামের কয়েকটি ছোটমেয়েকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। বাবা কাকার সাথে ওরাও মেলায় এসেছিল। আমারও ঠাঁই হল সেখানে। বাবা ঢুকলেন মেলায় কেনাকাটার জন্য।
আমার দেওয়া পরবীর পয়সা দিয়ে কিনে আনলেন পালকি আর কয়েকটি পুতুল। পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের ছেলে পুতুল, বাচ্চা কোলে খোঁপাওয়ালা মা পুতুল। দ্বিতীয় দফায় কিনে আনলেন লাল এবং সবুজ রঙের মাছ সাবান। আমাদের দেশে একরকম সুগন্ধি খৈ পাওয়া যেত,তাকে বলত বিন্নি ধানের খৈ, তাও কিনে আনলেন। লাল এবং সাদা, চিনির আর গুড়ের তৈরি দুই রঙের হাতি ঘোড়া, পাখি, খেলনা (মঠ) এসব কিনে আনলেন বাবা। কাপড়ের পোঁটলায় বেঁধে নিলেন খেলনা মঠ আর বিন্নি ধানের খৈ। (দেশে তখন হাট বাজারের কোন থলে বা ব্যাগ ছিল না। ধামায় করে সওদা আসত।) আমার চঞ্চল মন কিছু শান্ত হল খেলনা আর বিন্নি খৈ পেয়ে। সঙ্গীসাথী মিলে যে যার পোঁটলা থেকে ইচ্ছামত মিষ্টি মঠ, আর বিন্নির খৈ খেয়ে জলতেষ্টা পেল। ঘরের পিছনের একটি পাতকুয়া থেকে আমরা জল তুললাম একটি বড় ঘটির গলায় দড়ি বেঁধে। কুয়োর জল ছিল পাতাপচা, নোংরা। আমাদের তখনও স্বাস্থ্যসচেতনতা তৈরি হয়নি। সকলে মিলে বিনাদ্বিধায় কুয়োর সেই পাতাপচা জলেই তেষ্টা নিবারণ করলাম। এবার বাবা ঢুকলেন ঘরে। কিনে এনেছেন রঙিন কাগজের ফরফরে (যাকে এখন বলে ঘুরুন্তি)। তবে আমাদের সময়কার ফরফরেগুলি অন্য আকৃতির ছিল। ভালো কাগজে তৈরি, মজবুত আর টেঁকসই ছিল। বেশ লম্বা একখানা কাঠির মাথায় বলের মত ঘূর্ণায়মান সহস্র পাপড়ির বিভিন্ন রং এর কাগজের ফরফরে থাকত। একটি মোটা বাঁশের মাথায় অনেকগুলি করে ফরফরে একত্র ঢুকিয়ে ফেরিওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছিল মেলায়। দেখতে যেন রং বেরং এর মস্ত একখানা ছাতা। দেখতে ভারি অদ্ভুত সুন্দর।

চৈত্রে শুক্লা অষ্টমীতে হত আরেকটি স্নানের উৎসব। সেটা ছিল অন্য ধরনের, সেটাকে বলত ‘অশোক অষ্টমী স্নান’, যেতে হত ব্রহ্মপুত্রে। রেলগাড়ি চড়েও দূরদুরান্ত থেকে মানুষ আসত ব্রহ্মপুত্রে অষ্টমী স্নান করে, পাপস্খালন করে পুণ্যার্জন করতে। ছেলেবেলায় শুনতাম পৌরাণিক গাথায় আছে, দেশের সমস্ত নদীগুলি নাকি তাদের মহিমা নিয়ে অশোক অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিলিত হয়। তাই দেশ দেশান্তরের পুণ্যলোভাতুর নরনারী আসত ব্রহ্মপুত্রে অষ্টমী স্নানে। স্নানযাত্রার সময় সঙ্গে নিয়ে যেত চার-পাঁচ দিনের মত খাবার। চিঁড়ে, গুড়, কলা, তেঁতুল এসব শুকনো খাবার আনত সঙ্গে বড় বড় পোঁটলায় ভরে। যাদের উক্ত স্নানে রাত্রিবাস করার মত কোন নির্দিষ্ট জায়গা থাকত না তারা দলবদ্ধ হয়ে রাত কাটাত ব্রহ্মপুত্রের উঁচু পাড়ে, বসে রাত জেগে নানারকম গান বাজনা, গল্পগাছা করে। আনন্দের সঙ্গেই রাত কাটাত। এই অশোকাষ্টমীর স্নান তিথি অনুসারে কোন কোনবার বৈশাখেও হত।
চৈত্র যায় আসে বৈশাখ আসে। চৈত্র সংক্রান্তিকে বলা হতো মহাবিষ্ণু বা মহাবিষুব সংক্রান্তি। এ ছিল ছাতু সংক্রান্তি, ভাইছাতু উৎসবের দিন। বাংলাদেশে ঘরে ঘরে এই ভাইছাতু উৎসব পালিত হত। ভাইয়ের হাতে বোনরা নানারকম মিষ্টি উপাচারের সঙ্গে তুলে দিত ছাতু। এটিও ভাইদের মঙ্গলকামনার উৎসব। সন্ধ্যাবেলায় ভাইয়ের হাতে ছাতু দেওয়া হত ওড়ানোর জন্য। রাস্তার তেমাথায় দাঁড়িয়ে ভাই সেই ছাতু ওড়াত পায়ের তলা দিয়ে। মন্ত্র বলা হত--‘ছাতু যায় উইড়্যা (উড়ে), দুশমন বাদী মরে পায়ের তলায় পইড়্যা (পড়ে)। ভাইয়ের শত্রুদের এভাবে ছাতুর মত উড়িয়ে দেওয়া হত, ভাইকে নিরাপদ রাখার জন্য। তাছাড়া নানা রকম রান্না ভোগ, নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করা হতো মহাবিষ্ণুকে।
এদিন শিবের গাজন হত কোন বটতলায় বা শিবতলায়। গভীর রাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচ দেখাতে আসত ‘কাচ’ নাচের দল। হরপার্বতী, নন্দী-ভৃঙ্গী, দুর্গা, অসুর, সিংহ সেজে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা দেখাত। ঘুম চোখে ছোটরা অদ্ভুত ওইসব মূর্তির নাচ দেখে আর বাজনা শুনে ভয়ে চিৎকার করে পালাত।