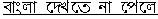ঠিক সেই মুহূর্তে অনিবার্যভাবে তিনিই যেন গেয়ে উঠলেন - "তুমি রবে নীরবে"। সেই ক্ষয়িষ্ণু নারীর চোখের দিকে তাকিয়ে।
মন্দিরার জন্ম হয়েছিলো এক সচ্ছল পরিবারে। তার বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারি। আর মা ছিলেন পাড়ার স্কুলেরই গানের দিদিমনি। মন্দিরাই তাদের একমাত্র সন্তান। লেখাপড়ায় বিরাট কিছু মেধাবী না হলেও মা সরস্বতীর কৃপায় মন্দিরার গলায় সুর ছিলো। আর বাড়িতে ছিলো গানবাজনার উজ্জল পরিবেশ। মন্দিরার বাবা মুকুলবাবু ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের একান্ত ভক্ত। মুকুলবাবুর উৎসাহেই মন্দিরা স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে 'দূরদেশি সেই রাখাল ছেলে' শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলো। তখন তার বয়স মাত্র আট।
রাধুবাবু অর্থাৎ রাধিকাপ্রসাদ সেন ছিলেন এক আপনভোলা সংগীতসাধক। দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই সুরপাগল অকৃতদার মানুষটি মাঝেমাঝে কলকাতায় আসতেন। তাঁর উত্তর কলকাতার প্রাচীন জন্মভিটেতে। রাধিকাপ্রসাদের ছোটোভাই অম্বিকাপ্রসাদ আর মুকুলবাবু এক অফিসেই কাজ করতেন। সেইসূত্রে মুকুলবাবু একদিন অম্বিকাপ্রসাদকে অনেক ধরেকরে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। উদ্দেশ্য — মেয়ের গান শোনানো। একটিমাত্র গান শুনলেই তিনি বাধিত হবেন। একটি নয়। রাধুবাবু পরপর তিনটি গান শুনেছিলেন। তারপর বলেছিলেন — "শুধু গানের গলা দিয়ে আর রেওয়াজ দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায় না। গানের কথার ভিতরে, কথার পরতে পরতে যে কত অজস্র রং বোলানো আছে তা দেখতে না পেলে আর যাইহোক রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয় না।" মন্দিরা ছলছল চোখে তাকিয়েছিলো তাঁর দিকে। রাধুবাবু বুঝেছিলেন মন্দিরা তাঁর কথায় আঘাত পেয়েছে। মন্দিরার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গেয়ে উঠেছিলেন — 'সঘন গহন রাত্রি...ঝরিছে শ্রাবণধারা...' এখানে চোখ বন্ধ করে তোমায় অন্ধকার রাতের বৃষ্টিটাকে অনুভব করতে হবে... তবে গানটা, সার্থকভাবে গাওয়া যাবে।" তারপরেই বলেছিলেন — ঠিক আছে। ভয় পেও না। কথার ভিতর দিয়ে সুর কিভাবে ছবি আঁকে তা আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো।" মুকুলবাবু বিশ্বাস করতে পারেন নি যা শুনলেন। পঙ্কজ মল্লিকের বিশেষ স্নেহভাজন অসামান্য প্রতিভাধর এই ক্ষ্যাপাটে মানুষটা তার মেয়েকে গান শেখাবেন? কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছিলো। রাধুবাবু মন্দিরাকে প্রাণ ঢেলে শিখিয়েছিলেন। মন্দিরাও চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি।
রাধুবাবু বিগত হয়েছেন বহুকাল। রাধুবাবুর পর মন্দিরা আর কারো কাছে শিখতে যায় নি। তাঁর কথাগুলি মনে রেখে মন্দিরা গাইতে চেষ্টা করতো। চোখের সামনে গানের খাতাটি না রেখে চোখ বুজে গানটিকে দেখতে দেখতে গাওয়ার যে সাধনা সে শিখেছিলো তার মাস্টারমশায়ের কাছে, তাই সে অন্তর থেকে করে যাওয়ার চেষ্টা করতো বরাবর। তাই সামনে কে বা কারা রয়েছে কিংবা তারা কিভাবে তাকে শুনছে এসব মন্দিরার চোখে পড়তো না। তাই প্রীতমকে তার চোখেই পড়ে নি।
প্রীতম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একটি কোম্পানিতে সবে যোগ দিয়েছিলো। কলেজে থাকতে গান বাজনা নাটক কবিতা এইসব নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছে সে। একটা ঘরোয়া রবীন্দ্রসংগীতের আসরে সে শুনছিলো — "হৃদয় আমার প্রকাশ হলো..."। তার তখন মনে হচ্ছিলো এত নিমগ্ন সংগীত সে খুব কমই শুনেছে। মন্দিরা অবশ্য প্রীতমের এই মুগ্ধতা লক্ষ্যই করে নি।
এর ঠিক একবছর বাদে ওই অনুষ্ঠানেই প্রীতম মন্দিরার গলায় শুনেছিলো — 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে...'। সেদিন অবশ্য মন্দিরা বুঝেছিলো একজন সত্যিই তার গানের ওপারে আকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সে আর দ্বিধা করে নি। তাই প্রীতমের সঙ্গে একপথে একসাথে জীবনে চলা শুরু হয়েছিলো তার এরপর থেকেই। এর ঠিক একবছর পরের এক রাতে প্রীতম যখন প্রাণভরে গাইছিলো — 'আজি যত তারা আছে আকাশে' মন্দিরা তখন বসেছিলো তার সামনে। এইভাবে সত্যিই তারাভরা প্রকাণ্ড নীল আকাশের নীচে প্রীতম আর মন্দিরা তাদের নিজস্ব নীড় রচনা করেছিলো ওই সদ্যোলব্ধ দাম্পত্য জীবনে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই ছোট্ট নীড়টিতে চোখ মেললো ছোট্ট একটি প্রাণ। প্রীতম ও মন্দিরার সন্তান সেঁজুতি। নামটা প্রীতমেরই দেওয়া।
মাথায় গলায় হাতে ছোট্ট ছোট্ট জুঁইয়ের মালা পরা, চোখে কাজল টানা চার বছরের ছোট্ট সেঁজুতি যখন আধো আধো গলায় টলমলে পা ফেলে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' — বলে নাচতে পারলো বৈশাখের সেই নির্দিষ্ট সন্ধেয় — প্রীতম আর মন্দিরা তখন খুসিতে ভেসে গিয়েছিলো — ওদের মনে হয়েছিলো ওদের উত্তরসূরীকেও ওরা রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসতে পেরেছে। এইভাবে বিদেশ বিভূঁইতে আত্মীয়স্বজন বর্জিত হয়েও ওরা ছিলো আনন্দে। এর ঠিক পরের বছর, সেঁজুতির পাঁচ বছরের জন্মদিনে মন্দিরা তাকে নিয়ে হাততালি দিয়ে গাইয়েছিলো — 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে..'। এর কদিন বাদেই তাদের ভাগ্যের আকাশে তা তা থৈ থৈ করে যে কি ঘনিয়ে আসছে তার বিন্দুমাত্র আভাস পায় নি মন্দিরা।
"ওমা! এখনো শোও নি? কটা বাজে দেখেছো?" — এক কিশোরী কন্ঠের আওয়াজ এলো ঘরের কোন থেকে।
"ঠিক আছে! ঠিক আছে! তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না। ঘুমিয়ে পড়ো। আর আমায় কাজটা ঠিক মতো করতে দাও।" — মায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে গেলো সেই কিশোরী মেয়েটি। আর বালিশের আড়াল থেকে দেখলো কি ভাবে চোখ মুছতে মুছতে ক্রুশের কাঁটায় হাত রাখলো তার মা।
বিছানার একদিকে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে একগাদা উলের বোনা জামা। তার পাশেই কতো রকমের বাহারি সুতো। কতো রঙ বেরঙের উলের গোলা। ছোটো বড়ো সরু মোটা কতো ধরনের বোনার কাঁটা। আড়াল করে চোখ খুলে একবার দেখলো মেয়েটি। মাঝে মাঝে তার খুব ইচ্ছে হয় আঙুল দিয়ে ছোঁয় সেই রেশম রেশম মিহি মিহি রঙিন সুতোগুলোকে। কিন্তু নাহ। আর কক্ষণো করবে না সে এই কাজ। কারণ কয়েক বছর আগে একটা ধবধবে শাদা উলের গোলায় হাত দিতে গিয়ে দাগ লাগিয়ে ফেলেছিলো সে। এর জন্য পরদিন তার মায়ের কাছে এমন ঠ্যাঙানি খেয়েছিলো যে ডান চোখের তলার কালসিটের দাগ ছিলো প্রায় একমাস।
এইসব কাপড়চোপড়ের স্তূপে যেন একটা ঢিবির মতো বসে আছে তার মা। কিন্তু তার হাতদুটো চলছে যেন মেশিনের মতো। দূরে কোথায় একটা পাখি ডেকে উঠলো। আলতো ঘুমে ঢেকে গেলো তার চোখদুটো।
টিকটিক করে টেবিলঘড়িটার কাঁটাদুটো এগোচ্ছে। আর সেই সাথে বাড়ছে ওই মহিলার হাতের আঙুলের ওঠানামার গতি। এই নিঝুম রাতেই তাকে এই কাজটা করতে হয়। সারাদিন ঘরেবাইরের কাজ সামলে। এখন হাতে নিয়েছে একটা ক্রুশের কাজ। একটা ধবধবে সাদা লেসের গোল টেবিল ক্লথ। অর্ডারি কাজ। বেশি মজুরির। সেন বাড়ির। এরা তার পুরোনো কাস্টমার। কাজের মান রাখতেই হবে। তাই খুব যত্ন করে আঙুল চলে তার প্রতিটি সুতোর টানে।
মাঝেমাঝে সে নিজেই অবাক হয়ে যায় এই সুতোগুলোর বান্ডিলের দিকে, উলের গোলার স্তূপের দিকে তাকিয়ে — এই নিয়ে তাকে কাটাতে হবে রাতের পর রাত — এইসব রঙিন সুতোর টানাপোড়েনে । তাও তো তাতে শেষ অবধি কিছ ফুটে ওঠে — একটা কিছু তৈরি হয় — একটা সোয়েটার — বা একটা স্কার্ফ। কিন্তু তার জীবনে কিছু কি তৈরি হবে শেষ পর্যন্ত?
অথচ গতমাসেই তো একটা বড় কাজ পেয়েছিলো। একটা বিরাট লেসের চাদর। ক্রুশের কাজ। পুরো মাসটাই প্রায় লেগে গিয়েছিলো বুনতে। আর যা মজুরি পেয়েছিলো তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। ভেবেছিলো মেয়ের জন্যে একটা ভালো ফ্রক কিনে আনবে। কোথাও পরে যাওয়ার মতো কিচ্ছু নেই মেয়েটার। কিন্তু কিছুই কেনা হয় নি। কারণ বাড়ি ফিরে দেখেছিলো তার মেয়ের ধুম জ্বর। টাকাগুলো সব বেরিয়ে গিয়েছিলো ওষুধ আর ডাক্তারের পিছনে।
ওষুধ-ডাক্তার-টিচার-স্কুল-ঘরভাড়া এইসব মেটাতে মেটাতে মানিব্যাগে তার খুচরো দু-দশ টাকার বেশি থাকে না। গত পরশুদিনই দুপুরবেলায় কতগুলো কাঁথা চৌধুরি ম্যানসনে দিয়ে প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর একটা কোল্ডড্রিঙ্ক খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো। কিন্তু কিনতে গিয়েই মনে পড়েছিলো তার মেয়েটার কথা। গত সপ্তাহে স্কুল থেকে ফেরার পথে কিভাবে তাকিয়ে দেখছিলো আইসক্রিমের গাড়িটার দিকে। তাই বাড়ি ফিরে কলসির জল খেয়েই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলো নিয়মমাফিক রঙিন সুতোর জালে। অর্ডারি মালের স্তূপে।
কারণ সারা বছর তো আর সোয়েটার কার্ডিগান স্কার্ফ এসবের বাজার থাকে না। তাই অন্যান্য জিনিসও করতে হয়। ক্রুশের কাজ। কাঁথা সেলাই। এমনকি বেডকভার পেন্টিং পর্যন্ত। ভাগ্যিস আঁকার হাতটা ছিলো। পাড়ার স্কুলের সেলাই দিদিমনির কাজটা তো না থাকারই মতো। হঠাৎ কয়েকটা কাক ডেকে উঠলো। বাইরের আকাশ প্রায় সাদা। এইসব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে বেশ দেরি হয়ে গেলো। ডেলিভারিটা আজ করতেই হবে। কি বার আজকে? ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে দেখলো — বুধবার। ৫ই মে।
৫ই মে! কি আশ্চর্য! কাজের চাপে খেয়ালই ছিলো না! এর আগের দিনটায় ও কিছুই যেন করতে পারে না। পাগলের মতো আজো ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে। দেখতে দেখতে দশ দশটা বছর কেটে গেলো!
সেই ৫ ই মে। উনিশশো ছিয়াশি। অন্যান্য দিনের মতো সেটাও ছিলো তার সেই জীবনের একটা ঝলমলে সকাল। বেলা গড়াচ্ছিলো সহজেই। খবরটা এলো বিকেল বেলায়। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তার জীবনের সব আলো নিভে গেলো। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নিমেষে চুরমার হয়ে গেলো তার অত সাধের জীবন। শ্বশুরবাড়ি বলতে কিছুই নেই। আর বাপের বাড়ি বলতে শুধু বিধবা মা। অফিসের কোয়ার্টার ছেড়ে আশ্রয় জুটলো মাসতুতো দিদির বাড়িতে। পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে। সেই চরম কষ্টের দিনে ইভাদির কথায় তার এই সেলাইয়ের কাজে নামা। লেখাপড়া যা শিখেছিলো তা দিয়ে ওই বাজারে কোনো চাকরি সম্ভব ছিলো না। টেবিলঘড়িটায় টিং টিং করে অ্যালার্ম বেজে উঠলো। সকাল ছটা। মেয়েকে ঘুম থেকে ওঠানোর টাইম। হাতে সময় খুব কম। কি হবে এসব পুরোনো কথা ভেবে?
"দারুণ হয়েছে বৌদি — এত সূক্ষ্ম আর সুন্দর ক্রুশের কাজ — চোখ ফেরানো যায় না — আর আপনি এসেছেনও একেবারে ঠিক সময়ে" — উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছিলেন রাধিকা। অর্থাৎ রাধিকা সেন। ইন্সপেক্টর সুহাস সেনের স্ত্রী।
ম্লান হেসে সে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার গোড়ায়। কারণ আজ ১২ ই মে। অর্থাৎ সাতদিন হয়ে গেছে। টাকাটা এখনো ওরা পাঠায় নি । অগত্যা তাকেই আসতে হয়েছে। এই লেসের তৈরি টেবিল ক্লথটার মজুরি দিয়ে তার মেয়ের স্কুলের তিনমাসের বাকি মাইনেটা দিতে হবে। আজই। বেলা বারোটার মধ্যেই।
"এসো না — ভিতরে এসো না — এসে দ্যাখো কিভাবে সাজিয়ে রেখেছি তোমার জিনিসটাকে" — অতি উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে রাধিকা সেনের মেয়েটি। সে বিস্মিত হয়ে তাকায় মেয়েটির মুখের দিকে — তার মেয়ের বয়সিই হবে — মেয়েটি ততক্ষণে তাকে নিয়ে গেছে ভিতরের ঘরে। "দ্যাখো দ্যাখো কি সুন্দর মানিয়েছে না — এই শ্বেতপাথরের টেবিল আর ছবিটার সঙ্গে?"
তার বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই রাধিকা সেন বলে উঠলেন — "আজ তো ২৫শে বৈশাখ... আমাদের বাড়িতে এই দিনটা উদযাপন করা হবেই... আসলে তোমার দাদা এতবড় পুলিশ অফিসার হয়েও এই ব্যাপারটায়..."
২৫শে বৈশাখ! ২৫শে বৈশাখ! কথাটা যেন বহুযুগ পরে তার কানে এসে বিঁধলো! আপনা থেকেই চোখ দুটোয় ঝাপটা দিলো একটা কালো অন্ধকার।
"টাকাটা ঠিক করে নাও। পরের মাসে পারলে একবার এসো। একটা লেসের রুমাল বানাতে হবে..." — রাধিকার কথাগুলি তার কানে ঢুকলো না। তার বন্ধ চোখের পাতা ভেদ টপটপ করে খসে পড়লো কয়েকটি তপ্ত জলের ফোঁটা।
দশ বছর আগে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো তার জীবনের সমস্ত গীতাঞ্জলি...অনেক অভিমানে...শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে... তার ছোট্ট সন্তানটিকে নিয়ে... আজ এই মুহূর্তে সে কিভাবে চোখ মেলে তাকাবে তাঁর দিকে?
অথচ তাকে দেখতে হলো — একটা প্রকাণ্ড কাঁচের ফ্রেমে — বিরাট রজনীগন্ধার মালার পিছনে — দারুণ সুন্দর শ্বেতপাথরের টেবিলে -- তারই হাতে তৈরি ক্রুশের কাজের উপর তিনি রয়েছেন!
কোনোক্রমে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তেই পাশে রাখা সাউন্ডসিস্টেমে বেজে উঠলো — 'তুমি রবে নীরবে'
এইবার সে তাকালো — তাঁর দিকে — তাঁর সেই মর্মভেদী চোখ দুটির দিকে — অতি কুন্ঠিতভাবে — শুনতে পেলো... 'জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি....'
এরপর...
এরপর যেন পালিয়ে যাচ্ছে সেই “সেলাই দিদিমনি মন্দিরা....
যেন লুকিয়ে নিশ্চুপে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে....
তিনশো টাকা মজুরি হাতে নিয়ে...
মেয়ের স্কুলের পাওনা মেটাতে......
কিন্ত দু এক পা এগিয়েই তাকে স্থির হয়ে যেতে হয় —
এক আশ্চর্য সুর অথবা সত্যের সামনে.... 'তুমি ভরিবে সৌরভে....' "
(পরবাস-৬৭, জুন ২০১৭)