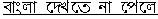সত্যি সাবিত্রী;—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯; দে'জ পাবলিশিং - কলকাতা; পৃষ্ঠাঃ ৩৪৩
সত্যি সাবিত্রী;—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯; দে'জ পাবলিশিং - কলকাতা; পৃষ্ঠাঃ ৩৪৩
“উপস্থিত আর একটা ধুয়া মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, যে স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন করবার জন্য ভদ্রমহিলাগণ stage as profession গ্রহণ করতে পারেন কি না তার বিচার হওয়া উচিত। আমাদের সমাজের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কটাকে একেবারে ওলট্পালট্ না করলে সেটা যে সম্ভব হবে না তা বলাই বাহুল্য। ... সত্যিকারের ভদ্রমহিলা - professional actress আর সোনার পাথরবাটী একই জিনিষ।”
১৯২৯ সালে প্রবর্ত্তক পত্রিকার এপ্রিল-মে সংখ্যায় ‘ভদ্রমহিলার নটীবৃত্তি’ শিরোনামে এক আলোচনায় জনৈক চারুচন্দ্র রায় যখন উপরোক্ত মন্তব্য করছেন, আর ওই লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে ওই বছরেরই প্রবাসী পত্রিকার জুন-জুলাই সংখ্যায়, তার এক-দেড় দশকের মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেবেন। থিয়েটার ও সিনেমা হয়ে উঠবে তাঁদের জীবিকা অর্জনের মুখ্য উপায়। এই বদলের প্রেক্ষাপট চল্লিশের দশকের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক সংকট, ওই দশকের শেষে দেশভাগের দরুণ যে সংকট তীব্রতর হল, জন্ম দিল এক উত্তাল সামাজিক পরিস্থিতির, অস্থির মূল্যবোধের।
প্রকাশ্যে অভিনয় করে দর্শকের মনোরঞ্জনের বিনিময়ে রোজগারের পথটা বাঙালি মেয়েদের একাংশ অবশ্য বেছে নিয়েছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। তবে তাঁরা ভদ্রমহিলা হিসেবে গণ্য হতেন না। ১৯০১ সালের জনগণনার তথ্য অনুসারে সে-কালীন বাংলা প্রদেশে প্রায় ৩০ হাজার মেয়ে নাচ, গান, অভিনয় করে ও শারীরিক কসরত দেখিয়ে রোজগার করতেন। এক দশক পরে ১৯১১ সালের জনগণনায় সংখ্যাটা অবিশ্বাস্যভাবে কমে দাঁড়ায় কয়েকশো-তে। ১৯২১ ও ১৯৩১-এর জনগণনার হিসাবেও নাচ-গান-অভিনয়ের বৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের সংখ্যা দেখা যায় নেহাত হাতে গোনা।
অথচ উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে নাগরিক বাঙালির জীবনে প্রথমে থিয়েটার ও পরে সিনেমার আকর্ষণ ও গুরুত্ব দুইই ক্রমশ বেড়েছিল। কলকাতা শহরের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় গড়ে উঠেছিল একের পর এক পাবলিক থিয়েটার বা জননাট্যমঞ্চ। সমকালীন সংবাদপত্রে ওইসব থিয়েটারে অভিনয়ের যে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হত তাতে অভিনেতাদের পাশাপাশি থাকত বহু অভিনেত্রীরও নাম। স্মৃতিকথায় হদিস মেলে সেকালের সাড়া জাগানো অভিনেত্রীদের। বিনোদিনী, কাননদেবী, কেতকী দত্ত, রেবা রায়চৌধুরী অথবা শোভা সেন নিজেরাই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁদের অভিনয় জীবনের বিবরণ। বাঙালি অভিনেত্রীদের আত্মকথনের এই সমৃদ্ধ ধারাটিতে সর্বশেষ সংযোজন ‘সত্যি সাবিত্রী’—বাংলা সিনেমার কিংবদন্তী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আত্মকথন। বইটির ভূমিকা লিখেছেন আরেক কিংবদন্তী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আখ্যানপত্রে লেখা রয়েছে গ্রন্থটি নির্মাণ করেছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। মানেটা ঠিক স্পষ্ট হয়নি। লীনা কি অনুলিখন করেছেন? একজনের জীবন কি অন্য কেউ নির্মাণ করতে পারেন—তাও আবার সাবিত্রীর মতো মানুষের জীবন?
বিনোদিনীর ‘আমার কথা’, কাননের ‘সবারে আমি নমি’, রেবা-র ‘জীবনের টানে শিল্পের টানে’, শোভা-র ‘নবান্ন থেকে লাল দুর্গ’ কেতকী-র ‘নিজের কথায় টুকরো লেখায়’ আর সাবিত্রীর ‘সত্যি সাবিত্রী’—এই সবকটিই অভিনেত্রীর আত্মকথন। কিন্তু রচয়িতাদের মধ্যে কেবল সময়কালের নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থানের নিরিখেও বিস্তর ফারাক।
বিনোদিনী এবং তাঁর সমকালীন বেশিরভাগ অভিনেত্রী মধ্যবিত্ত পারিবারিক কাঠামোর আশ্রয়ে বেড়ে ওঠেননি। প্রথম কয়েকটি প্রজন্মের পেশাদার অভিনেত্রীরা প্রায় সবাই ছিলেন পরিবারচ্যুত, থিয়েটারে তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছিল দেহব্যবসার বাজার থেকে। রোজগার করে টিঁকে থাকা ও নিকটজনকে টিঁকিয়ে রাখার তাগিদেই এঁরা দেহব্যবসায় এসেছিলেন, মুখ্যত একই কারণে বেছে নিয়েছিলেন মঞ্চে পেশাদার অভিনয়। সেকালের তথাকথিত ভদ্রলোক-সমাজের একাংশের মঞ্চ সম্পর্কে, মেয়েদের রোজগার করা সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গির উৎস প্রথম যুগের এই রোজগেরে মেয়েদের সামাজিক প্রক্ষাপট। এই শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাবের দরুণই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের পক্ষে পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করতে আসা সম্ভব হয়নি বহুদিন। মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশের বিরূপতাই সম্ভবত অভিনয় করে রোজগার করা বহু মেয়েকে বাধ্য করেছিল নিজের বৃত্তি গোপন রাখতে। ১৯০১ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে জনগণনার হিসাবে অভিনেত্রীর সংখ্যা পূর্বতন বাংলাপ্রদেশে নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ার পিছনে অভিনয়কে পেশা বলে স্বীকার করতে অনীহাকে অন্যতম মুখ্য কারণ বলে মনে করেছেন স্বাধীন ভারতের জনগণনার রূপকার অশোক মিত্র। তাই স্বাধীনতার কয়েক দশক আগে থেকেই একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মেয়েরা অভিনয়কে জীবিকা হিসেবে বেছে নিলেও, সরকারি নথিতে ক্রমাগত অন্য ছবি ধরা পড়ে।
৩০-এর দশকে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে একমাত্র যে মেয়েরা প্রকাশ্যে অভিনয় করতে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পেশাদার নয়, ‘অ্যামেচার’ বা শখের থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। পরিচালক ও অভিনেতা, মধু বসু তাঁর আত্মকথা ‘আমার জীবন’ গ্রন্থে জানিয়েছেন সেকালের মঞ্চে পেশাদার ও অ্যামেচার শব্দ দুটির বৈপরীত্যের ঠিক কী তাৎপর্য ছিল: “প্রথমে ঠিক করেছিলাম যে এই নাট্যসংস্থার [মধু বসুর তৈরি সংস্থা] নাম দেব ‘ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স’, কিন্তু সকলে পরামর্শ দিল যে ‘অ্যামেচার’ কথাটা উল্লেখ করা বিশেষ দরকার, নইলে কোনো বাপ-মা তাদের মেয়েকে আমাদের দলে দিতে রাজি হবে না। সুতরাং নাম হল ‘ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স’।” মধু বসু আরও লিখেছেন, মধ্যবিত্ত মেয়েরা যাতে গ্রামোফোনে গান রেকর্ড করাতে নিশ্চিন্তে আসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কীভাবে এইচ.এম.ভি-র রিহার্সাল ঘর চিৎপুর এলাকা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল।
রোজগারের জন্য অভিনয় করছেন না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে মধ্যবিত্ত মেয়েরা প্রকাশ্যে মঞ্চে আসতে পেরেছিলেন। এমন কি গণনাট্য সংঘে বামপন্থী ঘরানার অভিনয় করতে আসা তৃপ্তি মিত্র অথবা শোভা সেন-ও জোর দিয়েছিলেন টাকার জন্য যে তাঁরা অভিনয় করছেন না সেই কথাটার উপর। অর্থাৎ সকলেই অভিনেত্রী, কিন্তু বিনোদিনী, তিনকড়ি, কেতকীরা একদলে—শোভা, রেবা, তৃপ্তি আরেক দলে। রোজগারের জন্য অভিনয়কে বাছেন চিৎপুরের মতো ‘খারাপ পাড়া’-র ‘খারাপ মেয়েরা’। আর ‘ভদ্রঘরের’ ভালো মেয়েরা যদি বা অভিনয় করতে আসেও তাহলে তা শখের অথবা আদর্শের জন্য।
মন্দ-ভালো-র এই বৈপরীত্যে ‘সত্যি সাবিত্রী’ ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে? বিনোদিনী, উমাশশী, কানন অথবা তাঁদের মতো আরও অনেক মেয়েই যেমন খুব অল্প বয়সে রোজগারের জন্য মঞ্চে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সাবিত্রীর অভিজ্ঞতাও তেমনই। কিন্তু কিশোরী সাবিত্রীকে মহানগরের মঞ্চে ঠেলে তুলেছিল এক উত্তাল বৃহৎ ইতিহাস, বৃহৎ সময়। শিক্ষিত, সচ্ছল, মফঃস্বলী মধ্যবিত্ত পরিবারে নিশ্চিন্ত শৈশব থেকে তাঁকে এক ঝটকায় কলকাতার রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল দেশভাগ—দেশান্তর। রাতারাতি অন্য দেশ হয়ে যাওয়া মাতৃভূমি থেকে উৎখাত আরও বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের মতোই সাবিত্রীর পরিবারও মেয়েদের রোজগার করা সম্বন্ধে মনোভাব বদল করতে বাধ্য হয়েছিল নিতান্ত আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে। বস্তুত ছিন্নমূল পরিবারকে শহরে টিঁকিয়ে রাখার পুরোটা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সাবিত্রীরা কয়েক বোন মিলে। এক দিদি স্বামী-সন্তান-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন নিরাশ্রয় ছোট বোনেদের সঙ্গে নিয়ে থাকবেন বলে। ৫০-এর দশকের কলকাতায় ঘর ভাড়া নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তিন বোন ও বোনঝি-র এক অন্যরকম সংসার। ভরসা কেবল বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্র পড়ানোর রোজগার। সাবিত্রীর নিজের মুখে সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা শোনা যাক:
“ভবানীপুরের স্কুল রোডে এক দোতলা বাড়ির রুমালের মতো একফালি ঘরে আমরা চারজন মেয়ে উঠে এলাম। ... নতুন বাড়িতে এসে সোনাদিদি আরও একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল, সংসারের হাজারটা ছিদ্র কিছুতেই আরতিদির একার টিউশনির টাকায় তালি দেওয়া যাচ্ছিল না। আরতিদি তখন উদয়াস্ত টিউশনি করে। তার মধ্যেই তার কলেজ, নিজের লেখাপড়া সামলায়। ... সোনাদিদিও বাইরে বেরোতে শুরু করল। সেও ছাত্র পড়াতে লাগল ... তখনকার দিনে কোনও বউমানুষ লোকের বাড়ি ঘুরে ছেলেমেয়ে পড়াতে যাচ্ছে, এমন ঘটনা খুব সম্মানের চোখে দেখা হত না।”তবু ৫০-এর দশকে ছিন্নমূল বাঙালি ভদ্রলোকের মূল্যবোধ অনেকটাই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। উচ্চশিক্ষিত শরণার্থী যুবক যে-কোন কাজ করে দেওয়ার শর্তে মাথা গোঁজার একটু জায়গা চায়—এমন বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে হামেশাই চোখে পড়ত ৫০-এর কলকাতায়। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যৎসামান্য মজুরিতে কাজের লোক হয়ে মধ্যবিত্ত বাড়িতে থাকতে চাইছিল শরণার্থী মেয়েদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। এই উদ্বাস্তু মেয়েদের কেউ কেউ সাবিত্রীর দিদিদের মতোই স্কুল-কলেজে পড়া। স্বাধীনতার আগে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রেওয়াজ যেটুকু ছিল তা ওই পূর্ববঙ্গেই দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত নিরাশ্রয় শরাণার্থী মেয়েদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বিচিত্র সব দাবি করতে সক্ষম হয়েছিল শহুরে নিয়োগকর্তারা। ঘরোয়া কাজের পাশাপাশি শরণার্থী মহিলা বাড়ির শিশুদের পড়াশোনায় তালিম দেওয়ার ভার-ও নিক এমন আব্দার নিয়ে কাজের লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দুর্লভ ছিল না।
সাবিত্রীর পূর্বসূরী কানন দেবীর শৈশব কেটেছিল আত্মীয়বাড়িতে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনা মজুরির ‘ঝি-গিরি’ করে। সাবিত্রীর জীবনটা যে অন্যখাতে বইল তার কারণ বোনেদের যৌথ লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত।
অবশ্য শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসে বোনেদের নিয়ে আলাদা সংসার গড়ার সিদ্ধান্ত যতটা বৈপ্লবিক ছিল, বৃত্তি হিসেবে মেয়েদের গৃহশিক্ষকের কাজ করাটা তত ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল না। ঔপনিবেশিক বাংলায় তথাকথিত ভদ্রঘরের মেয়েরা যে-দুটি বৃত্তিতে কিছুটা পরিমাণে নিযুক্ত হয়েছিলেন তা হল এই শিক্ষকতা ও চিকিৎসা-পরিষেবা। সাবিত্রী ভদ্রমহিলার জন্য নির্দিষ্ট সেই বৃত্তির গণ্ডিও পেরোলেন। পাঁচ টাকা রোজগারের তাগিদে শুরু করলেন থিয়েটারে অভিনয়, এমন এক সময়ে মধ্যবিত্তের শুচিবায়ু যখনও রীতিমতো প্রবল:
“ওদের [আত্মীয়-স্বজন] চোখে আমি তখন একটা খারাপ মেয়ে। ... পুরুষের সঙ্গে এক সঙ্গে নাটক করছি মানেই আমি উচ্ছন্নে গিয়েছি ...।সাবিত্রীর বাবা-মা অবশ্য মেয়ের অভিনয় করে রোজগারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছিলেন এবং দেশ ছেড়ে এসে আজীবন আশ্রয় নিয়েছিলেন রোজগেরে মেয়ের কাছেই। কিন্তু প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, পারিবারিক নিরাপত্তায় শৈশব কাটানো এক কিশোরীর জীবনে আকস্মিক মোড়বদল ও ক্রমশ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় হয়ে ওঠার যাত্রাটা কি কেবল দেশভাগ দেশান্তরের বড় ইতিহাস খুঁজে পুরোটা বোঝা সম্ভব? খোঁজ নিতে হবে ব্যক্তি-ইতিহাসে। উঁকি দিতে হবে এমন এক কিশোরীর মনোজগতে যে তার সমবয়সীদের তুলনায় একটু বেশিই যেন ভাবুক প্রকৃতির, অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়, আর কাল্পনিক চরিত্রদের সঙ্গে কাল্পনিক সংলাপে স্বচ্ছন্দ। এই অতি কল্পনাপ্রবণ মফঃস্বলী মেয়েটি শহরে এসে রুপোলি জগতের আকর্ষণে সাড়া দেবে তা যেন প্রায় অনিবার্য ছিল:আমাদের দেশে আজও নাটক অথবা সিনেমা সিরিয়ালে যদি কেউ অভিনয় করতে আসে, তাকে লক্ষ্য করে বলা হয় — অমুক সিনেমায় নেমেছে। কেন যে নাটক-সিনেমা করতে এলেই ‘নেমে যাওয়া’ হয়, তা আজও বুঝলাম না। কেন যে এগুলো একটা মানুষের ‘ওপরে ওঠার’ মাপকাঠি হয়ে উঠতে পারল না জানি না।”
“দিদির শ্বশুরবাড়ির সবাই ধরেই নিয়েছিল আমি একটা বয়ে যাওয়া মেয়ে। ... তখন [শহরে এসে প্রথমে দিদির শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার সময়] আমি একমাত্র শান্তি পেতাম সিনেমা দেখলে কিংবা সিনেমার কথা ভাবলে ... রোজ হল-এর সিনেমা শুরু হওয়ার আগে গিয়ে হল-এর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আর হল ভাঙলে বাড়ি ফিরতাম। হল-এর বাইরে দাঁড়িয়েও তখন ভেতরের কিছু কিছু কথা, গান, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গলার স্বর শুনতে পেতাম।”এইভাবে একদিন হল ম্যানেজারের চোখে পড়ে যায় নেহাত ছোট্ট মেয়েটি। তারপর ম্যানেজারের অনুগ্রহে মেলে ভিতরে বসার অনুমতি—রোজ রোজ একই সিনেমা দেখে যাওয়া প্রাণমন ভরে আর কল্পনায় তালিম নেওয়া। এই আশ্চর্য অধ্যবসায় চিনিয়ে দেয় গড় কিশোর-কিশোরীর তুলনায় কতটা স্বতন্ত্র ছিল ভবিষ্যতের এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর মনোজগৎ। খালি পেটে, তালি মারা দুটি ফ্রক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরে যাবতীয় অপমানের সঙ্গে যুঝে সে বাঁচিয়ে রাখে তার আশ্চর্য মনটি। লড়াইয়ে কখনো বা পাশে পায় অনাত্মীয়, অপরিচিত এমন কাউকে যে কিশোরীর হাত ধরে শেখাতে চায় শহরে টিঁকে থাকার কৌশল: “ভানুদা বললেন—‘বুইন রে কইলকাতার রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটা যায় না। ... কাঁকর বিছানো পথ দিয়া হাঁটতে গ্যালে পাওদুইখান রক্তে ভিজব। তাই তরে জুতা পইরা হাঁটতে হইব। জুতো হইল একখান বর্ম’।"
তবু বর্ম পরতে শিখলেন কই সাবিত্রী? অসম্মানে বঞ্চনায় বারবারই তো ক্ষতবিক্ষত হলেন। থিয়েটার থেকে চলচ্চিত্রে—সমান্তরাল ভাবে মঞ্চে ও পর্দায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করলেন—পৌঁছলেন সাফল্যের চূড়ায়, বহু টাকা রোজগারও করলেন। কিন্তু অনুশাসন, বঞ্চনা, অপমান তাঁর পিছু ছাড়ল না। তাই বোধহয় কখনই ভুলতে পারলেন না নিজের শিকড়: “এক সম্ভ্রান্ত সচ্ছল পরিবারের কাঠামোয় খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া মেয়েটাকে প্রায় ভিখিরির মতো দিনের-পর-দিন অর্ধাহারে, অনাহারে সামান্য রুমালের মতো একফালি একটা খোলার ঘরে পুরো পরিবার নিয়ে থাকতে হয়েছে। পেটের জ্বালায় যে কোনও কাজ করে বাঁচতে হয়েছে। স্টুডিওর ভিড়ে দাঁড়িয়ে দালালকে পাঁচ টাকা দিয়ে নিজে পাঁচ-টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছি ...।”
ভুলতে পারলেন না কিছু মধ্যবিত্ত মূল্যবোধও। নিজের জীবন, নিজের রোজগার সম্বন্ধে মেনে নিলেন তাঁরই ওপরে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল বাবার যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ। নামজাদা পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জির ডাকে বলিউডে পা রাখার সুযোগ হারালেন পারিবারিক অনুশাসনকে মর্যাদা দিতে গিয়ে:
“[বাবা] স্পষ্ট গলায় বলে দিলেন, ‘এত দূর যা করছ, করছ। এই সব দিল্লি-বম্বে যাওয়া হইব না। আমার মত নাই’।মেয়ে অভিনয় করে রোজগার করবে আর সেই টাকায় সংসার চলবে—তাতে বাবার আপত্তি নেই, কিন্তু কেরিয়ারের জন্য দূরে যেতে চাইলে অমত। কেন এই দ্বিচারিতা সেই প্রশ্ন কিন্তু রয়ে গেল নিরুচ্চার। ব্যক্তিগত সম্পর্কে এক প্রশ্নহীন আনুগত্য আর অসম্ভব আবেগ সাবিত্রীর জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি বলে মনে হয়। তিনি প্রেমে পড়েন, ঠকেন, বিখ্যাত প্রেমিকের মিথ্যাচার ও স্বার্থপরতা তাঁকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দেয়—ফের উঠে দাঁড়ান কিন্তু ভ্রষ্ট প্রেমিককে হৃদয় থেকে বিদায় দেন না। আত্মকথন থেকে কখনো কখনো মনে হয়, ব্যক্তিপ্রেমের আবেগ অভিনয়ের জন্য তাঁর আবেগকেও যেন বা ছাপিয়ে গেছে। নইলে উত্তমকুমারের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর দীর্ঘকাল অভিনয় ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারেন তাঁর মাপের এক অভিনেত্রী! শেষ পর্যন্ত মঞ্চের আকর্ষণেই অবশ্য অবসাদ থেকে উঠে দাঁড়ান, রুখে দাঁড়ান তাঁর কেরিয়ার নষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রাক্তন প্রেমিকের উদ্যোগের বিরুদ্ধে:... দু’চোখ জলে ভেসে গেল। তবু বাবার কথার প্রতিবাদ করে জোর করে কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার সাহস পেলাম না।
... আজ ভাবি, আমার বাবার ইচ্ছেতেই একদিন এ লাইনে এসেছিলাম। আবার আমার বাবার ইচ্ছেতেই এই জগতের একটা বড় দরজা চিরদিন বন্ধ হয়ে রইল আমার কাছে।”
“একদিন একজন প্রোডিউসার ফোন করলেন বাড়িতে। ... আমতা-আমতা করে বললেন, ‘আসলে উত্তম কুমারের বিপরীতে আপনাকে ভেবেছিলাম। কিন্তু উনি বললেন, আপনি এখন কাজ করতে পারবেন না। আপনি অসুস্থ। ওঁর কাছেই তো জানলাম আপনার টিবি হয়েছে’।”এই ষড়যন্ত্র ঠেকাতে সাবিত্রী পুরোদমে কাজে তো ফেরেনই, সপাটে জবাবও দেন, কিন্তু তবুও মন থেকে কোনদিনই মুছতে পারেন না তাঁর প্রথম প্রেম। সাফল্যের চূড়ায় উঠেও প্রেমের অভাবে, সংসারের অভাবে নিঃসঙ্গতায় ক্ষতবিক্ষত হন। তারপর আবার নতুন প্রেমে পড়েন। ফের আঘাত পান—স্বামী-সংসার নিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত সংসার কোনদিনই গড়া হয় না। অন্যের ঘর ভাঙা উচিত নয়—এই মূল্যবোধ তাঁকে বিবাহিত প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধা থেকে দূরে রাখে।
কেরিয়ারের প্রান্তে পৌঁছে এই অকপট আত্মকথনটি না পেলে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধের হয়তো কখনো জানাই হত না, রুপোলি পর্দায় যৌথ পরিবারের বধূর যে ভূমিকায় অভিনয় তাঁর একচেটিয়া ছিল, জীবনে সেই ভূমিকার জন্য সাবিত্রীর কী অসীম আকাঙ্ক্ষা:
“মনে মনে তো বরাবরই একটা স্বপ্ন ছিল, আমার একদিন অনেক বড় বাড়িতে বিয়ে হবে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে ... আমি হব বাড়ির বড় বউ। সন্ধেবেলা অতবড় সাতমহলা বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরে প্রদীপ দেখাব। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করব সকলের মঙ্গল কামনায়। শঙ্খের আওয়াজে সব বিপদ দূরে সরিয়ে রাখব। কিছুই আমার জীবনে সত্যি হয়নি।”আত্মকথনের শেষ পর্বে পৌঁছে চিরাচরিত সংসারের জন্য এই তীব্র আক্ষেপ, প্রেমের জন্য হাহাকার যেন খানিকটা ধন্দে ফেলে। এ কোন সাবিত্রী? মিষ্টির দোকানের সামনে একরাশ খিদে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যেন মর্ডান টাইম্স-এর সেই কিশোরী অথবা অসমবয়সী শুভার্থীর হাত ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অবিরত যেন সিটিলাইটস্-এর সেই তরুণী? কেরিয়ারের প্রান্তে পৌঁছে যিনি বলতে পারেন:
“বেঁচে আছি প্রবলভাবে। আজও অভিনয় আমাকে ছেড়ে যায়নি, আমিও শক্ত মুঠিতে ধরে আছি অভিনয়কে। আমি বুঝে গিয়েছি, আমার জীবনের সেরা বন্ধু আমৃত্যু থাকবে আমার সঙ্গে। আর যেই বিশ্বাসঘাতকতা করুক সে করবে না। ... আর সেও জানে আমিও তাকে প্রাণ না যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেব না।”কোনটা সত্যি সাবিত্রী? মনে হয় সব কটাই। চরিত্রের এই বহুমাত্রিকতা, দ্বান্দ্বিকতার জন্যই সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এত জীবন্ত—রুপোলি পর্দার নায়িকার চেয়ে সত্যি সাবিত্রী-র কথক একটুও কম আকর্ষণীয় নন।

(পরবাস-৭৫, ৩০ জুন ২০১৯)