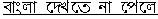শুনতে পাই ডাক্তার ঠ্যাঙানো ব্যাপারটা আপাতত নাকি বঙ্গসংস্কৃতির মূলধারায় ঢুকে পড়েছে। আমাদের মতন যেসব বাঙালি ডাক্তাররা সেই প্রাক-ইন্টারনেট সত্যযুগে দেশত্যাগ করেছিল, তাদের এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য না করাই উচিৎ। যে মানুষ পলাতক সে বিচারক হতে তো পারেই না, সমীক্ষক হওয়াও তার পক্ষে কঠিন। তাও এই নিবন্ধ লিখতে বসেছি কেননা বিশ্বাস আছে যে বিষয়টি যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক চিকিৎসা সংকট, পাঠক এর সঙ্গে দেশের পরিস্থিতির অনেকটাই মিল পাবেন, কিছু অন্তর্দৃষ্টিও মিলে যাওয়া অসম্ভব নয়। অপচিকিৎসা কথাটা প্রথম শুনেছিলাম প্রায় বছরবারো আগে একটা সেমিনারে, বক্তা ছিলেন ডঃ কুণাল সাহা, আমাদেরই মতন এক আমেরিকাপ্রবাসী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। মিডিয়ার কল্যাণে সেই কিস্যা আপনাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী কলকাতায় অসুস্থ হয়ে মারা যান, তাঁর চিকিৎসায় নাকি বড়োরকমের গলতি হয়েছিল, এবং কলকাতার কিছু নামকরা চিকিৎসক ঘটনাটিকে যথাবিধি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে সুবিচার না পেয়ে ডঃ সাহা শেষ অবধি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট অবধি ধাওয়া করে মামলা জেতেন এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের শাস্তি হয় এবং ডঃ সাহা “পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্ট” নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন করে ভারতীয় অপচিকিৎসার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ চালিয়ে যেতে থাকেন। ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ডাক্তার পেটানোর জনপ্রিয় পদ্ধতির থেকে মূলগতভাবে আলাদা, কেননা সেটা ছিল আইনের বিচার, মিডিয়া কিংবা পাবলিকের বিচার নয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, অনেক অপচিকিৎসার অভিযোগ, সেইসব অভিযোগের তাৎক্ষণিক বিচার এবং দণ্ডবিধান এসবই বেশ সহজ সরল হয়ে এসেছে এখন। কিছু কিছু শব্দ পয়দা হয়েই বেশ জবরদস্ত হয়ে ওঠে, যেমন নাকি সন্ত্রাসবাদী শব্দটা। একবার কারুর ঘাড়ে সেই শব্দের ছাপ্পা লাগিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে, তারপর সেই লোকের ইতিহাস, ভূগোল নিয়ে কেউ আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না, বরং পত্রপাঠ প্যাঁদানি দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে।
অপচিকিৎসার ইতিহাস শুরু করার আগে একটা সাদা সরল তথ্য হাজির করতে চাই। বেশ কিছুদিন ধরে দেশে-বিদেশে সর্বত্রই ডাক্তারদের বেশ একটা সাধারণ শনির দশা চলছে। অস্যার্থ এই নয় যে তাঁদের ব্যবসা মার খাচ্ছে, বরং তার উল্টোটাই। মার খেয়ে চলেছেন ডাক্তাররা, কোথাও হাতে কোথাও বা ভাতে, কোথাও স্রেফ তাঁদের নিজস্ব মানসিক জগতের গোলকধাঁধায়। দুঃখের কথা এটাই যে সাম্প্রতিক কালে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা ব্যবসা, দুটোই যে হারে উন্নতি করেছে ডাক্তারদের ব্যক্তিগত জীবনমান (quality of life) প্রায় সেই হারেই নিন্মগামী। এই পরিপ্রেক্ষিতে দগ্ধপ্রাণ চিকিৎসক অর্থাৎ ‘Physician Burnout’ শব্দটি এদেশে এখন বহুচর্চিত। আমাদের চোখের সামনে গত দশ বছরে এই অভিনব ধারণাটি আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ আর ক্যানাডা ছাড়িয়ে চীনদেশ অবধি পৌঁছে গেছে। ২০১৯ সালের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার শতকরা চুয়াল্লিশজন ডাক্তার দগ্ধে দগ্ধে মরছেন, নিজেদের জীবনমান নিয়ে তাঁরা যারপরনাই অসন্তুষ্ট। ডাক্তারদের মধ্যে মাদকাসক্তি, পরকীয়া, ডিভোর্স, অবসাদ, আত্মহত্যা ইত্যাদি বাড়ছে তো বাড়ছেই। সুতরাং হে রোগীবৃন্দ, কৃপা করে অবহিত হোন যে আপনাদের ভগবানতুল্য চিকিৎসকরাও কিন্তু নানান কারণে ক্লিষ্ট। সেই কারণগুলোর সঙ্গে রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, নিরাপত্তাহীনতা থেকে মূল্যবোধের সংকট ইত্যাদি নানান জটিলতা জড়িয়ে রয়েছে। তাকে নগদ ধোলাই দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চাইলে, শেষ অবধি আপনি কিন্তু কুঠার হাতে কালিদাস।

Burnout is a syndrome defined by the 3 principal components. 1) emotional exhaustion, 2) depersonalization, and 3) diminished feelings of personal accomplishment. Unlike major depressive disorder, which pervades all aspects of a patient's life, burnout is a distinct work-related syndrome. Burnout is most likely to occur in jobs that require extensive care of other people. JAMA. 2004; 291(5):633. doi:10.1001/jama.291.5.633
এই সব গল্প আজকে শুরু হয়নি। আজ থেকে তিন দশক আগে আগে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ডাক্তারি দুনিয়ায় প্রমাণনির্ভর চিকিৎসা (Evidence based medicine) কথাটি চালু হয়। সর্বনাশের শুরু সেখান থেকেই। তার আগে ব্যপারটা অনেক সহজ ছিলো। সেই হিপোক্রেটিসের আমল থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে সম্মান, শোভনতা এবং সুনীতির যেমন একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় ছিল ঠিক তেমনটাই ছিল রহস্যময়তার। মানুষের শরীরটা ঠিক কিভাবে চলে এবং অসুখ কেন হয় এই দুই এলাকাতেই শতকরা দশভাগ তথ্য থাকলে বাকি শতকরা নব্বইভাগই ছিল ধোঁয়াটে আন্দাজ আর ব্যক্তিগত মতামত। বিশ শতক শুরু হবার আগে ওষুধপত্রও ছিল হাতে গোনা। সেই আমলে ডাক্তারদের ভাবমূর্তি ছিল কিছুটা আধিভৌতিক, রোগী বাঁচলে তিনি ভগবান, মরলেও প্রায় তাই, শুধু সেক্ষেত্রে রোগীর ভাগ্য খারাপ ধরে নেওয়া হতো। সেই পিতৃতান্ত্রিক যুগে রোগী আর ডাক্তারের সম্পর্কটা ছিল পিতা আর সন্তানের মতন। ইচ্ছে করে কোন্ পিতাই বা সন্তানের অমঙ্গল চাইতে পারেন? তাই সেই আমলে ডাক্তারের গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার আগেও লোকে অনেকবার ভাবতো। তাই বলে ক্ষোভ ছিলোনা এমন নয়, অপচিকিৎসার ধারণাটিও মোটেই অজানা ছিলোনা। রোগীর অসহায়তা আর চিকিৎসকের ঔদ্ধত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর বার্নার্ড শ থেকে শুরু করে পরশুরাম অবধি অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন। আরো বহুকাল আগে সেই খ্রীষ্টপূর্ব দুহাজার সালে লেখা কোড অফ হাম্বুরাবি থেকে অর্থশাস্ত্র, রোমান আইন থেকে¬ ব্রিটিশ কমন ল অবধি সর্বত্রই রোগীর অধিকার নিয়ে কথাবার্তা আছে কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগ করার খুব একটা নজির নেই। আমেরিকার মতন মামলাবাজ দেশেও প্রথম মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাক্টিসের মামলা হয় ১৭৯৪ সালে। অবশ্য সেই আমলে মামলা করে হতোই বা কি? রোগনির্ণয় থেকে চিকিৎসা, সবটাই যখন অনুমাননির্ভর এবং ব্যক্তিগত মতামতের ওপরে নির্ভরশীল তখন গলতি প্রমাণ করাটা সহজসাধ্য নয়। রোমান চিকিৎসাবিদ গ্যালেনের থিয়োরি এক হাজার বছরের বেশি টিঁকেছিল যদিও তার বেশিরভাগই ছিল অর্ধসত্য কিংবা ডাহা ভুল। সেই সময়ে প্রাণের দামও খুব বেশি ছিলোনা। ১৯০০ সাল নাগাদ খোদ আমেরিকায় মানুষের গড় আয়ু (Life expectancy) ছিল মাত্র সাতচল্লিশ বছর, আমাদের দেশে ১৯৫০ সালেও সংখ্যাটা বত্রিশ বছরের বেশি ছিলোনা। সাম্প্রতিক কালে উন্নত দেশগুলোর গড় আয়ু আশি বছর, আমাদের সত্তর। এই বিপুল পরিবর্তনের ভেতরেই অপচিকিৎসা এবং ডাক্তার ঠ্যাঙানোর রহস্য লুকিয়ে আছে।
ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে ডাক্তারবাবুরা তো ভালোই ছিলেন, সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করতো। সেই কবে ছোটবেলায় পাড়ার ডাক্তারজেঠু আর মণি কম্পাউন্ডারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেখে একাধারে সন্ত্রস্ত এবং মোহিত হয়েছিলাম। হাইস্কুলে পড়ার সময় বায়োলজি শিক্ষকের কাছে জানা গেছিল যে ডাক্তারি করা মানে একাধারে বিজ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা এবং লক্ষ্মীলাভ -- যাকে বলে সোনায় সোহাগা, দেবভোগ্য নোবল প্রফেশন। সেই মহান আশা বুকে নিয়ে ১৯৮২ সালে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পরবর্তী সাড়ে সাত বছর যদিও ধাপে ধাপে স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস, তাও নিজেকে কোনদিন ঠিক পুরোদস্তুর হতচ্ছাড়া মনে হয়নি। সেটা শুরু হলো অনেক বছর পরে, যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়ো প্রদেশে, যখন আমি ক্লীভল্যান্ড ক্লিনিক নামক দুনিয়া কাঁপানো হাসপাতাল থেকে ফেলোশিপ শেষ করে, বাকি জীবনটার মাথামুণ্ডু বোঝার চেষ্টায় আছি।
বিশ শতকের প্রথম অর্ধেকটায়, যখন এই পৃথিবীর প্রভুর দল পরস্পরের সঙ্গে মারপিট করতে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়টাতেই বৌদ্ধিক জগতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত বদল (Paradigm shift) হয়ে গেছিল। ইতিহাসে এই প্রথম ব্যক্তির জায়গা নিয়ে নিলো সমষ্টি, নেতৃত্ব চলে গেল প্রতিষ্ঠানের হাতে, মতামত আর সত্য দৃষ্টির বদলে গুরুত্ব পেলো পরীক্ষানিরীক্ষা। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অন্যান্য ধারাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিকিৎসার জগতেও দেখা দিল নানান ম্যাজিক --অ্যান্টিবায়োটিক, ক্যানসার কেমোথেরাপি, এক্স-রে, ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম ইত্যাদি যারা নাকি রোগ নির্ণয় আর চিকিৎসা দুটোকেই আমূল বদলে দেবে। মহাযুদ্ধ শেষ হয়েও হলোনা, তার বদলে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হলো, সেই সঙ্গে চলতে থাকলো টেকনোলজির জয়যাত্রা। ১৯৫০-৫৫ সালের মধ্যে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি যাবতীয় জৈব অণু এবং তাদের আণুবীক্ষণিক কাণ্ডকারখানা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার পরের দুই দশকের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য এবং প্রকৌশল জমা পড়েছে তার এক ভগ্নাংশও কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়, তাই গোটা ব্যাপারটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র দিতেই হবে। তার জন্য দরকার তথ্যপ্রযুক্তি, টিমওয়ার্ক, ম্যানেজমেন্ট এবং বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়। সেই বুদ্ধদেবের আমল থেকেই জরা, ব্যাধি আর মৃত্যু মানুষের মজ্জাগত আতঙ্কের এলাকা। সেখানে আশার আলো দেখাতে পারলে ধনীরা গ্যাঁট খুলতে আপত্তি করবেনা, কিন্তু যাদের পয়সা নেই তাদেরও জোট বাঁধার ক্ষমতা আছে, তারাই বা ছাড়বে কেন? অন্যদিকে লাভের গন্ধ পেয়ে ডাক্তার ছাড়াও আরো অনেক খেলুড়ে মাঠে নেমে পড়েছেন, তাঁরা সকলেই যে যার আইডিয়া বাজারে বেচতে উৎসুক। যে ডাক্তারবাবুরা পাড়ায় পাড়ায় মিক্সচার আর পুরিয়া দিয়ে প্রশান্ত বদনে প্র্যাকটিস চালাচ্ছিলেন, তাঁদের সামনে অজান্তেই একটা চ্যালেঞ্জ খাড়া হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে সেই চ্যালেঞ্জ ছড়িয়ে গেল রাজনীতির ময়দানে। মনে রাখতে হবে যে শুধু প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ-পরবর্তী কয়েক দশক অতিশয় দোদুল্যমান। প্রশ্ন উঠে গেল যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যখন এতটাই উন্নতি করেছে তখন নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা করাটা কি দেশের সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত নয়? এই সব চিন্তাভাবনার ফলে দুনিয়ার তাবৎ উদারপন্থীর স্বপ্ন সফল করে ১৯৪৬ সালে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির স্বাস্থ্যসচিব মিঃ বেভান ন্যাশন্যাল হেলথ সার্ভিস অ্যাক্ট নামক ঐতিহাসিক আইন পাশ করিয়ে ফেললেন। ১৯৪৮ সালের ৫ই জুলাই থেকে ইংল্যান্ডের প্রতিটি নাগরিকের দোলনা থেকে কফিন (Cradle to grave) অবধি সুস্বাস্থ্যের যাবতীয় দায়িত্ব সরকারের কাঁধে চলে গেল। কমিউনিস্ট দুনিয়া তো বটেই, পশ্চিম ইউরোপের ধনী দেশগুলি, ক্যানাডা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া একে একে সকলেই ওই রাস্তায় হাঁটলেন, নতুন স্বাধীন হওয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও একই খোয়াবে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। এই সমাজতান্ত্রিক স্বর্গের বিপক্ষে ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকলো একলা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে চালু রইলো ফ্যালো কড়ি মাখো তেল অর্থাৎ ফি ফর সার্ভিস মডেল। সেই ফি যখন বাড়তে বাড়তে আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে তখন তার মোকাবিলা করতে জন্ম নিলো আরেক দানবিক প্রতিষ্ঠান যার নাম স্বাস্থ্যবীমা অথবা হেলথ ইন্সিওরেন্স।
ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার বনাম প্রাইভেট হেলথ কেয়ার অর্থাৎ ইউরোপ বনাম আমেরিকা — এই তাত্ত্বিক জঙ্গলে প্রবেশ করার আগে দেশি অপচিকিৎসা নিয়ে কয়েকটা দরকারি কথা না বলে নিলেই নয়। ডক্টর কুণাল সাহার টার্গেট, কলকাতার সেই সব তথাকথিত অপচিকিৎসকরা আসলে আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন। সত্তর থেকে আশির দশকে সেই সব রথী মহারথী এবং তাঁদের গুরুরা প্রায় সবাই ব্রিটিশ মডেলে ট্রেনিং পেয়েছেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ ডাক্তারদের যাবতীয় মুদ্রাদোষ পরম শ্রদ্ধায় নকল করেছেন। ব্রিটিশরা রক্ষণশীল জাত, তারা নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণ করেও ডাক্তারির সাবেক চালটা বজায় রেখে দিয়েছিল। সেই ডাক্তারের ইমেজ অনেকটাই পিতৃপ্রতিম, খানিকটা গাম্ভীর্য, খানিকটা বৈদগ্ধ, খানিকটা রহস্যে জড়ানো। ইংল্যান্ডের সাবেক বাসিন্দারা নিয়ম আর ট্র্যাডিশন মেনে চলতে ভালোবাসে, কিছুদিন আগে অবধি তারা যে-কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিই বেজায় শ্রদ্ধাশীল ছিল। ন্যাশন্যাল হেলথ সার্ভিস তাদের শরীর স্বাস্থ্যের যথাযথ দেখভাল করছে, এই নিয়ে তাদের সন্দেহ ছিলোনা, তার জন্যে ট্যাক্স দিতে তাদের আপত্তি হয়নি। সরকারী স্বাস্থ্যদপ্তরগুলোয় যোগ্য লোকেরা কাজ করেছে, নতুন যন্ত্রপাতি, ওষুধ এবং প্রকৌশল, সবই এসেছে ধীরে ধীরে, পেশাদারী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং যথাসম্ভব ভ্রষ্টাচার মুক্ত পরিবেশে। তার মানে এই নয় যে সাহেবরা নীতিগতভাবে আমাদের তুলনায় উচ্চস্তরের জীব। পশ্চিম দুনিয়ায় যে কেউ, অতি বাড় বাড়ার চেষ্টা করলেই পা পিছলে প্রশাসনিক গাড্ডায় পড়ে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আইন কারোকে ছেড়ে কথা বলবেনা -- সে তুমি প্রেসিডেন্ট হও কিংবা ধর্মগুরু বা রক স্টার। এই প্রবন্ধের লেখক হাড়ে হাড়ে জানেন যে সামনে বসে থাকা ভিজে বেড়াল পেশেন্টটি ঠিকঠাক সুযোগ পেলেই এক টানে তাঁকে উলঙ্গ করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম। এই উপলব্ধিই তাঁর বিচার, ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলে প্রতিদিন। কিন্তু সেই ষাট-সত্তরের দশকে আমাদের মাস্টারমশাইরা যখন বিলেতফেরত হয়ে দেশীয় বাজারে বিরাজমান হলেন তখন তাঁদের পরিস্থিতিকে যাদুবাস্তবিক ছাড়া কিছুই বলা যায়না। একদিকে তাঁরা সাহেব মানুষ, কলকাতার উৎকট গরমেও নিয়মিত স্যুট-টাই পরে হাসপাতালে আসেন কিন্তু লন্ডন কিংবা এডিনবরায় যে পরিবেশে তাঁরা শিক্ষিত হয়েছেন, দেশে কোথাও তার চিহ্নও নেই। সরকার ব্রিটিশ মডেলে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ব্লুপ্রিন্ট বানিয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে যে বাজেট তা দিয়ে ইংল্যান্ড, জার্মানি কিংবা আমেরিকার কোনো হাসপাতালে ঝাড়ুদারদের (এদের ভাষায় custodian) মাইনেও দেওয়া যাবেনা। ভারতবর্ষ তো কিউবা নয় যে সরকার ঘাড়ে ধরে সবার মাইনেপত্র ঠিক করবে, যেখানে ডাক্তার আর ঝাড়ুদারের মাইনে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় সমান, তফাৎ শুধু সম্মানে আর সামাজিক সচেতনতায়। সাহেবরা বিদায় নিয়েছে বটে কিন্তু নেহরু পরিবারের নেতৃত্বে দেশটা তার ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে এক কদম পিছু হঠতেও অপারগ। সেই বিভ্রান্তিকর পরিবেশে বাধ্য হয়ে বিলেতফেরত ডাক্তারবাবুরা শিক্ষকও হলেন, তার পাশাপাশি প্রাইভেট প্র্যাকটিসেও নেমে পড়লেন। এমন একটা পরিবেশের সূচনা হলো যেখানে পেশাদারি মনোভাবের চেয়ে চালবাজি দেখে জনতা মুগ্ধ হয়, দ্বিচারিতা অর্থাৎ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড যেখানে পরম ধর্ম। আশির দশকে আমরা যখন ডাক্তারি পড়তে গেছিলাম বাকি দুনিয়ায় তখন তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে অথচ কলকাতায় আমাদের সে সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ ধারণাও নেই। সারা দিনে আমাদের এতবার সশ্রদ্ধ কণ্ঠে ‘স্যার’ কথাটা বলতে হতো, আর গরমকালে স্যুট পরিহিত মাস্টারমশাইদের আমরা এতটাই সুপারম্যান মনে করতাম যে বাকি দুনিয়ার হালহকিকৎ সেখানে বিলকুল অবান্তর ছিল। আজ, এতটা পথ পেরিয়ে এসে সেই সব মাস্টারমশাইদের জন্য আমার মনে মনে করুণা হয়। ওঁদের যে রোগে ধরেছিল তার দুটো উপসর্গ -- একটার নাম এনটাইটেলমেন্ট (entitlement) অন্যটা ইমপিউনিটি (impunity)। এই সব শব্দের বাংলা কি খোদায় মালুম কিন্তু মোদ্দা কথা এই যে নিজেদের আভিজাত্য এবং প্রশ্নহীন বিশ্বাসযোগ্যতা, সাধারণবিচার বিবেচনার ঊর্ধে নিজেদের অবস্থান নিয়ে কোনরকম সংশয় ওঁদের মনে ছিলোনা। গোটা সমাজটাই যখন কুয়োর ব্যাং এবং বাক্সের কাঁকড়াদের রাজত্ব সেখানে বিগত যুগের ধ্যানধারণা যে ওঁদের কাছে অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয় মনে হয়েছিল, তাই নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই। সেই ধ্যানধারণা অনুযায়ী ওঁরা অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত মতামতের ওপরে যতখানি নির্ভর করতেন, তথ্য, প্রমাণ এবং প্রযুক্তির ওপরে তার এক শতাংশও নয়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের যে বীজমন্ত্র -- তথ্যনির্ভর চিকিৎসা (Evidence based medicine) -- সেই পুরো গল্পটাকেই ওঁরা সযত্নে পরিহার করে চলেছিলেন। তাঁদের চ্যালা হিসাবে আমরা নব্বইয়ের দশকে পুরোদস্তুর বিভ্রান্ত এক ডাক্তারি প্রজন্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলাম। আমাদের মধ্যে যারা বিদেশে পালিয়েছিলাম তাদের নতুন শিক্ষা পাবার আগে প্রচুর কষ্ট করে পুরনো শিক্ষা ভুলতে হলো। যারা বুক ঠুকে দেশে রয়ে গেল তাদের জন্য রইলো এক অদ্ভুত অন্ধকার। না ঘরকা, না ঘাটকা, না ব্রিটিশ, না কিউবান, না রাশিয়ান না আমেরিকান এবং সবচেয়ে ভয়ানক -- না ভারতীয়, কেননা ভারতীয় স্বাস্থ্যনীতি বলতে কি বোঝায় তাই কেউ ভালো করে জানেনা।
স্বাধীনতার পরে আমরা গড়ে তুলেছিলাম দুনিয়ার সবচেয়ে অগোছালো আর অনিয়ন্ত্রিত এক স্বাস্থ্যব্যবস্থা। একদিকে জনতার সামনে শিখণ্ডীর মতন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে দাঁড় করানো হয়েছে সেটা ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ারের মডেলে গড়া যদিও হেলথ কেয়ার ট্যাক্স বলে এদেশে কোনো বস্তু নেই। তার পাশাপাশি গড়ে উঠলো অজস্র ছোটবড়ো নার্সিং হোম, ওষুধ কোম্পানি, ডায়াগনোস্টিক ল্যাবরেটরি, রেডিওলজি সেন্টার, তারা সবাই ইচ্ছেমতন চুটিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করে দিল। তারা ফি-ফর-সার্ভিস মডেল অনুসরণ করছে কিন্তু সেখানে কোয়ালিটি কনট্রোল বা স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার বলে কিছু নেই, কিংবা থাকলেও তারা নখদন্তহীন। পশ্চিম দুনিয়ায় প্রতিটি অসুখ এবং তাদের চিকিৎসার একটা গুণগত মান (standard of care) বেঁধে দেওয়া আছে সেখানে হিসাব না মিললে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানকে জবাহদিহি করতে হবে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রতিটি ছোটোবড়ো বিষয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, বেডপ্যান থেকে সি-টি-স্ক্যান অবধি সবকিছুর ওপর নিয়মিত নজর রাখার জন্য হাজার রকম বোর্ড আর কমিটি সহস্রচক্ষু হয়ে পাহারা দিচ্ছে। সেখানে পান থেকে চুণ খসলেই সাইটেশন অথবা জরিমানা তো হবেই, চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। অন্যদিকে সাবেক সোভিয়েত দুনিয়ায় সরকারই মা-বাপ, তিনি বিনাপয়সায় যা দিচ্ছেন তাই নিয়ে সকলের খুশি থাকা বাধ্যতামূলক। সেই স্বর্গে সবাই সমান, শুধু কেউ কেউ বেশি সমান, তাঁরা দরকার মতন বিলেত-আমেরিক পাড়ি দেন। আমাদের দেশে পয়দা হল এক অদ্ভুত খিচুড়ি ব্যবস্থা। রোগী এবং ডাক্তার সকলেই এক অদ্ভুত বিপন্নতার স্রোতে ভাসমান, যেখানে কপাল ভালো থাকলে খুবই ভালো চিকিৎসা হতে পারে, কপাল খারাপ থাকলে অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তি। এমত অবস্থায় চোখের সামনে স্টেথোস্কোপধারী যাকে পাওয়া যাচ্ছে তাকেই নির্বিচারে পেটানোর সংস্কৃতি চালু হয়ে গেছে। ফলত হাসপাতালগুলোয় এখন আতঙ্কের পরিবেশ এবং নতুন পাশ করা আতঙ্কগ্রস্ত ডাক্তার ওঝার থেকেও খারাপ। পারস্পরিক আস্থার অভাব হলে ডাক্তার-রোগী সম্পর্কটাই দাঁড়ায় না, সার্থক চিকিৎসা সেখানে অসম্ভব। সমস্যাটা শুধু ডাক্তারের নয়, যে সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ডাক্তারকে তৈরি করেছে সমস্যাটা আসলে সেখানেই। দায়বদ্ধতার খোঁজে বেরোলে সারা সমাজটাকেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে, শুধু যখন যাকে বেকায়দায় পাওয়া যায় খবরের কাগজে তার গুষ্টির তুষ্টি করলেই চলবেনা।
আদত কথা এটাই যে অপচিকিৎসা আসলে সর্বব্যাপী। যেহেতু আমরা এই মুহূর্তে আমেরিকাকে দাদা মেনেছি, তাই সেখানকার অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখতেই হবে আমাদের। অনেকের মতে এখানেও ঘোরতর অপচিকিৎসা চলছে। এভাবে চলতে থাকলে মরার আগে আপনি রোবট ছাড়া কারুর দেখা পাবেন না। আমেরিকায় যা কিছু হয় তার কুলকুণ্ডলিনীতে থাকেন মুনাফা। ডাক্তারি শাস্ত্রের তিনটি প্রধান বিভাগ রয়েছে -- ওষুধপত্র বা ফার্মাসিউটিক্যালস, রোগনির্ণয় বা ডায়াগনোস্টিকস এবং গবেষণা বা রিসার্চ। আমেরিকায় এই তিনটির সঙ্গেই বেসরকারি বিনিয়োগ এবং শেয়ার বাজারের গভীর সম্পর্ক। এঁদের মতে শুধু হেলথ কেয়ার নয় দীনদুনিয়ার যে কোনো এলাকার অবাধ বিকাশ নির্ভর করে তার বাজারদরের ওপর। যেহেতু বেসররকারি পুঁজি মুনাফা না হলে স্বয়ং ভগবানের দিকেও ফিরে তাকায় না তাই এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা বেশ একটা লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠতে পারে। কট্টর বাজারপন্থীদের মতে এটাই একমাত্র উপায় কেননা মুনাফা না থাকলে প্রগতিও বন্ধ হয়ে যাবে, পয়সা উসুল হবেনা এবং ইউরোপের উদারপন্থীরাও বৃহন্নলার দশা প্রাপ্ত হবেন। মোদ্দা কথা আমেরিকা হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের এঞ্জিন, সে আছে বলেই খোলা বাজার আছে, ইউরোপ, জাপান বা অস্ট্রেলিয়া সেই এঞ্জিনের সঙ্গে লটকে দেওয়া ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট, তাদের পেছনে সেকেন্ড ক্লাস এবং থার্ড ক্লাসে দুনিয়ার বাকি সকলে ঝুলে রয়েছে। মজা এইখানে যে লাভের সম্ভাবনা থাকলে পয়সা ঢালতে এদের আপত্তি নেই, ১৯৫০ সাল থেকে এখন অবধি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বায়োমেডিক্যাল গবেষণা বাবদ যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে তা এক কথায় অমানুষিক। ২০১৯ সালে এই বাবদে সরকারি বাজেট ৩৯ বিলিয়ন ডলার, যার কর্ণধার ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ সংক্ষেপে NIH, যার কৃপা প্রার্থনা করে এই অধম লেখক সমেত অনেক রথী মহারথী বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে কম করে আরো পাঁচগুণ। লক্ষ লক্ষ প্রপোজাল এবং প্যাটেন্ট রং মাখা বেশ্যার মতন দাঁড়িয়ে থেকেছে ওয়াল স্ট্রীটের ফুটপাথে। বেছে বেছে তাদের মধ্যে যারা সম্ভাবনাময় তাদের তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়েছে ওয়াল স্ট্রীট, সেই সব রাত্রির নিবিড় অভিঘাতে পরের দিন নড়াচড়া করেছে শেয়ার বাজার। এই রাজসূয় যজ্ঞের ইন্ধন যোগাতে হাজির আছেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানিরা, তাঁরাও প্রতি বছর প্রিমিয়াম বাড়িয়ে চলেছেন। ওদিকে হাসপাতালের আশেপাশেই ওঁত পেতে বসে আছেন মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাক্টিসের উকিলবাবুরা, আমেরিকার যে কোন হাইওয়ের দুপাশে বড়ো বড়ো হোর্ডিং জোড়া তাঁদের হাসিমুখ জ্বলজ্বল করছে। স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ারের এক চুল এদিক ওদিক হলেই নগদ টাকার ক্ষতিপূরণ। তাঁদের খিদে মেটাতে ডাক্তারবাবুরাও মোটা দরের ম্যালপ্রাক্টিস ইন্সিওরেন্স করে বসে আছেন, সেই টাকাও হয় পেশেন্টের পকেট থেকে আসছে, নয় সরকারি তহবিল থেকে। টাকার পেছনে টাকা ছুটছে, কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলছেনা কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে একটা সমঝোতা রয়েছে। এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক আর পাঁচটা সার্ভিস সেক্টরের মতন, সেখানে সব কিছু শর্ত মেনে বিনিময় হয়, মতের অমিল হলে প্রথমে সালিশি তারপরে কোর্টকাছারি কিন্তু তার মধ্যে পুলিশ, গুণ্ডা বা পলিটিশিয়ানদের কোনই জায়গা নেই। সরকারের কতগুলো নীতি আছে যেমন মেডিকেয়ার (৬৫ বছরের বেশি বয়েসী নাগরিকদের জন্য সরকারী ইন্সিওরেন্স যার প্রিমিয়াম হিসাবে সরকার আগে থেকেই ট্যাক্স নিয়ে রেখেছে। প্রতিবন্ধী এবং ডায়ালিসিসের রোগীরা যে-কোন বয়সে এই সুবিধা পেতে পারেন) এবং মেডিকেইড (দারিদ্রসীমার তলায় বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য রাজ্য সরকারগুলির দাতব্য ইন্সিওরেন্স)। মনে রাখতে হবে ইন্সিওরেন্স সরকার দিলেও চিকিৎসা কিন্তু সেই প্রাইভেট হাসপাতালেই হচ্ছে, এবং সেখানেও স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার একই, ওষুধপত্রের একই দাম। সরকার সরাসরি দায়িত্ব নিয়েছেন শুধু বিশেষ কয়েক জাতের লোকেদের -- এক পাগল, দুই কয়েদী, তিন রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যারা এখনও টিঁকে আছে, এবং চার সৈন্যবাহিনী, যারা নাকি দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রান্তে মারদাঙ্গা করে নিজেরা ল্যাংড়া, নুলো, হতবুদ্ধি এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছে। বাকি লোকজনের দায়িত্ব প্রাইভেট হাসপাতাল আর ক্লিনিক যাদের খাজনা যেমন বাজনাও তার থেকে কম নয়। সারা দুনিয়ার মধ্যে আমেরিকায় চিকিৎসা বাবদ খরচ হয় সবথেকে বেশি -- ২০১৭ সালের হিসাব মোতাবেক সংখ্যাটা ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার, মাথাপিছু বছরে ১০৭২৯ ডলার, জি-ডি-পি’র ১৭.৯ শতাংশ, অন্যান্য ধনী দেশগুলোর তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ বেশি। এই বিপুল অর্থব্যায় সত্ত্বেও দেশটার স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান উদ্ভট রকম পরস্পরবিরোধী। চিকিৎসার মান এবং দ্রুতি (quality and speed of medical care) এখানে প্রথম শ্রেণীর কিন্তু নাগরিকদের গড় স্বাস্থ্য আর আয়ুর দিক থেকে বিচার করলে আমেরিকার জায়গা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বেশ তলার দিকে।


Data Source: WHO. Life expectancy at birth (years) Mortality and global health estimates. 2015. http://apps.who.int/gho/data/node.main.688 Updated: September 11, 2015. Accessed: November 10, 2016.
All other OECD countries with health expenditures more than 10% of GDP have a lower infant mortality rate and a higher life expectancy than the United States.
উপরের পরিসংখ্যানগুলো খুঁটিয়ে দেখলে যা বোঝা যাবে তা আমরা সবাই জানি কিন্তু মানতে চাইনা। যেসব দেশে সম্পদ বেশি, জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং যেখানে লোকে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়না সেখানে ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ারের তুলনা নেই। কিন্তু সমাজ যেখানে বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যময়, যেখানে অজস্র সামাজিক স্তর, ইমিগ্রেশন, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকারি, ভ্রষ্টাচার, ট্যাক্স ফাঁকি সেখানে সমস্যাটিও আড়াইপ্যাঁচি জিলিপির মতন জটিল। আমেরিকার সাদা শহুরে ভদ্রলোক জনতা (চট করে বলে দিই, ভারতীয়রা নিজেদের সাদা ভাবে) চড়া দামে স্বাস্থ্য কিনতে রাজি, তারা ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার মোটেই চায়না। অন্যদিকে কালো, গরীব আর ইমিগ্র্যান্টদের গল্প একদম আলাদা, তারা যতটা পারে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে চায়। এদিকে বাজারে প্রতি বছর নতুন নতুন বিশল্যকরণী ওষুধ আর প্রাণদায়িনী যন্ত্রপাতির আমদানি হয়ে চলেছে সেখানে আরোগ্য যতটা লক্ষ্য, মুনাফাও ততটাই। জীবনের শেষ কয়েকটি বছরে মানুষকে কোনওরকমে জ্যান্ত রেখে দেবার জন্য খর্চা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ ডলার। এ কথা ভাবা হয়নি যে দশজনকে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার বদলে একশো জনকে অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কিনা। বরং ওই দশজন আই-সি-ইউ রোগীর ইন্সিওরেন্স থেকে কোটিখানেক ডলার কামিয়ে নেবার দিকেই বুঝি ডাক্তার-হাসপাতাল সকলের নজর। কাজটা সাবধানে করতে হবে কেননা কোথাও ভুলচুক হয়ে গেলেই উকিলবাবুরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাঁরা অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে ছোটেন, হাসপাতালের ঘরে ঘরে গিয়ে রোগীকে নিজেদের কার্ড ধরিয়ে আসেন, বাচ্চা হবার দশ বছর পরেও গাইনিকোলজিস্টের পিছু ছাড়েননা, কে জানে হয়তো বা ডাক্তারের দোষেই বাচ্চা পরীক্ষায় ফেল করছে। এই পরিবেশে ডাক্তার অগ্নীশ্বর ঘোরতর অপ্রাসঙ্গিক। এই বাজারে আদর্শ এবং করুণার কোনই জায়গা নেই, সেবা, সহমর্মিতার মুখোসের আড়ালে সবকিছুই এখানে যান্ত্রিক ও হিসেবী। ডাক্তার নানান দিক থেকে চাপে থাকতে থাকতে হুঁশিয়ার, সে নিজের স্বার্থ বাঁচাতে ব্যস্ত, তাকে একই সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক অথচ পেশাদার হতে হবে যাতে রোগীকে পরামর্শ দেবার আগে বিজ্ঞান এবং মানবতা বাদ দিয়ে আরো দশটা দরকারি জিনিস খতিয়ে দেখা যায়। ইন্সিওরেন্স কোম্পানি সর্বদাই ধান্ধায় আছে কি করে পয়সা কাটা যায়, ডাক্তার ভাবছে বিলটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিতে পারলে অন্তত কিছু তো আদায় হবে, উকিল ভাবছে ডাক্তার ব্যাটা একটা ভুল করলেই পোয়াবারো, তখন বুকে বাঁশ ডলে দশগুন পয়সা উসুল করা যাবে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছেনা, সরকারী আমলা, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি, চিকিৎসক, উকিল এবং রোগী, সবাই একে অপরের শত্রু। মাঝখান থেকে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠছে শুধু নথিপত্র আর ব্যুরোক্র্যাসি। পরিচালক মাইকেল মূর তাঁর “সিকো” তথ্যচিত্র এই হৃদয়হীন মুনফাবাজ স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে তুলোধোনা করেছেন, যদিও কোনো সমাধান দিতে পারেননি। কেই বা পেরেছে? হাজার হোক, দুনিয়ার সব মুল্লুক থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা আমেরিকার দিকে আসছেন তো আসছেনই। কেননা এখানে আছে নগদ টাকার ঝনঝনানি। ডাক্তাররাও তো মানুষ তারা কি করে বাকি সমাজটার থেকে পৃথক হবেন?
সেও তো প্রায় এক যুগ হতে চলল, প্রেসিডেন্ট ওবামা যখন তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার খোল নলচে বদলাতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই রূপকথার সকালবেলায় অনেকের সঙ্গে এই অধম প্রবন্ধ লেখকও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। ওবামা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ সাধ্যমতন ট্যাক্স দিক, তার সাধ্যে না কুলোলে সরকার সেই পরিমাণ অর্থ জমা করবেন। সারা দেশে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ইন্সিওরেন্স এক্সচেঞ্জ চালু হোক যাতে প্রত্যেকটি লোক স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আসে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্ত নথি কম্পিউটারে জমা হবে, হাসপাতালের প্রতিটি ঘর থেকে ডাক্তাররা সেই নথিপত্র দেখতে পাবেন। একই পরীক্ষা যাতে বারংবার না হয়, প্রতিটি মানুষ যাতে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবার পুরো হদিশ রাখতে পারবেন। হায়, আজ ট্রাম্পের রাজত্বে বসে আমরা নেই-আশার সমাধির দিকে তাকিয়ে বসে আছি। কিছুই বদলায়নি, না মানুষ না প্রতিষ্ঠান। হাসপাতাল, ম্যালপ্র্যাকটিস, ওষুধ কোম্পানি, বীমা কোম্পানি, এতদিন এই চারটি আটশো পাউন্ড গরিলা প্রতিটি ডাক্তারের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল। প্রেসিডেন্ট ওবামার কল্যাণে আজ তার ওপরে আগুন ফোঁকা গডজিলার মতন হাজির হয়েছে ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড। এবার ক্লিনিকে বসে হাঁচি কাশি, বাহ্য, প্রস্রাব সবকিছুর হিসাব রাখতে হবে নইলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানি এক পয়সাও ঠেকাবে না।
সব মিলিয়ে আটলান্টিকের এপারেও এখন ঘোরতর অপচিকিৎসার পরিবেশ। তফাৎ শুধু একটা জায়গায়। এখানে সবাই আইনের শাসনে বিশ্বাস করে। হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই ধরে ধোলাই দেবার মতন অসামাজিক মনোবৃত্তি এদের নেই। সেইরকম কোন ঘটনা যদি ঘটেই যায় তবে সুশীল সমাজের একজনও -- সে ডাক্তার হোক কিংবা উকিল, রাজনীতিবিদ অথবা সাংবাদিক, বেকার কিংবা বাউণ্ডুলে, অধ্যাপক কিংবা আর্টিস্ট, কেউ কিন্তু গুণ্ডাদের স্বপক্ষে এবং ডাক্তারদের বিপক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করবেন না। তাঁরা সকলে চাইবেন যে আইন তার পথে চলুক, যে বেআইনি কাজ করছে তার শাস্তি হোক। সেইখানেই কিপলিং তাঁর অসহ্য থিসিস নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছেন আর এতদিন বাদেও আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি।
OH, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat;
একটার পরে একটা দিন আসে আর চলে যায়, আমার গায়ে কেউ হাত তোলেনা, কিন্তু আঘাতের যন্ত্রণা আর অপমান আমার বুকের মধ্যে ঘুরপাক খায়। আমার মাথার ভেতরে একটা পুরনো গানের সুর ডানাকাটা পাখির মতন ঝটপট করতে থাকে।
হায় সেই নাড়ি টেপা শাস্ত্র,
ভোঁতা সূঁচ, বেঁকে যাওয়া অস্ত্র,
স্টেথোস্কোপের সেই ফিসফাস,
রোগীদের চোখে ভরা বিশ্বাস,
হায় সেই আঁকা বাঁকা, প্রেসক্রিপশন লেখা, কাগজের স্মৃতি আমি বহি রে।
(পরবাস-৭৮, ৮ই এপ্রিল, ২০২০)
অলংকরণ: আন্তর্জাল থেকে