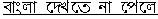দেশ ছেড়ে সেই যে এলাম এর পরে বেশীদিন দেশে থাকা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু ও শেষের মধ্যেই দেশের বাড়ির পরিবেশে মানুষদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ ছিল, সেই মিলনের পরিবেশে বিঘ্নিত হতে শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমাদের পরিবারের এক পূর্বপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমাদের মনে পড়ে গেল। তিনি নাকি বলেছিলেন যে, তাঁর বংশের সপ্তম পুরুষে দেশছাড়া হতে হবে। ঘটনাটা শুনেছিলাম আমার বাবার মুখে। কাহিনীটা ছিল এইরকম....
আমার পিতৃকূলে অনুপনারায়ণ আমে এক সিদ্ধপুরুষ জন্মেছিলেন। আমার বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের চারপুরুষ আগের মানুষ তিনি। আমার বাবা ছিলেন পঞ্চম পুরুষ। আশৈশব তিনি ছিলেন সংসারের প্রতি মোহহীন, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকতেন সর্বক্ষণ। এগারো কি বারো বছর বয়সেই পুত্রের মধ্যে সংসার বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখে, পুত্রের কোষ্ঠীর গণনা মনে পড়ে যায় বিধবা মায়ের। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে সংসারের বাঁধনে বাঁধবার ব্যবস্থা করলেন। আট বছর বয়সী এক কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু যিনি ঈশ্বরপ্রেরিত, নরদেহে ঈশ্বরীয় অনুভূতি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁকে কি সংসারের মায়া বাঁধতে পারে! যেমন পারেনি নিমাইকে, বুদ্ধদেবকে, তেমনি পারল না আমাদের পূর্বজ সেই সিদ্ধপুরুষ অনুপনারায়ণকে।
বিবাহের দুই বছর পর বধূর সন্তানসম্ভাবনায় অন্তরে বিচলিত হয়ে পড়লেন। সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ার পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয়ে যাচ্ছে দেখে গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবাল্য সহচর এক বিশ্বস্ত গৃহভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে এক রাত্রে গৃহত্যাগ করলেন। নৌকাযোগে চলে গেলেন কাশীধামে।
সারা উত্তরভারতে তখন বারাণসী অর্থাৎ শিবপুরী কাশী ছিল সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল, সাধনার উপযক্ত স্থান, অনাথা বিধবাদের নিরাপদ আশ্রয়। কাশীতে মৃত্যু ছিল বার্ধক্যের স্বপ্ন। আমার অনুমা অনুযায়ী সে সময়কাল নদেরচাঁদ নিমাইয়ের সমকালই হবে, প্রায় পাঁচশো বছর আগেকার কথা। সে সময় কাশীতে গৃহনির্মাণ করে বা মঠ-মন্দির স্থাপন করে বসবাস করার সুবিধা ছিল, সস্তাও ছিল নিশ্চয়ই। এছাড়া সেখানকার ধনী মানুষেরা, রাজা, মন্ত্রীরাও অকাতরে দানধ্যান করতেন। ব্রাহ্মণ, সাধু সন্ন্যাসী হলে তো কথাই ছিল না। সেখানে তিনি কিভাবে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন, ধ্যান-জপে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠেছিলেন সে বিবরণ কেউই জানতেন না। তবে যে ঈশ্বর-সাধনা, ঈশ্বরের সান্নিধ্য-লাভের জন্য যে তিনি কিশোরী স্ত্রী ও মাকে ত্যাগ করেছিলেন সে উদ্দেশ্যে তাঁর সফল হয়েছিল।
দীর্ঘকাল পরে তিনি নিজের মৃত্যু সমাসন্ন বুঝে, নিজের মঠে প্রতিষ্ঠিত বাণলিঙ্গ শিব, নারায়ণের পিতলের তৈরি অপুর্ব এক মূর্তি, আর নারায়ণ শিলা তিনি তিনি নিজের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভৃত্যকে দেবমূর্তিসহ দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেন ও হাতচিঠিতে লিখে জানান, "আমি যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের খোঁজে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আমার পূর্বজীবনের সংসারে যদি কোন নূতন অতিথি আসিয়া থাকে তবে তাহার নাম যেন প্রেমনারায়ণ রাখা হয়। আর এই বংশে পঞ্চম পুরুষে একজন সিদ্ধপুরুষের জন্ম হইবে, কিন্তু পরবর্তী জীবন তাঁহার কষ্টে কাটিবে। আর সপ্তম পুরুষে এই পরিবার ভিটেমাটি ছাড়া হইবে।"
শেষের ভবিষ্যদ্ববাণীটি সফল হয়েছিল সেই সপ্তম পুরুষেই। আমার ভাইপো হল সেই সপ্তম পুরুষ। রাজনৈতিক কারণে দ্রেশ থেকে বহিষ্কৃত আমার বড়দার বড় পুত্র শঙ্কর, যার কথা আগে এক-জায়গায় লিখেছি। তার কৈশোরেই আমাদের দেশছাড়া হতে হল, খন্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভের দাম চুকাতে। অপরদিকে, পঞ্চম পুরুষ, আমার বাবা, সত্যই একজন সিদ্ধপুরুষের মত সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ কোনও দিন বাদ দেননি। একবার বাংলাদেশ থেকেই তিনি কামাখ্যা গিয়েছিলেন, সেখানে আমার সেজদিদির শ্বশুরবাড়ি ছিল। সেই কামাখ্যা মন্দিরে একদিন দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে, ব্রাহ্মমুহূর্তে আত্মমগ্ন হয়ে বিরামহীন জপ করতে করতে জীবন্ত মায়েরই সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ক্ষণিকের জন্য।
অনুপনারায়ণ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর দিব্য-ঘটনা পরিবারের মানুষ শুনেছিলেন সেই ভৃত্যের কাছে। পরে কাশী-নিবাসী আমাদের গ্রামের অনেকের কাছে শুনেছিলেন আমার বাবা। ইচ্ছামৃত্যু ব্রহ্মচারী নিজের মৃত্যু দিনক্ষণ নিজেই স্থির করেছিলেন। অনুপনারায়ণের প্রেরিত সেইসব দেবমূর্তি আজও আমার দাদার গৃহে নিত্য-পূজিত হন। অপূর্ব নারায়ণ মূর্তিটির নাকমুখ প্রায় সমান হয়ে গেছে মূর্তির গাত্রমার্জনা করতে করতে। এবার আসি তাঁর তনুত্যাগের আশ্চর্য ঘটনার কথায়।
ব্রহ্মচারী যেদিন গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেছিলেন সেদিন সকালে উঠে নিজের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের দরজার সামনে পঞ্চবটিটি সাজানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ভৃত্যকে। বলেছিলেন, "আজ মধ্যাহ্নে, সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিষ্ঠান করবেন সে সময় আম দেহত্যাগ করব।"
প্রভাতে গঙ্গাস্নান করে এসে বসেছিলেন আসনে। আর নিজ উক্ত নির্ধারিত সময়েই দেহত্যাগ করেন। প্রিয় সহচর ভৃত্যটি প্রভুর সৎকারের পর প্রভুর নির্দেশমতোই বিগ্রহগুলি গলায় ঝোলানো থলিতে নিয়ে সাশ্রু-নয়নে দেশে ফিরে এসেছিল।
দেশভাগের পর, এদেশে এসে বাবা প্রথমেই গিয়েছিলেন কাশীধামে। সেই সিদ্ধবাক্ মহাপুরুষের পুণ্য পদরজ-স্পর্শ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই ছিল তাঁর কাশী-যাত্রা। কাশীর বৃদ্ধ পান্ডাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে অনুপনারায়ণের সাধন মন্দিরের খোঁজ পেয়েছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন ধ্বংস্তূপে পরিণত হওয়া শিবমন্দিরের। অনেক নিরীক্ষণের পর মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পড়ে থাকা একখন্ড পাথরের উপরে লেখা একটি নামের আদ্যক্ষর দুটি পড়তে পেরেছিলেন। সব অক্ষর মুছে গেলেও অনু.....অক্ষর দুটি উদ্ধার করেছিলেন। এরপর বাবা যে কয়েকদিন কাশীতে ছিলেন সেই ক'দিনই, সেই মহাত্মাকে অনুভব করার আশায় সেই স্থানে গিয়ে বসে থাকতেন দিনের অনেকটা সময়। তবে, এদেশে আমাদের শিকড়হীন অবস্থায় ফেলে গেছেন, তাই অবিলম্বেই ফিরে এসেছিলেন নৈহাটিতে।
চলে যাই অন্য কাহিনীতে।
এবার পঞ্চম পুরুষের এক কন্যা, আমার পিসিমার কথা একটু লিখি। আগেই লিখেছি মাত্র দশ বছরের মেয়ে পিসিমা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। কাশীর প্রসঙ্গ উঠতে তাঁর রঙহীন জীবনের কথা একটু লিখতে মন চাইল। আমি বা আমরা ছোটরা আমাদের ছেলেবেলায় পিসিমাকে দেখিনি, বহু পূর্বেই তিনি কাশী-বাসী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের উপান্তে আমি তাঁকে দেখেছিলাম যেদিন তিনি দীর্ঘকাল পরে একবার এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তাঁর রূপের বর্ণনা বা জীবনের ঘটনা সবই ছিল মা-জ্যাঠাইমার কাছে গল্প শোনা। তবে তাঁকে দেখবার দিনটি আমি আজও ভুলতে পারিনি। তাঁর দিব্য-কান্তি রূপের বর্ণনা আমি ঠিকমত লিখতে পারব কিনা জানি না।
বাল্যবিধবা পিসিমা দীর্ঘকাল ভাদের পরিবারে কাটানোর পর কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখনকার দিনে মেয়েদের নামে সম্পত্তি থাকতো না। বাংলাদেশে পরিবারে মেয়েদের তো কোনদিনই বংশের কেউ মনে করা হত না। তবে ভারতের কোথাও মেয়েদের যে নিজের বংশের কেউ ভাবা হয় না সেটা তো সত্যি। মেয়ে মানেই সে পরের ঘরে যাবার বস্তু মাত্র। তাই সম্পত্তিতে তাদের অধিকার থাকতে পারে সেকথা শ্বশুরকুল, পিতৃকুল কোন কুলেই ভাবা হতনা। পিসিমার ক্ষেত্রেও সেটার ব্যাতিক্রম হয়নি। শ্বশুরগৃহে স্বামী না থাকলে বেশীর ভাগ বিধবার আশ্রয় হত বাপের বাড়িতে। দু-একজন ভাগ্যবতীর ভাগ্যে থাকলে শ্বশুর বাড়িতে ভিটেতে থাকার সুযোগটুকু পেতেন, তবে সেরকম ঘটনা খুবই বিরল ছিল।
পিসিমার কাশী যাওয়ার ইচ্ছা শুনে বাবা পিসিমাকে নিজে সঙ্গে করে কাশী নিয়ে যান। সেখানে তখন এইসব কাশীবাসীদের জন্য স্বল্প ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যেত। অনেক বিধবা মেয়েরা, প্রৌঢ়ারা একসঙ্গে একটি বাড়িতে থাকতেন, তবে আলাদা আলাদা। পিসিমাও গিয়ে উঠলেন, বজরং আহীর নামে একজন বিহারী মালিকের বাড়িতে, ভাড়া ছিল পাঁচ টাকা। এসব যখনকার কথা তখন আমার জন্ম হয়নি। আমি পিসিমাকে যখন দেখেছি তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়। তবুও সেই বয়সেই তাঁর যা রূপ দেখছি সে আজও ভুলতে পারিনি। আমার জ্যাঠামশাই মারা গেলেন, খবর পেয়ে পিসিমা দেশে এলেন, শেষ জীবনে দেশের বাড়িকে একবার স্বচক্ষে দেখতে। যেদিন তাঁকে দেখি সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে।
তখন ভরা বর্ষাকাল, দিনরাত ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি লেগেই থাকত। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে দিক-দিগন্ত জলে থৈ থৈ, চারিদিকে শুধু জল আর জল। পথঘাট জনশূন্য। এ-বাড়ি ও-বাড়ির প্রবীণারা বর্ষার অবকাশে একসঙ্গে বসে গল্পগাছা করছেন। জ্যাঠাইমার ঘরে আমরা মেয়েরা পুতুল খেলছিলাম।
এইসময় বৃষ্টি মাথায় হৈ হৈ করে কয়েকটি ছোটো ছেলে এসে জানাল কেউ একহন আমাদের বাড়ি খুঁজছেন। শুনে তো বড়দের সঙ্গে আমরা ছোটোরাও ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঠাকুর আঙিনা পর্যন্ত এসেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।
দেখি অপূর্ব সুন্দরী এক বৃদ্ধ মহিলা, কাঁচা হলুদের মত উজ্জ্বল গায়ের রঙ। দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে মস্ত চেহারা। মাথায় কালো কুচকুচে একমাথা চুল, ছোট ছোট করে ছাঁটা, পরণে গেরুয়া খান, হাতে, কব্জিতে রুদ্রাক্ষের মালা, টানা টানা চোখ, ভুরু। যেম কাশী-বাসিনী এক দীপ্তিময় সন্ন্যাসিনী পূণ্যজ্যোতির ছটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সদরের পথে।
দীর্ঘ বছরে গ্রামের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট,পরিবেশ সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তাই প্রথমে বাড়ির পথ চিনতে পারেননি পিসিমা। এই সময় জ্যাঠাইমা গজর থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুরঝি বলে জড়িয়ে ধরলেন, আমরা বুঝলাম এই তবে পিসিমা।
পিসিমার কাশীবাসকালীন খরচের টাকা পাঠাতেন আমার বাবা। মানি অর্ডার প্রাপ্তির সংবাদ পাঠাতেন পিসিমা, পোস্টকার্ডে এক লাইন লিখতেন, আকার, ইকার থাকত না, শুরুতে শুরুতে 'ছোদাদা' অর্থাৎ 'ছোড়দাদা'। পত্র লেখার প্রয়োজনে নিজের চেষ্টায় অক্ষর চিনেছিলেন, লিখতে শিখেছিলেন।
বাবার হাতে একভাণ্ড দই ধরিয়ে দিয়ে, বাঁকটি কাঁধে নিয়ে লোকটি দৌড় লাগাল। তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে আসছে, বনপথ অন্ধকার হয়ে যাবে। যে সময়ের কথা সে সময়ে গ্রামদেশে বাঘের উৎপাত খানিক বেড়েছিল, কারণ বন কেটে বসতি বাড়ছিল, বনে ওদের জায়গা আর খাবার দুইই কমে আসছিল, তাই লোকালয়ে ঢুকে আসছিল শিকারের আশায়। পরে গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রাইফেল এসেছিল যা দিয়ে বাঘের আক্রমণ আর ডাকাতের আক্রমণ প্রতিহত করা যেত। এর ফলে বাঘের আক্রমণ কমে আসছিল।
এরপর তিনটি বছর তিনি দেশের বাড়িতে ছিলেন। তারপর আবার কাশীতে ফিরে গিয়েছিলেন।
শেষ বয়সে দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন পিসীমা। কাসীতে ফিরে যাবার কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।
আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, বছরের একটা সময়, প্রধানত কার্তিক মাসেই কাশী থেকে কিছু পান্ডা আসতেন দেশে গাঁয়ে। কাশীতে যারা তীর্থ করতে যেতেন তাঁদের প্রত্যেকের নাম ঠিকানা থাকত পান্ডাদের খাতায়। এইসময় নিজের নিজের যজমানদের বাড়ি বাড়ি যেতেন এঁরা, কিছু দানসামগ্রী টাকাপয়সা সংগ্রহের জন্য।
এঁদের মধ্যে একজন পান্ডার নাম ছিল ভোলানাথ। নানা গাঁয়ে ঘুরে শেষে আসতেন আমাদের বাড়ি, পিসিমার চিঠি থাকলে পৌঁছে দিতেন, সঙ্গে আনতেন বিশ্বনাথের প্রসাদ, নির্মাল্য।
বিশাল চেহারার ভোলানাথ পান্ডাজির মাথা ছিল নেড়া, পরনে গেরুয়া বস্ত্র, লুঙ্গির মত করে পরা। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। প্রশস্ত কপালে তিন লাইন শ্বেতচন্দনের দাগ। পরে জেনেছি এই চিহ্নের নাম ত্রিপুণ্ড্রক। কাঁধের উপর দিয়ে সামনে পিছনে ঝোলানো থাকতো একটি লম্বা ঝোলা। ঝোলাতেই থাকত, দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা সামগ্রী। এদের বিষয়ে বাকি কথা আগেই লিখেছি।
আসি বাবার কথায়। শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন আমার বাবা। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বাবার শাস্ত্র আলোচনা শুনতে উৎসুক ছিল। একজন ধর্মপিপাসু মুসলমান আসতেন আমার বাবার কাচজে শাস্ত্র আলোচনা শুনতে। নাম ছিল তাঁর আতর আলী। দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। একমাথা সাদা লম্বা চুল ও সাদা দাড়ি ছিল, ফর্সা টুকটুকে খাটো চেহারার লোকটি সাদা ধবধবে কাপড় পরতেন লুঙ্গির মত করে। গায়ে পরতেন সাদা ঢিলাহাতা পাঞ্জাবী। পায়ে খড়ম। হাতে দড়িতে ঝুলিয়ে একটা ঘটি বেঁধে তাতে গরুর দুধ নিয়ে আসতেন ধর্মালোচনা শোনার সেলামীস্বরূপ। দেশে তখন ছোঁয়াছুঁয়ির এক বিচিত্র নিয়ম ছিল। মুসলমানের আনা দুধ নেওয়া চলত, কিন্তু তাতে এক ফোঁটাও জল থাকলে পৈতেধারী পুরুষরা সেই দুধ খেতেন না, সেই দুধ আমরা ছোটরা খেয়ে নিতাম।
তখনকার দিনে অন্যান্য প্রাণীজ ও উদ্ভিজ খাদ্যবস্তু ছিল সুলভ আর অঢেল। তাই ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার অধিক ছিল। মুসলমানদের পোষা হাঁসের ডিম হিন্দুরা খেত না, কারণ মুসলমানদের বাড়িতে হাঁস, আর অস্পৃশ্য মুরগী একজায়গায় থাকত। আজকাল সেসব দিনের কথা মনে হলে হাসি পায়। এখন তো হাঁস বাদ, মুরগীর ডিম আর মুরগীর মাংসই হয়েছে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে প্রধান আমিষ খাদ্য। ভয় হয় অদূর ভবিষ্যতে মুরগীর মাংস দেবতার ভোগেও না স্থান করে নেয়।
যাক দেশের কথা আর বেশি কী লিখব, এবার শুরু করি এদেশে অর্থাৎ এখন যেটা আমার দেশ সেই দেশের নানা কথা। বিয়ের পর আমর এদেসক্সহে আসা আবার ফিরে যাওয়ার কথাও লিখেছি। এবার লিখি কেমনভাবে শুরু হয়েছিল আমার শ্বশুরবাড়ির নতুন জীবন।
বিবাহের পূর্বে দেওয়া গুরুজনদের উপদেশ স্মরণে রেখে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী শ্বশুরবাড়ির গুরুজনদের আদেশ উপদেশ পালনে অভ্যস্ত হতে লাগলাম। অপ্রত্যাশিতভাবেই নানা নিয়মকানুনের বেড়াজালে অচিরেই বাঁধা পড়লাম।
গুরুজনদের ঘুম থেকে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠতে হবে। রাতে শুতে যেতে হবে সকলের শেষে। জোরে শব্দ করে কথা বলা, জোরে শব্দ করে হাসি নিন্দনীয় তাই বর্জনীয়। কিছু গুরুজন, যেমন ভাশুর, শ্বশুর, মামাশ্বশুর প্রমুখ শ্বশুরদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরে থাক, পদস্পর্শ করে প্রণাম করাও ছিল মহাপাপের তুল্য। এইসব গুরুজন স্থানীয়দের সামনে দিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হলে মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে, মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে চলতে হবে এই ছিল নির্দেশ। দিনের অধিকাংশ সময় কার্যত রান্নাঘরেই কাটত। দুপুরে সকলের খাওয়াদাওয়া মিটে গেলে, খানিকক্ষণ বিশ্রামের সময় মিলত। বিশ্রামের জায়গাও ছিল দরজা-বন্ধ রান্নাঘরের মাটিতে লাইন করে পাতা সিঁড়ির সারির উপর।
বিয়ের পর প্রথম দিকে ঘোমটা ব্যাপারটা খুবই কষ্টকর ছিল। এটা সব বউদেরই হত। প্রয়োজনবোধে বারবার ঘোমটা ওঠানো নামানো করতে করতে মাথার চুল জট পাকাত।
এই সময়ে শাড়ির সঙ্গে শায়া, ব্লাউজের চল ছিল না। সেমিজ পরা হত। তবে সেই সেমিজ তৈরির কাপড়ের মান সবার একরকম হ'ত তা নয়। সেমিজ অনেক ডিজাইনের হত। ঘটি হাতা, মেগিয়া হাতা, কনুই পর্যন্ত হাতাও হত। কোন সেমিজের আবার গলায় কুঁচি দিয়ে একটু সুন্দর করার চেষ্টা করা হত। গোলা থেকে পা পর্যন্ত সেই সেমিজ আজকাল আবার ফিরে এসেছে ম্যাক্সি রূপে। নানা রঙের শাড়ির মধ্যে ছিল নীলাম্বরী, টিয়া রঙের শাড়ি, বাগেরহাটের শাড়ি, গোদাবরী শাড়ি। বাগেরহাটি শাড়িগুলির রঙ ছিল পাকা, আর খুব টেকসই হত সেগুলি।
দেশে তখন এক সম্প্রদায়ের লোকের বাস ছিল, তাদের জাতি ছিল যুগী-জোলা। এরা নানা হাতের কাজে, কারিগরী বিদ্যায় নিপুণ ছিল। পাকা বাঁশ দিয়ে এরা যে তাঁত তৈরি করত, সেগুলিকে বলা হত 'হাততাঁত'। এইসব তাঁতে যুগীরা শাড়ী প্রস্তুত করত, সেগুলি 'যুইগ্যা' (অর্থাৎ যুগীদের তৈরি) শাড়ি বলে পরিচিত ছিল।
এই গ্রাম্য কারিগররা ভেজালের কারিগর ছিল না, তাই এদের বোনা শাড়ি খুব মসৃণ সুতোর না হলেও, খুব টেকসই হত আর রঙ হত পাকা। এইসব মোটা শাড়ি পরে রান্না ঘরে কাঠের ধোঁয়ার আগুনে রান্না করতে বাড়ির বৌদের যে কী অবর্ণ্নীয় কষ্ট হত সে কথায় ভাষায় বোঝানো সম্ভব না। গরমের দিনগুলিতে বউদের গা ভর্তি ঘামাচির চুলকানি সহ্য করেই সেইসব শাড়ি-সেমিজ পরেই কাজ করতে হত। সেসব দিনগুলির অকথ্য যন্ত্রণার কথা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানত।
তবে হ্যাঁ, ঘোমটা দেওয়াটি কষ্টকর হলেও সামাজিক কারণে তা একেবারে অমূলক ছিল বলে মনে হয় না। সমাজবন্ধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন হলেও বহু ঘোমটা পরা মা দেশমাতাকে বহু কৃতী সন্তান উপহার দিয়েছেন। ঘোমটার নিয়ন্ত্রণে থেকেও বহু মহীয়সী নারী দেশমাতার চরণে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, আবার স্বজাতির (মহিলাদের) অত্যাচারী মহিলাদের নিন্দা, সমালোচনার প্রতিবাদে কলম ধরেছেন সে খবরও শুনেছি। যদিও তাঁরা আমাদের মত অজ গাঁ-গঞ্জের নারী ছিলেন না।
সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রাচীনা ও নবীনার মুখর প্রতিবাদের পরিচয় পেয়েছি। সমাজে না ঘটলে তা সাহিত্যে উঠে সাসা সম্ভব নয়। তাই এগুলি সত্যিই ঘটত বলে মনে হয়। মারা দেশ গাঁয়ে সবসময় সেসব খবর জানতে পারতাম না। যাঁদের অক্ষর পরিচয় ছিল না, যেসব বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত না, তাঁদের তো জানাই হত না কত কিছু।
আবার একটু ছেলেবেলার কথায় ফিরে যাই। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার দূরকে নিকট করেছে। আমাদের ছেলেবেলায় ঘরে বসেই দূরের জিনিস দেখা বা দূরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের কথা ভাবতেই পারতাম না। আজকের দিনের, দূরভাষ যন্ত্র, দূরদর্শন যেটা সম্ভব করেছে সেসব ছিল অকল্পনীয়। আমাদের একটু বড় বেলায় দেখেছি কলের গান (গ্রামোফোন)। মনে পরে আমার বাপের বাড়ির গ্রামে একজনের বাড়িতে একটি কলের গান এসেছিল। সে বাড়ির একজন শৌখিন মানুষ সেটি কিনে এনেছিলেন গান শোনার জন্য। যন্ত্রটির নীচে ছিলে একটি বাক্সের উপরে একটি গোল চাক্তি, সেটা আবার ঘোরে। আর আওয়াজ বেরোবার মুখটি ছিল বড়সড় একটি ধুতুরা ফুলের মত। বাড়ির সৌখিন কর্তাটি কাছারিঘরের দরজা বন্ধ করে কলের গান ছালাতেন, সম্ভবত শ্রোতাদের এড়াতে। কিন্তু, শব্দ কি আর বাধা মানে! তিনি যেই গান চালাতেন অমনি পাড়ার ছেলেপুলের দল তাঁর বাড়ির জানলায় জানলায় উঁকি দিত, কেউ কেউ যন্ত্রটিকে দেখার জন্য ঘরের পাশের গাছের ডালে উঠে বাদুড়ঝোলা হয়ে জানলা দিয়ে সেটি দেখার চেষ্টা করত।
একদিনের কথা মনে পড়ে। আমাদের বাড়ির সামনের সরু পায়েচলা পথটি বেয়ে দুটি মুসলমান ছেলে ছুটে যাচ্ছে, যেটি বড়, সে তাড়াতাড়ি ছুটছে আর পিছিয়ে পড়া ছোট ভাইটিকে চীৎকার করে ডাকছে, "তাড়াতাড়ি আয় বাক্সোর গান চলে যাবে"। সে-সময় মাথায় করে একটি বাক্স নিয়ে আসত একটি লোক। গ্রামের নানা প্রায় সেই বাক্স মাথায় ঘুরে বেড়াত সে। বাক্সের গায়ে ছিল অনেকগুলো গর্ত, গর্তগুলির মুখগুলো ঢাকনি দিয়ে ঢাকা দেওয়া। পয়সা দিলেই সেই বাক্সের ভিতরে দেখার অধিকার মিলত। ঢাকনিটি খুলে সেখানে চোখ রাখলে নানা দৃশ্য দেখা যেত, দেবদেবীর ছবি দেখা যেত। দেশের বাড়িতে সে-সব দিনে এ ছিল এক আজব জিনিস। আজ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষকে কী না দিয়েছে, কিন্তু হারিয়ে গেছে সেইসব দেশী মানুষের মনোরঞ্জনের উপকরণ, হারিয়ে গেছে সেসব জীবিকার উপকরণ।
ফিরে আসি আবার নিজের নতুন ঠিকানার কথায়। শ্বশুর বাড়িতে সারাদিন সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের ক্লান্তি অপনোদনের সঙ্গী হল আমার চার বছর বয়সের ছোট্ট দেওর। সারাদিন আমার সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াত। একদিন দুপুরে মধ্যাহ্ন আহারের পর সকলে যখন দিবানিদ্রায়, সে সময় আমি আর ছোট্ট সঙ্গীটি রান্নাঘর আর শনের ছাওয়া শোবার ঘরের মাঝখানের সরু গলি পথে গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়ির পিছন দিকে। সেখানে বিরাট এলাকা নিয়ে ছিল প্রাত:কৃত্য সারার জঙ্গলা, আর ছিল অনেক বড় বড় গাছপালা। কাঁঠাল, জাম, জাম্বুরা (বাতাবি), আম, গোলাপজাম, ভুবি এসব গাছ ছিল। এখানে একটি গাছ ছিল সে গাছের ফলগুলি দেখতে ছিল খানিকটা টমেটোর মত। খেতে ভীষণ টক, চলতি নাম ছিল 'থৈকর'। সেই গাছে থোকা থোকা থৈকর ঝুলছিল।
শিশু দেবরকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছি সেই আছের দিকে তাকিয়ে। নিস্তব্ধ দুপুর। গাছের পাতার ছায়ায় ছায়ায় ডালে ডালে বসে আছে নানা জাতের, নানা রঙের পাখি। কেউ বা বসে ঝিমুচ্ছে আর সঙ্গীটি তার গায়ের পাখনাগুলিকে ঠোঁট দিয়ে খুঁটে আরাম দিচ্ছে, হয়তো এভাবেই মৌণ প্রিয় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।
থৈকর গাছটির একটা ডালে একজোড়া কুটুম পাখি বসেছিল, একজন আরেকজনের পিঠের পালকে মুখ গুঁজে বসে অলস তন্দ্রা উপভোগ করছিল পরম নিশ্চিন্তে। এভাবেই গাছে চলছিল পাখিদের অলস মধ্যাহ্ন যাপন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি থৈকরের সবুজ গুচ্ছের মাঝখানে কিছু লাল রঙের পাকা টসটসে থৈকর ঝুলে আছে পাতার নীচে। খুব লোভ হল। কিন্তু অনেক উঁচুতে, হাতের নাগালের বাইরে, পেড়ে আনার উপায় কী? চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। অমনি শিশু দেওরটিকে কোল থেকে নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে উঠলাম গিয়ে গাছে। খেয়াল করিনি যে গাছের পাতার নীচে বাসা করে আছে এক ধরনের বড় বড় পিঁপড়ে, গায়ের রঙ আগুনে লাল। লালা দিয়ে নিপুণ দক্ষতায় পাতার নীচে বলের মত গোলা বাসা বানিয়েছে। এদের বাসায় থাকত মুড়ির মত সাইজের ডিম। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে এই ডিমগুলি মাছ ধরার টোপ হত।
ফলের লোভে গাছে উঠতেই আক্রমণ করল পিঁপড়ের দল। সমানে গায়ে, মাথায়, মুখে বাইতে শুরু করতেই নেমে আসতে চাইলাম, তাড়াহুড়োয় ধপাস করে পড়ে গেলাম মাটিতে। উঠেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলাম কেউ দেখেছে কিনা। আর সঙ্গে সঙ্গে দেওরের হাত ধরে গলিপথে দে দৌড়, একেবারে রান্নাঘরে এসে ঢুকলাম।
আসি শ্বশুরমহাশায়ের পিতৃকূলের পরিচয়ে। সবই শুনেছিলাম শ্বশুরমহাশয়ের মুখে। আমার বিয়ের কিছুদিন পর থেকে তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে একটা ছিল আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করা। খানিক আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন তিনি। সন্ধ্যারাত্রেই আহারের পর্ব মিটে যেত। আহারের পর হুঁকোর নলটি মুখে দিয়ে পিঁড়ি পেতে বস্তেন তিনি, আমাকে শোনাতেন দেশ রাজ্যের নানা গল্প। তাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটয়ান বলতেন তিনি। তাই আমার লেখাতে এই বাড়ির কথা যা কিছু লিখব সবই তাঁর কাছে শোনা বিবরণ।
আমার শ্বশুরমহাশয়ের ঠাকুরদা কমলাকান্ত সার্বভৌম ছলেন নি:সন্তান। প্রভূত সম্পত্তির মালিক। সার্বভৌম মহাশয় দত্তকপুত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।
সেই গ্রামেই বাস ছিল একটি পরিবারের। সদ্বংশজাত, সম্পর্কে আমাদের এগারো দিনের জ্ঞাতি। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় দুটি শিশুপুত্র আর স্ত্রীকে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাতেন তাঁরা। সেই ব্রাহ্মণীর তৃতীয় সন্তানের বেলায় সার্বভৌম মহাশয় উক্ত নবজাতককে দত্তক নেবার সঙ্কল্প জানালেন সেই ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ রাজি হলে তাঁর পরিবারের সকলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলেন তিনি। সার্বভৌমের পত্নী সেই অন্ত:স্বত্ত্বা মহিলার তত্ত্বাবধানের জন্য দাসদাসী নিযুক্ত করে দিলেন।
নিশ্ছিদ্র তত্ত্বাবধানে আর নানারকম স্বাচ্ছন্দে থেকে উক্ত মহিলা যথাসময় হৃষ্টপুষ্ট, পরম সুন্দর এক পুতের জন্ম দিলেন। অভিলাষ পূর্ণ হতে যাচ্ছে দেখে প্রসূতির আর তাঁর পরিবারের যত্নআত্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন কমলাকান্ত। শিশুটিও দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বেড়ে উঠতে লাগল।
এরপর যথাসময়ে, শুভদিন দেখে শুভ সময়ে আচার নিয়মের মধ্য দিয়ে বিধিপূর্বক, যাগযজ্ঞ করে, মহাসমারোহে গর্ভধারিণীর কোল থেকে সার্বভৌম পত্নীর কোলে স্থানান্তরিত হয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে নূতন জন্মগ্রহণ করলেন সেই শিশু। নামকরণ অনুষ্ঠানে নাম রাখা হল 'জয়চন্দ্র'। এর কিছুদিনের মধ্যেই মধ্যেই স্বামী আর দুই পুত্র রেখে জয়চন্দ্রের গর্ভধারিণী ইহলোক ত্যাগ করলেন।
সহৃদয় সার্বভৌম মহাশয় জয়চন্দ্রের মৃত গর্ভধারিণীর পরিবারবর্গের বংশপরম্পরায় ভরণ-পোষণের জন্য ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পিতাকে প্রভূত সুফলা সম্পত্তি দান করে আয়ের পথ করে দিলেন।
জয়চন্দ্র মহাশয়ের পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠানটি মহাসমারোহে সম্পন্ন হল বটে, কিন্তু সার্বভৌম পত্নীর ভাগ্যে সন্তান নিয়ে আনন্দ উপভোগ সইল না। বিদ্যারম্ভের কিছুদিনের মধ্যেই তিনিও ইহলোক ত্যাগ করিলেন।
বয়োবৃদ্ধ সার্বভৌমের সংসারে শিশুপুত্রটি ছাড়া আর কেউই রইল না। দাসদাসীদের পরম যত্নে শিশুটি বড় হতে লাগল। আজকালকার মত তখনকার দিনে ভৃত্যভৃত্যারা বেতনভোগী স্বল্পস্থায়ী কর্মচারী ছিল না। তারা বাড়িরই সদস্যের মত থাকত। এই দাসদাসীরা প্রায় সকলেই ছিল খুবই প্রভুভক্ত। এরা পুরুষাণুক্রমে মালিকের প্রদত্ত ভূমিস্বত্ব ভোগ করত, প্রতিদানে মালিকের বিষয়-আশয়, চাষবাস, জমিজমার দেখভাল করত। সাংসারিক ভালোমন্দ, আয়ব্যয়, স্থিতি সব কিছুর দিকেই সদাসতর্ক নজর রাখত। কোনোপ্রকারেই মনিবের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দিত না। এরা থাকত অধীনস্থ প্রজা হিসাবে। এদের পরিবারের মহিলাদের মধ্যে কোন কোন সহায়সম্বলহীনা বালবিধবা তার পিতৃকুলের সঙ্গেই মনিবের বাড়িতেই প্রতিপালিত হত যাবজ্জীবন।

বিস্তর সম্পত্তি, বাড়িঘর, এত দাসদাসী ও সার্বভৌমপুত্রের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল সোনামনী দাসীর উপরে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেই দাসী জয়চন্দ্রের দিকে নজর রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভূসম্পত্তি রক্ষা, চাষবাসের কাজের তদারকি, দাসদাসীদের পরিচালনা করতে লাগলেন। সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী সোনামনি চাষবাস দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন পুরোনো ভাগচাষীদের হাতেই, যাতে তারা বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারে। সব দিকে নজর তদারকিতেই রাখতেন। অধীনস্থ শুভান্যুধায়ী প্রজাকুলের দায়িত্বেই সিব ঠিকঠাক চলতে লাগল।
যে সময়ের কথা লিখছি বর্ণবৈষম্যের প্রতাপ তখন প্রবল। এই প্রভুনিষ্ঠ প্রকাজুল উচ্চবর্ণের মানুষদের যারপরনাই ভক্তিশ্রদ্ধা করত, এমনকি তাঁদের ছায়াটুকুও এড়িয়ে, সমীহ করে চলত।
সবদিক সামলে সোনামণি দাসী সংসার ঠিকঠাক চালাতে লাগলেন। প্রভুপুত্রের যেন ধর্মনাশ না হয়, সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। উপবীতধারী কিশোর পুত্রের দৈনিক আহ্নিকের ব্যবস্থা করতেন তিনি। প্রভাতে উঠে তিনি স্নান সেরে, শুদ্ধবস্ত্র পরে তিনি জয়চন্দ্রের আহ্নিকের জোগাড় করে দিয়ে দূরে বসে তাঁকে আহ্নিক করাতেন। তাঁর জলযোগের ব্যবস্থা করতেন। চিঁড়ে, মুড়ি, দুধ, খই, কলা, ফলমূল এসব দিয়েই তখনকার দিনে প্রাতরাশ হত। শুকনো এই খাবারের ব্যবস্থা তিনিই করে দিতেন। এরপর ছিল দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা। কাঠের জ্বালের উনুনে পেতলের সরায় আন্দাজমত জল গরম করে, তাতে সবজি আর চাল ধুয়ে দিতেন। ভাত ফুটতে দিয়ে বসে থাকতেন কাছে। আন্দাজমত জল দেওয়াতে ভাতের মাড় গালবার দরকার হত না। ছোট ছেলে তো ভাতের মাড় গালতে পারবে না। আর তিনিও নীচ জাতির বলে পক্ক অন্ন স্পর্শ করবেন না। তাই এভাবেই চলত সিদ্ধভাত তৈরির ব্যবস্থা। ভাত হয়ে গেলে, আলগোছে উনুনের নীচের জ্বলন্ত কাঠ বের করে নিয়ে উনুন নিভিয়ে দিয়ে শেষ হত তাঁর কাজ। আধুনিক কালের ভৃত্যদের দেখি আর ভাবি কেমন বিশ্বস্ততা ছিল সে-যুগের ভৃত্যদের অন্তরে। আজ সেসব ভাবাই যায় না। সার্বভৌমের মত বিচক্ষণ আর দয়ালু ব্রাহ্মণও সে যুগে বিশেষ না।
অন্নপাত্রটি ঠান্ডা হয়ে এলে বিচালির গোছা ধরে দিতেন ছেলের হাতে, সে নিজে উনুন থেকে প্তার নামিয়ে, হাতা দিয়ে ভাত বেড়ে নিত। দুধ, কলা, গুড়ের বাসন পাশে রেখে দিতেন আর নির্দেশ দিয়ে দিয়ে জয়চন্দ্রকে খেতে শেখাতেন। এইভাবে চলতে চলতে কিছুদিনের মধ্যে জয়চন্দ্র নিজেই কিছুকিছু কাজ করতে শিখলেন। খাবার সময় অবশ্য সোনামণি কাছেই বসে থাকতেন। দাসীর তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে তাঁর বয়স বাড়ল। জয়চন্দ্র অনেকটা স্বাবলম্বীও হয়ে উঠলেন ক্রমে। পন্ডিত রেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন সোনামণি দাসী।
পনেরো কি ষোলো বছর বয়সের যুবক জয়চন্দ্রের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন সোনামণি। অধুনা বাংলাদেশের যশোদল নিবাসী বনমালী ন্যায়রত্নের অষ্টম বর্ষীয়া প্রথমা কন্যা মনমোহিণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল জয়চন্দ্রের।
(ক্রমশ)