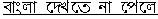আমার বাবা-মাদের দেশ ছাড়ার বাধা এসেছিল সুস্থবুদ্ধি মুসলমানদের কাছ থেকে। একদিন তো তাদের বাধায় ট্রেন ফেল করলেন। পরদিন, অন্ধকার থাকতে থাকতে এদের অগোচরে বেরিয়ে পড়লেন, ঘুরপথে স্বল্পদৈর্ঘ্য রাস্তায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন আঠারোবাড়ি স্টেশনে, ভোরের ট্রেনে ময়মনসিং টাউনে রওয়ানা হলেন।
এদিকে আমার শ্বশুরালয়ের পরিবারেও যেন সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরবণ তৈরি হল। সামাজিক বিষাক্ত আবহাওয়া পরিবারগুলিতেও সংক্রামিত হল। শ্বশুরমশাইদের তিন ভাইয়ের সংসারে ধীরে ধীরে নানা অম্ল-মধুর-তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভরপুর এক জীবনযাত্রা শুরু হল। আবাল্য যে সারল্যে ভরপুর, আনন্দময় পরিবেশে কন্যাজীবন কাটিয়েছিলাম, জগৎকে দেখেছিলাম, এখন সব আমূল পাল্টিয়ে যেতে লাগল। নতুন সংসারে নানা অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আমার চোখের সামনের পর্দা সরে যেতে লাগল। চিনলাম আর একধরনের জীবনকে। এক নতুন বোধশক্তির উন্মেষ ঘটল। মনে মনে ভাবতে লাগলাম এইভাবে কি জীবন কাটবে, কোনও উন্নততর জীবন যাপন করা সম্ভব কি হবে?
এরই মধ্যে আমাদেরও দেশ ছাড়ার ঘন্টা বেজে গেল। আমার বিয়ের পর থেকেই দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিদ্বেষের বিষবাষ্পে ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল, গ্রামেগঞ্জে ছেচল্লিশের দাঙ্গার খবর ছড়িয়েছিল। মান ও প্রাণ বাঁচাতে হিন্দুদের দেশছাড়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। একদিন রাতে আমার স্বামীর ছেলেবেলার বিশিষ্ট বন্ধু ও আমার শ্বশুরবাড়ির হিতৈষী নবাব আলি মাস্টারের সঙ্গে আমার শ্বশুর মশায়ের কথাবার্তা থেকে বিপদের অনেকটাই আঁচ পেলাম।
সেদিন রাতে নবাব আলি এলেন আমাদের বাড়ি, শ্বশুরমশায়কে কিছু বলার জন্য। তাঁকে দেখেই শ্বশুরমশায় জমিদারী মেজাজে, স্বভাবসম্মত কর্তাগিরি সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কী শুরু করেছ? আমাদের কি একটু নিশ্চিন্তে, শান্তিতে থাকতেও দেবে না!’ মার্জিত স্বভাবের মাস্টার নবাব আলী বিনয়ের সঙ্গেই বিপদের আশঙ্কার কথা জানালো— ‘মধ্যমকর্তা, ছেলেবেলা থিক্যাই আপনাগো ছায়ায়, আপনাগো লুন খাইয়াই বড় হইছি, জান থাকতে আপনাগো অনিষ্ট হইতে দিমু না। আপনাগো জন্ম এইখানে, জীবন কাটাইছেন এইখানে। আপনেরা থাকেন এইখানে। কিন্তু একখান কথা, খালি বড় বউঠান (আমার জ্যাঠতুতো বড় জা), গোরা বউঠান (আমি) আর মহামায়া দিদিরে (আমার অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী খুড়তুতো ননদ) কইলকাতায় পাঠাইয়া দ্যান। নাইলা (না হলে) বিপদ হইতে পারে।’ প্রসঙ্গক্রমে বলি এই ননদটি এইদেশে এসেও বেশিদিন বাঁচেনি, প্রথম সন্তান প্রসবের সময় অ্যাক্লেমশিয়ায় (সূতিকা-উন্মাদ রোগ) মারা গিয়েছিল।
বিপদের আঁচ পেয়ে শ্বশুরমশায় সিদ্ধান্ত নিলেন, সামনের দুর্গাপূজাটা মিটলেই আমাকে কলকাতায় রেখে আসবেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে দীপান্বিতা কালীপূজার দিন সকালে আমাকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। বেলা আড়াইটায় পৌঁছলাম ময়মনসিং শহরে। গোদারার নাও (পারাপারের নৌকা)-এর অপেক্ষায় বসে রইলাম অনেকক্ষণ। একখানা নৌকায় বারে বারে ব্রহ্মপুত্র পার হচ্ছে হাজারে হাজারে মানুষ। জন্মভূমি ছেড়ে, প্রাণ হাতে করে অজানা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে, আত্মীয়পরিজন নিয়ে, সামান্য সম্বল হাতে করে। দেশের টালমাটাল অবস্থায় দেশ ছেড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতে যাবার জন্য সকলেরই তাড়াহুড়ো, ভরসা ব্রহ্মপুত্রের বুকের এই মনপবনের নাওখানি। এই সময়ে যানবাহনের যে অবরুদ্ধ, গোলমেলে অবস্থা হয়েছিল, বিচ্ছিন্নতাকামীদের চেষ্টায় আর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে, সে-সব কথা সবাই জানে, আমি আগেও লিখেছি সেদিনের কলকাতা আসার পথের ট্রেনের ভিতরের ভয়ঙ্কর বর্ণনা। নির্বান্ধব অবস্থায় সান্তাহার স্টেশনে বিশাল ভিড়ের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক নিয়ে আমার বৃদ্ধ শ্বশুরমশায় উৎকন্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন ট্রেনের জন্য। রাত তখন আড়াইটা, ট্রেনের সময় তিনটে। সারাক্ষণ তিনি আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন। আশপাশে আরও যেসব মানুষ দেশ ছেড়ে আসছিলেন, সবাই ছিলেন আমাদের হিন্দু প্রজা। তাদের নারীপুরুষের দঙ্গলের মধ্যে, আলো থেকে দূরে, আঁধারের মধ্যে আমাকে রেখে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই উৎকন্ঠার কারণ তখন বুঝিনি, বর্তমানে দেশের নানা ঘটনা শুনে বুঝি একটি বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে তিনি কী বিপদের মধ্যে দিয়ে চলেছিলেন। যা হোক ট্রেনের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে সবাই, আশংকা এই না কোনও স্টেশনে আবার গুণ্ডাদের আক্রমণ হয়।
পরদিন বিকেলে সেই আতঙ্কময় যাত্রার অবসান হল। বিকেল চারটেয় ট্রেন থেকে নেমে গেলাম কাঁঠালপাড়ায় মেজননদের বাড়ি। সেখানে দুদিন থেকে চলে গেলাম রেলের পূর্বপাড়ে গ্রামের দিকে একটি ভাড়া বাড়িতে। ওই বাড়ির মালকিন বিধবা মহিলার অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি নতুন দেশে, নতুন পরিস্থিতিতে ঠিকভাবে সংসার চালিয়ে নিতে। তিনি শিখিয়েছিলেন উনুনে আঁচ দিতে, আটা মেখে রুটি তৈরি করতে, সেঁকতে। যে বিষয়গুলি আমার কাছে ছিল একেবারে নতুন।
এই বাড়িতে এক বছর কাটতে চলল। এই সময় ১৯৪৮ সালে একদিন সন্ধ্যায়, আবার চারিদিকে লোকজনের হইচই, ছোটাছুটির শব্দ শুনতে পেলাম, বাড়ির ভিতর থেকে। শীতকাল সন্ধে নেমে এসেছে ৫টাতেই। কাছেই অবস্থাপন্ন কোন একজনের বাড়ির রেডিওতে বাজতে লাগল ‘রঘুপতি রাঘব রাজারাম’-রামধুনের সুর। এই সময়ে আমার কর্তা অফিস থেকে দ্রুত বাড়ি ফিরলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম মহাত্মাজিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমার মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় নেড়ামাথা গান্ধীজির ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার উল্টিয়ে রাখার কথা।
কয়েকদিন চারিদিকে খুব হইচই চলতে লাগল। এইভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সাল শেষ হয়ে ১৯৪৯ সাল শুরু হল। ৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আমার কোল আলো করে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যাসন্তান এল। আমার প্রথম সন্তান ‘কৃষ্ণা’।
পূর্ববঙ্গের অর্থাৎ পূর্বপাকিস্থানে হিন্দুদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হতে লাগল। ৪৯ - ৫০ সালে যেন বানের জলের মত দেশছাড়া ছন্নছাড়া মানুষের ঢল নামল পশ্চিমবঙ্গে, প্রধান উদ্দেশ্য প্রাণে বাঁচা, মানে বাঁচা। দ্বিতীয়টা সবাই বাঁচাতে পারেনি, বিশেষত অল্পবয়সী মেয়ে আর বউরা। তাঁদের কতজন যে মান ইজ্জত হারিয়েছে, কোথায় হারিয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। পায়ের নীচে নিজের জমি নেই, মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই, খাদ্যের সংস্থান নেই। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নেওয়া সর্বহারা মানুষেরা সামান্য পুঁজি আর প্রয়োজনীয় জিনিসের পুঁটুলি নিজেদের হাতে হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়ত নানাদিকে। একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাঁই, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সারাদিন নানাদিকে, প্রধানত গ্রামের দিকে ঘুরেফিরে সন্ধেবেলায় এসে ঠাঁই নিত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, বা পথের ধারে কোন বাড়ির খোলা বারান্দায়, কখনো বা গাছতলায়।
স্টেশনচত্বরে এত মানুষের থাকবার সংস্থান কোথায়? প্রতিদিনই তো কাতারে কাতারে মানুষ চলে আসছে এদেশে! অতএব এইভাবে কিছুদিন যাযাবরবৃত্তি চলবার পর এই ছিন্নমূল মানুষরা সংঘবদ্ধ হতে লাগল। গ্রামের দিকে কোন পোড়ো বাড়ি, বা খোলা জায়গার খোঁজ করতে লাগল যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে।
দেউলপাড়া গ্রামের পূর্ব অংশে এইরকম একটা বিরাট পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ি ছিল। ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কাদের বাড়ি সে বিষয়ে স্থানীয়রা কেউ কিছু বলতে পারেনি। কয়েকটি পরিবার একসঙ্গে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে বাড়িটি বাসের যোগ্য করে তুলল, আশ্রয় নিল সেখানে। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামসুবাদে আত্মীয় ছিল তারা, তাই উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের কথা তাদের মুখ থেকেই কিছু কিছু শুনেছিলাম। আমি তো তখন শিশুকন্যা আর সংসারের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। তবে বর্তমান বাসস্থানের আশেপাশে ফাঁকা জমিতে যারা এসে আশ্রয় নিয়ে ক্রমে প্রতিবেশী হয়ে উঠেছিল তাদের কাছে শুনেছি সেসব দিনের দুর্দশার কষ্টকর কাহিনী।
যাই হোক সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে যারা বাস করতে শুরু করেছিল তারা নাকি রাতের বেলায় ভিতর দিকের একটি ঘরে নানা অশরীরীর পায়ে হাঁটার শব্দ পেত। ওই ঘর বাদ দিয়ে প্রশস্ত উঠোনের চারদিকে চালা বেঁধেও কিছু লোক বাস করতে লাগল। একদিন এক তিন সদস্যের পরিবার থাকার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সেই বাড়ির ফেলে রাখা ঘরটির সন্ধান পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেল। সব শোনার পরেও তারা সাহসে ভর করে সেই ঘরে থাকতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের পরিবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল। আবার নিরাশ্রয় হল।
এই বাড়িতে আমাদের যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা ছিলেন তাঁদের কাছে সেই ভূতুড়ে বাড়িতে বাস করার অভিজ্ঞতার কথা, আর কিভাবে সেই অশরীরীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করেছিল সে কথায় পরে আসছি।
এই ফাঁকে একটু দেখে নেওয়া যাক পূর্ববঙ্গের হিন্দুনিধন যজ্ঞের ফলে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির চিত্রটা কেমন হয়েছিল। এই অঞ্চলের প্রতিবেশের চিত্রটার আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করল কিছুদিনের মধ্যেই।
কাতারে কাতারে দেশছাড়া ছিন্নমূল মানুষদের প্রাত্যহিক দুর্দশা এমনই সঙ্গীন হয়ে উঠল যা সহ্য করতে পারল না কিছু যুবক। এরাও কেউ এদেশের ছিল না। কিছুদিন আগে বা পরে দেশ ছেড়ে আসা বাস্তুহারা পরিবারেরই ছেলে। এরা সকলেই ছিল খুবই দুঃসাহসী আর বুদ্ধিমান। দেখল যে ভারত সরকারের কাছ থেকে সেই অবস্থায় কিছু সাহায্য পাওয়ার চিন্তা বৃথা, সে আশাও নেই। তাই তারা ঠিক করল চাইলে যখন পাওয়া যাবে না কিছুই, কোন সংস্থান সরকার করছে না, তখন জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে। নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। অবশ্য এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অত্যাচার করে নয়। অনেক জমি, জঙ্গল অনাবাদী, অব্যবহৃত পড়ে ছিল। মালিক কোথায় কেউ জানে না। সেইসব জমি দখল করে তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই বানাবে ঠিক করল। রেলের পূর্বদিকে দেউলপাড়া গ্রাম বাদ দিয়ে দু’পাশে প্রচুর খালি জমি পড়েছিল, সেগুলি দখল করে কিছু পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সচেষ্ট হল।
স্বাধীন ভারতে, পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার (বর্তমানে উত্তর) বিজয়নগরে গঠিত হল প্রথম ‘বাস্তুহারা সমিতি’। দিনটি ছিল ১৯৪৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর। আমার কন্যা তখন আট মাসের। এরপর জমি সংগ্রহের চেষ্টা আরও নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে কাটল কিছুদিন। সমিতির সকল সদস্যদেরই কাজে হাত লাগাতে হত, চাঁদা দিতে হত ঘরবাড়ি তৈরি করার সরঞ্জাম কিনতে। ১৯৫০ সালের কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে, রাতারাতি স্থাপিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম উদ্বাস্তু কলোনি--১নং বিজয়নগর কলোনি। যারা ভারত স্বাধীন হওয়ার দাম চুকিয়েছিল নিজেদের সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছিল, তারা ভারতের মধ্যে ভারতীয়দেরই নতুন উপনিবেশ স্থাপন করল। পরে জেনেছি দ্বিতীয় কলোনিটি এরপর স্থাপিত হয়েছিল কলকাতার বিজয়গড় নামক স্থানে।
যেদিন রাতে কলোনি স্থাপিত হয় সেদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। কলোনি স্থাপনে উদ্যোগী যুবকদের মধ্যে একজন ছিল ভূপেন চৌধুরী। শক্তসমর্থ, অসমসাহসী সেই যুবক ছিল গ্রামসম্পর্কে আমার শ্বাশুড়ি মায়ের ভাইপো। সম্পর্কে আমার কর্তার ভাগ্নে। সেদিন সন্ধেবেলা ভূপেন-ভাগ্নে আমাদের ভাড়াবাড়িতে এল, সঙ্গে বিরাট এক ঝাঁকাভর্তি হাঁসের ডিম, আর বস্তায় চাল-ডাল, নুন। বড় বড় দু তিনটে নতুন হাঁড়ি, হাতা, কড়াই। আমাদের ঘরের বারান্দায় রেখে খুব নীচু গলায় আমার কর্তাকে কিছু বলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করায় তিনি কিছুই বললেন না। আসলে বাড়ির পুরুষেরা অনেক কথা মেয়েদের কাছে বলা দরকার মনে করতেন না। এত রান্নার উপকরণ দেখে আমি বুঝলাম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আজ।

সকালে উঠে মানুষ দেখল, অনাবাদী, পড়ে থাকা সেই প্রান্তরে এক রাতের মধ্যে অসংখ্য অস্থায়ী ঘর উঠে গেছে। চারপাশে চারটে বাঁশের খুঁটির মাথায় হোগলা পাতার ছাউনি। ঘরের চারদিক মেয়েদের পরনের শাড়ি দিয়ে ঘেরা দেওয়া। ভিতরে মাটির হাঁড়ি, কড়াই, জলের কলসি, উনুন আর থালা-বাসন যার যা ছিল নিয়ে বসে আছে এক একজন দখলদার। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্পের মত রাতারাতি একটা গ্রাম বসে গেছে। প্রবেশপথের দুপাশের দুটি নারকেল গাছের কাণ্ডে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা সাদা কাপড়ের সাইনবোর্ড। সেটির উপরে আলতা দিয়ে সাল-তারিখসহ লেখা ‘এক নম্বর বিজয়নগর কলোনি’।
এরপরে পূর্বে, উত্তরে, দক্ষিণে খুব দ্রুত স্থাপিত হতে লাগল আরও কলোনি। স্থাপনের তারিখ অনুযায়ী সেগুলির নাম হল ১, ২, ৩ ইত্যাদি নম্বর সহযোগে বিজয়নগর কলোনি। পরে দীর্ঘদিন ধরে প্রতি কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এক নম্বর বিজয়নগর কলোনির সেই অস্থায়ী প্রবেশপথের সামনে সমবেত জনতা পালন করত কলোনির জন্মদিবস।
যেসব মানুষদের আপ্রাণ চেষ্টায় ও সহযোগিতায় এই জবরদখলি কলোনি গড়ে উঠেছিল, উন্মূলিত মানুষদের মাথার উপরে আচ্ছাদন, পায়ের নীচে মাটি সুদৃঢ় হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম আমার মনে আছে, যেমন মাখন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সমাজপতি, দ্বিজেন ঘোষ, নৈহাটির প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী পঞ্চানন ঘোষ, স্বর্ণব্যবসায়ী রাখাল কর্মকার, ভূপেন চৌধুরী, মহাদেব ভট্টাচার্য, এছাড়া আরও অনেকে।
একটা স্থায়ী আস্তানার প্রাপ্তি ছিন্নমূল হতাশ মানুষদের মনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার ঘটল। মনের জোর ফিরে পেয়ে তারা নতুন উদ্যমে উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত হল। উদ্যোক্তাদের প্রেরণা আর সাহচর্যে কিছুদিনের মধ্যেই এখানে ঘটে গেল আর এক অভূতপূর্ব কাণ্ড।
আমাদের তৎকালীন বাসার কাছেই ছিল এক মালিকের বিরাট বাঁশবাগান, তিনি দূরে কোথাও থাকতেন। আর একজনের সম্পন্ন চাষীর ছিল বিরাট বিরাট খড়ের গাদা। একদিন রাতারাতি সেই দুটিই লুঠ হয়ে গেল। যে পথে দিনের বেলায় যাতায়াত করতে হতো নুয়ে পড়া বাঁশগাছের তলা দিয়ে, আলোআঁধারির মধ্য দিয়ে পুকুরে যেতে হত, সকালে উঠে দেখি সব ফর্সা। বাঁশবাগান আলোয় আলোময়, বাঁশবাগানে পড়ে আছে কাটা বাঁশের গোড়াগুলো। অন্যদিকে কলোনির বাসিন্দাদের ঘরের খুঁটি হল পোক্ত বাঁশের আর চাল হল খড়ের। হোগলার চাল নামিয়ে হল ঘরের বেড়া, সামর্থ অনুযায়ী কারো কারো হল মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া ঘর। নতুন দেশের এক অঞ্চলে গঠিত হল এক নতুন জনপদ, আর দেশহারানো মানুষদের নতুন ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা শুরু হল।
আজ দীর্ঘ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে আসা বিজয়নগরের আর সেদিনের রূপ নেই, তাকে আর চেনা যায় না। বাঁশ, টালি বা টিনের ছাউনির বেড়ার ঘরের জায়গায় আজ তৈরি হয়েছে একতলা বা দোতলা পাকা বাড়ি, অনেক বাড়ি আবার বিরাট বিরাট আর সুন্দর। ঝোপঝাড় প্রায় সব উধাও, কয়েকটি পুকুর রয়ে গেছে। রাস্তায় আর রাতের বেলা অন্ধকারে পথ চলতে হয় না। ইলেকট্রিকের আলোয় চারিদিক আলোকিত। আধুনিক আমোদের প্রায় সবরকম উপকরণ অধিকাংশ বাড়িতেই মজুদ। প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল, খেলার মাঠ, ডাক্তারখানা, মায় একটা হাসপাতালও আছে। সর্বহারা যে মানুষেরা একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই বানাতে মরীয়া হয়ে জবরদখলি কলোনি গড়ে তুলেছিল, তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম আজ সুযোগ-সুবিধা, বিলাস বৈভবের প্রাচুর্যে ডুবে আছে। এলাকায় নম্বর চিহ্নিত বিজয়নগর নামের আরও সাতটি কলোনি পরে পরেই স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু পথপ্রদর্শক এক নম্বর বিজয়নগরের রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় মনে পড়ে যায় সেই সবহারানো মানুষদের সমস্যা আর সংগ্রামদীর্ণ দিনগুলির কথা। সেদিনের চারখুঁটির ঘর নামক এলাকার মধ্যে দখল নিয়ে বসে থাকা মানুষগুলির আশঙ্কাদীর্ণ, দৈন্যপীড়িত মুখগুলি ভেসে ওঠে মনে, বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠা চোখ ঝাপসা করে দেয় দৃষ্টিকে।
মনে পড়ে যায় সেই দাঙ্গাপীড়িত পূর্ববঙ্গের দিনগুলির বীভৎসতার কথা। আমি তখন এদেশের বাসিন্দা, বাড়ি থেকে বের হই না, কারণ যাওয়ার কোনও জায়গা এদেশে নেই, কোনও আত্মীয়-পরিজনও বিশেষ নেই। লোকমুখে আর কর্তার মুখে শুনেছি সেইসব দৃশ্যের বর্ণনা। ১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গায় উভয় দেশেই সীমান্তের নিকটস্থ এলাকাগুলির অবস্থা ভয়াবহ। ওদেশে যেমন হিন্দুরা মারা যাচ্ছে অগণিত, সেই খবরে এদেশে চলে আসা মানুষদের মধ্যেও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল। এদেশেও মুসলমান নিধন শুরু হচ্ছিল। কারণ অবশ্যই ছিল। দেশভাগে অগণিত উদ্বাস্তু মানুষ প্রাণ হাতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দেশ ছাড়ছে ভারতে এসে প্রাণে বাঁচতে। তখনও দুই দেশের মধ্যে রেলচলাচলে নিষেধ আরোপিত হয়নি। প্রতিদিন পূর্ববঙ্গ থেকে শিয়ালদহ ট্রেন চলাচল করত। নৈহাটি স্টেশনে ট্রেন পৌঁছুলে কখনো কখনো দেখা যেত কামরাতে কোন জীবিত মানুষ নেই। প্রায় সকলেই চলন্ত ট্রেনে, বন্দী অবস্থায় মুসলমান দাঙ্গাবাজদের হাতে নৃসংশভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। কামরাভর্তি রক্তাক্ত মৃতদেহের রক্ত শুকিয়ে গেছে, ট্রেনের কামরা থেকে নেমে আসা রক্তের ধারা শুকিয়ে গেছে।
এই হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করেও যদি কোনও উপায়ে কেউ লুকিয়ে বেঁচে থাকত, সে আর সুস্থ থাকত না। বাকরুদ্ধ হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পুতুলের মত হয়ে যেত। কেউ বা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে। দু-একজন শক্ত মনের মানুষ, যারা সুস্থ এসে পৌঁছেছেন এখানে, তাঁদের কাছেই শোনা গেছে যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মানুষেরা জান হাতে ট্রেনে চেপেই ভেবেছে নিরাপদ, কিন্তু অচিরেই ভুল ভেঙেছে চলন্ত ট্রেনে অস্ত্র হাতে উঠে আসা ঘাতকদের দেখে।
ওদেশের মধ্যে থাকতে থাকতেই ‘সারা ব্রিজ’-এর উপর ট্রেন দাঁড় করিয়ে ঘাতকের দল ট্রেনের দুদিকে লাইনের উপরে দাঁড়িয়েছিল, যাতে কেউ লাফ দিয়ে পালাতে না পারে। বাকিরা ট্রেনের মধ্যে ঢুকে নির্বিচারে লাঞ্ছনা করেছে মেয়েদের, মায়েদের, তারপর নির্বিচারে হত্যা করেছে সকলকে। মৃতদেহের বহমান রক্তস্রোত দেখে পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করেছে, ট্রেন ছেড়ে গেছে মৃতদেহের স্তূপ বহন করে। অনেক দেহ ফেলে দিয়েছে নদীর জলে।
এই দৃশ্য দেখতে দেখতে নৈহাটিতে আগে আসা পূর্ববঙ্গীয় পরিবারের যুবক-বৃদ্ধ সকলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এইস্থানে যে সকল ধনী মুসলমান ছিল, ব্যবসা ছিল, দোকান ছিল এই যুবকেরা তাদের উপর পালটা আক্রমণ শুরু করে দিল। নির্বিচারে এদের বাড়িঘর, দোকান-পাট লুঠ করে বিলিয়ে দিতে লাগল গরিব উদ্বাস্তুদের মধ্যে। এদের বাড়িঘর, স্থাবর সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করতে লাগল। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে দিতে লাগল এদের। হত্যা করা এদের উদ্দেশ্য ছিলনা, উদ্দেশ্য ওদেশের মুসলমানদের বোঝানো যে, এদেশে তাদেরও জাতভাই, আত্মীয়স্বজন আছে, অগণিত হিন্দুনিধনের ফলে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, হবে।
সন্ধের পর যখন আপ-ডাউন ট্রেনগুলি নৈহাটি স্টেশনে পৌঁছত, তখন লাঠিসোঁটা হাতে রেলের লাইনের দুধারে এরা পাহারা দিত, আর নিরাপদে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যেতে ইচ্ছুক মুসলমানদের টেনে নামিয়ে আনত, মারধোর, অত্যাচার এমনকি হত্যাও করেছে। কিছু কিছু হয়তো পরিবারের লোকজন ছেড়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছে, জখম হয়েছে, আবার পালিয়েও গেছে। ক্রমে এরাও হিন্দুনিধনের বদলায় মুসলমান নিধনে লিপ্ত হয়েছে।
সে এক দুর্বিসহ, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। বাজারে সমস্ত দ্রব্যই অমিল। পাওয়া গেলেও দুর্মূল্য। খাদ্যদ্রব্যের খোঁজ পেলেই মানুষ ভিড় করেছে লুঠ করে ছিনিয়ে নিতে। নিরাপত্তা নেই, ডাক্তার নেই, চিকিৎসার ওষুধ নেই । সেই দুর্দিনের আঘাত নেমে এল আমার জীবনেও। এপ্রিল মাসের গরম, আমার এক বছর দুই মাস বয়সী কন্যা কৃষ্ণা তখন প্রবল হামজ্বরে আক্রান্ত, দেহের উত্তাপে বেহুঁশ। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক পরিস্থিতিও তখন চরম উত্তপ্ত। সন্ধের সব পাকা বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। থমথমে পরিবেশ। প্রতিটি বাড়ির মানুষই ভীত, ত্রস্ত, নিশ্চুপ। রাস্তায় শুধু কিছু মানুষকে কিছু মানুষের তাড়া করে যাওয়া ছুটন্ত পায়ের শব্দ ছাড়া সব নিস্তব্ধ। এই পরিস্থিতিতে সুচিকিৎসা আর ঔষধের অভাবে আমার অসুস্থ কন্যা চৌত্রিশ দিন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে হার মানল। এই অশান্ত, কুটিল পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেল চিরশান্তির দেশে।

আমার তখন পাগল পাগল অবস্থা, খাওয়া-দাওয়া তো দূর অস্ত, নিদ্রা নাই। শূন্য মনে সেই আদরের ধনের স্মৃতি চৈত্রের শুষ্ক হাওয়ার মতই আমার মনেও হু হু করে ঘুরে বেড়াত সর্বক্ষণ। ঘরের মধ্যে ঢুকলে শূন্য বিছানা, শূন্য প্রাঙ্গন আমাকে যেন গ্রাস করতে আসত। মাঝেমাঝেই শুনতে পেতাম আধো আধো বুলিতে মা মা ডাক। কিন্তু মেয়েদের তো শান্তিতে মরবারও জো নাই। জীবনভোর কেবল সংসারের কাজ আর দায়িত্ব। এই দুটি বিষয় আমাদের সব ভুলে যেতে বাধ্য করে। তবে শূন্য জীবনে এই কাজের চাপ যেন আমাকে প্রকৃতিস্থ থাকতে সাহায্য করেছিল।
এদিকে দর্শনা দিয়ে সরকারি বর্ডার স্লিপ নিয়ে যাতায়াত শুরু হওয়াতে আমার শ্বশুরমশায় পাকাপাকিভাবে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ সে সময়ে ওদেশের ভিতরের পরিস্থিতি দিনদিন ভয়াবহ হয়ে উঠছে। পুরোপুরি নিজ দায়িত্বে পাঁচটি ছেলেমেয়ে আর রুগ্না স্ত্রী নিয়ে তিনি ট্রেনে এদেশে আসার চেষ্টা করেননি। বুদ্ধির জোরে ট্রেনে কচুকাটা হওয়া থেকে বেঁচেছিলেন সপরিবারে। সরকারি বর্ডার স্লিপ পাওয়ার খবরে খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজের জ্ঞাতিদের কাউকে পাশে পেলেন না। পাশাপাশি অন্য কয়টি পরিবারের সঙ্গে রওনা দিলেন। তিনটি ছেলেই নাবালক, ছোট ছেলে--আমার সেই ছোট্ট দেওর আর তার থেকে এক বছরের বড় ননদ নিতান্তই শিশু। এদের নিয়ে নাজেহাল বৃদ্ধ শ্বশুরমশায় বহু বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে দর্শনা চেকপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছলেন। এখানে এসেই চেকপোস্টের অসাধু কারবারীদের পাল্লায় পড়ে হেস্তনেস্ত হলেন। আবার অন্যদিকে আমার শ্বশ্রুমাতাকে নিয়ে বিপদে পড়লেন। তাঁর ছিল হিস্টিরিয়া--মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাবার ব্যামো। মার্চ মাসের কাঠফাটা গরমে, পথশ্রমে আর ক্ষুধায় তিনি শ্রান্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে চেকপোস্টের হাঙ্গামায় চিন্তায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বারবার জ্ঞান হারাতে লাগলেন।
এদিকে স্লিপের আশায় আসা মানুষদের ঠেলাঠেলি থেকে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টায় শ্বশুরমহাশয় কাছে দেখলেন একটি দু’মুখ খোলা মোটা জলের পাইপ খালি পড়ে আছে। তিনি মাতাঠাকুরানীকে সেই পাইপের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন, ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে পাইপের দুপাশে ঠায় বসে থাকতে বলে নিজে গেলেন উপায়ের সন্ধানে। যাইহোক কোনক্রমে লোকজন ধরাধরি করে, চেকপোষ্টের হাঙ্গামা মিটিয়ে, স্ত্রীর জ্ঞান ফিরলে রওনা দিলেন, বর্ডার পার হয়ে কোনক্রমে এসে পৌঁছুলেন নৈহাটি।
এসে দেখেন আমার কন্যা গুরুতর অসুস্থ। সে অবস্থায় আর কেউ নেই, তাই সেই ক্লান্ত অভুক্ত মানুষগুলির খাবারের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হল। একদিকে অসুস্থ, মৃত্যুমুখী কন্যা, অন্যদিকে সাতজন ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষ। এখন মনে হয় সেই পরিস্থিতিতে আমি যেন ভূতগ্রস্ত মানুষের মত যান্ত্রিকভাবে সব কাজকর্ম করে গেছি। তাঁদের আসার কিছুদিনের মধ্যেই আমার কৃষ্ণা পরপারে চলে গেল। কিন্তু জীবনে কর্মের তো শেষ নেই।
ভাড়াবাড়িতে বেশিদিন এতগুলি মানুষের থাকার জায়গা কম। তাই শ্বশুরমশায় বাড়ির কাজে হাত দিলেন। বাড়ি শেষ হবার আগেই আমার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যময়ী কন্যার জীবন শেষ। তবুও বাড়ির কাজ শেষ হল, পয়লা মে গৃহপ্রবেশও হল। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে এলাম, কিন্তু মৃতা কন্যার স্মৃতি সারাক্ষণ মনকে কুরে কুরে খেতে লাগলো। কলের পুতুলের মত কাজকর্ম করি, কিন্তু এতগুলি মানুষের কাজকর্ম, রান্নাবান্না আমার শরীরে কুলাচ্ছিল না। আমার শাশুড়িমায়ের অধিক কাজকর্ম করার ক্ষমতা কোনদিনই বেশি ছিল না। ফলে অচিরেই সংসারে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা।
(ক্রমশ)