-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ৮৯ | জানুয়ারি ২০২৩ | প্রবন্ধ
Share -
গোয়েন্দাসাহিত্য এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল : সুমিতা চক্রবর্তী


 সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) মশাই তাঁর ‘ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি’ (১৯৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স) নামের গবেষণাগ্রন্থটিতে সাহিত্যে গোয়েন্দা-গল্পের উপাদান লক্ষ করেছেন বেদের কাল থেকেই। সরমা নামের স্বর্গকুক্কুরী-র সাহায্যে সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল স্বর্গের অপহৃত গরুগুলির। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখি প্রাক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সফোক্লিস রচিত ‘রাজা ইদিপাস’ নাটকটি অতি সুলিখিত এক গোয়েন্দা-গল্প, যার কেন্দ্রীয় বিষয় হল হত্যাকারীর সন্ধান। তারপর ইউরোপে এবং এশিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের গোয়েন্দা গল্পের অতি সমৃদ্ধ সম্ভার দেখা গেছে। সেই ইতিহাস থেকে শুরু করতে গেলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)-এর কর্নেল পর্যন্ত এসে পৌঁছোনো খুবই দুরূহ হবে। সেই চেষ্টা না করে খুব সংক্ষেপে বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনি সম্পর্কে একটি প্রাক্-কথনের পর মূল প্রসঙ্গে আসব।
সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) মশাই তাঁর ‘ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি’ (১৯৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স) নামের গবেষণাগ্রন্থটিতে সাহিত্যে গোয়েন্দা-গল্পের উপাদান লক্ষ করেছেন বেদের কাল থেকেই। সরমা নামের স্বর্গকুক্কুরী-র সাহায্যে সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল স্বর্গের অপহৃত গরুগুলির। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখি প্রাক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সফোক্লিস রচিত ‘রাজা ইদিপাস’ নাটকটি অতি সুলিখিত এক গোয়েন্দা-গল্প, যার কেন্দ্রীয় বিষয় হল হত্যাকারীর সন্ধান। তারপর ইউরোপে এবং এশিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের গোয়েন্দা গল্পের অতি সমৃদ্ধ সম্ভার দেখা গেছে। সেই ইতিহাস থেকে শুরু করতে গেলে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)-এর কর্নেল পর্যন্ত এসে পৌঁছোনো খুবই দুরূহ হবে। সেই চেষ্টা না করে খুব সংক্ষেপে বাংলা গোয়েন্দা-কাহিনি সম্পর্কে একটি প্রাক্-কথনের পর মূল প্রসঙ্গে আসব।
বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯৪৭)-এর উনিশ শতকে লেখা ‘দারোগার দপ্তর’ (প্রথম প্রকাশ: ১৮৯৩) ছিল এক প্রকৃত দারোগার অভিজ্ঞতালব্ধ আখ্যানমালা। উনিশ শতকের শেষের দিকে ‘বাঁকাউল্লার দপ্তর’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল একটি ক্রাইম-থ্রিলার। বারোটি গল্পের সংকলন। সুকুমার সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। আখ্যাপত্রে লেখকের নামবিহীন এই গল্পগুলি সুকুমার সেনের অনুমানে বরকতউল্লা নামে এক দারোগার লেখা। কিন্তু গবেষক শ্রী অশোক উপাধ্যায় খুঁটিনাটি তথ্য উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, এটি কাল্পনিক গল্পের সংকলন; লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। অশোক উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের শারদীয় ‘এক্ষণ’ পত্রিকায়। তারপর গোয়েন্দা-গল্প লিখেছিলেন পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫) এবং দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩)। পাঁচকড়ি দে-র লেখায় বিদেশি গল্পের ছায়া আছে, কিন্তু মৌলিকত্বও দেখা যায়। তাঁর ডিটেকটিভ দেবেন্দ্রবিজয় ছিল খুবই বিখ্যাত। পাঁচকড়ি দে-র অনেক গ্রন্থের মধ্যে ‘নীলবসনা সুন্দরী’র নাম এখনও শোনা যায়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) ‘সখা ও সাথী’ পত্রিকায় ১৮৯৪ থেকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সংখ্যায় ‘আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড’ নামে একটি গল্প লিখেছিলেন যাকে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় কিশোরদের জন্য রচিত প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনি। শরচ্চন্দ্র সরকার নামের আরও একজন লেখক প্রায় ওই সময়ই ‘গোয়েন্দা কাহিনী’ নামে ডিটেকটিভ গল্পের একটি সিরিজ প্রকাশ করতেন। প্রকাশক ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ মিত্র। প্রথমে সপ্তাহে দুবার, তারপর প্রতি মাসে একটি করে বই প্রকাশিত হত। সেগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। শরচ্চন্দ্র সরকারের জীবন সম্পর্কে কোনও তথ্যেরও সন্ধান পাইনি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘কুন্তলীন পুরস্কার’-এর নাম সকলেই জানেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে সফল বাঙালি ব্যবসায়ী হেমেন্দ্রমোহন বসু
 (১৮৬৬-১৯১৬) একই সঙ্গে তাঁর উৎপাদিত প্রসাধন-দ্রব্যের প্রচার এবং বাংলা সাহিত্যের সেবার জন্য এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি আহ্বান করলেন গল্প-প্রতিযোগিতা যেখানে শর্ত একটাই— গল্পের কোথাও থাকবে তাঁর কোম্পানির কেশতৈল বা সুগন্ধির নাম। প্রতি বছর তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলির সঙ্গে আরও কিছু গল্প নির্বাচন করে একটি সংকলন প্রকাশ করতেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সংকলনের প্রকাশ শুরু হয়; ১৯১২-১৩ পর্যন্ত এই সিরিজে বহু বাঙালি লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল যাঁদের অনেকেই বিখ্যাত হয়েছিলেন পরবর্তী কালে। এই সিরিজে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সরলাবালা দাসীর ‘ঘড়ি চুরি’ নামের গল্পটি ষষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল। সরলাবালা দাসীকেই বাংলা গোয়েন্দা-গল্পের প্রথম লেখক বলা যায়। তাঁর সম্পর্কেও জানতে পারিনি আর কোনও সংবাদ। এই পর্বে অর্থাৎ ১৯২০-২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি-দুটি করে গোয়েন্দা-গল্প অনেকেই লিখেছিলেন যেগুলি প্রধানত প্রকাশিত হত ‘ভারতী’ পত্রিকায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিশোর পত্রিকা ‘রামধনু’-র (প্রথম প্রকাশ ১৯২৮) সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (১৯০৩-১৯৩৯) সৃষ্ট জাপানি ডিটেকটিভ হুকা কাশি। সংখ্যায় কম লিখলেও খুবই জনপ্রিয় ছিল তাঁর লেখা।
(১৮৬৬-১৯১৬) একই সঙ্গে তাঁর উৎপাদিত প্রসাধন-দ্রব্যের প্রচার এবং বাংলা সাহিত্যের সেবার জন্য এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি আহ্বান করলেন গল্প-প্রতিযোগিতা যেখানে শর্ত একটাই— গল্পের কোথাও থাকবে তাঁর কোম্পানির কেশতৈল বা সুগন্ধির নাম। প্রতি বছর তিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলির সঙ্গে আরও কিছু গল্প নির্বাচন করে একটি সংকলন প্রকাশ করতেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সংকলনের প্রকাশ শুরু হয়; ১৯১২-১৩ পর্যন্ত এই সিরিজে বহু বাঙালি লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল যাঁদের অনেকেই বিখ্যাত হয়েছিলেন পরবর্তী কালে। এই সিরিজে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সরলাবালা দাসীর ‘ঘড়ি চুরি’ নামের গল্পটি ষষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল। সরলাবালা দাসীকেই বাংলা গোয়েন্দা-গল্পের প্রথম লেখক বলা যায়। তাঁর সম্পর্কেও জানতে পারিনি আর কোনও সংবাদ। এই পর্বে অর্থাৎ ১৯২০-২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি-দুটি করে গোয়েন্দা-গল্প অনেকেই লিখেছিলেন যেগুলি প্রধানত প্রকাশিত হত ‘ভারতী’ পত্রিকায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিশোর পত্রিকা ‘রামধনু’-র (প্রথম প্রকাশ ১৯২৮) সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (১৯০৩-১৯৩৯) সৃষ্ট জাপানি ডিটেকটিভ হুকা কাশি। সংখ্যায় কম লিখলেও খুবই জনপ্রিয় ছিল তাঁর লেখা।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা-গল্প লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩)। তাঁর ডিটেকটিভ ও তার সহকারী জয়ন্ত এবং মানিক। প্রধানত কিশোরদের জন্যই লিখিত হয়েছিল সেগুলি। তারপরে এলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) এবং নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬)। নীহাররঞ্জনের ডিটেকটিভ কিরীটী রায় ও তার সহকারী সুব্রত-রও জনপ্রিয়তা কম ছিল না। শরদিন্দুর লেখা প্রথম গোয়েন্দা গল্প-র প্রকাশ ১৯৩২-এ (মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। তারপরেই সব বয়সের বাঙালি পাঠকের মন কেড়ে নিলেন সত্যজিৎ রায় (১৯২১- ১৯৯২)। অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের আগে যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)। তাঁর কল্পনাপ্রসূত ডিটেকটিভ পরাশর বর্মাকে আমরা মনে রাখিনি কারণ এই গল্পগুলি তেমন রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। কিন্তু আরও দুটি চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—একজন ভূত-শিকারি মেজোকর্তা। আর একজন বিজ্ঞান-রহস্যের সন্ধানী মামাবাবু। ঘনশ্যাম দাস তথা ঘনাদাকেও অনেকটা ডিটেকটিভ বলা যায়। এই তিনজনেরই ক্রিয়া-কলাপে অনেক রহস্য সমাধানের উদাহরণ আছে। পাঁচ ও ছয়ের দশকে অতি অল্প দামের এবং নিতান্তই কিশোরদের কাছে আকর্ষক ছোটো ছোটো ডিটেকটিভ উপন্যাস পাওয়া যেত। লেখক স্বপনকুমার। অবিশ্বাস্য ধরনের রোমহর্ষক কিন্তু প্রায় শিল্পগুণহীন এই চটি উপন্যাসগুলি আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা অনেকেই পড়েছেন।
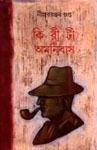

একটি পত্রিকার কথা এখানে বলা উচিত বলে মনে হয়। ‘রোমাঞ্চ’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর কলকাতার হরীতকী বাগান লেন থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সহযোগী ছিলেন আরও অনেকেই। পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই পত্রিকার পরিকল্পনায় এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল। ডিটেকটিভ প্রতুল লাহিড়ী ও তার সহকারী বিশু প্রতিটি গল্পেই আছে, কিন্তু লেখকেরা পৃথক। এক এক সংখ্যায় লিখেছেন বিভিন্ন লেখক। ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি মাসে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পত্রিকাটি ১৯৯০ পর্যন্ত জীবিত ছিল। তবে ১৯৬০-৬৫-র পর থেকে তার জনপ্রিয়তা আর আগের মতো ছিল না। কিন্তু ১৯৩২-এর পর থেকে ১৯৬০-৬৫ পর্যন্ত ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকার আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। এই পত্রিকায় ডিটেকটিভ গল্প লিখেছিলেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৭৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৮১), পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬), বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), আনন্দ বাগচী (১৯৩২-২০১২) এবং আরও অনেকেই যাঁরা স্বভাবত গোয়েন্দা-গল্পের লেখক নন। বিশ শতকের মধ্যভাগে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২)-র দুই তরুণী গোয়েন্দা কৃষ্ণা ও শিখাও বেশ জনপ্রিয় ছিল। ‘কাঞ্চনজা’ এবং ‘প্রহেলিকা’ সিরিজের এই বইগুলির প্রকাশক ছিল ‘দেব সাহিত্য কুটির’।




তারপরেই আমরা লক্ষ করি বাংলা ভাষায় গোয়েন্দা-গল্প লেখবার একটি অপ্রতিরোধ্য স্রোত দেখা দিয়েছে। সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) বালক গোয়েন্দা গোগোল এবং প্রাপ্তবয়স্ক গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর, সমরেশ মজুমদারের (১৯৪২-) কিশোর গোয়েন্দা অর্জুন, নলিনী দাশের (১৯১৬-১৯৯৩) ‘গোয়েন্দা গন্ডালু’ (চারজন কিশোরীর যৌথ গোয়েন্দাগিরি), ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৪১-) পাঁচজন কিশোর-কিশোরীর গোয়েন্দা গোষ্ঠী ‘পাণ্ডব গোয়েন্দা’ ইত্যাদির পর দেখা যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৮), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩৫-) মতো প্রবীণদের সঙ্গে ঈষৎ পরবর্তীকালের সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫) থেকে শুরু করে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭- ) পর্যন্ত এবং আরও অনেকেই লিখেছেন ও লিখছেন গোয়েন্দা-গল্প। অথচ শেষোক্ত লেখকদের মধ্যে অনেকেই অনেকদিন আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কবিতা এবং কথা-সাহিত্যের ভিন্নতর ক্ষেত্রে। সেখানে কবিতা এবং সমাজ ও মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য রচিত কথাসাহিত্যই তাঁদের বিচরণক্ষেত্র। এই লেখকদের মধ্যেই অন্যতম সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনি গোয়েন্দা-গল্প লেখা শুরু করেছেন সত্তর দশকের গোড়ার দিক থেকে।
কিন্তু এত গোয়েন্দা-গল্প লেখার কারণ কী? অনেকটাই প্রকাশকদের আগ্রহ অর্থাৎ বাজারের টান। ‘বাজার’ শব্দটিকে নিশ্চয়ই আমরা তুচ্ছ করব না। মানব-সমাজ এবং মানব-সভ্যতার প্রধান ভিত্তিই হল বাণিজ্য-বুদ্ধি অর্থাৎ বাজার-ব্যবস্থা। এই লেখকদের প্রধান পরিচয় কিন্তু গোয়েন্দা-গল্পের লেখক রূপে নয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আর সত্যজিৎ রায়কে একটু সরিয়ে রাখছি। যদিও অন্য ধরনের লেখার জন্যও এই দুই লেখক আমাদের কাছে পরিচিত, তবু তাঁদের নাম করলে গোয়েন্দা-গল্পের কথাই প্রথমে মনে আসে। কিন্তু অপর লেখকদের ক্ষেত্রে একটি কথাই বলা যায়, প্রকাশকের চাহিদা থাকলেও লেখকদের নিজেদেরও গোয়েন্দা গল্প লেখবার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে অনেকেরই থেকে যায়।সাহিত্যিক সিরাজের নাম করলে একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক চরিত্রের কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদ জেলার নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী এবং ভূস্বামী সম্প্রদায়সহ জীবনের বিবিধ সংগ্রাম ও বৈচিত্র্যকে তুলে এনেছেন তিনি। মনে পড়ে তাঁর ‘তৃণভূমি’, ‘মায়ামৃদঙ্গ’, ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাস। কিন্তু ডিটেকটিভ কর্নেলও তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র।
 সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কীভাবে কর্নেল সিরিজ-এর ডিটেকটিভ গল্প ও উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে কলম রাখলেন - সে বিষয়ে নিজে তিনি কী লিখেছেন তা দেখা যাক। বিষয়টি তিনি নিজেই বিশদ করেছেন তাঁর ‘কর্নেল রচনাসমগ্র’ (দে’জ পাবলিশিং) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়। তাঁর কথায় - সত্তরের গোড়ার দিকে ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০০) দ্রুত একটি উপন্যাস চাইলেন – “রুজির ধান্দায় সাধ্যাতীত লিখে লিখে মগজ খালি।” এ তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি। তখন তাঁর মনে পড়ল ১৯৫৬ সনের কাছাকাছি মুর্শিদাবাদের লালবাগে দেখেছিলেন একটি মানুষকে। প্রৌঢ়, গৌরবর্ণ, সমর্থ শরীর। মনে হয়েছিল ট্যুরিস্ট। অবশ্য পরিচয় হয়নি। কিন্তু দেড় দশক পরে একজন গোয়েন্দা চরিত্রের সন্ধানে মনে পড়ল সেই ব্যক্তিকে। এর পর এই মানুষটির চেহারার আদলে একজন গোয়েন্দাকে ভাবলেন এবং তাঁকে নিয়েই লিখে ফেললেন প্রথম গোয়েন্দা-উপন্যাস। সম্পাদক মণীন্দ্র রায় মুদ্রিত করলেন সেই লেখা। এরপর থেকেই গোয়েন্দা-গল্পের নিয়মিত লেখক রূপেও সিরাজ প্রতিষ্ঠিত।
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কীভাবে কর্নেল সিরিজ-এর ডিটেকটিভ গল্প ও উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে কলম রাখলেন - সে বিষয়ে নিজে তিনি কী লিখেছেন তা দেখা যাক। বিষয়টি তিনি নিজেই বিশদ করেছেন তাঁর ‘কর্নেল রচনাসমগ্র’ (দে’জ পাবলিশিং) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়। তাঁর কথায় - সত্তরের গোড়ার দিকে ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০০) দ্রুত একটি উপন্যাস চাইলেন – “রুজির ধান্দায় সাধ্যাতীত লিখে লিখে মগজ খালি।” এ তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি। তখন তাঁর মনে পড়ল ১৯৫৬ সনের কাছাকাছি মুর্শিদাবাদের লালবাগে দেখেছিলেন একটি মানুষকে। প্রৌঢ়, গৌরবর্ণ, সমর্থ শরীর। মনে হয়েছিল ট্যুরিস্ট। অবশ্য পরিচয় হয়নি। কিন্তু দেড় দশক পরে একজন গোয়েন্দা চরিত্রের সন্ধানে মনে পড়ল সেই ব্যক্তিকে। এর পর এই মানুষটির চেহারার আদলে একজন গোয়েন্দাকে ভাবলেন এবং তাঁকে নিয়েই লিখে ফেললেন প্রথম গোয়েন্দা-উপন্যাস। সম্পাদক মণীন্দ্র রায় মুদ্রিত করলেন সেই লেখা। এরপর থেকেই গোয়েন্দা-গল্পের নিয়মিত লেখক রূপেও সিরাজ প্রতিষ্ঠিত।
তাঁর কাছে গোয়েন্দা-গল্পের চরিত্র কী তা-ও তিনি ওই ভূমিকাতেই লেখেন – “আমার কাছে রহস্যকাহিনি তাস নিয়ে পেশেন্স খেলা। গা জোয়ারি করে সিরিয়াস সাহিত্য হয় না। রহস্যকাহিনি স্রেফ বিনোদন, নিরাপদ এবং তাতে মগজ তাজা থাকে।” উক্তিটি তলিয়ে দেখলে দুটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমত, ‘গা-জোয়ারি’ করে সিরিয়াস সাহিত্য হয় না, কিন্তু গোয়েন্দা-সাহিত্য হয়। দ্বিতীয়ত, রহস্যকাহিনি হল ‘বিনোদন’ এবং ‘নিরাপদ’। ‘নিরাপদ’ শব্দটি কী ভেবে ব্যবহার করেছিলেন? বিক্রির দিক থেকে নিরাপদ? যদি ভেবে থাকেন তা সত্যই। যে কোনও ধরনের গোয়েন্দা-গল্পেরই পাঠক-সংখ্যা সিরিয়াস সাহিত্যের চেয়ে বেশি। কিন্তু একথা বলবার পরেও সিরাজ লেখেন – “কর্নেলকে ছাড়তে পারব না... তিনি আমার দ্বিতীয় সত্তা।” এই কথা কেন বলেন তিনি? তারই সন্ধানে এই নিবন্ধ।
ডিটেকটিভ ফিকশন সম্পর্কে এই ধারণা অনেকেরই আছে যে, সিরিয়াস সাহিত্যের তুলনায় তার সাহিত্যমূল্য কিছু কম। ধারণাটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নয়। তার কারণ ডিটেকটিভ গল্পে একটি নির্দিষ্ট ছক থাকে –
কাহিনির ছক : সমস্যা, সন্ধান, রহস্যভেদ।
চরিত্রের ছক : প্রায় সর্বদা সফল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ন্যায়ের পক্ষে থাকা ডিটেকটিভ।
অন্যদিকে অপরাধী - বুদ্ধিমান হলেও ডিটেকটিভের চেয়ে কম বুদ্ধি।
অপরাধের উদ্দেশ্যের ছক : প্রধানত - অর্থ অথবা বিষয়-সম্পত্তির লোভ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, ত্রিকোণ প্রেম অথবা যে কোনও ধরণের আধিপত্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। এর বাইরে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীকে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের রোগী বলে দেখাবার দৃষ্টান্তও আছে। এখানে ‘গোয়েন্দা পীঠ লালবাজার’ (আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, ২০২২, পৃষ্ঠা- ১০৯) থেকে সুপ্রতিম সরকারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি--
“’The Murder Room’, অন্যতম সেরা উপন্যাস ফিলিস ডরোথি জেমসের। যে প্রখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দাকাহিনি লেখিকা পিডি জেমস নামেই পরিচিত পাঠকদের কাছে। উপন্যাসটিতে লিখেছিলেন, “All the motives for murder are covered by four Ls : Love, Lust, Lucre and Loathing.”
ইংরেজ লেখক ফিলিস ডরোথি জেমস (১৯২০-২০১৪), পি. ডি. জেমস নামে একাধিক ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর ডিটেকটিভের নাম অ্যাডাম ড্যালগ্লিয়েশ; তিনি একাধারে পুলিশ কমান্ডার এবং কবি।ছকে বাঁধা আখ্যান, যেখানে পাঠক প্রথম থেকেই আখ্যানের পরিণাম সম্পর্কে অনেকটাই জ্ঞাত থাকেন সেখানে মহৎ সাহিত্য পাঠে জীবনবোধের যে বিস্তার ও গভীরতা অনুভূত হয় তা সাধারণত গোয়েন্দা-সাহিত্য থেকে পাওয়া যায় না।
প্রথমে গোয়েন্দা গল্পের চরিত্রগুলিকে দেখি। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ডিটেকটিভ চরিত্রে বিপুল বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সে- বিবরণে না গিয়ে কেবল বলে নেওয়া ভালো, বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত গোয়েন্দারা সকলেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কেবল ক্রিস্টির এরকিউল পোয়ারো অবসর গ্রহণের আগে ছিলেন পুলিশ বিভাগে। আগাথা ক্রিস্টির (১৮৯০-১৯৭৬) পরিকল্পনায় সিক্রেট সার্ভিস-এর কোনও কোনও ব্যক্তিকেও পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) কাকাবাবু সিরিজের অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় রহস্য-সন্ধানী কাকাবাবুর (ঠিক ডিটেকটিভ নন) কোনও কোনও বন্ধুকে পাওয়া যায় যাঁরা সিক্রেট সার্ভিস-এ আছেন বা ছিলেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গোয়েন্দা-গল্পের চরিত্রগুলির দিকে তাকানো যাক।
কর্নেল নীলাদ্রি সরকার: প্রৌঢ়, গৌরবর্ণ, শক্ত শরীর, চুরুট কফি, টাক, টুপি, বাইনোকুলার এবং সঙ্গে কীট-পতঙ্গ ধরবার জাল; আগ্রহ: গাছপালা, পাখি, পোকা এবং অবশ্যই অপরাধ। গোয়েন্দা-গল্পের পৃথিবীতে বহু বিচিত্র গোয়েন্দার দেখা পাওয়া যায়—বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, বালক; নারী ও পুরুষ। লক্ষ করা যায়, ডিটেকটিভদের প্রায়শই নিজস্ব সংসারের সন্ধান পাওয়া যায় না। এদেশে এবং বিদেশেও। ব্যতিক্রম শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ। তার আছে স্ত্রী-পুত্র-শ্যালক। আর ব্যতিক্রম বাংলা সাহিত্যের দুই নারী গোয়েন্দা - সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন আর তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গী। মেয়েদের ঘর-সংসার থাকবে না - এরকম বোধ হয় ভাবতে পারেননি লেখকেরা। মেয়েরা সংসারে থেকে, স্বামী-সন্তান সামলে, তাদের সমর্থনে ও সহযোগিতায় গোয়েন্দাগিরি করবে - এটাই বেশ নিরাপদ। মেয়ে-গোয়েন্দা একা থাকবে—এটা ভাবতে ভারতীয় লেখকদের এখনও কিছুদিন লাগবে। আগাথা ক্রিস্টি কিন্তু সৃষ্টি করেছেন মিস মার্পল-কে। ইংল্যান্ড-এর শহরতলিতে একা থাকেন বৃদ্ধা। অবশ্য তাঁর এক ভাইপো এবং তার স্ত্রী আছে - কখনও কখনও আসে। বিচিত্র এক ডিটেকটিভের কথা না বলে পারছি না। গবেষক পণ্ডিত সুকুমার সেন মশাই তাঁর স্রষ্টা, তিনি হলেন বিখ্যাত কবি কালিদাস। প্রখর বুদ্ধি আর মানবচরিত্র-জ্ঞানের সম্মিলনে তিনি প্রাচীন যুগের অনেক সমস্যা সমাধান করেছিলেন। কোথাও কোথাও তাঁর পত্নীই তাঁর সহকারী। তাঁর দু-জন চরও আছে, যারা সংবাদ সংগ্রহ করে দেয়। গল্পগুলি বেশ জমাট এবং নতুন স্বাদের।
গোয়েন্দার সহকারী : ডিটেকটিভ-এর সহকারী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন কোনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০)-এর ওয়াটসন এবং আগাথা ক্রিস্টির (১৮৯০-১৯৭৬) হেস্টিংস-এর চরিত্রে। বাংলা সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মানিক, নীহাররঞ্জন গুপ্তের সুব্রত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজিতও সমানই বিখ্যাত। তারপর কিশোর-পাঠকদের মুখ চেয়ে সত্যজিৎ রায় নিয়ে এলেন প্রদোষ মিত্রের কিশোর-সহকারী তপেশকে। এই পরম্পরাও বাংলা সাহিত্যে খানিকটা আছে। অনেক সময় দেখা যায়, ঠিক সহকারী না থাকলেও ডিটেকটিভ-এর একজন সঙ্গী আছেন। বিমল করের (১৯২১-২০০৩) ম্যাজিশিয়ান গোয়েন্দা কিকিরা বা কিংকর কিশোর রায়ের সঙ্গী ছিল কয়েকজন তরুণ। অনেক সময় একজন সঙ্গী আখ্যানের কথক। ওয়াটসন, হেস্টিংস, অজিত এবং তপেশ কথক হিসেবে খুব চেনা। নীলাদ্রি সরকারেরও আছেন তেমন একজন সঙ্গী-সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। তিনিও সিরাজের কোনও কোনও গোয়েন্দা-গল্পের বিবৃতিকার।
দ্বিতীয় গোয়েন্দা : এই পরিকল্পনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আগাথা ক্রিস্টি এরকিউল পোয়ারো-র কোনও কোনও আখ্যানে পুলিশ বিভাগের নামকরা ডিটেকটিভ-দের এনেছেন। কিন্তু সেখানে সেই দ্বিতীয় গোয়েন্দার ব্যর্থতা প্রমাণ করে তাঁকে করে তুলেছেন কিছুটা হাস্যকর। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ-কে এনেছেন, তাঁর নাম কৃতান্ত কুমার হালদার। তিনি নীলাদ্রি সরকারের বন্ধুর মতোই, প্রতিদ্বন্ধী নন। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলেন এবং কিছুটা হাস্যরসের জোগান দেন। এই দ্বিতীয় ডিটেকটিভ সিরাজের গল্পগুলির গঠনে এবং আবহে কোনও কাজে আসেননি। ডিটেকটিভ গল্প তো হাসির গল্প নয়। হাস্যরসকে ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্গে অসামান্য কুশলতায় যিনি মেলাতে পেরেছেন তিনি বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় রহিত সেই হাস্যরসের শিল্পী শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)। বাংলা গোয়েন্দা-গল্পে একসময়ে ‘রামধনু’ (প্রকাশ ১৯২৮) পত্রিকার সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৩-১৯৩৯) জাপানি ডিটেকটিভ হুকা কাশিকে নিয়ে কয়েকটি গল্প লিখে বেশ সাড়া ফেলেছিলেন। তাঁকে ও তাঁর ডিটেকটিভকে স্মরণে রেখেই শিবরাম চক্রবর্তী-র আশ্চর্য সৃষ্টি ডিটেকটিভ কল্কে কাশি। অগ্রজ লেখকের ঋণ স্মরণে রেখেই এই নাম দিয়েছিলেন শিবরাম - হুকা বা হুঁকার ছোটো ভাই কল্কে। কিন্তু কল্কে কাশিকে নিয়ে লেখা গল্পগুলি অসামান্য। ডিটেকটিভ উপাদানের সঙ্গে হাস্যরসের এমন প্রতিভাদীপ্ত সমন্বয় বিশ্বসাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ। সিরাজের কৃতান্ত কুমার হালদারের ভূমিকা তাঁর ডিটেকটিভ-গল্পে অকিঞ্চিৎকর।
পুলিশ অফিসার : গোয়েন্দা-গল্পে প্রায়শই এক বা একাধিক পুলিশ অফিসার থাকেন। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোনও অপরাধের তদন্ত করতে গেলে এমন অনেক তথ্য এবং সহায়তা তাঁর প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক যেগুলি এককভাবে সহজে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। যেমন ফরেন্সিক রিপোর্ট, কোনও ব্যক্তির অতীত অপরাধের ইতিহাস, পুলিশ-ডাক্তার-এর অভিমত, সম্ভাব্য অপরাধীদের পরিচয় গোপন চর নিয়োগ করা ইত্যাদি। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায়, প্রাইভেট ডিটেকটিভ-এর সঙ্গে থানার অফিসারদের সংযোগ আছে। যেমন, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখায় সুন্দরবাবু, আগাথা ক্রিস্টির লেখায় ইন্সপেক্টর ইয়াপ (Japp)। প্রায়ই দেখা যায়, ডিটেকটিভ-এর তুলনায় পুলিশ অফিসারের তদন্ত-বুদ্ধি কিছু কম। তবে সত্যজিৎ রায়ের গল্পে প্রদোষ মিত্রের পরিচিত পুলিশ অফিসারেরা দক্ষ এবং দায়িত্বশীল; কোনও একজন নির্দিষ্ট অফিসার নেই। সিরাজের গল্পে অশোক গুপ্ত নামের এক পুলিশ অফিসার আছেন যাঁর ভূমিকা মোটের ওপর ইতিবাচক কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয়। পুলিশ অফিসারের কথায় মনে পড়ে, আগাথা ক্রিস্টির একাধিক গল্পে ইন্সপেক্টর ব্যাট্ল্ অতি উচ্চস্তরের একজন পুলিশ-ডিটেকটিভ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ডিটেকটিভ শবরও পুলিশের গোয়েন্দা।
গোয়েন্দার পরিচারক : শখের ডিটেকটিভদের একজন করে পরিচারক থাকে। যেমন শরদিন্দুর ব্যোমকেশের পুঁটিরাম। তেমনই কর্নেল-এর পরিচারকের নাম ষষ্ঠীচরণ। আগাথা ক্রিস্টির পোয়ারো-র বিশ্বস্ত ভ্যালে হল জর্জ। এই জর্জ-এর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খুবই চিহ্নিত। পোয়ারো অনেক সময় তার বিচার-বুদ্ধি এবং সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরও করেন। অন্য লেখকদের লেখায় এ ধরনের কিছু পাওয়া যায় না। পরিচারকদের কাজ কেবল অভ্যাগতদের ডেকে বসানো এবং চা-কফি ইত্যাদি পরিবেশন করা।
স্থান প্রসঙ্গে আসা যাক। সিরাজের গোয়েন্দা-গল্পে স্থানের ব্যাপারটা একটু ভাবিয়ে তুলতে পারে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নাম করলেই তাঁর কথাসাহিত্যের পটভূমি রূপে মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ জমি, তৃণভূমি, গ্রামপ্রান্তিক জঙ্গল ও নদী, বাংলাদেশ সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকা ইত্যাদি মনে পড়ে। কিন্তু তাঁর গোয়েন্দা-গল্পে আছে কলকাতা শহর - এলিয়ট রোড, থিয়েটার রোড, পার্ক স্ট্রিট, ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট, এককালের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়া। কর্নেল থাকেন শহরের স্বচ্ছল এলাকার ফ্ল্যাট ‘সানি ভিলা’য়। কলকাতা শহরের বাইরে যখন তিনি যান তা একেবারে অন্যধরনের স্থানপট - ধানবাদের খনি-অঞ্চল, উত্তরবঙ্গের অয়েল রিফাইনারি, নেপাল সীমান্তের ডমরুনাথ, সমুদ্রতীরের চন্দনপুর, মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল। সেসব জায়গায় কর্নেল থাকেন হোটেল, রিসর্ট, ফরেস্ট বাংলো, পুরোনো জমিদারবাড়ির অতিথিভবনে। সাধারণভাবেও লক্ষ করা যায়, অধিকাংশ গোয়েন্দাই নগরবাসী। এখানেও ব্যতিক্রম ক্রিস্টির মিস মার্পল। তিনি থাকেন গ্রামে এবং মনে করেন যে, অপরাধের চরিত্র গ্রাম এবং শহর - সর্বত্রই একই রকম। তাদের বাইরের চেহারায় পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু ভিতরের মনস্তাত্ত্বিক বিন্দুটি এক। এখন কথা হল, এই শহুরে ডিটেকটিভ কর্নেল কি সিরাজের দ্বিতীয় সত্তা? — যেমন তিনি বলেছেন তাঁর নিজের লেখা ভূমিকায়। এ প্রসঙ্গটি নিবন্ধের শেষে তুলে আনবার চেষ্টা করব।
তৃতীয়ত আসে, গোয়েন্দা-গল্পের সিচুয়েশনের প্রশ্ন। অধিকাংশ গোয়েন্দা-গল্পে সিচুয়েশনের বিশেষ পার্থক্য থাকে না। চুরি, খুন, কিডন্যাপ, নিরুদ্দেশ, ব্ল্যাকমেল, উড়োচিঠি, ভুল ঠিকানা, ছদ্ম পরিচয়, ডুপ্লিকেট চাবি ইত্যাদি। সিরাজের গল্পেও সেরকমই দেখা যায়। একটি উপন্যাসে আছে নাটকের একটি হত্যাদৃশ্যের মধ্যে সত্যিকারের খুন। আর একটি বড়ো গল্পে আছে জ্যান্ত মানুষকে মৃত সাজিয়ে মজা করবার চেষ্টা, কিন্তু ঘটে যায় সত্যিকারের মৃত্যু। এই দুটি সিচুয়েশনই আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসেও দেখেছি। বস্তুত বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য ডিটেকটিভ গল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুসরণ নিয়ে একটা গবেষণাই করা যায়। সেই প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্তও এই ধারা বহমান।
সব শেষে আসে, গোয়েন্দা গল্পে অপরাধীর উদ্দেশ্যের কথা। এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে, এখানে তারই পুনরুক্তি করছি—টাকা ও সম্পত্তির লোভ, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, ত্রিকোণ প্রেম - বিশ্বের সব অপরাধেরই উদ্দেশ্য এরই মধ্যে ঘোরাফেরা করে । এছাড়াও ব্যতিক্রমী দু-একটি উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, একজন ঘৃণ্য অপরাধীকে শাস্তি দেবার অন্য উপায় না দেখে তাকে সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হত্যা করা; অথবা বিকৃত-মস্তিষ্ক কোনও অপরাধীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া, অথবা নিছকই আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কাউকে হত্যা করা। রাজনৈতিক হত্যা এর মধ্যে পড়ে। আরও আছে নিজের বিপদের ভয়ে কাউকে হত্যা করা।
 একথাটি স্পষ্ট থাকাই ভালো যে, গোয়েন্দা-গল্প এবং বাস্তরের গোয়েন্দাদের কর্মপদ্ধতি অনেকটাই আলাদা। যেখানে প্রকৃত অপরাধ ঘটেছে এবং পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দারা তার তদন্ত করছেন -সেখানে কর্ম-পদ্ধতি অন্য রকম। সেখানে ডিটেকটিভ একা বসে মাথা ঘামিয়ে রহস্যের সমাধান করে ফেলবেন - তেমন কোনও পরিস্থিতি দেখাই দেয় না। প্রথম থেকেই পুলিশ বিভাগের তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল প্রতিটি বিন্দুতে অনুসন্ধান করেন; ঘটনার কাছাকাছি উপস্থিত ব্যক্তিদের এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকবার সম্ভাবনা আছে এমন দূরের মানুষদেরও বার বার জেরা করেন; সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তির পিছনে চর লাগিয়ে রাখেন; হাত-পা-এর ছাপ এবং জামা-কাপড়, চাদর, পর্দা, কার্পেট ব্যবহৃত বস্তু— সব কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ রাসায়নিক পরীক্ষা হয়। প্রয়োজনে পুলিশের নিজস্ব সোর্স ব্যবহার করা হয়। পুলিশ-বিভাগের দায়িত্ব কেবল অপরাধী শনাক্ত করাতেই শেষ হয়ে যায় না। অপরাধীর বিরুদ্ধে কেস সাজিয়ে আদালতে বিচারকের সামনে তা উপস্থিত করা পর্যন্ত পুলিশের কাজ থাকে অক্লান্ত। কেস চলতে চলতেও পুলিশকে সম্ভাব্য সূত্র উঠে আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে লক-আপ-এ তুলে নিয়ে গিয়ে কমবেশি নির্যাতনের সাহায্যে তার কাছ থেকে তথ্য আদায় করে নেবার অধিকারও পুলিশের আছে। সাম্প্রতিক কালে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন অতীত কেস-এর বিবরণ দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসার সুপ্রতিম সরকার। তাঁর বিবৃত ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’ সিরিজ-এর আখ্যানগুলি থেকে বোঝা যাবে প্রকৃত গোয়েন্দা আর গল্পের গোয়েন্দার পার্থক্য কোথায়। একটি বড়ো পার্থক্য এই যে - গল্পের গোয়েন্দা রহস্যের সমাধান করেন প্রায় একক ভাবে; পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে একা কাজ করবার কোনও পরিস্থিতি বা ভাবনাই দেখা দেয় না। এই সুপ্রতিম সরকার তাঁর ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’ প্রথম খণ্ডের এক জায়গায় বলেছেন, পুলিশের তদন্তকারীর কাছে জীবনের মধুরতম বাক্যটি হল – “মারবেন না সার, সব বলছি।” এই ধরনের সুযোগ প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিতে পারেন না। এরকম ক্ষেত্রে তাঁকে পুলিশেরই সাহায্য নিতে হয়। এজনাই গল্পের গোয়েন্দাদের সঙ্গে পুলিশ-বিভাগের সু-সম্পর্কের একটি রাস্তা প্রায় সব লেখকই খুলে রাখেন। গোয়েন্দা-গল্পের নিরপেক্ষ পাঠককে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, গল্পের চেয়ে পুলিশ বিভাগের প্রকৃত অপরাধ-কাহিনি পাঠের উত্তেজনা তীক্ষ্ণতর। এধরনের একটি অসামান্য প্রকৃত গোয়েন্দা-কাহিনি সাহিত্যে অমরত্ব পেয়েছে—সেটি হল ফ্রেডারিক ফোরসাইথ (১৯৩৮-) লিখিত, ১৯৭১-এ প্রকাশিত ‘দ্য ডে অব দ্য জ্যাক্যাল’। ফ্রান্স-এর প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ফরাসি ডিটেকটিভ বিভাগের প্রাণপণ প্রয়াসের এই বিবরণের কাছাকাছি কোনও বানানো ডিটেকটিভ গল্প পৌঁছোতে পারে না। অবশ্য গোয়েন্দা-গল্পের লেখকদের উদ্দেশ্যও তা নয়। নিঃসন্দেহেই গোয়েন্দা-গল্প লেখা হয় বিশেষ ধরনের বিনোদনের উদ্দেশ্যে। বাস্তব ঘটনার দর্পণ নির্মাণ করবার আকাঙ্ক্ষা গোয়েন্দা-গল্পের লেখকদের থাকেও না। বরং গল্প-লেখকদের কলমে উঠে আসে সমাজের ছবি।
একথাটি স্পষ্ট থাকাই ভালো যে, গোয়েন্দা-গল্প এবং বাস্তরের গোয়েন্দাদের কর্মপদ্ধতি অনেকটাই আলাদা। যেখানে প্রকৃত অপরাধ ঘটেছে এবং পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দারা তার তদন্ত করছেন -সেখানে কর্ম-পদ্ধতি অন্য রকম। সেখানে ডিটেকটিভ একা বসে মাথা ঘামিয়ে রহস্যের সমাধান করে ফেলবেন - তেমন কোনও পরিস্থিতি দেখাই দেয় না। প্রথম থেকেই পুলিশ বিভাগের তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল প্রতিটি বিন্দুতে অনুসন্ধান করেন; ঘটনার কাছাকাছি উপস্থিত ব্যক্তিদের এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকবার সম্ভাবনা আছে এমন দূরের মানুষদেরও বার বার জেরা করেন; সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তির পিছনে চর লাগিয়ে রাখেন; হাত-পা-এর ছাপ এবং জামা-কাপড়, চাদর, পর্দা, কার্পেট ব্যবহৃত বস্তু— সব কিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ রাসায়নিক পরীক্ষা হয়। প্রয়োজনে পুলিশের নিজস্ব সোর্স ব্যবহার করা হয়। পুলিশ-বিভাগের দায়িত্ব কেবল অপরাধী শনাক্ত করাতেই শেষ হয়ে যায় না। অপরাধীর বিরুদ্ধে কেস সাজিয়ে আদালতে বিচারকের সামনে তা উপস্থিত করা পর্যন্ত পুলিশের কাজ থাকে অক্লান্ত। কেস চলতে চলতেও পুলিশকে সম্ভাব্য সূত্র উঠে আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে লক-আপ-এ তুলে নিয়ে গিয়ে কমবেশি নির্যাতনের সাহায্যে তার কাছ থেকে তথ্য আদায় করে নেবার অধিকারও পুলিশের আছে। সাম্প্রতিক কালে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন অতীত কেস-এর বিবরণ দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন অভিজ্ঞ আইপিএস অফিসার সুপ্রতিম সরকার। তাঁর বিবৃত ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’ সিরিজ-এর আখ্যানগুলি থেকে বোঝা যাবে প্রকৃত গোয়েন্দা আর গল্পের গোয়েন্দার পার্থক্য কোথায়। একটি বড়ো পার্থক্য এই যে - গল্পের গোয়েন্দা রহস্যের সমাধান করেন প্রায় একক ভাবে; পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে একা কাজ করবার কোনও পরিস্থিতি বা ভাবনাই দেখা দেয় না। এই সুপ্রতিম সরকার তাঁর ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’ প্রথম খণ্ডের এক জায়গায় বলেছেন, পুলিশের তদন্তকারীর কাছে জীবনের মধুরতম বাক্যটি হল – “মারবেন না সার, সব বলছি।” এই ধরনের সুযোগ প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিতে পারেন না। এরকম ক্ষেত্রে তাঁকে পুলিশেরই সাহায্য নিতে হয়। এজনাই গল্পের গোয়েন্দাদের সঙ্গে পুলিশ-বিভাগের সু-সম্পর্কের একটি রাস্তা প্রায় সব লেখকই খুলে রাখেন। গোয়েন্দা-গল্পের নিরপেক্ষ পাঠককে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, গল্পের চেয়ে পুলিশ বিভাগের প্রকৃত অপরাধ-কাহিনি পাঠের উত্তেজনা তীক্ষ্ণতর। এধরনের একটি অসামান্য প্রকৃত গোয়েন্দা-কাহিনি সাহিত্যে অমরত্ব পেয়েছে—সেটি হল ফ্রেডারিক ফোরসাইথ (১৯৩৮-) লিখিত, ১৯৭১-এ প্রকাশিত ‘দ্য ডে অব দ্য জ্যাক্যাল’। ফ্রান্স-এর প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ফরাসি ডিটেকটিভ বিভাগের প্রাণপণ প্রয়াসের এই বিবরণের কাছাকাছি কোনও বানানো ডিটেকটিভ গল্প পৌঁছোতে পারে না। অবশ্য গোয়েন্দা-গল্পের লেখকদের উদ্দেশ্যও তা নয়। নিঃসন্দেহেই গোয়েন্দা-গল্প লেখা হয় বিশেষ ধরনের বিনোদনের উদ্দেশ্যে। বাস্তব ঘটনার দর্পণ নির্মাণ করবার আকাঙ্ক্ষা গোয়েন্দা-গল্পের লেখকদের থাকেও না। বরং গল্প-লেখকদের কলমে উঠে আসে সমাজের ছবি।
নিবন্ধের শেষে পূর্ব উল্লিখিত প্রশ্নটিকে সামনে রাখব। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কেন কর্নেল-কে তাঁর ‘দ্বিতীয় সত্তা’ বলে উল্লেখ করলেন? মনে হয় একথা বললে কেউ আহত হবেন না যে, তাঁর ‘তৃণভূমি’, ‘মায়ামৃদঙ্গ’ বা ‘অলীক মানুষ’ উপন্যাসের কাছাকাছি পৌঁছবে না তাঁর ‘গোয়েন্দা-উপন্যাস’। তাঁর লেখা কোনও গোয়েন্দা-গল্পই স্পর্শ করতে পারবে না – ‘হরবোলা ছেলেটা’, ‘বাগাল’, ‘সোনার পিদিম’, ‘গোঘ্ন’, ‘গাছটা বলেছিল’ ইত্যাদি গল্পের অন্তর-তল। কেবল সিরাজ কেন? কোনও লেখকের ক্ষেত্রেই তা হয়নি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সমরেশ বসু থেকে শুরু করে সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় – কারও লেখা সম্পর্কেই বলা যাবে না যে তাঁদের গোয়েন্দা-গল্প তাঁদের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের তুল্য হতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের কথা ওঠে না কারণ তিনি ভিন্ন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির দিকে যাননি। একমাত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি - তাঁর ডিটেকটিভ গল্প তাঁর অন্য ধরনের লেখার সম-মান সম্পন্ন। শরদিন্দু সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকৃতপক্ষে পাঠক-মনোরঞ্জক রোমান্টিক উপন্যাস—খুব উত্তীর্ণ সাহিত্য নয়। কিন্তু তাঁর কিছু ছোটোগল্প সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না - যেমন ‘চুয়াচন্দন’, ‘রক্তসন্ধ্যা’। তাঁর কিছু ডিটেকটিভ গল্পও বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসে স্থান পাবে। যেমন ‘অর্থমনর্থম’, ‘বিষের ধোঁয়া’, ‘সত্যকাম’। এই গল্পগুলিতে ডিটেকশন এবং মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম ভালোমন্দের খেলা একই সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে। তাই হয়ে উঠেছে সাহিত্য।
 প্রসঙ্গত, আর্থার কোনান ডয়েল এবং আগাথা ক্রিস্টি-র কথাও একটু বলে নেওয়া যায়। কোনান ডয়েল কিছু অন্য ধরনের গল্প লিখেছিলেন, তার কয়েকটি অন্তত বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। তবে আগাথা ক্রিস্টি - যদিও অন্যধরনের গল্প-উপন্যাস বেশ কিছু লিখেছেন - সেগুলি তাঁর ডিটেকটিভ সাহিত্যের উচ্চতা স্পর্শ করেনি। তার একটি কারণ আছে। ডিটেকশনের বৈচিত্র্য এবং মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছাড়াও তাঁর ডিটেকটিভ গল্পে পাওয়া যায় দুই বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন
প্রসঙ্গত, আর্থার কোনান ডয়েল এবং আগাথা ক্রিস্টি-র কথাও একটু বলে নেওয়া যায়। কোনান ডয়েল কিছু অন্য ধরনের গল্প লিখেছিলেন, তার কয়েকটি অন্তত বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। তবে আগাথা ক্রিস্টি - যদিও অন্যধরনের গল্প-উপন্যাস বেশ কিছু লিখেছেন - সেগুলি তাঁর ডিটেকটিভ সাহিত্যের উচ্চতা স্পর্শ করেনি। তার একটি কারণ আছে। ডিটেকশনের বৈচিত্র্য এবং মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছাড়াও তাঁর ডিটেকটিভ গল্পে পাওয়া যায় দুই বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ইউরোপ-এর বাস্তব সমাজচিত্র এবং অতুলনীয় রসবোধ। সেই সঙ্গে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা এবং মঞ্চ-জগৎ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের বিস্তারও তাঁর লেখাকে প্রকৃত সাহিত্যের যে স্বাদ দিয়েছে তা তাঁর অন্য ধরনের সাহিত্যে কিন্তু পাওয়া যায় না; ডিটেকটিভ গল্পেই পাওয়া যায়। কিন্তু ডিটেকটিভ গল্পের বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের ব্যাপার দেখা যায়নি। তবে আগাথা ক্রিস্টির লেখার একটি দুর্বলতা হল সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিরূপতার আতিশয্য।
ইউরোপ-এর বাস্তব সমাজচিত্র এবং অতুলনীয় রসবোধ। সেই সঙ্গে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা এবং মঞ্চ-জগৎ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের বিস্তারও তাঁর লেখাকে প্রকৃত সাহিত্যের যে স্বাদ দিয়েছে তা তাঁর অন্য ধরনের সাহিত্যে কিন্তু পাওয়া যায় না; ডিটেকটিভ গল্পেই পাওয়া যায়। কিন্তু ডিটেকটিভ গল্পের বাঙালি লেখকদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের ব্যাপার দেখা যায়নি। তবে আগাথা ক্রিস্টির লেখার একটি দুর্বলতা হল সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিরূপতার আতিশয্য।
কিন্তু মোটের উপর মহৎ সাহিত্য নয় জেনেও প্রতিষ্ঠিত বাঙালি লেখকেরা গোয়েন্দা-গল্প লেখেন, প্রভূত পরিমাণে পড়েন এবং আমরা পাঠকেরাও তাঁদের লেখা পড়ি। কেন এই আকর্ষণ? কীসের এই আকর্ষণ?
এক্ষেত্রে আমি কোনও যুক্তি বা তত্ত্ব উত্থাপনের চেষ্টা করব না। কেবল নিজের ভাবনা এবং অনুভব ব্যক্ত করবার চেষ্টা করব। মানুষের জীবনযাপনের বাস্তবতায় কখনও কখনও অদ্ভুত এক রহস্য জড়িয়ে যায়। আশ্চর্য কোনও এক চিত্তমথিত জিজ্ঞাসা যার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্নটিকে ফেলে রাখলে প্রাত্যহিকের সংসার-যাত্রায় হয়তো কোনও ক্ষতি হবে না, তবু সেই প্রশ্নটি যার মনে বিঁধে যায় তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি নেই। সেই প্রশ্নের সমাধান কখনও হয়, কখনও হয় না। যখন সমাধান হয় তখন প্রায়শই সেই সমাপ্তি ডেকে আনে দুঃখ ও যন্ত্রণা। কিন্তু তা হলেও সেই গভীর কষ্টকে অনুভব করবার মধ্যে দিয়েই জীবনকে যেন পূর্ণভাবে পায় সেই সন্ধানকারী মানুষটি - সমস্ত যন্ত্রণাসহ।
ধ্রুপদী উদাহরণ হল সফোক্লিস রচিত ট্র্যাজেডি ‘রাজা ইদিপাস’। এই নাটকের কাহিনি জানা আছে সকলেরই। থিবিস-এর রাজা লাইয়ুস-কে হত্যা করেছে কে? এই হত্যাকারীর সন্ধান করে বর্তমান রাজা ইদিপাস। সন্ধানের শেষে সত্য যখন উন্মোচিত হয় তখন ইদিপাস সেই অজ্ঞানকৃত পাপের শাস্তি গ্রহণ করেছিল নিজেই। স্বেচ্ছা-অন্ধ, স্বেচ্ছা-নির্বাসিত রাজা ইদিপাস জীবনের এক গভীর সত্যকে উপলব্ধি করেছিল মর্মান্তিক কষ্টের ভিতর দিয়ে। এই আখ্যানের গোপন রহস্য কেবল রহস্য হয়েই থাকেনি, হয়ে উঠেছে জীবন-উপলব্ধির সোপান।
অন্য ধরনের একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাসে দেখা যায়। রমেশ আর কমলা পরস্পরকে জানবার পর কয়েকটি দিন ভুল আইডেন্টিটির সম্পর্ককে বিশ্বাস করেছিল। কয়েকদিনের মধ্যে তাদের মনে মনে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল প্রথম দাম্পত্য প্রেমের এক মধুর সুর। তারপর যখন উদ্ঘাটিত হল সত্য, তখন তারা যুক্তি দিয়ে নিজেদের জীবনকে আবার অন্যপথে এবং সমাজ-সঙ্গত পথে চালিত করল। আপাতভাবে সংসারে সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু তাদের দুজনেরই মনের মধ্যে সেই কয়েকদিনের স্মৃতি-মাধুর্য একই সঙ্গে সুখ ও বেদনার তরঙ্গ তুলতে থাকবে বাকি জীবন। ঋতুপর্ণ ঘোষ (১৯৬৩-২০১৩) ‘নৌকাডুবি’ চলচ্চিত্রে বিষয়টি অসামান্য সূক্ষ্মতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন চলচ্চিত্রটি দেখবার পর উপন্যাসের পাতা উল্টে দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথও কিন্তু তাঁর অনবদ্য ভাষায় মূর্ত করেছিলেন ওই একই উপলব্ধি। ভাষার মধ্যে দিয়ে তা মস্তিষ্কে তখন পুরোটা প্রবেশ করেনি। চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও ভাষার সংযোগে সেই উপলব্ধি দর্শকদের আরও প্রত্যক্ষভাবে আলোড়িত করতে পেরেছিল।
 শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘নীলু হাজরার হত্যা রহস্য’ উপন্যাসে গল্পের বুনোটের মধ্যে দিয়ে হত্যা-রহস্যের যে সম্ভাব্য সমাধান উঠে আসে তা লেখকের শবর-সিরিজের যে কোনও উপন্যাসের চেয়ে শিল্পোত্তীর্ণ। উপরি-উক্ত তিনটি উপন্যাসের কোনওটিতেই কোনও নির্দিষ্ট ডিটেকটিভ নেই। জীবন থেকে উঠে আসা এক আখ্যানের মধ্যে গোপন রহস্যের উদ্ঘাটন কী অপরিসীম বেদনার সঙ্গে জীবনবোধের পরিণতি সাধন করে - তারই দৃষ্টান্ত এই তিনটি উপন্যাস।
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘নীলু হাজরার হত্যা রহস্য’ উপন্যাসে গল্পের বুনোটের মধ্যে দিয়ে হত্যা-রহস্যের যে সম্ভাব্য সমাধান উঠে আসে তা লেখকের শবর-সিরিজের যে কোনও উপন্যাসের চেয়ে শিল্পোত্তীর্ণ। উপরি-উক্ত তিনটি উপন্যাসের কোনওটিতেই কোনও নির্দিষ্ট ডিটেকটিভ নেই। জীবন থেকে উঠে আসা এক আখ্যানের মধ্যে গোপন রহস্যের উদ্ঘাটন কী অপরিসীম বেদনার সঙ্গে জীবনবোধের পরিণতি সাধন করে - তারই দৃষ্টান্ত এই তিনটি উপন্যাস। সমরেশ বসুর ‘বিবর’ উপন্যাসে এক আশ্চর্য গোয়েন্দা চরিত্র আছে। আততায়ী নায়ক তার খুনের জায়গায় বারবার ফিরে আসে। তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে ডিটেকটিভ। সেই গোয়েন্দার কোনো নাম নেই, সে কথা বলে না, কেবল মর্মভেদী চেয়ে থাকে। হত্যাকারী নিজেই ধরা দেয় তার কাছে। যেন সে হত্যাকারীর নিরুদ্ধ বিবেক, কিংবা বিশ্ববিধানের প্রতিনিধি।
সমরেশ বসুর ‘বিবর’ উপন্যাসে এক আশ্চর্য গোয়েন্দা চরিত্র আছে। আততায়ী নায়ক তার খুনের জায়গায় বারবার ফিরে আসে। তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে ডিটেকটিভ। সেই গোয়েন্দার কোনো নাম নেই, সে কথা বলে না, কেবল মর্মভেদী চেয়ে থাকে। হত্যাকারী নিজেই ধরা দেয় তার কাছে। যেন সে হত্যাকারীর নিরুদ্ধ বিবেক, কিংবা বিশ্ববিধানের প্রতিনিধি।
ডিটেকটিভ ছাড়া ডিটেকটিভ-উপন্যাসের দুটি কৌতুকরস-নিষিক্ত কিশোরপাঠ্য দৃষ্টান্ত শিবরাম চক্রবর্তীর ‘বর্মার মামা’ এবং লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭)-এর ‘পদীপিসির বর্মী বাক্স’। এই দুটিতেও দুটি বালক পরিস্থিতির বিন্যাসে যথাক্রমে আত্মরক্ষা ও রহস্যের সমাধান করেছে। সেই সঙ্গে দুটি লেখাতেই আছে অফুরন্ত মজা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘সোনার পিদিম’ এবং আরও কোনও কোনও গল্পে এভাবেই মিশে আছে গোপন রহস্যের রক্তাক্ত সংকেত। হয়তো জীবনের এই বিচিত্র রহস্যময়তার টানেই মানুষ ডিটেকটিভ-কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট হয়।
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কর্নেল-কে তাঁর ‘দ্বিতীয় সত্তা’ বলেছেন। এই উক্তির মূলে তাঁর শিল্পী-মনের গঠনের দিকটি উল্লেখ্য। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে এই হিংস্রতা এবং হনন-ইচ্ছা বার বার কি জ্বলে ওঠে না? মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলাদেশ-সীমান্তবর্তী যে অঞ্চল তাঁর অধিকাংশ লেখার পটভূমি সেখানে লোকায়ত মানুষের জীবনযাপনে অপরাধ-প্রবণতা এবং হিংসতা মিশে আছে অনেকখানি। সেখানে আইন-আদালতের হাত দ্রুত পৌঁছোয় না। সেখানে তথাকথিত নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন বড়ো কঠিন কারণ বেঁচে থাকার পথে সেখানে বিস্তর বাধা। সিরাজের লেখা গল্প-উপন্যাসে হত্যা, মৃত্যু, আত্মহত্যার ঘটনা বারবার আসে। কেবল ‘তৃণভূমি’ উপন্যাসটিতেই কতগুলি হত্যা এবং মৃত্যুর দৃশ্য আছে, ভেবে দেখুন। একটি উপন্যাসের পরিসরে সাত-আটটি মৃত্যু-র ঘটনা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই উপন্যাস পড়বার সময়ে পাঠকের মন কোনও প্রশ্ন তোলে না। সিরাজের গোয়েন্দা-গল্পেও এই হত্যা এবং মৃত্যুর প্রাধান্য। কথাটি এই কারণেই বলা, আরও অনেক গোয়েন্দা-গল্পে চৌর্যবৃত্তি, প্রতারণা, নিরুদ্দেশ হওয়া ইত্যাদি বিষয় বিশ্বের সর্বত্রই দেখা যায়। বিদেশি ডিটেকটিভ গল্পে প্রায়ই দেখি, পারিবারিক কারণে পুলিশকে জানানোর অনীহা-বশত প্রাইভেট ডিটেকটিভকে ডেকেছেন পরিবারের মানুষ। কিন্তু সিরাজের গোয়েন্দা-গল্পে হত্যার ঘটনা ঘটেছে প্রায় সর্বত্র। সেই হন্যতা-বৃত্তির সন্ধান করেন কর্নেল। সেজন্যই কি সিরাজ কর্নেল-কে তাঁর দ্বিতীয় সত্তা বলেছেন?
নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের আবারও আমার নিজের কথাটি বলব। অবশ্যই থাকতে পারে মতভেদ। কোনও শিল্পীর দ্বিতীয় সত্তা শিল্পের ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে বলে মনে করি না। সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে থাকতে পারে। একজন হত্যাকারী ভালোবাসে তার স্ত্রী-সন্তানকে। অথচ নিজের স্বার্থে হত্যা করতে তার এতটুকু বাধে না। চার্লি চ্যাপলিন (১৮৮৯-১৯৭৭) পরিচালিত ও অভিনীত ‘মঁসিয় ভের্দু (১৯৪৭) চলচ্চিত্রের কথা মনে করুন। শিল্পীরও দ্বিতীয় সত্তা থাকতে পারে কিন্তু তা শিল্পক্ষেত্রে নয়। সাহিত্যিক বা শিল্পী হতে পারেন প্রচণ্ড স্বার্থপর, মিথ্যাচারী, জুয়াড়ি, প্রতারক, চোরাচালানকারী, নীতিহীন, নারী অথবা পুরুষসঙ্গলোভী এবং হত্যাকারী। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেই শিল্পীর শিল্পক্ষেত্র-বহির্ভূত জীবনেই এই প্রবণতাগুলি সক্রিয় হয়। একজন শিল্পী তাঁর শিল্পক্ষেত্রের নির্দিষ্ট পরিসরে দুই সত্তার অধিকারী কি হতে পারেন? সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল তাঁর দ্বিতীয় সত্তা নয় বলেই মনে করি। সিরাজের কথাসাহিত্যের কথক-স্বর একজনেরই। সেই কথকের বাইরের চেহারার অবলম্বন কখনও কর্নেল, কখনও লেখক স্বয়ং - একই সত্তার দুই ব্যক্তিরূপ।
ঋণ:১) ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৮
২) ‘বিভাব’ পত্রিকা, বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, মে ১৯৮৭, আমন্ত্রিত সম্পাদক - ধরণী ঘোষ (১৯৪৪-১৯৯৭) ও সিদ্ধার্থ ঘোষ (১৯৪৮-২০০২)। (‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকা সম্পর্কিত তথ্য প্রায়ই সবই গৃহীত হয়েছে এই পত্রিকায় রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় লিখিত ‘গোয়েন্দা কাহিনীর বর্তমান’ নিবন্ধ থেকে)।
৩) গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার (বিভিন্ন খণ্ড), সুপ্রতিম সরকার, আনন্দ ২০১৮-২০২০।
৪) আগ্রহী পাঠক ‘এই সময়’ সংবাদ পত্রের রবিবারের ক্রোড়পত্রে ৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকাশিত অঙ্কন ঘোড়ই এর লেখা – “‘গোইন্দা’ থেকে ‘ডিটেকটিভ’, বঙ্গসমাজের পালাবদল” নিবন্ধটি দেখতে পারেন। আমার প্রবন্ধে সরাসরি এই লেখার কোনও তথ্য ব্যবহৃত না হলেও নিবন্ধটি কৌতূহল-উদ্দীপক ও তথ্যবহুল। অঙ্কন ঘোড়ই লিখেছেন—“ঐতিহাসিক ভাবে বাংলার পুলিশ ব্যবস্থায় ‘ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট’ নামে পৃথক একটি বিভাগ গড়ে উঠেছিল ১৮৬০-এর দশকে।” সুপ্রতিম সরকার ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সুনিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন – “কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন পত্তন ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে, ১৮৬৮ সালে। সর্বজনবিদিত তথ্য, কলকাতা পুলিশকে তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে, দেশব্যাপী এতটাই সুনাম ছিল গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের।”
অলংকরণ (Artwork) : রাজীব চক্রবর্তী - মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us