-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

Buy in India and USA
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

Cautionary Tales
BookLife Editor's Pick -

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | রম্যরচনা
Share -
অলস সঙ্গীদের আখড়ায় : ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত
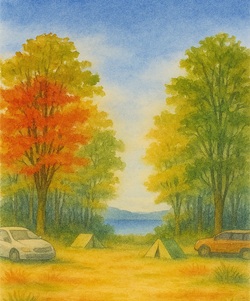
পরবাস আন্তর্জাল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে। তোড়জোড় চলেছিল অন্তত ছ-সাত মাস ধরে। সঠিক দিন ক্ষণ আর কার মনে আছে? নিজে কী নাম ব্যবহার করতাম তখন সেটাই ভালো করে মনে থাকে না। সম্বিৎ বসুর একটা অমূল্য লেখা আছে পরবাসের জন্ম নিয়ে – তথ্যে আর ঘটনায় বোঝাই। সম্বিৎ বলে দিয়েছে ১৯৯৬ সালে আমি বস্টনে থাকতাম, তাই এখন সেটা আর অস্বীকার করে লাভ নেই। সেই সব তথ্য কবুল করে বাকিটা বলি।
সম্পাদক সমীর ভট্টাচার্য, যাঁকে আমরা অনেকে সমীরদা নামে ডাকি, বোধহয় ২০০০ সাল থেকেই প্রত্যেক বছর সবাইকে তাগাদা দিতেন। পরবাস নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ কিছু লেখো। পোস্টম্যান, মিল্কম্যান, বাগানের ঘাস কাটতে আসা অবোধ শিশু… কী উত্তর দেবে ভেবে পেত না। আমার উপর সবচেয়ে বেশি চাপ। একে তো পাড়ার ছেলে, তার উপরে প্রথম চাকরিটা সমীরদার সুপারিশে পাওয়া। কী করে না বলি? অথচ সমীরদা বাদে সবাই জানে যে বাংলায় আমি সত্যি কথা লিখতে বা বলতে পারি না। বাধো বাধো ঠেকে। মনে হয় মাতৃভাষাকে অবহেলা করছি; পাপ হবে। কাজটা আসলে আমার মামাবাড়িতে একদম নিষিদ্ধ ছিল। ‘বাই গড’ বলে শুরু করে নিজের পছন্দমতো একটা ‘তথ্য’ পরিবেশন করতে তারাই শিখিয়েছিল আমায়।
যাহোক, সমীরদাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন তিনি ষাঁড়ের কাছেও ঘটি হাতে দুধ নিতে চলে যান, এবং না নিয়ে ফেরেন না। অতএব এবার আমি তাঁকে ভরসা দিয়ে বলেছিলাম – দেব। তথ্যে ঠাসা নিবন্ধই দেব। তবে তার শিরোনামা যাই হোক না কেন, প্রধান লক্ষ্য হবেন আপনি। গভীর রাত। হোয়াট্স-আপে তড়বড়িয়ে লিখে কথোপকথন চলছিল আমাদের। স্বীকার করছি একটু এল-এস-ডি নেওয়া ছিল – যাতে অক্ষরগুলো কানে শোনা যায় (আর মিউজিক সিস্টেমের গান পরী হয়ে চোখের সামনে নাচে)। নিবন্ধের বিষয় জানার পর সমীরদার গলায় যেরকম বিশুদ্ধ প্যানিক শুনলাম তাতে নিশ্চিত হয়ে যাই যে কষ্ট করতে হলেও কাজটা অপরিহার্য।
এই হল সেই নিবন্ধ।
*** অনেক দিন আগের কথা। সেই ইউজ-নেটের যুগে…। সেরেছে! দয়া করে ইউজ-নেট কী জিজ্ঞেস করে আর লজ্জা দেবেন না। কেউ বোঝে না জিনিসটা কী তো আমার মতো গ্রামাফোনের হ্যাণ্ডেল কী বোঝাবে? সম্বিৎ নিরুপায় হয়ে একটা ভাসা ভাসা পরিচয় দিয়েছে। সম্পূর্ণ বানানো। এসব জিনিস অনেকটা ক্যাসেট টেপের মতো। কেউ জানে না তার ভিতরের ফিতেটা আগে কী কাজে ব্যবহার হত, এখন সবাই তা দিয়ে দাঁত ফ্লস করে (যা নতুন প্রজন্মকে আমরাই শিখিয়েছি, কারণ কেন ডাঁই করে ক্যাসেট জমিয়ে রাখতে হয় বা তার ব্যবহার কী সেটা তো নিজেরাই ভুলে গিয়েছিলাম)। যাহোক, সেই ১৯৯৩-৯৪ সালে যখন নিজের চেয়েও নিষ্কর্মা, অলস, এবং সম্ভাবনাহীন কাউকে খুঁজে পাওয়ার আশায় যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলোতে ইউজ-নেটের নিউজগ্রুপে সারাদিন লন্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন মোটামুটি একই সঙ্গে আমরা অনেকে সমীর ভট্টাচার্যের খপ্পরে পড়ে যাই।
প্রথম থেকেই নতুন আগন্তুকটির ব্যবহার আমাদের স্তম্ভিত, হতবাক করেছিল। বাজে তর্ক করছে না, গায়ে পড়ে ঝগড়া নয়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এর ওর প্রশংসাও করে ফেলে, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা আমাদের কাউকে অপমান করার নাম নেয় না। ইউজ-নেটের এতগুলো নিয়ম এরকম বেপরোয়া ভাবে আমরা আগে কাউকে ভাঙতে দেখিনি। গোপনে সকলেই চরিত্রটাকে এফ-বি-আই-এর চর হিসেবে শনাক্ত করি এবং সাবধান হয়ে যাই। সম্বিৎ-পারমিতা-শ্রাবণী-অর্ণব এরা ‘সমীরদা সমীরদা’ বলে গায়ে পড়ে ভাবও জমায়। আমাদের বন্ধু অপ্রতিম সরকার, যার কথা সম্বিৎ অন্যত্র লিখেছে, সে এসব করত না, কারণ তার ভালো চাকরি ছিল এবং সে অনেক টাকা মাইনে পেত। (পারমিতারও খাতায় কলমে একটা চাকরি ছিল, কিন্তু কম্পানির সেল যে হারে পড়ছিল, সকলেই জানতাম সে চাকরি ভরসা করার মতো নয়।) তো বাকিরা সবাই বেবাক বেকার। তারা কেউ বলছে – সমীরদা আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালো গান করেন। কেউ বলছে – আমি ঠিক জানি আপনার হাতের লেখা মুক্তোর মত। চরিত্রটি বিনয়ের সঙ্গে ‘না, না, না, না’ করছে। মনে রাখবেন ইউজ-নেটে গানও শোনা যেত না, হাতের লেখাও দেখা সম্ভব ছিল না। আমিও কী এদের মতো কিছু একটা বলতে পারতাম না? তবু আমি এসবের অনুকরণ করিনি। ইচ্ছে ছিল না বলে নয়, সাধ্য আর উপায় ছিল না বলে। প্রথমত ইউজ-নেটে আমি আর অপ্রতিম অন্যদের চেয়ে একটু আগে ঢুকেছিলাম। আমি বোধহয় সবার আগে। ঢুকেই খারাপ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যাই এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশের অযোগ্য ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করি। একবার ভাবমূর্তি কাদায় পড়ে গেলে তাকে আর কে ঘরে তোলে? দ্বিতীয়ত, আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সমীর ভট্টাচার্য কোনোদিন এফ-বি-আইয়ের চাকরি বাঁটতে শুরু করলেও লাইনে আমার আগে আট দশজন থাকবে। সুতরাং, কী লাভ?
তো এইভাবে ১৯৯৪-৯৫ এর সময়কালে ইউজ-নেটের বাংলা নিউজগ্রুপটাতে সমীর ভট্টাচার্যের সূক্ষ্ম প্রভাব বাড়তে বাড়তে খাতির এবং খাতির থেকে প্রতিপত্তিতে পরিণত হল। তিনি যদি লিখতেন – ভালো রেস্টুরেন্টে খেয়ে সেই আনন্দ নেই যেটা জয়নগরের রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে পাওয়া যায়, অমনি কয়েকজন বলে উঠত – ঠিক, ঠিক, গত বছর খড়দায় একটা লেড়ো বিস্কুট নর্দমায় ডুবিয়ে দেখি সেটা পান্তুয়া হয়ে গেছে! বা তিনি যদি বলতেন – আজ মেঘ করেছিল আহা, ছাত্র বয়সে বড়ুতে যেরকম দেখেছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ব্যাস্, আর যাবে কোথায়, অমনি সবার মন খারাপ। কেউ বলে – হায়, যাদবপুরে আমাদের একটা পারমিট-ছাড়া পাঁচিল ছিল। সেরকম আর কোথাও পাই না। কেউ বলে – কোথায় সেই লেকটাউনের পিচ ঢালা রাস্তা যেখানে দলে দলে শ্রীভূমি আর বাঙ্গুর থেকে মেয়েরা পান খেয়ে পিক ঢালার জন্য ছুটে আসত।
সমীর ভট্টাচার্য গুনে গুনে সবার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আসতেন। কাউকে বলতেন ‘ওয়েল সেইড!’। কাউকে দিতেন ‘নাইস্লি পুট!’। কেউ ‘ফ্যান্টাস্টিক!!’ পেয়ে গেলে বাকিরা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরত।
এইভাবে চলছে। নব্বইয়ের দশকের সেই বছরগুলোতে প্রতিদিন পৃথিবীটা পালটে যেত। কাল একটা পুরোনো ভিটি ২২০ টার্মিনালে কাজ করে বাড়ি ফিরেছি। আজ গিয়ে দেখি সেখানে একটা ভাঙা ভ্যাক্স মেশিন বসানো আছে। পরের দিন পেলাম সান ওয়ার্কস্টেশান, যেটা চৌদ্দ মিনিট ধরে শুধু নিজের নাম দেখায়। পাঠকরা কিছু বুঝতে না পারলে ভয় পাবেন না, আমরাও পারিনি। বুঝবার আগেই অলস হবার নতুন কায়দা এসে যেত। আমাদের বাংলা নিউজগ্রুপটাতেও যুগ পালটাচ্ছিল। হিন্দু-হিন্দী শ্রেষ্ঠতাবাদ ইত্যাদির ঝাণ্ডা নিয়ে হূণরা হানা দিতে থাকে। বাংলাদেশীদের একটা ছোট আড্ডাঘর ছিল। সেখানে বাংলাদেশীরাই সংখ্যালঘু হয়ে গেল। সম্বিৎ এসব নিয়ে লিখেছে। দেখা গেল বাঙালিরা কেউ পাল্টা আক্রমণ করছে না। গায়ের জোর যে জাতের নেই তার গালির জোর তো থাকা উচিত? তাও নেই। শুধু আমি কত করব? বড়ো একাকী লাগত। হাল ছেড়ে দেব ভাবছি যখন তখন ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। 'দোখনো'দের সেই অভ্যুত্থান চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য আমার জীবনের একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।
দোখনো মানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ। আমি তাদের বিষয়ে যতটুকু জানি সবই আমাদের গ্রুপের অপ্রতিম সরকারের মুখ থেকে শোনা। সে দোখনো বলে বুকে টুকি দিয়ে গর্ব করত এবং বলত তাদের মতো ফন্দিবাজ, ফেরেববাজ, মামলাবাজ, দোগলা, কুচক্রী ও ধড়িবাজ জাত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা নেই। সে আমায় বলেছিল গালি দিয়ে লাভ নেই, হূণদের আইন বানিয়ে তাড়াতে হয়। চেষ্টা সে মন্দ করেনি, কিন্তু ভোটাভুটিতে হেরে যাওয়ায় আইন পাশ হল না। সেই পরাজয়ের গরম ছাইয়ের মধ্যে থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে এসেছিল পরবাস।
*** পারমিতা দাসের কাছ থেকে সে পেয়েছিল বাঙালের গোঁ, সম্বিৎ বসু তাকে দিয়েছিল উত্তর কলকাতার উদ্দীপনা (যার আরেক নাম হুজুগ), আর সমীর ভট্টাচার্য নিয়ে এলেন ম্যানেজমেন্ট স্কিল - যাকে দুর্জনে বলত চক্রান্তের প্রতিভা। দুয়ে-দুয়ে-চার করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না এদের মধ্যে কে দোখনো! পারমিতা-সম্বিতের কাছে হয়তো ব্যাপারটা ছিল সাহিত্য পত্রিকার নামে আড্ডা দেওয়ার একটা নতুন বাহানা। কিন্তু সমীর ভট্টাচার্য জিনিসটাকে পরবর্তী ইয়াহু বা মাইক্রোসফ্টের চেয়ে কম ভাবতেন না। মনে রাখা উচিত গুগল্ এবং ফেসবুক তখন জন্মায়নি। আরো সব বড়ো বড়ো কম্পানির ফাউণ্ডাররাও জন্মেছে কিনা সন্দেহ।
তখন ওহায়ো থেকে যাদবপুরের দুই কর্মবিহীন স্নাতক-স্নাতিকা গুঁতোগুঁতি করে আমাদের দলে ঢোকার তালে ছিল। তাদের নাম অর্ণব গুপ্ত আর শ্রাবণী ব্যানার্জী। আমার মতো তাদের মনেও একটু খটকা জাগে। পত্রিকার নামে বেকারদের বিনে পয়সায় গাধার খাটুনি খাটানো হবে না তো? ইতিমধ্যে সম্বিৎ একদিন প্রস্তাব দেয় দুর্গম কোনো অরণ্যে গিয়ে গাছের তলায় বসে ঋষিদের মতো পরবাসের ভবিষ্যৎ দেখার। কথাটা অর্ণব-শ্রাবণীকে জানাতে তারা অভয় দিয়ে বলল - চিন্তা নেই, আমরাও সঙ্গে যাব এবং তোমায় বাঁচাব।
এই দুজনের উপর তখন আমার খানিকটা ভরসা হয়েছে। জাগতিক সমস্ত বিষয়ে এদের পরামর্শ নেবার পর তার উলটোটা করে নিয়মিত লাভবান হচ্ছি। কর্তব্য ঠিক করে ফেলে চুপচাপ বসে আছি, এমন সময়ে বিনা মেঘে বজ্রপাত। ওহায়োর দুই পান্টার একসঙ্গে বস্টনে এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, আমরাও অরণ্যে গিয়ে ঋষি হতে চাই। এক নতুন চাকরি পাওয়া মহিলা তখন আমায় বেকার-ভাতা দিতেন এবং তাঁর কথার অবাধ্য হবার জো ছিল না আমার। তিনি কাছে এসে মুখ চূণ করে বললেন – সেরেছে, কাল মাঝরাতে ওরা ফোন করে জানিয়েছিল। ঘুমের ঘোরে বোধহয় কথা দিয়ে ফেলেছি সঙ্গে নিয়ে যাব। এখন বুঝতে পারছি না গাড়ি কে চালাবে। তাঁর নতুন গাড়িটা কয়েকদিন আগে কেনার পর থেকে আসবাবের মতো সাজিয়ে রাখা। না তিনি চালাতে জানেন, না আমি। শেষ পর্যন্ত কোনো এক যাদুবলে সেই বাহনে চেপেই ক্যাটস্কিলের গভীর জঙ্গলে চারটে আত্মা পৌঁছে যাই। মাঝখানে কী ঘটে আমায় জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ গোটা রাস্তা আমার চোখ বন্ধ ছিল।
*** ক্যাটস্কিলের সেই অভয়ারণ্যে লোহালক্কড়ের একটা ভগ্নস্তূপের ভিতর সম্বিৎকে পাই আমরা। খুব সাবধানে ভাঙা মেটালের শীট সরিয়ে তাকে হাত ধরে টেনে বার করতে হয়। পরে শুনলাম সেটা তার গাড়ি, এখন তার মধ্যে আমাকেও ঢুকতে হবে। সেই ধ্বংসস্তূপটাকে দিব্যি চালিয়ে সে আমাকে টাউনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে যজ্ঞের সমিধ আর ভোজ্যদ্রব্য কেনার পর ফিরে এসে দেখি নাতিবৃহৎ বহরের চশমা পরা শিবাজীর মতো দেখতে একজন কাঠের বেড়ার উপর দরবার জমিয়ে বসে আছেন। শ্রাবণী আর অর্ণব দুদিকে দাঁড়িয়ে চামর ব্যঞ্জনে সেবা করছে। যাও না, যাও না! সম্বিৎ আর তার দেহরক্ষী পুষ্পল পিছন থেকে আমাকে একটা ভেড়ার মতো এগিয়ে দেয়। ততক্ষণে গল্পের প্লট পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই ভদ্রলোকের আসার খবর আর সবাই জানত, শুধু আমাকে বলেনি কেউ। এঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যই ওহায়োর পাখিরা অতদূর থেকে উড়ে এসেছে। গুটি গুটি এগিয়ে সমীরদাকে ক্যাম্পে পদধূলি দিতে অনুরোধ করি। সমীর ভট্টাচার্য কাঠের সিংহাসন থেকে ভূমিতে পদার্পণ করলেন। করতালিতে জঙ্গল ফেটে পড়েছে। পাখিরা গাছের ডাল ছেড়ে আকাশে উড়তে শুরু করেছিল। সমিধের ধোঁয়া সেই আকাশও অতিক্রম করে অন্তরীক্ষের দিকে যাত্রা করে।
পরের দিন এক প্রাগৈতিহাসিক হ্রদের ধারে বালির স্টেডিয়াম খুঁজে নিই আমরা। সূর্যাস্তের ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে সেখানে ফুটবল ম্যাচ আয়োজিত হয়েছিল। সমীরদা যোগ দেন, কিন্তু আমরা কেউ তাঁকে বলের পিছনে ছুটতে দেখলাম না। জটলা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তিনি দর্শকদের মতো দুপক্ষকেই ‘বাহবা বাহবা’, ‘কেয়া খুব, কেয়া বাত’ বলে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। নতুন ফুটবলটা কে নিয়ে এসেছিল মনে নেই, কিন্তু এরকম টেঁঠিয়া, ও বদতমীজ প্রাণী আমরা দ্বিতীয়টা দেখিনি। ছুঁতে গেলেই খরগোশের মত লাফিয়ে সরে যায়। ঘন্টাখানেক এইভাবে নাজেহাল হওয়ার পর যখন সবাই ভাবছি বাহবাগুলো কি আমাদের পাওনা না অন্য কারো, তখন আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে দেখি দূর থেকে সমীর ভট্টাচার্য হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকছেন।
এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম এমন সময়ে আচমকা বলটা আমাদের সবাইকে কাটিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলতে শুরু করে এবং সমীরদার পায়ের কাছে থামার পর পোষা কুকুরছানার মতো লেজ নাড়াতে থাকে। সমীরদা তাকে সস্নেহে ‘কেয়া খুব’ বলে আদর করার পর নিজের পছন্দমতো একটি দিকে ঠেলে দেন। আমাদের চোখের সামনে সেদিন প্রথম ও শেষবারের মতো বলটা নির্দিষ্ট গোলে ঢুকে গিয়েছিল।
এরপর যখন সমীরদা পরবাস ইন্ক নামের প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত আমাদের জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন আমরা তার (বিনা পারিশ্রমিকের) কর্মী হতে চাই কিনা, সবাই বুঝেছিলাম প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা।
*** তারপর দিনগুলো আরো দ্রুত ভোল পালটাতে থাকে। পুরোনো শতাব্দীটা ফুরিয়ে আসছিল, সকলে জানত শেষ দিন রাত বারোটার আগে জীবনে যা করার সব করে নেওয়া চাই। পঁচিশের নিচে একটা এমন খোকা কি খুকি ছিল না যে তিন-চারটে কম্পানি ফেঁদে ফেলেনি। সেই সব কম্পানি কীসের ব্যবসা করে ভাবার তখন সময় ছিল না। তিরিশের উপরে সবাই সব কিছুর শেয়ার কিনে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। সমীরদা বাদে আমরা এগ্জ্যাক্ট্ পঁচিশ থেকে তিরিশ। গিভ অর টেক। না ইধর কা, না উধর কা। পরবাস ইন্কেরও কারবার কী তা কাউকে জানানো হয়নি। তবে সমীর ভট্টাচার্য বুদ্ধি করে কম্পানির শেয়ারগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন, যাতে কেউ তাদের হদিশ না পায়।
পরবাসের কোনো কারবার না থাকলেও আমরা রাতদিন কীসের যেন কারখানা চালাতাম। পারমিতা একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিলেন যা ব্যবহার করলে মেশিনগুলো চালু হয়ে যেত। শ্রাবণী হয়ে যায় প্রধান শ্রমিক। অর্ণব আরদালি। সমীরদা স্বয়ং ফ্লোরে পায়চারি করতেন। টেম্পোরারি লোক দরকার হলে সম্বিৎ যাকে পেত ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসত। আমাকে যে মহিলা রেখেছিলেন আমি তাঁর কথা শুনে সব কিছু থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম কিন্তু শ্রাবণী বা অর্ণব যখন তখন আমাকে চ্যাংদোলা করে মেশিনগুলোর মধ্যে ফেলে দিত যাতে চাক্কা জ্যাম হয়ে যায় আর তারা কিছুক্ষণের জন্য জিরিয়ে নিতে পারে।
এইভাবে চাক্কা জ্যাম হতে হতেই একদিন কারখানাটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে একটা যন্ত্রদানবের মতো চলতে থাকে আর তার ভিতরে, বাইরে, ও আশে-পাশে যারা ছিল সবাইকে কুড়িয়ে লোহার দাঁত দিয়ে পেষার পর ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।
ইতিমধ্যে এফ-বি-আইতে চাকরি পাওয়ার জন্য যারা এককালে সমীরদার প্রত্যেকটা কথার পর লাফিয়ে উঠে ঝুমঝুমি বাজাত আর পমপম নাড়াত, তাদের সকলকে ছেড়ে তিনি আমাকেই নিজের টপ সিক্রেট অফিসে ঢুকিয়ে নিলেন। এফ-বি-আই নয়, সেটা ছিল আরো রহস্যময় একটা ব্যবসা। অন্যরা যা করছে সেটা ভালো করে শিখে নিয়ে একান্তে জানাও, সমীরদা বলেছিলেন আমায়। বছর পাঁচেক নিরলস গোয়েন্দাগিরির পর বুঝে যাই যে আরো বহুযুগ আগে থেকে অফিসের বাকি সবার একমাত্র কাজ সমীর ভট্টাচার্য কী করেন সেটা জানার চেষ্টা করা। ততদিনে স্পাই হিসেবে আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। সমীরদার কাছে ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করার অল্প দিনের মধ্যে ইস্তিফাও মঞ্জুর হয়ে যায়।অতঃ কিম? আমার আর পিছুটান ছিল না। না কোনো বন্ধন, না কোনো মালিক। ভেসে গেলাম। সমীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত উটকো স্কুল-লবির একপ্রান্তে। ভর সন্ধ্যে। ধারে কাছে কেউ নেই। চিন্তা হয়ে যেত। - একা একা কী করছেন? আপনার ভূতের ভয় হয় না? উত্তর আসত – এটা আমার বইয়ের স্টল। ছেড়ে যাব কোথায়? রবাহুত পার্টিতে গিয়ে দেখতাম এক কোণে বসে কিছু ভাবছেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুলকি চালে চলে যেতাম কাছে। জিজ্ঞেস করতাম - কখন এলেন? সমীরদা চশমা মুছতে মুছতে জানাতেন – তুমি আসার আগেই। এই বাড়িটা যেদিন কিনি সেদিন থেকে আছি এখানে। - ওঃ, তাই বলুন। কিছু চাই কি আপনার? চা, কফি, পোচ্ড পেয়ার্স ইন রেড ওয়াইন? উত্তরের বদলে সমীর ভট্টাচার্য আঙুল ঘুরিয়ে যেন ভুতুড়ে ফোন ডায়াল করে দিতেন। অমনি ফ্রিজ থেকে একটা হৃষ্টপুষ্ট নাশপাতি লাফ দিয়ে বেরিয়ে একটা ওয়াইনের বোতলকেও কান ধরে বিছানা থেকে তুলত এবং টানতে টানতে নিয়ে যেত রান্নাঘরের দিকে। আমি বলতে বাধ্য হতাম – কেন আপনি সবার পিছনে হাত ধুয়ে পড়ে যান? একটা ওয়াইনের বোতলকে এইভাবে কষ্ট দিয়ে কী আনন্দ পাবেন? পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অন্য কারণও তো আছে? পরবাসের সম্পাদক হাতটা এলোমেলো ভাবে নাড়াতেন আর চোখের সামনে ক্যালেন্ডারের এক একটা মাস শুকনো পাতার মতো ঝরতে শুরু করত। আকাশে মেঘের যবনিকা নেমে এসে আবার উঠে যেত। চিনেমাটির কাপের ভিতর সুরক্ষিত স্টিলের চামচগুলো জলতরঙ্গের মতো আওয়াজ শুরু করলে বুঝতাম বাড়িটা ঝিরঝির করে নড়ছে। ভয়ে আমরা তল্লাট ছেড়ে পালাতাম।
*** এর পর থেকে যতটা সম্ভব দূরেই থাকতাম। সমীর ভট্টাচার্য গাড়িতে উঠলে আমি ট্রেনে। তিনি আমাদের পাড়ার বাজারে ঘোরাঘুরি শুরু করার পর বাড়িই পালটে ফেলি। পুরোনো ভেক নাম আর পরিচয়পত্রগুলো পুড়িয়ে নতুন ভেক নাম আর পরিচয় নিতে থাকি। তাও ছায়ার আকৃতিরা পিছু ছাড়ত না। অল্পবয়সে পাতিয়ে ফেলা সম্পর্কগুলো ধাওয়া করে যেত। অন্ধকার গলিতে এরকম কোনো মায়াবী মানুষ পিছু নিলে আমি একটা বাঁক নেবার পর দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে যেতাম পদশব্দগুলো কাছে আসার অপেক্ষায়। আকৃতিটা মোড় ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে জুতোর সোল দিয়ে হাঁটুর মালাইচাকি ঠেলে দেবার মুহূর্তে খেয়াল হত সেও আমারই মতো কারখানার যন্ত্রে ফেলে দেওয়া একটা আবর্জনার ডাব্বা। - কে তোকে আমার পিছনে পাঠিয়েছে, বেওকুফ? কলার ধরে প্রশ্ন করে প্রতিবার এই উত্তরটা পাওয়া যেত – কেউ পাঠায়নি। শুধু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে এসেছিলাম। - কী প্রশ্ন? - সমীর ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্য কী? কীসের ব্যবসা? লোকে বলে তাল-বেতাল আছে কব্জায়, সেটা কি সত্যি?
মাথায় চাপড় মেরে বলি – কোনো উদ্দেশ্য নেই, পোপটলাল। আর থাকলেও সেটা নান অফ আওয়ার কনসার্ন্! শুনে মায়াবীটা আর্তনাদ করে উঠত। - স্ট্র না লাগিয়েই আমার আকাশ থেকে নীল ড্রাগনের ধোঁয়া শুষে নিচ্ছে কেউ আর সেটা নান অফ মাই কনসার্ন্? নিরুপায় হয়ে বোঝাতাম – তিনি কাজ গছালে করতে নেই। কিছু চাইলে দিতে নেই। দলিল অনুবাদ করতে বললে, ‘এই তো দিচ্ছি’ ভাব দেখিয়ে হারিয়ে ফেলতে হয়। ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনো গলিতে ঢোকাতে চাইলে ঢুকতে নেই। এটুকু তো আমিও পারি, তুই পারবি না কেন, ফালুদার শুঁড়? কান্নাটা এর পর আর থামানো যেত না। ছায়া মানব হেঁচকি তুলে তুলে বলত - কারণ আমার সমস্ত পথ বন্ধ।
এই লুজারদের জগত আমাদের নয় জেনে আবার বাড়িঘর তুলে পরিবার পরিজন সহ পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, কখনো গুহায়, কখনো সাগরের নিচে, কখনো আগ্নেয়গিরির ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তবু প্রতি বছর কোনো একটা দিন আকাশগঙ্গার নক্ষত্র থেকে ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো ঝরে পড়ত আমাদের উপর। গাছের ডালগুলোও চিনেমাটির কাপের ভিতর রাখা স্টিলের চামচের মতো ঠুনঠুন আওয়াজ তুলে কাঁপত। ঝিরঝির করে শিউরে উঠত জমি। অদৃশ্য আগন্তুকের আশঙ্কায় আবার দেশ ছাড়তাম। এইভাবে নিজেদের পায়ের ছাপ মুছতে মুছতে আমাদের একটা নয়, অনেকগুলো যুগ কেটে গিয়েছিল। যতবারই ঠিকানা পালটাই, যেখানেই লুকোই না কেন, ফি বছর কাগজের মোড়কে কিছু শারদীয় বই দরজার পাশে বা থামের আড়ালে আবিষ্কার করতাম। কখনো সদ্য জন্মানো আকাশের তারা টেবিলের নিচে রাংতার তোষকের উপর আড়মোড়া ভাঙন্ত অবস্থায় কুড়িয়ে পেতাম। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোনো পায়ের ছাপ, কি একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো পাওয়া যেত না। কে রেখে গেল? নাকি কেউ রাখেনি, দূর থেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল হাওয়ায়?
আসলে পালিয়ে কোনো লাভ ছিল না। কারণ আমাদেরও আকাশ থেকে নীল ড্রাগনের দীর্ঘশ্বাস বহুদিন আগেই শুষে নিয়েছিল কেউ। গাছের পাতাগুলোতে লাগিয়ে দিয়েছিল গিরিধূলো আর শ্বেততর ফ্যাকাসের স্তর। মাটি করে দিয়েছিল কমলা। ঘাসের উপর জ্যাকসন পোলকের মতো পাগলাটে চন্দনের ফোঁটা। ইতিহাসের খাতার পরতে গুঁজে দিয়েছিল নকল নোট। যেখানে যেতাম, দেখতাম একটা প্যাঁচা ডান পায়ে বা একটা কাক বাঁ পায়ে ভর দিয়ে দিনদুপুরে ঘুমোবার ছলে আমাদের কথা শুনছে।
এগুলো কীসের সঙ্কেত তা মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু ছায়া মানবদের পর একসময়ে আমরাও বুঝেছিলাম যে কোনো উদ্দেশ্য নেই এমন একটা মানুষ আমাদের মতো একদল পারমিট ছাড়া পাঁচিলের গোটা পৃথিবীকেই অনেকদিন আগে নিজের ইচ্ছে অনুসারে পালটে দিয়েছিল। এখন শুধু একটু একটু করে সেটা চিনে নেবার অপেক্ষা।
বাই গড।
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us