-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

Buy in India and USA
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

Cautionary Tales
BookLife Editor's Pick -

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ১০০ | অক্টোবর ২০২৫ | গ্রন্থ-সমালোচনা
Share -
গ্রন্থ-সমালোচনা : ভবভূতি ভট্টাচার্য
|| বুকস আর ওয়েল রিটন্... || 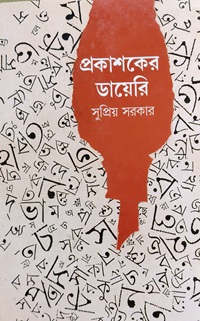 প্রকাশকের ডায়েরি—সুপ্রিয় সরকার; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯; প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০০; ISBN 978-81-721525-3-6
প্রকাশকের ডায়েরি—সুপ্রিয় সরকার; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯; প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০০; ISBN 978-81-721525-3-6পুরনো হলেও কিছু বইয়ের পুনঃপাঠ যথেষ্ট মনোমুগ্ধকর, বিশেষত তা যদি বই ও বইপাড়া ও প্রকাশনাজগৎ নিয়ে হয়।
তা, নয় নয় করে পরবাস পত্রিকার এই কলামে এই গোত্রের আত্মজীবনীর গ্র.স.-ও গোটা পাঁচ-সাত লেখা হয়ে গেল—সে লিস্টিতে যেমন সাগরময় ঘোষ আছেন তেমনি ভানুবাবু (মিত্র-ঘোষ), দেবসাহিত্য, প্রতাপ রায়-ও রয়েছেন। বলতে গেলে, বাংলা প্রকাশনা জগতের বড়দা হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘আনন্দ’ আজ দশক দুই-আড়াই হবে। অতঃপর, মেজ-সেজ দাদার মধ্যে মেসার্স এম. সি. সরকার আসবেই, বিশেষত দুই পরিবারের মধ্যে একটা জ্ঞাতি-সম্পর্কও রয়েছে যখন—আনন্দবাজারের প্রফুল্লকুমার সরকারের সহধর্মিণী নির্ঝরিণী দেবী সম্পর্কে হতেন বর্তমান গ্রন্থটির লেখক সুপ্রিয়বাবুর জ্যেঠতুতো দিদি। বয়সের হিসেবে এই পুস্তক-প্রকাশনালয় মেসার্স এম. সি. সরকার যদিও অনেক জ্যেষ্ঠ (প্রতিষ্ঠা ১৯১০), আনন্দ পাবলিশার্সের প্রতিষ্ঠা ১৯৫৭-এ’।
***
বাংলাসাহিত্যর কথা নয়, একটু অন্য প্রসঙ্গে আমাদের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। বার্ষিক এক তথ্যগ্রন্থ হিসেবে কেরলের মালয়ালা মনোরমা ইয়ারবুকের আজ রমরমা সারা ভারত জুড়ে। আমরা ভুলে যাই, ভারতে প্রথম এমন বই বার্ষিক Hindustan Yearbook & Who’s Who প্রকাশ করেছিলেন (১৯৩২) সুধীরচন্দ্র সরকার মশাই, যিনি ছিলেন মেসার্স এম. সি. সরকারের কর্ণধার। বর্তমান বইটির লেখক সুপ্রিয় সরকারের (জ. ১৯২৪) পিতৃদেব। সেকালে সারা ভারত জুড়ে এই হিন্দুস্তান ইয়ারবুকের যে কী প্রচণ্ড চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল—ভাবা যায় না। আই এ এসের মতো সব কম্পিটিটিভ পরীক্ষার্থীরা উন্মুখ হয়ে থাকত এই বইটির বার্ষিক সংখ্যা কবে বেরোবে! ভারতের প্রকাশনা জগতে এটি ছিল এক ভাগীরথী উদ্যোগ!
তবে, এম সি সরকার প্রকাশনালয়কে যদি আজকেও একটিমাত্র কারণে মাথায় তুলে রাখতে হয়, সেটা তার ‘মৌচাক’ শিশুপত্রিকার জন্যে।
১৯২০-নাগাদ যখন সুকুমার রায়ের অসুস্থতার কারণে ‘সন্দেশ’ পত্রিকা নিভুনিভু, সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হৈ হৈ করে এসে পড়ল এম সি সরকার হাউজের ‘মৌচাক’ পত্রিকা, যার প্রথম বর্ষ থেকেই ‘বুড়ো আংলা’ লিখতে শুরু করেন স্বয়ং অবন ঠাকুর ! আর ১৯৭০এ পত্রিকাটির রজতজয়ন্তীপূর্তি সমারোহে প্রবোধচন্দ্র সান্যাল মশাই লিখলেন, ‘…আজ পঞ্চাশ বছর ধরে মৌচাক সকল সাহিত্যিকের অন্তরের শিশুটিকে জাগিয়ে রেখেছে। এমন কোনো সাহিত্যিক দেখি না যে লেখনী-মুখে তার হৃদয়ের মধু বিন্দু বিন্দু করে মৌচাকে সঞ্চয় করেনি।’
শিশুসাহিত্য যে একটা জাতির মেরুদণ্ড গড়ে দিতে কত বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে—সেটা যিনি বা যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেন ও নিবেদিত হন তাতে, তাঁদের প্রতি জাতির একটা চিরকালীন কৃতজ্ঞতা থাকবেই। সাধে কি আর কিপলিং সাহেবের কিশোর-উপন্যাস ‘কিম্’ পড়ে নালেঝোলে হতেন স্বয়ং নীরদ সি? ১১৫-তম বছরে পা দেওয়া বাংলা-প্রকাশনালয় মেসার্স এম সি সরকার তাই এই নিরিখেই বাঙালির নমস্য।
***
বর্তমান আত্মজীবনীগ্রন্থটির লেখক রাশভারী সুপ্রিয় সরকার মশাই বহুকাল ধরে ছিলেন ‘পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড’-এর সভাপতি, ‘কলকাতা পুস্তকমেলার’ একজন মাথা। আজ জার্মানি তো কাল আমেরিকা করে বেড়িয়েছেন পুস্তক প্রকাশনার কাজে। কিন্তু তাঁর কলমখানি যে এত মিঠে, এ’বই না পড়লে তা জানা যেত? একাধারে এই গ্রন্থে যেমন কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বিধৃত রয়েছে, তেমনি সাহিত্যিকাড্ডা থেকে ছুট্কাহানীর (anecdote) ছড়াছড়ি! নৈলে, বন্ধুবর প্রেমেন্দ্র মিত্রের আসল নাম যে ‘প্রেমেন্দ্রহরি মিত্র’ সেটা লিখে ফেলায় প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ববিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল—সে মজার কাহিনী আর কোত্থেকে জানতে পেতাম? বা, ‘শ্লীল-অশ্লীল’ বিতর্কে বুদ্ধদেবের ‘বন্দীর বন্দনা’ কবিতার অংশবিশেষ কাঁচি দিয়ে কেটে দিলীপকুমার রায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দের কাছে, পণ্ডিচেরি আশ্রমে—সে গল্প!
***
পুস্তক-প্রকাশক হিসেবে তাঁর দীর্ঘ চলার পথে কত না মানুষজনের সংস্পর্শে এসেছেন সুপ্রিয়বাবু! রাজশেখর-অন্নদাশংকর-স্যর যদুনাথের কত কত ব্যক্তিগত গল্প উঠে এসেছে। তবে, এ’বইয়ে বিশেষ পাওয়া বহু বিস্মৃত বা বিস্মৃতপ্রায় লেখকের উল্লেখ যাঁদের প্রতি লেখকের অসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু আজকের প্রজন্ম তাঁদের নামও শুনেছে কিনা সন্দেহ। যেমন, বিশু মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল রায়।
প্রকাশনা-ব্যবসার নানান সমস্যার কথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন সুপ্রিয়,—পাইরেসি, বিপণন, বিজ্ঞাপন-ও-প্রচার। তথ্যভারাক্রান্ত হয়নি, তবু ছোট পরিসরে পড়তে/জানতে ভালো লাগে। লেখার মধ্যে এই পরিমিতিবোধটি সদাই অন্তঃসলিলা বয়ে গেছে তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রকাশনার মতো সুকুমার পেশায় কী করে তিনি এত সফল ছিলেন!
পাঠশেষে একটা সুর ধরে নিয়ে ঘরে চলে যাইঃ
সাহিত্য অশ্লীলতার প্রশ্নে বুদ্ধদেব বসুর ‘রাত ভ’রে বৃষ্টি’ প্রসঙ্গে লেখক স্মরণ করেছেন অস্কার ওয়াইল্ডকে, নৈতিকতার ভিক্টোরিয়ান কালাপাহাড়কে তুড়ি মেরে যিনি বলেছিলেন, “Books are well written, or badly written. That is all.”
বই বই-ই। তার ভালোমন্দ তাতেই নিবদ্ধ!
বই, একটি সুলিখিত ভালো বই!!
|| অমৃতবাজার-কথা ‘অমৃতসমান’ ! || 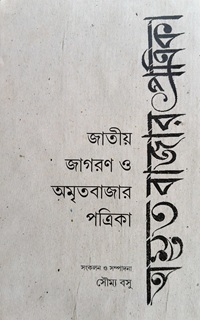 জাতীয় জাগরণ ও অমৃতবাজার পত্রিকা--সংকলন ও সম্পাদনাঃ সৌম্য বসু; নির্ঝর প্রকাশনালয়; কলকাতা-১২২;প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০২৫;
ISBN 978-81-984821-8-1
জাতীয় জাগরণ ও অমৃতবাজার পত্রিকা--সংকলন ও সম্পাদনাঃ সৌম্য বসু; নির্ঝর প্রকাশনালয়; কলকাতা-১২২;প্রথম প্রকাশ অগাস্ট ২০২৫;
ISBN 978-81-984821-8-1
গ্রামের নাম মাণ্ডুরা, তা থেকে মাগুরা। জেলাশহর যশোহর থেকে সাতাশ মাইল যেতে হবে উত্তর-পূর্ব দিকে, ফরিদপুরের রাস্তায়। সেকালে মাগুরা যশোরের মধ্যেই ছিল, এখন নিজেই এক জেলা।
সেকাল, মানে কোন্ কাল?
সন ১৮৬৮ খ্রি., বালক রবীন্দ্রনাথ তখনও ইস্কুলে যেতে শুরু করেনি। এদিকে যশোহর আদালতের নামী ব্যবহারজীবী হরিনারায়ণ ঘোষ তদ্দিনে চক্ষু মুদেছেন; সংসারে রেখে গেছেন বিধবা অমৃতময়ী, আট পুত্র ও তিন কন্যাকে। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ঘোষেদের আর্থিক সঙ্গতি মন্দ ছিল না; আইন-ব্যবসায়ের পাশাপাশি হরিনারায়ণের অন্যান্য ব্যবসাদিও ছিল। যশোহর শহরে একটি বাজার বসান তিনি, স্ত্রী অমৃতময়ীর নামে নাম দিলেন ‘অমৃতবাজার’। অনন্তর, ‘দেশের জন্যে কিছু একটা করিবার তাগিদে’ মধ্যমপুত্র শিশিরকুমার যখন নগদ বত্রিশ টঙ্কা দিয়ে একটি কাষ্ঠনির্মিত লেটারপ্রেস কিনে এনে রীতিমত এক সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করে দিলেন, মায়ের নামে নাম দিলেন তার ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’, মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে যার কণ্ঠরোধ করবার প্রয়াসে স্বয়ং বড়লাট লর্ড লিটনকে ‘ভার্নাকুলার প্রেস এক্ট’ আনতে হবে!
ভাবা যায়?
কী এমন করে ফেলেছিলেন শিশিরকুমার যে… সেটা বলার আগে এটা জানি যে তিন বৎসরের মধ্যে সন ১৮৭১ খ্রি. থেকে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ যশোহর থেকে চলে এসে শহর কলিকাতা থেকেই ছেপে বেরোতে শুরু করে।
পাশাপাশি আরেকটি তথ্যও ধরা থাকঃ
শ্রীমত্যা অমৃতময়ীর ভগিনী আনন্দময়ীর প্রতি উকিল হরিনারায়ণের ছিল ভগিনীসমা স্নেহ, শিশির-মতিলালরাও মাসীমাকে বড্ড ভালোবাসতেন। তাই, সন ১৮৭৬এ ঐ মাগুরা গ্রাম থেকেই যে আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শিশিরকুমার শুরু করলেন, ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’-র সাথে মিলিয়ে মাসীর নামে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ নাম রাখলেন তার! বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই দুটি পত্রিকাই শতবর্ষ পূর্ণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮৬-তে এই সাপ্তাহিক ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ বন্ধ হয়ে গিয়ে ১৯২২ খ্রি. থেকে যে দৈনিক হিসাবে নাগাড়ে আজও প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষ পেরিয়ে গিয়েছে তাতে শুরুর দিকে অমৃতবাজারের প্রতি ঋণস্বীকার ঘোষিত ছাপা থাকত। আনন্দবাজারের প্রথম সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের পত্নী নির্ঝরিণী দেবী সম্পর্কে হতেন শিশিরকুমারের ভাগ্নী সরলাবালা সরকারের কন্যা। (যদিও পরে এই দুই প্রকাশন-সংস্থার ‘আদ্রক-কদলী’ সম্পর্ক কারোর অজ্ঞাত নয়!)
১২৩ বৎসর পথ চলার পরে ক্লান্ত অমৃতবাজার বন্ধ হয়ে গেল ১৯৯১-এর ৬ ফেব্রুয়ারি, যাকে স্বয়ং গান্ধিজী ‘প্রকৃতই অমৃত’ বলে উল্লেখ করতেন। এই গোষ্ঠীরই বাংলা দৈনিক ‘যুগান্তর’-এরও গঙ্গালাভ একই সঙ্গে। যদিও, ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত অমৃতবাজার হাউজের ব্র্যান্ডভ্যালু আনন্দবাজারের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল, সারা উত্তরভারত জুড়ে এঁদের হাউজেরই ইংরিজি ‘নর্দার্ন ইণ্ডিয়া’ দৈনিক বেরোত চারটি বড় শহর থেকে, সঙ্গে হিন্দি দৈনিক ‘অমৃত প্রভাত’!
কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়!
শুরুর দিন থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রশ্নে সদর্থক পদক্ষেপ করেছে অমৃতবাজার, সে নীলচাষ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করা হোক্ বা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জ্বালাময়ী খবর মস্কোয় বসে ভ্লাদিমির লেনিন প্রথম জানতে পারলেন অমৃতবাজার পড়ে! চিঠি লিখেছিলেন এডিটর শিশিরকুমারকে। ছেপে বেরিয়েছিল সে চিঠি। তৎপুত্র তুষারকান্তির দীর্ঘ সম্পাদকীয় আমলে (১৯৩১-১৯৯১) এক বিশেষ মর্যাদা পেল এই কাগজ, ‘The grand old man of Indian journalism’ বলতে যাঁকে আজও বোঝে সারা ভারতবর্ষ।
***
অমৃতবাজার পত্রিকার গুণকীর্তন করা তো এই ‘গ্রন্থ-সমালোচনা’-টি লিখতে বসবার উদ্দেশ্য নয়, বইটি সম্বন্ধে বলিঃ
নবীন যে একটি প্রকাশনা-হাউজ নবীনতর এক সম্পাদকের স্কন্ধে প্রাচীনতম এক পত্রিকার ইতিকথা লেখবার দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে তাতে দু’পক্ষই দশে দশ পায়। যে বাইশটি অধ্যায়ের অবতারণা সৌম্য করেছেন তাদের হেডিংগুলিতে চোখ বোলালেই বইটির দিশার হদিশ মেলে। উপরন্তু, তাতে উনি সাহায্য পেয়ে গেছেন অমৃতবাজারকে নিয়ে পূর্বপ্রকাশিত নানান রচনাবলী থেকে, যেমন,
* নীল-আন্দোলন ও শিশিরকুমারকে নিয়ে লেখা যোগেশ বাগলের রচনা, বা
* শিশিরকুমার ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ নিয়ে দেবনারয়ণ গুপ্তের লেখা, বা
* অমৃতবাজারের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তারাশঙ্করের লেখা রচনা… এমনকি,
* হিন্দুমেলার উপরে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি মূল্যবান কবিতাও স্থান পেয়ে সংকলনটির ধার-মান বাড়িয়েছে। আর, এই সংকলনটির জন্য বিশেষ করে যে কলম ধরা, ‘অ-সাংবাদিক’ শ্রী সোমেন সেনগুপ্তের সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ রচনা, অলংকার! সামান্য পরিসরে শতবর্ষপ্রাচীন এই পত্রিকার জীবনী লিখে ফেলা সহজ ছিল না। এই মানের লেখা কম পড়তে পাওয়া যায়।
***
হিকি-র ‘বেঙ্গল গেজেট’-এর আনটোল্ড স্টোরি সম্প্রতি লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছেন নবীন মার্কিন সাংবাদিক এন্ড্রু ওটিস (পেঙ্গুইন, ২০১৮)। তারও পাঁচ বছর আগে হার্পার ইণ্ডিয়া থেকে বেরিয়েছিল সঙ্গীতা মালহানের ‘The TOI story’. আর, মাত্র দুই সংখ্যা আগেই আমরা সুবর্ণ বসু লিখিত ‘আনন্দবাজারে’র শতবর্ষের ইতিহাসের কথা পড়েছি [ Parabaas : গ্রন্থ-সমালোচনা ]
তরুণ গবেষক সৌম্য বসু-সম্পাদিত বর্তমান সংকলনগ্রন্থটি ইতিহাসের সেই কোটি-তে স্থান করে নেবে সসম্মান!
|| মোদের গরব মোদের আশা ||  পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা—কোরক সংকলন--সম্পাদনাঃ তাপস ভৌমিক; কোরক (পত্রিকা) প্রকাশন, কলকাতা-৫৯; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণঃ জানুয়ারি, ২০১৩;
ISBN / ISSN নেই
পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা—কোরক সংকলন--সম্পাদনাঃ তাপস ভৌমিক; কোরক (পত্রিকা) প্রকাশন, কলকাতা-৫৯; প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণঃ জানুয়ারি, ২০১৩;
ISBN / ISSN নেই
এ’বইয়ের রিভিউ লিখতে হলে গ্রন্থ-সমালোচককে শুধুমাত্র যে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত বিশটি জেলার কথ্যভাষা জানতে হবে তা-ই নয়, টোটো, বোড়ো, কামরূপী ভাষা সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই, কারণ এই এই ভাষার উপরেও প্রবন্ধ রয়েছে এই সংকলনটিতে।
তা বলে কি এ’হেন গ্রন্থের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরা যাবে না, লেখা যাবে না সমালোচনা? নৈলে কী করে তাঁরা অবগত হবেন যে নগর কলিকাতার এক কোণে বসে এক নিভৃতচারী তপস্বী-সম্পাদক দীর্ঘকাল ধরে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের কী অসাধারণ সেবা করে চলেছেন! ‘কোরক’ প্রকাশনী সাধারণত এক একটি থীম ধরে নিয়ে তার উপরে নিবেদিত-সংখ্যাটি নির্মাণ করে থাকে। ওঁদের ‘জেলখানা’, ‘ধর্মপরিচয়’, ‘বিদ্রোহ’, ‘সুনীতিকুমার’ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি ইতোমধ্যেই পড়ে আনন্দ পেয়েছি; ওঁদের ‘হরিচরণ’ সংখ্যাটির কথা ৬৩-সংখ্যা পরবাসে লিখেছিলাম। এ’ছাড়াও ‘কোরক’ বিশেষ-সংখ্যার মধ্যে আছে ‘গীতিকার/সুরকার’, ‘প্রাচীন বিদ্যালয়’, ‘শেষের প্রহর’, ‘ভ্রমণসাহিত্য’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বহুবিস্তৃত গ্রন্থতালিকা ও তার বিস্তারিত সূচিপত্রে চোখ বোলালে সম্পাদকের কাজের পরিব্যাপ্তী ও গভীরতাটা বোঝা যায়। কোন্ বিষয়ে কোন্ এক শহরের কোণে বসে আছেন এক যোগ্য লেখক। তাঁকে খুঁজে এনে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিলেন সম্পাদক মহাশয়। যেমন, এই সংখ্যায় টোটো ভাষার উপরে প্রবন্ধটি লিখেছেন এক বর্ষীয়ান গবেষক শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার, যিনি ডুয়ার্স অঞ্চলেই ক্ষেত্র-গবেষণা ও শিক্ষকতা করে নির্বাহ করেছেন সারাটা জীবন। ‘দৈনিক বসুমতী’-পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী হরেন ঘোষ এক শ্রদ্ধেয় নাম। কিন্তু তিনি যে আদতে দার্জিলিঙের ভূমিপুত্র ও সে-অঞ্চলের এক কলেজশিক্ষক ছিলেন সেটা জানতাম না। দার্জিলিং জেলায় প্রচলিত লেপচা-মেচ-ধীমল ভাষার সঙ্গে বাংলার সংযোগ নিয়ে একটি মূল্যবান রচনা রয়েছে তাঁর এই সংকলনে। (যেমন, মনে পড়ছে, কোরকের ‘জেলখানা’ সংকলনটিতে ‘কারাগারে নজরুল’ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন বাংলাদেশের নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম সাহেব।)
অধ্যাপক পবিত্র সরকার-লিখিত সুদীর্ঘ প্রথম প্রবন্ধটিই এ’গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ (‘কলকাত্তাই বুলি’)। বিভিন্ন সাহিত্যিক তথা লোকজ উদাহরণ টেনে এনে এক প্রাজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন এক ‘কৃত্রিম’ ভাষা হওয়া সত্ত্বেও নগর কলিকাতার এই আঞ্চলিক রূপটি কী করে আধুনিক বাংলাভাষার এক মান্য রূপ পরিগ্রহ করে নিয়েছে। শেষের দীর্ঘ গ্রন্থসূচিটি উপযোগী, বিশেষ করে যাঁরা গবেষণার লক্ষ্যে পড়বেন (এ’কলমচি তো শখের পাঠক মাত্র)।
প্রয়োজনীয় গ্রন্থসূত্র অবশ্য অনেকগুলি প্রবন্ধের শেষেই দেওয়া আছে। মালদহের কথ্যভাষার উপরে বর্ষীয়ান অধ্যাপক শ্রী পুষ্পজিৎ রায়ের লেখাটির শেষে শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির রেফারেন্স দেখে ভালো লাগল। জাত-ওয়াহাবী এই জনগোষ্ঠী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আদিকাল থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। ভাষা ও ধর্মের মেলবন্ধনের এক উদাহরণ হল শেরশাবাদিয়া ভাষা, যাতে অনেক ফার্সি শব্দ অনায়াসে ঢুকে এসেছে।
মোট বাইশটি প্রবন্ধ রয়েছে গ্রন্থটিতে, তাতে যেমন জেলাভিত্তিক হুগলি-হাওড়া-নদীয়া আছে, তেমনই সুন্দরবন বা ‘কামতাপুরী’ অঞ্চলের ভাষাভঙ্গির উল্লেখও এসেছে। বেশ সুখপাঠ, যেমন, কামতাপুরী কি আদৌ একটি উপভাষা—এই প্রশ্ন এসেছে, কারণ এটি একটি কথ্য উপভাষা মাত্র।
ভাষাতত্ত্ব, সাধারণত, নীরস বিষয় বলে পরিচিত। তাকে আম-পাঠকের দরবারে সরস করে উপস্থাপনা করা মুন্সীয়ানার কাজ, যাতে বর্তমান সম্পাদক দশে দশ পান।
|| টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ || 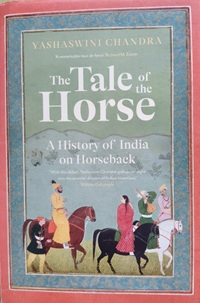 The Tale of the Horse: A History of India on Horseback-- Yashaswini Chandra; Picador India, New Delhi 110001; First published 2021; ISBN 978-93-89109-91-7
The Tale of the Horse: A History of India on Horseback-- Yashaswini Chandra; Picador India, New Delhi 110001; First published 2021; ISBN 978-93-89109-91-7এমন কিছু বই হয় না যা হাতে নিলে আর রাখতে ইচ্ছা করে না, তা সে পড়া শেষ হয়ে গেলেও!
৯২-সংখ্যায় মধ্যভারতের গাছগাছালির উপরে বইটির কথা বলেছিলাম, ৭৫-সংখ্যায় ভূমধ্যসাগরের উপরে বইটি, আর সেই কবে ৪৩-সংখ্যায় বাংলার জলার গাছের উপরে মনোরম পুস্তিকাটির কথা! আজও ভুলিনি।
যেমন, আজকে হাতের এই বইটি! কোনো ‘ঘোটকপুরাণ’ নয়, কিন্তু ভারতে অশ্ব-চারণার ইতিহাস-ভূগোল নিয়ে যে এই মানের এক আনপুটডাউনেবল বই লেখা যায় না পড়লে বিশ্বাস হতো না।
একটু পড়িঃ
ভারতসম্রাট আকবরের পশুপ্রীতির কথা সবাই জানত। তাঁর সংগ্রহে হাতি-ঘোড়া-ময়ূরের কমতি ছিল না। তা, তাঁর এক মামাশ্বশুরমশাই একটি পারস্যদেশীয় ঘোড়া উপহার দিয়েছেন বাদশাহকে, অতি সুদর্শন ও কাবিল অশ্বটি কিন্তু বড়ই বদরাগী ও মুডি। একদিন সম্রাট ওর সওয়ার হয়ে নিজের যুদ্ধশিবির থেকে অনেক দূরে এক প্রান্তরের শেষে গিয়ে ধ্যানে বসেছেন। প্রার্থনা শেষে আর দেখতে পান না অশ্বটিকে। কোথায় চলে গেল সে? কী করে এবার শিবিরে ফিরবেন সম্রাট? এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে! তখন সম্রাট গলায় ধরলেন এক সুর! দূর থেকে তা শুনে ফিরে এসে স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল সে ঘোটক যতক্ষণ না বাদশাহ তার পিঠে চড়ে বসলেন। আদর করে বাদশাহ তার নাম রেখেছিলেন ‘হয়রান’, যে কিনা ভারতসম্রাটের আদেশকেও তোয়াক্কা করত না, হয়রানি করাতো—হাসতে হাসতে বলতেন আকবর তাঁর সভাসদদের। আসলে, সম্রাট লক্ষ করেছিলেন, কানে কোনো সুমধুর সুর না শুনলে ‘হয়রান’ খায়ই না ঘাস-বিচালি, মুডই আসে না তার!
না, শুধু যে এমন নানান ছুটকাহানীর মণিমুক্তো-ই ছড়িয়ে আছে তিনশত পৃষ্ঠার এই বইটি জুড়ে তা-ই নয়, এর সূচিপত্রের বিন্যাস দেখলে বইটির গভীরতার ঠাহর হয়।
তিনটি বিভাগে বিভক্ত বইটিতে নয়খানি অধ্যায়ে প্রথমে উপক্রমণিকা হিসেবে গোটা ভারতবর্ষে, তারপর বিশেষত রাজপুতানায়, অতঃপর সীমান্তপ্রদেশে অশ্বের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে এক এক অধ্যায় জুড়ে। অশ্বের ইতিহাস তো কেবল অশ্বেরই নয়, তাতে পড়ে বিশ্ব-ইতিহাসের ছায়া! বুকাফেলাস না হলে যেমন আলেক্সান্দার হন না, চেতক না হলে রাণাপ্রতাপ, তেমনি কণ্ঠক ঘোড়া না থাকলে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কার পিঠে চড়ে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে পড়তেন বুদ্ধ হবার পথে? একটু লঘুবাচন হয়ে গেল যদিও, তবু মনে রাখতে হবে সমুদ্রমন্থন করে দেবতাগণ পেয়েছিলেন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, গৌরবে যা ঐরাবতের থেকে কম নয়। অশ্বের এতই সমাদর আদিকাল হতে যে বর্তমান লেখিকা গুণে গুণে দেখিয়েছেন, ঋগ্বেদে ২১৫ বার অশ্বের উল্লেখ আছে, গো-মাতার চাইতে ৩৯ বার বেশি! কী করে ভুলি যে স্বয়ং পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে অশ্বরক্ত বয়ে চলেছে—নকুল-সহদেবের জনক অশ্বিনীকুমারদ্বয় ‘অশ্বদেব’-ও বটেন। শাস্ত্রমতে অশ্বমেধ যজ্ঞ-উপরান্ত রাজমহিষীকে মৃত অশ্বের সহিত যৌনাচারের ভান করতে হতো!
না, এই এই প্রকার শুধুমাত্র বেদ-পুরাণ-মহাভারতেই যে এ’বইয়ের অশ্বের গল্প নিবদ্ধ হয়ে আছে তা তো নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের অশ্ব-ব্যবসায়, সেইসব ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর লাভ-লোকসান থেকে যাত্রাপথের বিবরণ—পড়তে পড়তে মনে হয় উপন্যাস পড়ছি যেন একটা। নবীনা লেখিকা জে এন ইউ ও অশোকা-তে পড়িয়েছেন, বর্তমানে আছেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারতের প্রেসিডেন্টস বডিগার্ড-বাহিনীর উপরেও এঁর কাজ আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই বাহিনীই আজকের পৃথিবীতে একমাত্র অশ্বারোহী-বাহিনী যা কার্যকর রয়েছে।
সমরাঙ্গন ছাড়া আর যে দুটি ক্ষেত্রে অশ্বের বহুল ব্যবহার হয়ে এসেছে তা হল ক্রীড়াক্ষেত্র। এ’বইয়ে চমৎকার চমৎকার পেইন্টিং/ফটোগ্রাফ দেখতে পাই—বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর রাজকুমারদের সঙ্গে পোলো খেলছেন (মুঘল মিনিয়েচার), বা ব্রিটিশ আমলে মণিপুররাজ চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে ইংরেজ পোলো-প্লেয়ার।
পোলো খেলা নিয়ে কত কত কাহিনী! শিলচরে খেলা হচ্ছে। খেটো ধুতি মালকোচা মেরে পরে আদুর গায়ের মণিপুরী খেলোয়াড়দের কাছে নাস্তানাবুদ হল সিলেটের বেঙ্গল লাইট ইনফ্যান্ট্রির ব্রিটিশ বাহিনী। ‘এদের কাছ থেকে খেলাটা শিখে নিতে হবে তো!’, ভাবলেন লেফটেন্যান্ট জোসেফ শেরর, যাঁকে ভারতে আধুনিক পোলো-র জনক মানা হয়। এ’ হলো সিপাহী বিদ্রোহের সময় সময়কার কথা। পাঁচ বছরের মধ্যে শেরর তাঁর পোলো টীম নিয়ে কলকাতায় এসে মাতিয়ে দিলেন। জয়জয়কার পড়ে গেল! শোনা যায়, ক্যালকাটার হর্তাকর্তারা আকাশছোঁয়া দামে সেই সব মণিপুরী ঘোড়াগুলি কিনে নিয়েছিল।
সেকালে কলকাতার ‘রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব’-এর রেসিং সীজনের উদ্ঘাটন করতেন স্বয়ং বড়লাটসাহেব!
বইটির পরিশিষ্টে যে দীর্ঘ গ্রন্থতালিকা দেওয়া রয়েছে সেটির স্টাডি করতেই একটা দিন লেগে যাবে। কী খেটে কাজ! এবং প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ক্রস-রেফারেন্স নোটের তালিকাটিও অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ—বহু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা সমেত। স্যালুট!
সাধে কি আর ডালরিম্পল সাহেব সূচনায় ‘যশস্বিনী প্রথম গ্রন্থেই টগবগ করে এসে পড়েছেন’-বলে তারিফ করেছেন?
আর হ্যাঁ, ইনি কিন্তু কেবল কপিবুক লেখিকা নন, নিজেও হর্সরাইড করেন। এঁর প্রিয় ঘোটকীর নাম ‘সু’!
দশে দশ দিই এমন বইকে। বা, বারো!
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us