-
পরবাস
বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
Parabaas, a Bengali webzine since 1997 ... ISSN 1563-8685 -
ছোটদের পরবাস
Satyajit Ray
Rabindranath Tagore
Buddhadeva Bose
Jibanananda Das
Shakti Chattopadhyay
সাক্ষাৎকার -
English
Written in English
Book Reviews
Memoirs
Essays
Translated into English
Stories
Poems
Essays
Memoirs
Novels
Plays
-

পুত্রবধূর চোখে গৌরী আইয়ুব এবং প্রসঙ্গত
-

বিশ্বের ইতিহাসে হুগলি নদী
-

বেদখল ও অন্যান্য গল্প
-

Audiobook
Looking For An Address
Nabaneeta Dev Sen
Available on Amazon, Spotify, Google Play, Apple Books and other platforms.
-

পরবাস গল্প সংকলন-
নির্বাচন ও সম্পাদনা:
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়)
-

Parabaas : পরবাস : বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি -
পরবাস | সংখ্যা ৯৯ | জুলাই ২০২৫ | উপন্যাস
Share -
শিকড় (শেষ পর্ব) : কৌশিক ভট্টাচার্য

।।২৬।। দিলীপ সাহু ডেকে পাঠিয়েছিল একটু আগে। কিছু ইকনমিক সিরিজের ফোরকাস্ট দরকার, মার্চের শেষে কি হবে, কোথায় থাকবেন তেনারা সকলে সেই সময়টাতে, সেসব নাকি আগে থাকতে জানা দরকার অফিসের বড় হুলোদের।
একটু অবাক হয়েছিল কিংশুক। এই ফোরকাস্ট তো করবার কথা স্ট্যাটিসটিক্স ডিপার্টমেন্টের ফোরকাস্টিং ডিভিশনের। ওরা কি এবার এ কাজ করবে না? একটু দ্বিধার সাথে প্রশ্নটা দিলীপ সাহুকে করেই ফেলল কিংশুক শেষ অবধি।
সামান্য বিরক্তির সঙ্গে সাহু বলল, “ওরা করলেই যে ঠিক করবে তার কি মানে?”
এর অর্থ, ওই একই কাজ কিংশুককেও করতে হবে। কেন? একথা সবার জানা যে সামনে প্রোমোশনের ইন্টারভিউ দিলীপ সাহুর। রামা রাও রিটায়ার করার পর এখন দিলীপ সাহুর একটা বড় খুঁটি অফিস থেকে বিদায় নিয়েছে। একথা সবার জানা যে নতুন হেড দেবানন্দন ওকে খুব একটা পছন্দ করে না। ও কি দেবানন্দনকে দেখাতে চাইছে যে ফোরকাস্টিং এর কাজও ও নিজে করতে পারে?
দিলীপ সাহুর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে ওর সাথে কথা বলতে বলতেই দ্রুত খেলাটা বুঝবার চেষ্টা করে কিংশুক। একথা ঠিক যে টপ ম্যানেজমেন্টে যেতে হলে, কেউ যদি দেখাতে পারে যে সে সব ধরনের কাজ করতে পারে -- বলা ভালো, করিয়ে নিতে পারে -- সে অন্যদের তুলনায় একটু এগিয়ে থাকে। কিন্তু ফোরকাস্টিংয়ের এই কাজটি কি ঠিক এতটাই গুরুত্বপূর্ণ? নিয়মিত হয়ে আসছে এই কাজ ফোরকাস্টিং ডিভিশন থেকে। এই কাজ সাধারণত করে জুনিয়র রিসার্চ অফিসারেরা, আর কাজটা ঠিকঠাক হল কিনা দেখার জন্য খুব বেশি উপরের লেভেলে যাবার দরকার পড়ে না।
উঁহু, দিলীপের প্রয়োজনটা মনে হচ্ছে প্রমোশন নিয়ে নয়। নির্ঘাত কোনো লোভনীয় ফরেইন ট্রেনিং আসছে ফোরকাস্টিং নিয়ে। এই ট্রেনিং পাবার কথা ফোরকাস্টিং ডিভিশনের হেড যে তার। দিলীপ সাহু জানে যে কিংশুক এর আগে এই ধরনের কাজ ভালোভাবে নামিয়েছে, তাই কিংশুককে ব্যবহার করে ও এই ট্রেনিংয়ে থাবা বসাতে চায়, যাতে অফিসের পয়সায় বিদেশ ঘুরে আসতে পারে আর যেখানে যাচ্ছে সেখানে লাইনবাজি করে আসতে পারে।
কাজটা হয়তো করে দেওয়া সম্ভব কিন্তু ঝুঁকিটা হল যে ওর করা ফোরকাস্ট ফোরকাস্টিং ডিভিশনের থেকে আলাদা হলে তাই নিয়ে ভবিষ্যতে প্রচুর হল্লা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দিলীপ সাহু কিংশুককেই কামানের মুখে এগিয়ে দেবে।
ঠিক আছে।
তুমি চল ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়।
বসের কেবিন থেকে বেরিয়েই ফোরকাস্টিং ডিভিশনের অশোককে ফোন লাগাল কিংশুক।
-- হ্যালো! অশোক? তোদের বাজারে জিডিপি গ্রোথ আর ইনফ্লেশনের কত রেট যাচ্ছে রে?
খুব চালু ছেলে অশোক। ঝকঝকে স্মার্ট, কিন্তু একই সাথে মনটাও খুব ভালো। অফিসের বাইরে এক দুবার ওর সাথে ফোরকাস্টিং নিয়ে আলোচনা হয়েছে এর আগে। তারপর থেকে কিংশুককে খুব পছন্দ করে অশোক।
কিংশুকের আর অশোকের দুই বস এখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেজন্য ওদের দুজনেরও এখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া উচিত। কিন্তু এতদিনে ঠেকে ঠেকে ওরাও এখন ত্যাঁদড়া অফিসার। বসেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে চায়? করুক! লড়াইয়ের শেষে একজন (অথবা দুজনেই) যদি মরে, কী যায় আসে ওদের?
এক লহমায় অশোক বুঝে গেল সব। অযথা নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ের কোনো মানে হয় না। ওরা দুজন একই ফোরকাস্ট দেবে বসেদের, যাতে গন্ডগোল হলে একা কেউ না ফেঁসে যায়।
মিনিট পনের বাদে নিজের ব্যক্তিগত জি-মেইল অ্যাকাউন্ট চেক করল কিংশুক।
কথা রেখেছে অশোক।
মোট ছটা ইকনমিক সিরিজের শুধু ফোরকাস্ট-ই নয়, ডাটা আর মডেলগুলো-ও পাঠিয়ে দিয়েছে অশোক। এবারে কাজ বলতে মডেল-গুলো সামান্য পাল্টানো আর ডাটা-সিরিজে সাম্প্রতিকতম রিভিশনগুলো যোগ করা।
অশোকের বদান্যতায় মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে ফোরকাস্ট তৈরি হয়ে গেল কিংশুকের।
দিলীপ সাহুকে মেল করার পর অশোককে সেই মেলটাই ওর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিলো কিংশুক। অশোকেরও জানা দরকার কি ফোরকাস্ট দিলীপ সাহু দেবে বড় হুলোদের। ই-মেইলে একটা স্মাইলি ফেস সমেত বড় করে একটা থ্যাংকস জানাতেও ভুলল না।
*** দিলীপ সাহুর কেসটা সামলে মনটা খুশি ছিল বেশ। এবারে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল কিংশুক। সকালের কলের পরেও আরও দুটো মিসড কল রয়েছে অতসীর। নিশ্চয়ই চটে কাঁই হয়ে রয়েছে অতসী। ফোন করলে ঝাড় খাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবু ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায় তত ভালো। যত দেরি হবে তত রাগে, অপমানে ফুঁসতে থাকবে অতসী।
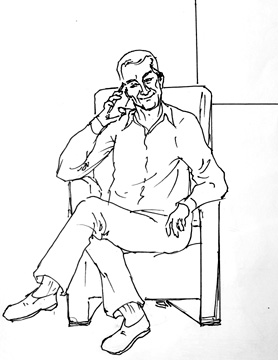
অতসীকে ফোন লাগাল কিংশুক:-- এতক্ষণে ফ্রি হলাম। হ্যাঁ, এবার বলো।
-- ফোন করেছিলাম এতবার তার কারণ বড় খবর আছে একটা। শোনো, আমি বোম্বে আসছি।
-- কবে? কতদিনের জন্য?
-- আরে পাকাপাকি চলে আসছি বোম্বেতে। ট্র্যান্সফার হয়েছে আমার, প্রমোশন সমেত। আমাদের বোম্বের অফিসের হেড করে দেওয়া হয়েছে আমাকে!
খবরটার আকস্মিকতা এত বেশি যে সেটা হজম করতে সময় লাগে কিংশুকের।
তিসির দিক থেকে খবরটা নিঃসন্দেহে খুব ভালো, তিসি তো শত্রু নয়, নিজেরই বৌ। কিন্তু কিংশুকের দিক থেকে সত্যিসত্যিই এটা ভালো খবর কি?
আবার বোম্বে ফিরছে তিসি। যখন ফেরার দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি, তখন পারে নি। একা একা সবকিছু কিংশুককেই সামলাতে হয়েছে তখন।
এখন শমীক হোস্টেলে, একা কিংশুক নিজের মতন করে থাকছিল, গুছিয়ে নিয়েছিল সবকিছু। এবারে সেই স্বাধীনতাটুকু বোধ হয় গেল আবার।
-- শমীককে বলেছো?
-- না। ফোন করে পেলাম না ওকে। তুমি আবার ওকে বলে দিও না যেন, ও আমার নিজের মুখ থেকে বলাটা এক্সপেক্ট করবে।
-- সত্যিকারের বড় সারপ্রাইজ দিলে একটা। ফোন করার সময় একেবারেই ভাবি নি এত ভালো একটা খবর থাকবে তোমার দিক থেকে। কি আর বলবো? বড় একটা কংগ্রাচুলেশন্স তোমায়। খুব খুশি হয়েছ নিশ্চয়ই?
খুব ফর্মাল হয়ে গেল কি কথাগুলো? কংগ্রাচুলেশন্সটা কি শুকনো হয়ে গেল?
যদি হয়েও থাকে সে নিয়ে কোনো কথা তুলল না অতসী। হয়তো এসব কথা তুলে আনন্দের মুহূর্তটাকে নষ্ট হতে দিতে চাইছে না ও।
*** অতসীকে ফোন করা শেষ হতে না হতেই আবার ফোন।
এবার শমীক।
-- হ্যালো!
-- বাবা?
-- কি রে এতক্ষণে সময় হল! বর্ধমান পৌঁছে ফোন করার কথা ছিল না!
-- ছিল তো, তবে দাদুর সাথে কথা বলছিলাম।
-- কেমন দেখলি দাদুকে?
-- এখনো অবধি খুব খারাপ নয়, তবে রোগা হয়ে গেছে ভীষণ আর খাওয়াদাওয়া ছেড়েই দিয়েছে প্রায়। তোমাকে পরে ডিটেলস বলবো। আমি আর একটু পরে এখান থেকে বেরোবো। এখন তৈরি হতে হবে। বাসে যেতে যেতে ফোন করব তোমায়, যদি অবশ্য নেটওয়ার্ক থাকে।
পরেই যদি ডিটেলস বলবেন পুত্ররত্ন তাহলে এখন ফোন কেন?
কিংশুককে এই নিয়ে আরো কিছু ভাববার কোনো অবকাশ না দিয়েই শমীক আবার বলল, “যে জন্য এখন ফোন করলাম সেটা বলি আগে। এই একটু আগে চিলেকোঠার ঘরটাতে তোমার স্কুলে প্রাইজ পাওয়া বইগুলো দেখলাম! আমাকে বল নি তো আগে এত বই প্রাইজ পেয়েছিলে তুমি?”
-- শুধু আমি নয়, ক্লাসের আরও দু এক জন পেতো। প্রচুর প্রাইজ দিত আমাদের বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাইজ ছিল আমাদের, অনেক সময় একটার বেশি। তখনকার দিনে অনেক লোক মরার আগে স্কুলকে বেশ কিছু টাকাপয়সা দিয়ে যেতেন ভালো ছাত্রদের প্রাইজ দেবার জন্য।
-- তবু দু’এক জনই তো পেতো, সবাই তো নয়?
কি যে ছিল শমীকের এই একটা কথায়, হঠাৎ করে মনটা খুব খুশি হয়ে গেল কিংশুকের।
-- যাক, এখন বিশ্বাস হল তো আমিও একটু আধটু লেখাপড়া জানি?
সেই ছোটবেলার মতন খিলখিল করে হাসল শমীক।
-- রাখছি, পরে ফোন করব আবার।
-- ঠিক আছে। সাবধানে কলকাতা যাস আর দয়া করে হোটেলে পৌঁছে একটা ফোন করিস।
মোবাইলটা পকেটে ঢোকানোর আগে ঘড়ি দেখল কিংশুক। পাঁচটা বেজে গেছে। অফিসের নিয়ম না ভেঙেই এখন বেরিয়ে পড়তে পারে কিংশুক। দিলীপ সাহুকে ফোরকাস্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আধ ঘন্টা হয়ে গেল। আশা করা অন্যায় হবে না যে দিলীপ সাহু মেইলটা পড়েছে। পড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যখন ওকে ডেকে পাঠায় নি, মনে হয় আর কোনো প্রশ্ন তুলবে না এ নিয়ে।
বাকি একটা দুটো যা কাজ রয়েছে এখনো, কাল দুপুরের মধ্যে শেষ করে দিলেই চলবে।
যাবার আগে শেষবারের মতন শুধু একবার মেসেজগুলো চেক করা দরকার, নতুন কোনো জরুরি কাজ এল কিনা দেখতে।
না, সেরকম জরুরি কোনো কাজের মেল নেই। তবে হোয়াটসঅ্যাপে অমিতাভর মেসেজ এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। ওকে একা নয়, ওদের পুরো ব্যাচকে লেখা।
চেয়ার প্রফেসর হয়েছে অমিতাভ। একটা পুরো রিসার্চ ইউনিটের ডিরেক্টর হবে এর ফলে। মাইনে ছাড়াও, অন্যান্য সুযোগসুবিধা -- বিশেষ করে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ঘুরে বেড়ানোর সুবিধা -- এক ধাপে বেড়ে যাবে অনেকখানি।
ব্যাচমেটদের থেকে এরই মধ্যে পাঁচখানা কংগ্রাচুলেশন্স এসে গেছে পনের মিনিটের মধ্যে। খুব তাড়াতাড়ি দু লাইনের একটা মেসেজ ঢেলে দেয় কিংশুক গ্ৰুপে। পরে অমিতাভকে আলাদা করে একটা মেসেজ পাঠাবে কিংশুক। সেটা এক দু দিন পরে পাঠালে ক্ষতি নেই।
কম্পিউটার বন্ধ করে, কেবিন লক করে নিচে নেমে এল কিংশুক। রাস্তা পেরিয়ে একটু এগোলে একটা ছোট উদুপি রেস্টুরেন্ট। বোম্বেতে এরকম অজস্র ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এই জায়গাটা অফিস-পাড়া বলে এখানে সেসব আরও বেশি। সারাদিন এইসব রেস্টুরেন্টগুলো লোকে গমগম করে। বেশির ভাগই বাঁধা খদ্দের। রাত আটটার পর পুরো অফিসপাড়া ফাঁকা হতে থাকে, এই সব ছোটখাট রেস্টুরেন্টগুলোতে তখন খদ্দের আর থাকে না বললেই চলে। এখনো সন্ধ্যা হয় নি বলে রেস্টুরেন্টটাতে বেশ ভিড়। কিংশুক এই রেস্টুরেন্টটা পছন্দ করে কারণ এখানে সস্তায় খুব ভালো ফিল্টার কফি পাওয়া যায়। এখন আর চার্চগেট স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খায় না কিংশুক, ছুটির পর এখানে বসে এক কাপ কফি খেয়ে তার পর ট্রেন ধরতে চার্চগেট ছোটে। ওয়েটাররা সকলেই ওকে চেনে। এদের মধ্যে একটা বাঙালি ছেলে রয়েছে, শ্যামল বলে, মেদিনীপুরে বাড়ি। বেশির ভাগ দিন শ্যামলই কফি এনে দেয় কিংশুক কিছু বলার আগেই।
কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে নিজের কথা ভাবছিল কিংশুক।
একসময় স্কুলে হরেক কিসিমের প্রাইজ পেত কিংশুক। কলেজেও এই প্রাইজ পাবার ব্যাপারটা, স্কুলের মতন অতটা না হলেও, থেমে থাকে নি।
কী যে হল তারপর। এত বছর কেটে গেল, নতুন কোনো সম্মান, নতুন কোনো পুরস্কার আর কপালে জুটল না কিংশুকের। বদলে জুটল শুধু অবহেলা আর তিরস্কার।
অমিতাভর থেকে তো পড়াশুনোয় অনেক ভালো ছিল কিংশুক। কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে অমিতাভ নম্বরের লড়াইয়ে কিংশুককে হারাতে পারে নি কখনো। কিন্তু আজ অমিতাভ কোথায় আর ও কোথায়?
কোথায় ভুল করল কিংশুক?
নিজের জন্য আলাদা করে সম্মান আদায় করার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি কিংশুক। ও তো চায় নি যে কেউ চিড়িয়াখানার জন্তুর মতন ওর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাক, “জানিস, ইনি হলেন কিংশুক চ্যাটার্জী। এত বড় হনুমান যে এনার লেজ ছাপ্পান্ন ইঞ্চি মোটা!” খ্যাতি, যশ, সম্মান -- এর সবকিছুকে বরাবরই খুব ঠুনকো মনে হয়েছে ওর। দুনিয়া ওকে হয়তো পাগল বা অস্বাভাবিক ভাববে, তবু খুব ছোটবেলা থেকেই কেন জানি না ওর মনে হয়েছে যে এগুলোর পিছনে দৌড়োনোটাই এক ধরনের পাগলামি।
না, অমিতাভর উপর একটুও হিংসা নেই কিংশুকের। একথা সত্যি যে নিজের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে বেশ স্বার্থপর অমিতাভ, কিন্তু যেখানে ওর নিজের স্বাৰ্থ সরাসরি জড়িত নেই সেখানে ও যথেষ্ট বন্ধুবৎসল আর উপকারী। এখনো দেশে এলে সময় করে সক্কলের সাথে দেখা করে। ওদের ব্যাচমেটদের নিজস্ব মেলামেশাগুলোর উদ্যোক্তাও বেশির ভাগ সময় অমিতাভ। এসবের খরচ-ও অনেক সময় ও একাই দিয়ে দেয়।
মুশকিলটা হল কিংশুক নিজে চাক বা না চাক, পৃথিবী অমিতাভর সাথে ওর তুলনা করতে ছাড়বে না। যেখানেই যাবে ও, অমিতাভ সেখানে থাকলে ওকে দেখিয়ে আড়াল থেকে লোকে বলবে, ওই দ্যাখো, ওই যাচ্ছে কিংশুক চ্যাটার্জী, স্কুলে প্রাইজ পেত নিয়মিত, এক সময়ে কলেজে অমিতাভর থেকে ভালো ছাত্র ছিল ও, এখন অবশ্য আস্ত একটা বাঁধাকপি …
অতসী জানতে পারলেও সেই এক কথা বলবে।
হয়তো অতসীই ঠিক। অতিরিক্ত সুখী হয়ে পড়েছিল কিংশুক। স্কুল কলেজের একসময়ের ভালো ছাত্র চাকরিতে যোগ দেবার পর আর ছাত্র থাকে নি। নিজেকে তৈরি করে নি ভেঙেচুড়ে নতুন করে। চাকরির শেষ ল্যাপে এসে তাই পদে পদে প্রচুর অসম্মান সহ্য করতে হচ্ছে। এত অসম্মান পাওনা ছিল না কিংশুকের।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিংশুক ভাবল যে ইঁদুর দৌড়ের নিয়মই হল যে একবার এতে ঢুকলে দৌড়োতে তোমাকে হবেই। না দৌড়োলে পিছনের লোকেরা ধাক্কা মেরে মাটিতে শুইয়ে দেবে। বাকি যারা অনেক পিছনে ছিল, তোমার উপর দিয়ে যাবার সময় তোমার মুখে একটা দুটো লাথি কষাতেও তারা ভুলবে না। এই দৌড়ের হাত থেকে একমাত্র মুক্তি সব্বাইকে ছাড়িয়ে গেলে, তাও পিছনদিকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে অতর্কিতে কোনো ধাক্কা না আসে।
সারা পৃথিবীটাই শালা পাগলে ভর্তি। তাই হয়তো সুস্থ স্বাভাবিক লোকদেরই পৃথিবী পাগল ভাবে।
বনের জন্তুরা যেমন একটু অন্য ধরনের প্রাণী দেখলেই তেড়ে আসে, এও যেন ঠিক তাই।
এই লোকটা আমাদের মতন নয়? অন্যরকম? তার মানে এ বিপজ্জনক প্রাণী।
সবাই দৌড়োচ্ছে, তুই শালা কোথাকার কে বে যে দৌড়বি না? মার হারামীটাকে সবাই মিলে। দে, চোখমুখ থেঁতো করে দে ওর, হামানদিস্তার বাড়ি মেরে!
শমীকের ফোনটা পাবার পর থেকে যে খুশি খুশি ভাবটা এসেছিল আবার চলে গেল দুম করে। মনটা হঠাৎ করে আবার অশান্ত লাগছে খুব।
এখন অশান্তিটা বাড়তে দিলে নিজেরই ক্ষতি। চট করে এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে মনটা আবার ভালো হয়ে যায়।
যদিও শীতকাল, তবু বোম্বেতে সন্ধ্যা নামতে একটু দেরি আছে। এই সময় আজ একবার মেরিন ড্রাইভ গেলে কেমন হয়? বহুদিন সামনা সামনি সমুদ্র দেখে নি কিংশুক। আজকের গোধূলিলগ্নে একমাত্র আরব সাগরের বিশালতাই পারবে ওর মনের সব অশান্তি ঘুচিয়ে দিতে।
২৭ ফোর্ট অফিসের গায়ের উদুপি রেস্টুরেন্টটার থেকে দু মিনিট হাঁটলেই ফ্লোরা ফাউন্টেন, যার বর্তমান নাম এখন হুতাত্মা চক। সেখান থেকে সিধে ওয়েস্টার্ন লাইনের চার্চগেট স্টেশনের রাস্তা। রাস্তায় হাজার হাজার লোক এখন। বেস্টের বাসগুলোতেও বেশ ভিড়। আশেপাশের সব অফিস এক এক করে ছুটি হচ্ছে এখন। ঘরে ফেরার তাড়ায় অনেকেই প্রায় ছুটতে ছুটতে চলেছে চার্চগেট স্টেশনের দিকে। এখন থেকে আরো প্রায় দু’ঘন্টা চার্চগেট স্টেশনে ট্রেন ঢোকার সময়টাতে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠতে না পারলে বসার সিট পাওয়া মুস্কিল।
কিংশুককে অবশ্য আজকাল এই সব লড়াইয়ের মধ্যে থাকতে হয় না। অফিস থেকে ও বেরোয় একটু দেরি করে, বান্দ্রা লোকালের সময় হিসেব করে। বান্দ্রা লোকাল সংখ্যায় অনেক কম, কিন্তু বান্দ্রা অবধি লোকও কম যায় বলে বান্দ্রা লোকালে কোনো তাড়াহুড়ো না করে ওঠা যায়। বসার জায়গাও পাওয়া যায় রোজ। আজকেও আটটা আটের বান্দ্রা লোকাল ধরলে বসার জায়গা পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।
চার্চগেট স্টেশনের উল্টোদিকে এশিয়াটিক বলে একটা বড় দোকান। দোকানের পাশ দিয়ে মেরিন ড্রাইভে যাবার রাস্তা। এদিকটাতে অত অফিস নেই বলে রাস্তায় ভিড় অনেক কম। একটু হেঁটে গেলে রাস্তার বাঁদিকে একটা পুরোনো ছবির দোকান। বিয়ের পরে নতুন ঘর সাজানোর জন্য ও আর অতসী এই দোকানটা থেকে একটা বড় ছবি কিনেছিল, Henry Raeburn-এর The Boy with a Rabbit। এখনো বান্দ্রা-কুর্লার বাড়ির বসবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে ছবিটা। নিছক কৌতূহলের বশে দোকানের বাইরের ডিসপ্লের দিকে তাকালো কিংশুক। না, মাসখানেক আগে যে ছবিগুলো ছিল এখনো সেগুলোই আছে। কারা কেনে ছবি এদের থেকে? দোকান চলে কিভাবে এদের? অথচ বহু বছর আগে যখন কড়কড়ে আটশ টাকা দিয়ে ছবিটা কিনেছিল ওরা তখন কি ভয় হয়েছিল ওদের দুজনের যে এক্ষুনি এটা কিনে না ফেললে পরে বোধ হয় আর পাবে না!
অতসী আর ও, দুজনেই কী বোকা ছিল তখন!
ছবির দোকানটা ছাড়িয়ে আরও মিনিটখানেক হাঁটার পরে পিজারিয়া। অর্ধবৃত্তাকার এই রেস্তোরাঁটার উল্টোদিকে, রাস্তা পার হয়ে যে জায়গাটা, মেরিন ড্রাইভে সেটাই সবচেয়ে প্রিয় জায়গা কিংশুকের।
বহু বিকেল আর সন্ধ্যে এখানে বসে কাটিয়েছে কিংশুক।
প্রথমে একা।
তারপর অতসীর সাথে।
এখন আবার একা।
সিগন্যাল সবুজ আছে। ধীরে ধীরে কোনো তাড়াহুড়ো না করে রাস্তা পার হল কিংশুক।
পিছনে আরব সাগর। মদের মতন লাল রঙিন জল, তবে শীতকালে আশ্চর্য শান্ত এই সাগর। সামনে চওড়া রাস্তায় সারি সারি গাড়ি চলেছে, ডবল ডেকার বাস আর প্রিমিয়ার পদ্মিনী ট্যাক্সি; এছাড়াও, মারুতি, টাটা আর মাহিন্দ্রর বিভিন্ন মডেল। অল্প কিছু মার্সিডিস বেনজও রয়েছে এদের মধ্যে। সারাদিন ধরে পয়সা উড়িয়ে আর পয়সা কুড়িয়ে মানুষ কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে এখন।
মেরিন ড্রাইভে বসে থাকা লোকও তাই বলে খুব কম নয়। প্রচুর যুবক-যুবতী আর অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে এদের মধ্যে। এরা আসে প্রেম করতে। বোম্বেতে লোকের তুলনায় পার্ক এত কম যে নিশ্চিন্তে খোলা জায়গায় বসে বা ঘুরে ঘুরে কথা বলতে হলে মেরিন ড্রাইভের জুড়ি নেই। অন্য শহর থেকে ঘুরতে আসা টুরিস্টরাও সাধারণত বিকেলের দিকটাতেই মেরিন ড্রাইভের দিকে আসে। এদের বেশির ভাগই সচ্ছল হলেও, কিছু লোককে দেখেই বোঝা যায় যে তারা দরিদ্র শ্রেণীর এবং সদ্য সদ্য গ্রাম থেকে আসা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের, বিশেষ করে তাদের মেয়েদের, চোখেমুখে একটা শহর ঘুরবার আহ্লাদের ছাপ। এদের বাদ দিলে, অল্প কিছু মধ্যবয়স্ক লোক আসে এখানে যাদের দেখলেই ভাগ্যহত বলে মনে হয়।
এখানে এসে অনেকেই অবশ্য চুপচাপ বসে থাকা পছন্দ করে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটির চেষ্টা করা লোকের সংখ্যাও তাই কম নয় এখানে। আশেপাশের যত দেড়শ-দুশ কিলোগ্রাম ওজনের পুরুষ এবং মহিলারা এখানে এসে হাঁটে ওজন কমানোর আশায়। এদের কারুর কারুর সাথে আবার তাদের পোষা কুকুরও থাকে, যদিও এদের মধ্যে বড়কর্তা-স্থানীয়রা সাধারণত বাড়ির চাকরের হাতেই এই মহা-দায়িত্বটি দেওয়া পছন্দ করেন। এত লোক এক সাথে বলে, একটু পরে পরে রাউন্ড দিয়ে যায় চা অথবা ভেলপুরীর ফেরিওয়ালারা।
আজকাল কোথাওই ভিড় জিনিসটা ভালো লাগে না কিংশুকের। আজও এত ভিড় যে কিংশুকের দুপাশে দুফুট করে জায়গাও খালি নেই। তবে কিংশুক জানে যে একটু সন্ধ্যা হলে এদের অনেকেই উঠে যাবে। মেরিন ড্রাইভের আসল জাদুর শুরু তাই সূর্যাস্তের বেশ কিছুটা পর থেকে।
অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে রাস্তা দেখল কিংশুক, তারপর রাস্তার দিকে পিছন ফিরে বসল, সমুদ্রের দিকে মুখ করে। ভিড় অনেকটাই ফাঁকা হয়ে এসেছে এখন।
অন্ধকার নামছে। লাল থেকে কালো হচ্ছে জল। মেরিন ড্রাইভের অর্ধবৃত্তাকার এই অংশ, যাকে কুইন’স নেকলেস বলা হয়, আলোয় ঝলমল করছে এখন। কিছু আলোর প্রতিবিম্ব কাঁপছে জলের উপরে। অল্প সামান্য ঢেউ জলে, এক স্তর থেকে আর এক স্তরে আলোয় কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে ঢেউ।
কিংশুকের জীবনও এমন একটা স্তর থেকে আর এক স্তরের দিকে চলেছে এখন।
অফিস থেকে আর নতুন কিছু পাবার নেই কিংশুকের। বড় হুলোদের যদি দয়া হয়, আর একটা প্রমোশন হয়তো পেতে পারে কিংশুক, তবে তাতে পুরোনো ক্ষতগুলো মিলিয়ে যাবে না।
প্রমোশন পেয়েই বা হবেটা কি? অফিসের দয়ায় পাওয়া বান্দ্রা-কুর্লা কমপ্লেক্সের তিন কামরার ফ্ল্যাটের চেয়ে আরো বড় ফ্ল্যাটের কোনো দরকার নেই কিংশুকের। থাকলে আরো অনেক আগেই মেরিন ড্রাইভের আরো অনেক কাছাকাছি বাড়ি পেয়ে যেত কিংশুক। প্রমোশন পেলেও মাইনে খুব একটা বাড়বে না। নতুন মাইনের টাকাতেও পানভেলের পায়রার খোপের মতন ফ্ল্যাটের চেয়ে বড় আর কোনো নিজস্ব ফ্ল্যাট কেনা হয়ে উঠবে না ওর, দরকারও নেই আর এর চেয়েও বড় ফ্ল্যাটের মালিক হবার।
বড় গাড়ি কিনবে? একার জন্য? কী হবে কিনে? তিসি বোম্বে ঘুরতে এলেও ওরা দুজন মাত্র। কতটা জায়গা দরকার একটা গাড়িতে মাত্র দুজনের জন্য?
জমানো টাকাপয়সা যা রয়েছে আর পেনশন যা পাবে তাতে দিব্যি চলে যাবে কিংশুকের। অন্য অনেক বন্ধুর মতন মদের প্রতি কোনো আলাদা আকর্ষণ বোধ করে নি কিংশুক। পাঁচতারা ছাপ্পা মারা খাবারেরও কোনো দরকার নেই ওর। হজমের ক্ষমতা কমে গেছে অনেক, তবু এখনো সাধারণ দোকানের সামান্য লুচি-তরকারি, কচুরি আলুর দম বা এগ রোল খেয়ে যা তৃপ্তি তা আর কিছুতে নেই। ব্র্যান্ডেড শার্টের দরকার নেই কিংশুকের, একজন সাধারণ পরিশ্রমী দর্জির নিজের হাতে বানানো সুতির শার্টের সাথে এই সব শার্টের কোথায় ঠিক তফাৎ তা আজও বুঝলো না কিংশুক। যা মাইনে পায় এখন তাতে বোম্বাইয়ের একজন গড়পড়তা মধ্যবিত্তের আরও যা যা প্রয়োজন, সবই কিনতে পারে কিংশুক। তাহলে আর প্রমোশন বা পয়সার পিছনে শুধু শুধু ছুটবে কেন ও?
কর্মজীবন নিয়ে তাই আর নতুন কিছু ভাবতে চায় না কিংশুক। অনেক কাজ করেছে জীবনে। পৃথিবীর কোনো বড় পরিবর্তন হয় নি তাতে। এখন সময় এসেছে একটু নিজের আশেপাশে তাকানোর।
অতসী ফিরছে বোম্বেতে। পাকাপাকিভাবে।
এ যেন প্রায় দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম বিয়ের সময় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটুও চিন্তিত ছিল না কিংশুক। কিরকম মুক্ত বিহঙ্গের মতন ছিল তখন ও, মনে শুধু আনন্দ আর উত্তেজনা। নেগেটিভ চিন্তা মাথাতেই আসে নি তখন কোনো। এবারে কিন্তু ভাবতে হচ্ছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সব ভাবাটাও একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার এখন। বেশি মাথা ঘামাতে এখন আর ভালো লাগে না কোনকিছু নিয়ে।
অথচ ভাবতে হবে আজ। প্রথম বিয়েতে যাই হয়ে থাক, এই কেউ-না-জানা দ্বিতীয় বিয়েটাকে টিঁকিয়ে রাখতে গেলে আজ ওকে ভেবে ভেবে বের করতেই হবে অতসীর সাথে সম্পর্কটা কেন এত বিগড়ে গেলো? ভুল কি শুধুমাত্র কিংশুকের? যদি তাই হয়, কোথায় কোথায় ভুল হলো ওর?
কিংশুক মন থেকে জানে বিয়ের পরে পরে সত্যি সত্যিই অতসীকে ভালোবেসে ফেলেছিল ও। হয়তো একান্ত নিজের মতন করে এই ভালোবাসা, যা অন্য কেউ বুঝবে না, এমনকি অতসীও নয়, তবু ভালোবাসা তো বটে।
বিয়ের পরের প্রথম অফিসিয়াল ট্যুরের কথাটাই ধরা যাক। দুদিনের জন্য একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে দিল্লি আই আই টি গিয়েছিল ও। অতসীর তখন পিরিয়ডস চলছে। কেন জানি না সেবার বেশ ব্যথায় ভুগেছিল অতসী। কিংশুকের ফেরার সময়েও পিরিয়ডস শেষ হয় নি। শোবার ঘরে খাটে শুয়েছিল অতসী, প্রায় কুকুরকুন্ডলী হয়ে, হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে। অতসীকে ওই অবস্থায় পড়ে পড়ে কাতরাতে দেখে সত্যিকারের কষ্ট পেয়েছিল কিংশুক।
এর কিছুদিন পরে পা ভেঙেছিল অতসীর। তিন দিন পরে একা একা ওর কলকাতা যাবার কথা ছিল। টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল ট্রেনের। সেজন্য ডাক্তার দেখানোতে তীব্র আপত্তি ছিল অতসীর। একটা রাত অসহায় যন্ত্রনা নিয়ে ওকে কাটাতে দেখে কিংশুকই জোর করে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।
সেবার অতসীর পায়ে প্লাস্টার ছিল পুরো এক মাস। খবর পেয়ে অতসীর মা-বাবা এই সময় একবার এসেছিলেন, তবে টিকিট পেতে দেরি হওয়ায় যখন আসেন ততদিনে প্লাস্টার পরে থাকার সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে।
ভাগ্যিস শমীক তখনও আসে নি। দুজনে মিলেই কোনোরকমে সবকিছু সামলেছিল ওরা। অফিসে সারাটা সময় তখন বাড়ির দিকে মন পড়ে থাকতো কিংশুকের, ভয়ঙ্কর টেনশন হতো অতসীর জন্য। কিংশুক বাড়িতে ঢুকলে অতসীও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতো সেই সময়টায়।
ফ্রক পরলে একদম বাচ্চা মেয়ের মতন লাগতো অতসীকে তখন।
দেখতে বাচ্চা বাচ্চা হলেও, অল্প বয়সে ভয়ঙ্কর মেজাজ ছিল অতসীর। সহ্যশক্তি কম ছিল, মা-বাবার আদরে মানুষ, তাই সংসারের যাঁতাকলে পড়ে মেজাজ ঠিক রাখতে পারতো না কারণে অকারণে। আর একবার রাগলে মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত লাভার স্রোত বেরোত। কিছুক্ষণ পরে রাগ মিটে গেলেই আবার সেই আদুরে বাচ্চা মেয়ে যেন। সেবার ডাক্তার পায়ে প্লাস্টার করে দেবার পরও চেঁচিয়ে কিংশুককে গালাগালি দিয়েছিল অতসী, অভিযোগ ছিল যে ওর কলকাতা যাওয়া পন্ড করতে এই সব করছে কিংশুক। তারপর অঝোরে কেঁদেছিল।
কিংশুক কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারতো না কোনো কিছু। সেই ছোটবেলার থেকে অপমানবোধ জিনিসটা অসম্ভব রকমের তীব্র ছিল কিংশুকের মধ্যে। মা বা বাবা কখনো বকলে সেটা ভুলতে ওর সময় লাগতো অনেকক্ষণ। স্কুলে ক্লাস ওয়ানে প্রথম যেদিন মার খেল কিংশুক, বাকি সারাটা পিরিয়ড সুটকেসে মাথা গুঁজে ছিল ও। জয়দেব স্যার কেন জানি না দেখেও সেটা দেখেন নি। দাদা বা দাদার বন্ধুদের অপমান ছোটবেলায় যে ক্ষত মনের মধ্যে তৈরী করে রেখেছে, আজ এত বছর পরেও তা ঠিক হয় নি। অতসীর খুঁচিয়ে বলা কথাগুলোও তাই ছুরির মতন বিঁধতো ওর বুকে, রক্ত ঝরে যেত ক্রমাগত। সেই সব সময়ে ছেলেবেলার মতই চুপচাপ নিজের মধ্যে আরো গুটিয়ে যেত কিংশুক। কোনদিন অতসী চিৎকার চেঁচামেচি করলে সেইদিন রাত্রে ভালো ঘুম হতো না। পরের দিন অফিসেও কাজে পুরো মন লাগতো না।
বিভিন্ন ব্যাপারে তখন ভয় পেত অতসী। আরশোলাকে ভয়, অন্ধকারে ভয়, অপরিচিত কোন জায়গায় যাবার ভয়, বাড়িতে কোনো অতিথি এলে রান্না বান্না ঠিকমতন নামাতে পারবে কিনা তাই নিয়ে ভয়। শমীকের জন্মের পর এই ভয় আবার অন্য মাত্রা পেল একটা। প্রতি পদে পদে তখন ভয় পেত অতসী শমীককে নিয়ে। শমীকের শরীর সামান্য খারাপ হলেও পাগলের মতন করত।
কিংশুকের উপরে কেন জানি না ততদিনে নির্ভরতা পুরোপুরি চলে গিয়েছিল অতসীর। কিংশুক তখন ওর জীবনের একজন শনি ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতসীর চাকরি, অতসীর স্বাধীনতা সব কিছু ধ্বংস করার জন্য তখন দায়ী কিংশুক। কিংশুক ঠান্ডা মাথায় তখন কিছু বোঝাতে গেলেও অতসী শুনতো না, ব্যঙ্গ করত কথায় কথায়, অপমানের বন্যা নামতো কিংশুকের উপরে।
অপমানিত হতে হতে এক সময় কিংশুকও বাধ্য হয়ে শুরু করলো আঘাত করা। কিংশুক ভালো করেই জানতো যে এর ফল কখনো ভালো হবে না, কিন্তু একজন কাপুরুষের মতন, নিজেকে বাঁচানোটাই তখন প্রথম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
একজন সত্যিকারের পুরুষমানুষের বুকের মধ্যে বোধ হয় বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন চব্বিশ ঘন্টা জুড়ে লোহায় গড়া একটা বর্ম থাকা চাই। যে কোন অপমানের আঘাত যেন সেই বর্মে এসে ছিটকে যায়। বিশেষ করে সেই আঘাত যদি নিকটজনের কাছ থেকে আসে।
না, অতসীর কিছু দোষ থাকলেও,কিংশুকের দোষও নেহাত কম নয়। চেহারাটা সাধারণ ভারতীয়দের তুলনায় বড়সড় হলেও কিংশুক সেদিন বোধ হয় সত্যিকারের পুরুষমানুষের মতন আচরণ করে নি। বুকের মধ্যে সেদিন লোহার কোনো বর্ম নিজের জন্য বানিয়ে নিতে পারে নি কিংশুক।
তারপর যা হয়!
ক্রমাগত আঘাত করতে করতে আর আঘাত খেতে খেতেও ক্লান্তি আসে একসময়।
ক্লান্ত হয়ে এক সময় আঘাত করাটাও বন্ধ করেছিল কিংশুক। অতসীর আঘাত কিন্তু তখনও থামে নি। অগত্যা নিজের খোলসের মধ্যেই আরো গুটিয়ে গেছে কিংশুক। সমস্যা তাতে জটিলই হয়েছে আরো।
এই অল্প কিছুদিন হল অতসীর গলাতেও যেন একটা ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করছে কিংশুক। আগের মতন চেঁচামেচি নয়, ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে সবকিছু নিজে বোঝা বা অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা যেন বেড়েছে একটু। এর বেশি আর কি-ই বা চাইতে পারে কিংশুক, অতসীর কাছে?
অতসীরই বা নতুন করে কি চাওয়ার আছে কিংশুকের কাছ থেকে?
বিয়ের পরে মা-বাবা-ভাই-কে ছেড়ে প্রায় দুহাজার মাইল দূরে এসেছিল অতসী। এসেছিল সম্পূর্ণ অচেনা একটা লোকের উপর ভরসা করে। কতটুকু ভরসা ওকে সেদিন দিতে পেরেছে কিংশুক?
একসময়ে শুধু একটা চাকরি চেয়েছিল অতসী। চেয়েছিল একটুখানি মুক্তির নিঃশ্বাস, কারুর উপর অতিরিক্ত নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে বাঁচতে। কিংশুক জানে, অতসীর ওর উপরে সব রাগের, সব অত্যাচারের আসল কারণ ওর ভিতরের ভয় আর নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে একগুচ্ছ হতাশা।
দেরি হলেও আজ সমস্ত কিছু পেয়েছে অতসী। দু হাত ভরে পেয়েছে। আজ অন্তত ভিতরের ফ্রাস্ট্রেশন থেকে নিজে জ্বলবার আর আশেপাশের অন্যান্যকে জ্বালাবার কোনো কারণ নেই ওর। একা একা নতুন শহরে নিজের মতন করে থেকে আর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ভয়ও অতসীর আগের থেকে কমে গেছে অনেক।
মজার ব্যাপার হল পাশার দান উল্টে গেছে এখন। গত দশ-বারো বছর ধরে নিজের কাজের জগৎ হতাশা ছাড়া আর কিছু দেয় নি কিংশুককে।
আর শরীরে শক্তি যত কমে আসছে ভয়ও তত যেন বাড়ছে। আজকাল সকাল-সন্ধ্যা ভয় পায় কিংশুক। মৃত্যুভয়, প্রতিবন্ধী হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার ভয়, শমীকের সাথে চিরজীবনের মতন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার ভয়, নিজের দাদুর মতন শেষ বয়সে মেন্টাল ব্যালান্স হারিয়ে ফেলার ভয়।
কিংশুকও কি তাহলে এখন জ্বলবে পুরোনো দিনের অতসীর মতন, আর ওকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে আগের মতন? কি লাভ হবে তাতে কিংশুকের?
ঠিক আছে, ফিরছে যখন ফিরতে দাও ওকে। শমীক হোস্টেলে যাবার পর থেকে একাকিত্ব জিনিসটা ঠিক কি সেটা যেন নতুন করে বুঝতে শিখেছে কিংশুক। কটাই বা কথা হত শমীকের সাথে সারাদিনে? তবু কেউ একটা তো ছিল বাড়িতে।
শমীককে প্রথমবার হোস্টেলে ছেড়ে আসার সময় অতসী ছিল সাথে। পরের দিন রাত্রে অফিস থেকে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে অসহ্য একটা কষ্ট হয়েছিল কিংশুকের।
তারপর থেকেও দেখতে দেখতে প্রায় আট বছর কেটে গেল।
না, অতসী এলে আর ঝগড়া করবে না কিংশুক। যতটা পারে মানিয়ে চলবার চেষ্টা করবে। বুকের মধ্যে সবসময় একটা বর্ম পরে থাকবে লোহার।
আর এবারে একটু ঘন ঘন কলকাতা আর বর্ধমান যাবে কিংশুক অতসীকে সাথে নিয়ে।
বিয়ের পর পর যখন তখন বাচ্চা মেয়ের মতন জেদ করত অতসী কলকাতা যাবার জন্য। একা থাকতে পারত না একদম অল্প বয়সে। তখন হাতে সময় ছিল না কিংশুকের, তবু চেষ্টা করলে আরও অনেক কিছু হয়তো অতসীকে দিতে পারত কিংশুক।
ভুল। ভুলের পরে ভুল করে গেছে কিংশুক অল্প বয়সে।
কে জানে, কিংশুক দিতে চাইলে এখন আবার অতসীর নেবার সময় থাকবে কিনা? নেবার ইচ্ছেটাও কি থাকবে?
বয়স সত্যি সত্যিই অনেক বেড়ে গেছে এর মধ্যে। বারো বছর কেটে গেল অতসী দিল্লি যাবার পর, পুরো একটা যুগ!
দ্বিতীয় শৈশব আসতে আর কতই বা বাকি কিংশুকের? একটা গড়পড়তা জীবন যদি পঁচাত্তর বছরের হয়, তাহলে দেখতে দেখতে তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কাটিয়ে ফেলেছে কিংশুক। অসংখ্য ভুল করেছে, নিজে ভুগেছে আর অন্যরাও সেইসব ভুলের মাশুল গুনেছে সাথে সাথে।
সবচেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে? একদম আগের মতই অবুঝ আর জেদি থেকে যাবে অতসী? ঝগড়া করবে গাছকোমর বেঁধে, দাঁতে দাঁত চেপে? অপমান করবে কিংশুককে পদে পদে?
না, তবু ঝগড়া আর নয়।
বেশি সমস্যা হলে অফিস থেকেই না হয় অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরবে কিংশুক, রোজ কয়েকঘন্টা চুপচাপ মেরিন ড্রাইভে বসে সমুদ্র দেখবে দরকার হলে।
বোম্বে ফিরছে তিসি। এখন অনেক সাহায্যের দরকার হতে পারে ওর কিংশুকের কাছ থেকে।
পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে অতসীকে ফোন লাগায় কিংশুক।
রিং হয়ে যায়।
সময় নেই অতসীর এখন।
২৮ আস্তে আস্তে পঞ্চাশ গজ মাটির রাস্তা পেরিয়ে বড় রাস্তার বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল রিক্সাটা।
যতক্ষণ দেখা গেল দাঁড়িয়ে রইলেন তমালবরণ।
বড় ভালো লাগল ছেলেটাকে, এতদিন পরে দেখে। শমীক … তাঁর নিজের নাতি … একমাত্র নাতি …
সুন্দর চেহারা, চমৎকার আচার-ব্যবহার, পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট -- এর বেশি আর কি চাই?
তবু কিছু যেন অজানা রয়ে গেল, মন খুঁতখুঁত করাটা তাই যায় না তমালবরণের, জানা হল না শমীক কোনোদিন বড় বটগাছ হয়ে উঠতে পারবে কিনা।
একবার যদি সেই সুযোগ পেতেন তমালবরণ, যদি আরো গভীরভাবে জানতে পারতেন ওকে, যদি ওকে তৈরি করতে পারতেন, অঘোরনাথ যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাঁকে …
সেই সুযোগটুকুই কেউ তাঁকে দিলো না।
মনকে নিজের মতন আবার বোঝাতে থাকেন তমালবরণ। সুযোগ পেলেও কি শমীক সত্যি সত্যিই তাঁর একেবারে মনের মতন হয়ে উঠতো? সুযোগ তো অঘোরনাথ-ও পেয়েছিলেন -- অখণ্ড সুযোগ, তবু নিজের ছেলেকেই কি বটগাছ বানাতে পেরেছিলেন? কেউ কি পারে? শমীককে আরো গভীরভাবে জানলে আর সেই জানাটা নিজের পছন্দ মতন না হলে কি হতো? সেটা কি আরও খারাপ হত না? নাঃ, তার চেয়ে এই ভালো।
ঘরের দিকে ফিরলেন তমালবরণ।
আজ থেকে তাঁর অখণ্ড অবসর।
জীবনের শেষ কাজ ছিল ওই স্মৃতিকথাটুকু লিখে রেখে যাওয়া। সেই কাজ আজ শেষ তো হয়ে গেছেই, আসন্ন মৃত্যুর আগে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নিজের হাতে সেটা পৌঁছে দিতে পেরেছেন। এর চেয়ে বড় আনন্দ এই সময়ে আর কি হতে পারে?
এখন থেকে রোজ সারাদিন আর কোনো কাজ নয়, শুধু বাগানে বসে থাকবেন -- যতদিন না পাকাপাকিভাবে বিছানা নিতে হচ্ছে।
বাগানে এখন রোদ পড়ে আসছে। সোয়েটার ছাড়াও একটা শাল জড়িয়ে নিলে আরাম হয়। ড্রয়িং রুমের সোফার উপর রাখা শালটা গায়ে জড়িয়ে নিতে ঘরে ঢুকলেন তমালবরণ।
সেন্টার টেবিলের উপর ওগুলো কি পড়ে? চমকে উঠলেন তমালবরণ!
তাঁর স্মৃতিকথা আর সেই অ্যালবামটা না? শিশুবাবু ওগুলো কি তাহলে নিয়ে যায় নি?
কাছে এসে দু-দুবার করে খুলে খুলে ওগুলো দেখলেন তমালবরণ। না, কোনো ভুল হয় নি। ওই দুটো জিনিস নিয়ে যায় নি শিশুবাবু!
মনটা ভীষণ, ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তমালবরণের।
চোখ ফেটে জল আসছে, অল্প অল্প ঘুরছে মাথাটাও। তাঁর এইটুকু ইচ্ছার-ও দাম দিলো না শিশুবাবু?
না, আর কোনো লাভ নেই ভেবে। এখন তিনি জানেন তিনি মরলে ও লেখার গতি হবে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে।
কি করবেন তমালবরণ? ধ্বংস করে ফেলবেন ওগুলো, নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে?
লেখাটা আর অ্যালবাম-টা বুকে চেপে ধরেন তমালবরণ। পিন্টুকে বলে দিতে হবে তিনি মরলে এ দুটো জিনিস যেন তাঁর চিতার সাথে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
*** কেন জানি না, ভীষণ অস্থির লাগছে।
রিক্সাটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাদু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র শমীকের জন্য কেউ কখনো এভাবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নি। ফ্ল্যাটবাড়িতে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখার সুযোগই বা কতটুকু?
দাঁড়িয়েই থেকেছিলেন শুধু দাদু। কোনোরকম চোখের জল এনে বা ভাবালু সব কথা বলে নিজের দুর্বলতাগুলোকে প্রশ্রয় দেন নি।
হয়তো সেজন্যই দৃশ্যটা মাথার থেকে যাচ্ছে না। নাকি যাচ্ছে না তার আসল কারণ দাদুর সাথে আর কখনো শমীকের দেখা হবে না বলে?
শুধু দাদুর সাথে দেখা হওয়াই নয়, শমীক জানে এই বাড়িতেও আর আসা হবে না শমীকের। দাদু মারা যাবার পর নিশ্চয়ই কিছুদিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাবে ওই বাড়ি। বাবার দ্বারা না হলেও, মা যদি একবার ফিল্ডে নামে তাহলে শেষ পর্যন্ত ওই বাড়ি বিক্রি করিয়েই ছাড়বে। অন্তু-সন্তু যদি শেষ পর্যন্ত বাড়িটাকে হেরিটেজ হোটেল-ও বানায়, তাহলে বাড়ি হয়তো থেকে যাবে, কিন্তু সেই বাড়িতে আসা আর হয়ে উঠবে না ওর।
এই বাড়িতে শমীক তো থাকে নি সেরকম। তাহলে হঠাৎ করে ওর এত কষ্ট হচ্ছে কেন? সে কি শুধুমাত্র ছোটবেলার আনন্দের স্মৃতিগুলোর কথা ভেবে? সেই স্মৃতিটুকুতো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না ওর কাছ থেকে! শমীকের সমস্ত যুক্তিবোধ বলছে বেশি ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না দিতে। আর ছোটবেলার সেই বাড়ি তো বদলে গেছে অনেক। যে বাড়ি শমীক দেখেছে, সেই বাড়ি নেই আর আগের মতন। তবু কেন ভিতরে ভিতরে এই পিছুটান?
শুধু এই বাড়ি নয়, বদলে গেছে আরও অনেক কিছু। বদলে গেছে বর্ধমান শহর। এই রাস্তার আশপাশ, বারো বছর আগে শেষ যেবার এসেছে শমীক, তখনও ফাঁকা ছিল। এখন চতুর্দিকে বাড়ি। বেশ কিছু বাড়ি বহুতল, একটা দুটো জায়গায় অনেকগুলো এমন বাড়ি নিয়ে শমীকদের বোম্বাইয়ের মতন কমপ্লেক্স তৈরী হয়ে গেছে এর মধ্যে। কিছু জায়গায় আবার এখনো বাড়ি বানানো হচ্ছে। মানুষ আসবে সেই সব বাড়ি শেষ হলে। শমীক বর্ধমান বলে যে ছিমছাম ঘরোয়া শহরটাকে চিনতো, সেই শহর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ভবিষ্যতে। চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে সেই শহর।
কিন্তু শহর তো শুধু ইঁট-কাঠ-সিমেন্ট দিয়ে নয়। চেনা মানুষ-ই বা কই শমীকের এই শহরে? অন্তু-সন্তু এখন দুবাইয়ে। ছোটখাট একটি প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করেই বিদেশ পাড়ি দিয়েছে ওরা। কিভাবে ওরা বিদেশে গেল সেটাও ধোয়াঁশা, কি যে করছে ওরা সেখানে সেটাও কেউ জানে না। ছোটবেলায় এত বন্ধুত্ব ছিল ওদের সাথে, অথচ এখন শমীক ইমেইল করলে তার কোনো জবাবও দেয় না ওরা। তবে এটা সবাই জানে যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ওদের এখন। শমীকের স্ট্রাইপেন্ডের তুলনায় অন্ততঃ বিশগুণ রোজগার ওদের এখনই।
রঘু, মণি, সুকান্ত, অরুণ, নির্মল, প্রদীপ, শুভ -- যাদের সাথে দাপিয়ে একসময় ফুটবল খেলেছে শমীক -- তাদের মধ্যে বেশির ভাগ নাকি এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে। পিন্টুদাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করেছে শমীক ওদের কথা জানবার জন্য। সব পিন্টুদাও জানে না। প্রদীপের বাবার বদলির চাকরি ছিল। তাই বর্ধমানে ওদের বাস যে মাত্র কয়েক বছরের জন্য হবে এটাই স্বাভাবিক। অরুণের আর শুভর খবর পিন্টুদা জানে না। রঘু ব্যাঙ্গালোরে এইটুকু শুধু জানে।
খালি মণি আর সুকান্ত-ই নাকি এখনো বর্ধমান আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল না ওদের, পড়াশুনোতেও ক্লাসের শেষদিকে থাকত ওরা। ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং তাই পড়া হয়ে ওঠে নি ওদের। মণি এখন বর্ধমানের বড় ছাত্রনেতা। আর সুকান্ত গুমটির মতন ছোট্ট একটা দোকান দিয়েছে পান-বিড়ি-সিগারেটের।
মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য তো আসা।
না, ওদের সাথে দেখা করার মানে হয় না। স্মৃতিটুকুই শুধু থাক ওদের, শমীকের মনের এক কোণে, ইতিহাস হয়ে।
এই ইতিহাস এক আজব জিনিস।
বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে ইতিহাসকে ঠিক বুঝতে পারে না শমীক।
কে জানত স্কুলে সন-তারিখ মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেওয়া ছাড়া ওর অন্য কোনো ভূমিকা থাকতে পারে শমীকের জীবনে?
এতদিন ধরে নিজের পারিবারিক অতীতকে একরকম জেনে এসেছে শমীক। এখন সব জানার পর হঠাৎ করে যেন নিজেকে অন্যরকম লাগছে। এ যেন আয়নাতে নিজের বদলে অন্য কারুর মুখ দেখা।
এত বিশাল ক্ষমতা এই ইতিহাসের?
আগে জানলে না হয় আর একটু মন দিয়ে ইতিহাসের টেক্সটবইগুলো পড়ত শমীক।
একা থাকলেই এখন মাথায় উলটোপালটা সব ভাবনা আসবে।
এত আস্তে আস্তে কেন চলছে রিক্সাটা? শমীকের এখন দরকার হাজার হাজার লোক, হইচই, হট্টগোল।এই নির্জন রাস্তা শেষ হলে তবেই যেন মুক্তি।
রিক্সাওয়ালা ছেলেটার বয়েস অল্প, শমীকের আশেপাশেই। ধৈর্য চেপে রাখতে না পেরে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল শমীক, “কতক্ষণ লাগবে ভাই বাস টার্মিনাস যেতে?”
-- আরও দশ মিনিট, বাবু।
দশ মিনিট! কি করবে শমীক এই দশ মিনিট? এই ঘেয়ো পিচ উঠে যাওয়া রাস্তায় কতগুলো গর্ত আছে গুনবে বসে বসে? কালকের প্রেজেন্টেশন-এর ড্রাফ্ট প্রিন্ট-আউটটা একবার দেখে রাখলে কেমন হয়? অনীশ স্যারকে খুশি রাখতে গেলে নিজের প্রিপারেশন জবরদস্ত রাখতে হবে সবসময়।
ব্যাগ খোলে শমীক আর খুলেই ভূত দেখার মতন চমকে ওঠে। একি! দাদুর দেওয়া অ্যালবাম-টা আর সেই স্মৃতিকথাটা গেল কই? পাগলের মতন দু মিনিট ধরে শমীক ব্যাগের সমস্ত খাঁজ, খানাখন্দ খুঁজে খুঁজে দেখে।
ছি ছি ছি! শমীক কি ওগুলো দাদুর বাড়িতেই ফেলে এল? এত দায়িত্বজ্ঞানহীন শমীক কি করে হতে পারলো?
কি করা যায় এখন? আবার ফিরে ওটা নিয়ে আসা যেতে পারে, কিন্তু তাহলে কলকাতায় হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা হয়ে যাবে। রাত্রে প্রেজেন্টেশন-এর বাকি কাজটুকু করার সময় প্রায় থাকবে না আর।
অনীশ স্যার-ও হয়তো হতাশ হবেন খুব।
কিছু করার নেই। শমীক জানে, ফিরতে হবে ওকে। না ফিরলে নিজের কাছেই বড় বেশি ছোটো হয়ে যাবে শমীক।
*** রিক্সা থেকে নেমে প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে দাদুর বাড়িতে ঢুকল শমীক।
ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেল পিন্টুদার সাথে। পিন্টুদাকে কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়েই বলল, “একটা জিনিস নিতে ভুলে গেছিলাম। দাদু কই?”
দাদু বাগানে।
দৌড়িয়ে এ-ঘর সে ঘর পার হয়ে খিড়কির দরজাটা খুলেই “দাদু” বলে চিৎকার করতে গিয়েও থমকে গেল শমীক।
ইঁদারাটার থেকে একটু দূরে বড় জামগাছটাতে একটা বড় কালো ঘুড়ি আটকে আছে। জাম গাছটার তলায় একটা ডেক চেয়ারে শমীকের দিকে পিঠ করে দাদু বসে। জামগাছের ফাঁক দিয়ে আসা লাল রঙের আলো-আঁধারি মায়ায় দাদু নিজেই যেন ছবি হয়ে গেছে।

দাদুর সামনে পুরোনো অ্যালবামটা খোলা। সামনে সেই ছবি, বুড়ো, প্রাচীন এক বটগাছের নিচে বন্দুক হাতে অঘোরনাথ দাঁড়িয়ে। আপনমনে অঘোরনাথের সাথে ফিসফিস করে কথা বলে যাচ্ছে দাদু।অজান্তেই আকাশের দিকে তাকাল শমীক। অল্প হাওয়ায় দুলছে কালো ঘুড়িটা, যেন মুক্তি পেতে চায় সমস্ত বন্ধন থেকে।
সূর্য অস্ত যেতে আর বেশি দেরি নেই।
অলংকরণ (Artwork) : রাহুল মজুমদার - পর্ব ১ | পর্ব ২ | পর্ব ৩ | পর্ব ৪ | পর্ব ৫ | পর্ব ৬ | পর্ব ৭ | পর্ব ৮ | পর্ব ৯ | পর্ব ১০ | শেষ পর্ব
- মন্তব্য জমা দিন / Make a comment
- মন্তব্য পড়ুন / Read comments
- কীভাবে লেখা পাঠাবেন তা জানতে এখানে ক্লিক করুন | "পরবাস"-এ প্রকাশিত রচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রচনাকারের/রচনাকারদের। "পরবাস"-এ বেরোনো কোনো লেখার মধ্যে দিয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা লেখকের/লেখকদের নিজস্ব। তজ্জনিত কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য "পরবাস"-এর প্রকাশক ও সম্পাদকরা দায়ী নন। | Email: parabaas@parabaas.com | Sign up for Parabaas updates | © 1997-2025 Parabaas Inc. All rights reserved. | About Us